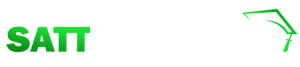সংঘবদ্ধ মানব জীবনে ব্যবস্থাপনা এক অতি অপরিহার্য বিষয় । কতিপয় ব্যক্তি যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয় তখন তাদের সঠিকভাবে পরিচালনার প্রয়োজন পড়ে। সেখানে যদি কেউ পরিচালক না থাকেন, যদি কেউ নেতৃত্ব না দেন তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক । আর এরূপ বিশৃঙ্খলা মানুষসহ সকল উপকরণের কার্যকর ব্যবহার অসম্ভব করে তোলে । তাই একদল মানুষকে তাদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেয়ার কার্যকর প্রয়াস বা শক্তিই হলো ব্যবস্থাপনা । আর যে বা যারা এ প্রয়াস চালান তাদেরকে ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, নির্বাহী, পরিচালক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় । এরূপ প্রয়াস শুধু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এরূপ প্রয়াস- প্রচেষ্টা সম্পর্কে সবারই সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ।
এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা (শিখন ফল)
১. ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
২. ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা । করতে পারবে ।
৩. ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
৪. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে
৫. ব্যবস্থাপনার আওতা সনাক্ত করতে পারবে ।
৬. ব্যবস্থাপনা চক্র বর্ণনা করতে পারবে ।
৭. ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৮. পেশা হিসেবে ব্যবস্থাপনার অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৯. ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
জনাব হক ছোট ব্যবসায় দিয়ে শুরু করে এখন অনেক বড় ব্যবসায় গড়ে তুলেছেন । এখন অনেক মানুষ তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে । কারখানায় নতুন নতুন মেশিন বসিয়েছেন । প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিটা মানুষ যাতে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে সেজন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকেন । তিনি কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও নানান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের উৎসাহ ধরে রাখতে চেষ্টা করেন । প্রতিটা কাজ আগেই ঠিক করে সবাইকে বুঝিয়ে দেন । কাজের খোঁজ-খবর রাখেন ও ভুল হলে তা শুধরে দেন। এরপরও কাজে সমস্যা হলে তা সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করেন । তার এই চেষ্টা-প্রচেষ্টাই তাকে সফলতা দিয়েছে । তিনি একজন সফল ব্যবস্থাপক । এক্ষেত্রে লক্ষ্যার্জনে গৃহীত জনাব হকের সকল কর্মপ্রয়াস ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত ।
ব্যবস্থাপনা শব্দটি ইংরেজি 'Management' শব্দের প্রতিশব্দ । ইংরেজি 'Management' শব্দটির সমার্থক শব্দ গণ্য করা হয় ‘to handle'- অর্থাৎ চালনা করা বা পরিচালনা । ইংরেজি এ শব্দটি অধিকাংশের মতে ল্যাটিন বা ইতালীয় ‘Maneggiare' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো 'to trained up the horses'-অর্থাৎ অশ্বকে প্রশিক্ষিত করে তোলা বা পরিচালনার উপযোগী করে তোলা । যা কালের বিবর্তনে মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তার নিকট থেকে কাজ আদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে ।
সহজ অর্থে, প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য এতে নিয়োজিত উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহারের সকল প্রয়াস- প্রচেষ্টাকে ব্যবস্থাপনা বলে। এরূপ প্রয়াস-প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ব্যবস্থাপক বলা হয়ে থাকে । সঠিকভাবে সবকিছু চালাতে পারার উপরই উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার ও লক্ষ্যার্জন নির্ভর করে। একটা প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের উপকরণ থাকে; মানবীয় ও বস্তুগত । মানবীয় উপকরণ বলতে মানুষ বা জনশক্তিকে বুঝায়। আর বস্তুগত উপকরণ বলতে যন্ত্রপাতি, মালামাল, অর্থ, বাজার ও পদ্ধতিকে বুঝানো হয়ে থাকে এদেরকে সংক্ষেপে 6'M (Men, Machine, Materials, Money, Market ও Method) বলে। এ সকল উপকরণের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হলেই একটা প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্খিত ফললাভ করতে পারে । তাই এদের কার্যকর ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রয়াস চালান। যাকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ প্রক্রিয়ার সাথে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পৃক্ত । তাই প্রকৃত অর্থে, উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার করে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়ে থাকে । নিম্নে এ সংক্রান্ত একটা ধারণা চিত্র প্রদত্ত হলো:
কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করতে হলে তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা আবশ্যক । কারণ প্রকৃতি হলো কোনো বিষয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General character)। অন্যদিকে বৈশিষ্ট্য হলো বিশেষভাবে নজরে পড়ে স্বতন্ত্রধর্মী এমন কিছু (Something especially noticeable)। পুরুষ ও নারী উভয়ই মানুষ । কিন্তু তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে দৃশ্যমান ভিন্নতা রয়েছে । কামাল ও কবীর দু'জন বন্ধু । দেখা যাবে তাদের চেহারা, গঠন, আচরণ ইত্যাদিতে পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । এভাবেই একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ভিন্নতা সহজেই নজরে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও পার্থক্য দৃশ্যমান । প্রতিটা কাজও এক ধরনের নয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক-এভাবে প্রত্যেকের কাজের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা রয়েছে । তাই ব্যবস্থাপনাকে বুঝতে হলে এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন । নিম্নে এরূপ কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:
১. প্রক্রিয়া বা কাজের সমাহার (Process or group of activities): পরস্পর নির্ভরশীল ধারাবাহিক কাজের সমষ্টিকে প্রক্রিয়া বলে। সেই বিচারে ব্যবস্থাপনাও একটি প্রক্রিয়া। কারণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাদি পরস্পর সম্পর্ক রেখে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয় । এর একটি কাজে সমস্যা হলে তা অন্য কাজকে সমস্যাগ্রস্ত করে । ফলে লক্ষ্যার্জন ব্যাহত হয় ।
২. সামাজিক প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম (Social process or activities): ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া । এরূপ প্রক্রিয়া বলতে ধারবাহিক কার্যসমষ্টির সাথে সমাজের বা সমাজ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পৃক্ততাকে বুঝায় । সেই সাথে এরূপ কাজের সামাজিক উদ্দেশ্যও ক্রিয়াশীল থাকা অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনা মানুষকে সংঘবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা তার কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করে থাকে ।
৩. লক্ষ্য অর্জনের উপায় (Means of achieving goals) : কোনো কাজের মূলে যে প্রত্যাশা থাকে তাকে লক্ষ্য বলে । যেকোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মূলে একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে । আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন । তাই ব্যবসায় বা এর ব্যবস্থাপনা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ কারণেই বিভিন্ন লেখক ব্যবস্থাপনাকে লক্ষ্যার্জনের উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন ।
৪. কাজ আদায়ের কৌশল (Technique of getting work): প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপায়-উপকরণের কার্যকর ব্যবহারের প্রতি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বারোপ করে । আর এজন্য ব্যবস্থাপনা সব সময়ই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির কাছ থেকে যথাযথ কাজ আদায়ে সচেষ্ট থাকে । এ লক্ষ্যেই পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান ইত্যাদি কাজ পরিচালিত হয় । এ জন্যই Rue & Byars বলেছেন, "Management is getting things done through others." অর্থাৎ অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার কৌশলই হলো ব্যবস্থাপনা ।
৫. অর্থনৈতিক সম্পদ (Economic resources): উৎপাদনের কাজে লাগে এমন কিছুকেই সম্পদ বলে। ব্যবস্থাপনা একটি মূল্যবান অর্থনৈতিক সম্পদ । সকল উপায়-উপকরণ কাম্য মানে থাকার পরও ব্যবস্থাপনা নামক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বা অদক্ষতার কারণে লক্ষ্যার্জন সম্ভব হয় না । একই সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় তার মুখ্য কারণ ব্যবস্থাপনার মানগত পার্থক্য । অনুন্নত - দেশসমূহে ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা কার্যত নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায় ।
৬. জ্ঞানের পৃথক শাখা (Separate branch of knowledge): জ্ঞানের পৃথক শাখা হিসেবে ব্যবস্থাপনা আজ সর্বত্রই স্বীকৃত । বৃহদায়তন প্রাতিষ্ঠানিক জগতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ছাড়া দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা অসম্ভব । বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা আজ সংঘবদ্ধ জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ।
৭. সর্বজনীনতা (Universality): সর্বজনীনতা বলতে সর্বত্রই এর প্রয়োগযোগ্যতা বা উপযোগিতা থাকাকে বুঝায় । ব্যবস্থাপনা এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যা যে কোনো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন, ‘ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন' অর্থাৎ দলবদ্ধ যেকোনো প্রচেষ্টায় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য । পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত যে কোনো সংঘবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টায় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় ।
সহজ অর্থে ব্যবস্থাপনা হলো অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার কৌশল । তাই মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হয়েছে, পেশা অবলম্বন করেছে, কাজ সম্পাদনে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করেছে তখন হতেই ব্যবস্থাপনা বিষয় ও এর চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তন শুরু হয়েছে । সমাজ যতই এগিয়েছে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রও ততই গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। নিম্নে ব্যবস্থাপনা তথা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরা হলো :
ক) প্রাচীন যুগ (৫০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টের মৃত্যুর পূর্ব সময় পর্যন্ত) (Ancient period) : প্রাচীন যুগে সমাজ উন্নয়নের ধারা ছিল খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। এ সময় বিভিন্ন সভ্যতাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন লক্ষ করা যায় । এই সভ্যতাকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র ও এর প্রয়োগে উন্নতি লাভ ঘটে। এর মধ্যে মিসরীয়, ব্যবিলনীয়, হিব্রু, চৈনিক, রোমান, গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা উল্লেখযোগ্য ।
খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দ হতে ৫২৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ের কীর্তিসমূহ সর্ব প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ব্যবস্থাপকীয় ও সাংগঠনিক কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে । এ সময়ের প্রাপ্ত কিছু উপদেশনামা হতে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উপাদান লক্ষ করা যায় । ব্যবিলনীয় সভ্যতায় ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নয়নে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। The Code of Hummurabi এর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। হিব্রু সভ্যতায় হযরত মূসা (আ:)-এর ভূমিকা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখে । আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনা ও মানব সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে ব্যবস্থাপক হিসেবে তাঁর অবদান লক্ষণীয় চৈনিক সভ্যতায় ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নতিতে লাও-জু (Lau-Tzu)-এর অবদান লক্ষ করা যায় । তিনি কার্যপদ্ধতি উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেন । তিনি মনে করতেন, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতাবোধ অভ্যাস করার মাধ্যমেই যথাযোগ্য চিন্তাধারা ও কর্ম পরিবেশ গড়ে উঠে । প্রাচীন চীনের প্রশাসনে বিশেষজ্ঞ কর্মী পরামর্শ (Staff advice) এর ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায় ।
ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিকাশে গ্রীক সভ্যতার বিশেষ অবদান রয়েছে । এ সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে । বিশেষায়ণ ও শ্রম বিভাগের ব্যাপক প্রচলনও এ সময়ে লক্ষ করা যায় । দার্শনিক প্লেটো একজন ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী একটি কাজ অর্পণ করার কথা বলেছেন। এ সভ্যতায় 'সর্বোত্তম পদ্ধতি' উদ্ভাবন ও ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। দার্শনিক সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন, ব্যবস্থাপনা একটি সর্বজনীন বিষয় এবং এটি একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক কাজ । তিনি তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে সর্বপ্রথম এ বিষয়টি তুলে ধরেন ।
খ) মধ্যযুগ (০০-১৭৫০) (Middle stage) : মধ্যযুগে বিশ্বব্যাপী সামন্তবাদের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়। এ সময়ে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। ফলে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নের হারও উল্লেখযোগ্য ছিল না। নয়শত খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনো লেখা পাওয়া যায় না । তবে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর আমলে শাসন ব্যবস্থা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয় তা বিভিন্ন বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। মধ্যযুগে যাঁরা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখেন তাদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:
১. আল ফারাবি : ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আল ফারাবি লিখিতভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন । তিনি তাঁর লেখনীতে নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ এবং পরিত্যাজ্য দোষসমূহ তুলে ধরেন ।
২. ইমাম গাজ্জালি : ১১০০ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালি (রঃ) 'নাসিহাত আল মুলক' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানেও শাসকশ্রেণির প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাজার আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তার মৃত্যুর পর রাজা-প্রজা সবাই তাকে হারানোর বেদনা অনুভব করে ।
৩. লুকা প্যাসিওলি : ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে লুকা প্যাসিওলি দু-তরফা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন । ইটালিতে এরূপ হিসাব পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ঘটে। যা হিসাব ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয় । এজন্য তাঁকে হিসাববিজ্ঞানে 'দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতির জনক' বলা হয়ে থাকে । এ সময়ে ইটালিতে অংশীদারি ও যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের প্রচলন লক্ষ করা যায় ।
8. থমাস মুর : মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নয়নে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে থমাস মুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি মনে করতেন, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় রোধ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব । এতে বিশেষায়ণ এবং মানবশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় ।
গ) শিল্প বিপ্লব কাল (১৭৫০-১৮৫০) (Industrial revolution period) : শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে । সর্বপ্রথম বৃটেনে এবং পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘটে যাওয়া এ বিপ্লবকালে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :
১. জেম্স স্টিউয়ার্ট : ১৭৬৭ সালে স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদান করা হয় এবং শিল্পোৎপাদনে যন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরা হয় ।
২. এ্যাডাম স্মিথ : ১৭৭২ সালে অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক এ্যাডাম স্মিথের ‘ওয়েলথ অব নেশন' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । এতে তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন । এ গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার বহুবিধ সমস্যা ও ধারণা তুলে ধরা হয় ।
৩. জেম্স ওয়াট ও ম্যাথে বোল্টন : জেম্স ওয়াটকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে। এ দুই বিজ্ঞ উদ্ভাবক মিলে স্টীম ইঞ্জিন তৈরির জন্য 'বোল্টন ওয়াট এন্ড সন্স' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন । ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এর সহযোগী সোহো ইঞ্জিনিয়ারিং ফাউন্ড্রিতে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ করা হয় ও যন্ত্রপাতি বিন্যাস এবং দ্রব্যের মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে। প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।
৪. রবার্ট ওয়েন : তিনি ১৮০০-১৮২৮ সাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন বস্ত্রশিল্পে ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব। পালন করেন । শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য তাঁকে 'আধুনিক শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, অন্যান্য সম্পদের ওপর বিনিয়োগের তুলনায় মানব শক্তি খাতে বিনিয়োগ কয়েকগুণ লাভজনক ।
৫. চার্লস ব্যাবেজ : তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক । কম্পিউটার যন্ত্রের আবিষ্কার তাঁর মহান কীর্তি। তিনি তাঁর গ্রন্থে সর্বপ্রথম জোর দিয়ে প্রমাণ করেন যে, একটি সফল ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গণিত শাস্ত্রের প্রয়োগে তিনি অবদান রেখেছেন। তাঁকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়ে থাকে ।
ঘ) শিল্প বিপ্লব-পরবর্তী যুগ (১৮৫০-১৯৫০) (Post industrial revolution period) : এ সময়ে যে সকল মনীষী ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তার মধ্যে এফ. ডব্লিউ, টেলর, হেনরি ফেয়ল, এইচ. এল. গ্যান্ট, গিলব্রেথ দম্পতি, ওলিভার শেলডন, এলটন মেয়ো (মানর সম্পর্ক মতবাদের জনক), চেস্টার আই. বার্নার্ড (পদ্ধতি বা সিস্টেম মতবাদের জনক) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে ব্যবস্থাপনা নীতি ও তত্ত্বের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একটি ব্যবস্থাপনা মতবাদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে । এ সময়ের দু'জন নামকরা মনীষী সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:
১. এফ. ডব্লিউ, টেলর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নেয়া এ অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক । তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে (১৮৭০-১৯১৫) সাধারণ শিক্ষানবিস শ্রমিক থেকে বড় কারখানার শীর্ষপদ দখল করেছিলেন। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের ঘাটতি থাকায় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহারের জন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন করেন। এতে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায় ও পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।
২. হেনরি ফেয়ল : তুরস্কে জন্মগ্রহণকারী ও ফ্রান্সের অধিবাসী এ মহান ব্যক্তি ১৮৬০-১৯১৮ সাল পর্যন্ত একজন খনি প্রকৌশলী হিসেবে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন । তিনি মনে করতেন, ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ শুধু কারবারি প্রতিষ্ঠানেই নয় সকল ধরনের সংগঠনেই প্রয়োগযোগ্য এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি । তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ব্যবস্থাপনা রীতি-পদ্ধতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। তিনি কার্য বিভাগীয়করণেরও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ১৪টি মূলনীতির নির্দেশ করেন। যা অদ্যাবধি সর্বজনগ্রাহ্য মূলনীতি হিসেবে অনুসৃত হয়। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্যই তাঁকে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বীয় ধারার অগ্রদূত ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক' বলা হয়ে থাকে ।
ঙ) আধুনিক যুগ (Modern stage) : শিল্প বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থাপকীয় তত্ত্ব ও এর প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে পরবর্তী সময়েও তা অব্যাহত রয়েছে । এ সময়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও আচরণ বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার দ্বারা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে । এর মধ্যে ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, হার্জবার্গ, পিটার এফ. ড্রাকার, উইলিয়াম ও'চি প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ই. এফ. এল. ব্রেক, নিউম্যান, কুঞ্জ ও ডোনাল, আরনেস্ট ডেল, ট্রিওয়াথা ও নিউপোর্ট প্রমুখ মনীষীদের লেখনী আধুনিক ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারাকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে সহায়তা করেছে । Z তত্ত্বের প্রবর্তক উইলিয়াম ও'চি-এর নাম আধুনিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত স্মরণীয় ।
যে কোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। এটি এমন এক শক্তি যা প্রতিষ্ঠানের সকল উপায়-উপকরণকে কার্যকরভাবে সংগঠিত ও লক্ষ্যপানে পরিচালিত করে। ব্যবস্থাপনাকার্য দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে পরিচালিত হলে তা যেমনি প্রতিষ্ঠানকে সফলতা দান করে তেমনি ব্যবস্থাপনা কার্যে অদক্ষতা প্রদর্শিত হলে উপায়-উপকরণ যত উন্নত হোক না কেন তা কোনো কার্যকর ফল দিতে পারে না । পাশাপাশি দু'টি হাসপাতাল । একই পরিমাণ মূলধন ও ভৌত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রতিষ্ঠান দু'টি যাত্রা শুরু করেছিল। একটা এগিয়ে যাচ্ছে ও অন্যটা পিছিয়ে পড়ছে। পার্থক্যের কারণ খুঁজলে দেখা যাবে একটার ব্যবস্থাপনা অন্যটির চেয়ে উত্তম । একই এলাকায় একাধিক কলেজ রয়েছে । দেখা যাবে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা কোনো কলেজে ভিড় জমাচ্ছে । কারণ ঐ কলেজটির ব্যবস্থাপনা অন্যটির চেয়ে ভালো । এভাবেই প্রতিটা পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রসহ সর্বত্রই সঠিক পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:
১. উপকরণাদির সুষ্ঠু ব্যবহার (Proper utilization of resources) : উপকরণ বলতে কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহার্য বস্তকে বুঝায় । তাই উৎপাদনের কাজে লাগে এমন প্রয়োজনীয় বস্তুকে উৎপাদনের উপকরণ বলে । ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণ কোথাও থাকাই উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয় । এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের জন্য যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাই ব্যবস্থাপনা । Terry ও Franklin বলেছেন, “ব্যবস্থাপনা হলো সেই ধরনের কাজ যা অসংগঠিত মানুষ ও বস্তুগত সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য ও ফলদায়ক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।” একজন ভালো কৃষক ভূমি, শ্রম, মূলধন, ট্রাক্টর, সেচযন্ত্র, সার, বীজ ইত্যাদির কার্যকর ব্যবহার করে অধিক ফসল ফলিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করে । একজন শিল্পমালিক তার জনশক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, অর্থ, বাজার, পদ্ধতি ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার করে শিল্পকে এগিয়ে নেয়। একজন সফল রাষ্ট্রপ্রধান যোগ্য নেতৃত্বদানের মাধ্যমে সবার মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে গতিশীলতা এনে দেশের সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগায় । তাই উপকরণের কার্যকর ব্যবহারে যোগ্য ব্যবস্থাপনার বা ব্যবস্থাপকের বিকল্প নেই।
২. দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase of efficiency) : দক্ষতা হলো কম খরচ (Input) এ বেশি কাজ বা ফল (Output) লাভের সামর্থ্য। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারাও দক্ষতা হিসেবে গণ্য। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কারণ উত্তম ব্যবস্থাপনার অধীনে এর প্রতিটা জনশক্তির দক্ষতা বাড়ে। ফলে বস্তুগত উপকরণ; যেমন- যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদির দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি একই ধরনের ও মানের দু'টি প্রতিষ্ঠান। একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা একই সময়ে যে পরিমাণ উৎপাদন করে অন্য প্রতিষ্ঠানে তার চেয়ে কম উৎপাদন হয় । এতে প্রথম প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় ভালো করবে । সেখানে অপচয় হ্রাস পাবে এবং মুনাফার পরিমাণ বাড়বে । অন্যদিকে পরের প্রতিষ্ঠানটিতে পূর্ববৎ অবস্থা চলতে থাকলে একদিন প্রতিযোগিতার বাজারে তা পিছিয়ে পড়বে । তাই একটা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনার ভাল-মন্দের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ।
৩. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা (Establishment of discipline) : শৃঙ্খলা বলতে রীতি, নিয়ম, নীতি, সুব্যবস্থা ইত্যাদিকে বুঝায় । একটা প্রতিষ্ঠানে যদি এগুলো না থাকে তবে ঐ প্রতিষ্ঠান কখনই ভালো চলতে পারে না। একটা পরিবারের কথাই ধরা যাক, যেখানে যদি কোনো নিয়ম-রীতি না থাকে, যে যার মতো চলে, কোনো মান্যতা ও ভব্যতা না থাকে তবে শান্তি ও উন্নতি সেখানে আশা করা যায় না । একটা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই এ বিষয়টি প্রযোজ্য । একটা প্রতিষ্ঠানে এই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থাকে মূলত পরিচালক বা ব্যবস্থাপকগণের ওপর । তারা যদি তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন তবে ঐ প্রতিষ্ঠান ভালো চলতে পারে না । আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা লক্ষণীয় এর পিছনে মূল কারণ হলো ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের অদক্ষতা ।
৪. উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা (Establishment of cordial relationship) : একটা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ; যেমন- মালিক, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক-কর্মী, ক্রেতা ও ভোক্তা, সরবরাহকারী ইত্যাদি সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা বর্তমানকালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । একটা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যবস্থাপনাই শুধুমাত্র তা নিশ্চিত করতে পারে । একটা পরিবারে বাবা-মার মধ্যে যদি উত্তম সম্পর্ক না থাকে তবে ঐ পরিবারে অশান্তির শেষ থাকে না । সন্তানদের মধ্যেও অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা জন্ম নেয় । একটা প্রতিষ্ঠানেও এ কথা সর্বোতভাবে প্রযোজ্য । মালিক বা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব থাকে, গ্রুপিং-লবিং যদি নিত্যকার বিষয় হয় তবে নিচের স্তরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মীরা তার দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়ে থাকে । এতে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও কর্মমুখী পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । একটা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যবস্থাপনাই শুধু সর্বস্তরে উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে সে অবস্থা থেকে প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষাদান ও সামনে এগিয়ে নিতে পারে ।
৫. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creation of employment opportunity) : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বলতে মানুষকে কাজে লাগানোর মতো নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টিকে বুঝায় । উত্তম ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নই নিশ্চিত করে না ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন ব্যবসায় গঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে স্কয়ার গ্রুপ, আকিজ গ্রুপ, প্রাণ গ্রুপসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে- তা তাদের ব্যবস্থাপনার দক্ষতার কারণেই সম্ভব হয়েছে । বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীগণের অনেকেই তাদের ব্যবস্থাপনার দক্ষতার কারণে নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নতুন নতুন কারখানা গড়ে হাজারো শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছেন । এতে দেশে যেমনি বেকার সমস্যার লাঘব হচ্ছে সেই সাথে মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ ও সমাজ উপকৃত হচ্ছে ।
ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পাদনে প্রয়োজনে লাগে এমন বস্তু বা সম্পদকেই ব্যবস্থাপনার উপকরণ বলে । ব্যবস্থাপনা হলো উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কৌশল বা প্রক্রিয়া । যার সাথে পরিকল্পনা সংগঠনসহ অন্যান্য কাজ সম্পৃক্ত । এরূপ উপকরণের মধ্যে মানবীয় ও বস্তুগত বিভিন্ন উপকরণ অন্তর্ভুক্ত। Terry ও Franklin তাকে 6'M' নামে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন । নিম্নে এরূপ উপকরণসমূহ আলোচনা করা হলো:
১. মানুষ (Men): মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব। স্রষ্টা সৃষ্টির সকল বস্তুগত উপকরণকে মানুষের জন্য কল্যাণকর করে সৃষ্টি করেছেন। যা মানুষ উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহার করে। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এই মানব সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে বা তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থাপক চেষ্টা চালায় । মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হলে আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অন্যান্য বস্তুগত উপকরণের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হয় ।
২. মালামাল (Materials): মালামাল বলতে উৎপাদন বা বিক্রয় কার্যে অথবা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার্য কাঁচামাল বা প্রস্তুত পণ্যকে বুঝায় । যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন বা তা সংগ্রহ করে বাজারজাত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে । সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা বিক্রয় করলেও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানান ধরনের মালামাল বা সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার করে । এরূপ মালামাল মানসম্মত না হলে মানবীয় প্রচেষ্টা ফলপ্রদ করা সম্ভব হয় না।
৩. যন্ত্রপাতি (Machines): প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের হাতিয়ারকে যন্ত্রপাতি বলে । ব্যবস্থাপনার মৌল উপকরণের মধ্যে যন্ত্রপাতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত মানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা না গেলে তা থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের পণ্য বা সেবা উৎপাদন সম্ভব হয় না । এ জন্য বর্তমানকালে প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা চালায় ।
৪. অর্থ (Money): অর্থ বলতে ধন, সম্পত্তি বা বিত্তকে বুঝায় । অর্থনীতির ভাষায় বিনিময়ের মাধ্যমকে অর্থ বলে । সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যুকৃত বিহিত মুদ্রাকে অর্থ বলা হয়। যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান হলো এই অর্থ । অর্থ বা পুঁজি ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানই কার্যত গঠন ও পরিচালনা করা যায় না । প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে সংগ্রহ, অর্থের কার্যকর ব্যবহার, এর যথাযথ পরিচালনা- এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় ।
৫. বাজার (Market): বাজার হলো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকায় কোনো পণ্য বা সেবার বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চাহিদার সমষ্টি । যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানকালে এই বাজার বা চাহিদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে গণ্য। ব্যবসায় গঠনে একজন দক্ষ উদ্যোক্তা সহজেই পুঁজি এবং স্বয়ংক্রিয় ও উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে বাজার সৃষ্টি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বাজার না থাকলে বা বাজার সৃষ্টি করা না গেলে কোনো ব্যবসায়ই সফলতা লাভ করতে পারে না । সৃষ্ট বাজার ধরে রাখাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ।
৬. পদ্ধতি (Method): কার্য সম্পাদনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে পদ্ধতি বলে । কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতিও ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপকরণ। যেকোনো প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘদিনের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে প্রতিটা কাজের সুবিধাজনক উপায় বা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে । কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সময়ের সাশ্রয় ঘটে এবং দ্রুত কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় । একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো চলার পিছনে উত্তম পরীক্ষা ও ক্লাস অনুষ্ঠান পদ্ধতির অবদান আমরা সহজেই লক্ষ করতে পারি ।
প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহারের প্রয়াস বা প্রক্রিয়াকেই ব্যবস্থাপনা বলে । প্রক্রিয়া বলতে পরস্পর নির্ভরশীল ধারাবাহিক কাজের সমষ্টিকে বুঝায় । যার প্রতিটা কাজ প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ ফল দিতে পারে না । একইভাবে কাজগুলো ধারবাহিকভাবে সম্পাদিত না হলে তাথেকেও কার্যকর ফললাভ অসম্ভব । যদি আমরা চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার কথা ধরি- তা হলে দেখা যাবে এর কাজগুলো ধারাবাহিক ও পরস্পর নির্ভরশীল নিম্নে সংক্ষেপে তা দেখানো হলো :
উল্লেখ্য এই প্রক্রিয়ার প্রতিটা ধাপ সুচারুভাবে সম্পাদিত হলেই সম্পূর্ণ চিনি পাওয়া সম্ভব । এর কোনো কাজে বিচ্যুতি ঘটলে প্রকৃত ফল অর্থাৎ সম্পূর্ণ চিনি পাওয়া সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে প্রতিটা কাজ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল এবং তা ধারাবাহিকতা মেনে সম্পন্ন হয়। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াতেও এমন কতকগুলো কাজ আমরা দেখতে পাই যা পরস্পর নির্ভরশীল ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সম্পন্ন হয়ে থাকে । প্রক্রিয়ার কাজগুলো নিমে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :
ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ ব্যবস্থাপনার এ কাজ বা কর্ম প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন । তার কতিপয় ছকের সাহায্যে নিম্নে তুলে ধরা হলো :
| বিশেষজ্ঞের নাম | ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি |
| ১. হেনরি ফেয়ল | পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশদান, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ । |
| ২. অইরিক ও কুঞ্জ | পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ । |
| ৩. এল. গুলিক | পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন, রিপোর্ট প্রদান ও বাজেট প্রণয়ন। (সংক্ষেপে-POSDCORB : P= Planning; O = Organizing; S = Staffing; D = Directing; Co = Co-ordinating; R = Reporting; B = Budgeting.) |
| ৪. আরনেস্ট ডেল | পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ, উদ্ভাবন ও উপস্থাপন । |
| ৫. হিস ও গুলেট | সৃষ্টিকরণ, পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রেষণা, যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ । |
ছকে উল্লেখ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রধান কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :
১. পরিকল্পনা (Planning): ভবিষ্যতে কী করা হবে তা আগাম ঠিক করাকেই পরিকল্পনা বলে । ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ হলো পরিকল্পনা । এটি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের ভিত্তিস্বরূপ । পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ ধারাবাহিকতা মেনে সম্পন্ন হয় । তাই পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যবস্থাপকগণকে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন পড়ে । শুধু কী করা হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই পরিকল্পনা হিসেবে না দেখে কখন ও কোথায় করা হবে, কত সময়ের মধ্যে করতে হবে, কে বা কারা তা সম্পাদন করবে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে। তবেই তা একটা আদর্শ পরিকল্পনা বিবেচিত হয় । ধরা যাক, কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে । অধ্যক্ষ স্যার একটা কমিটি করে দিলেন । কমিটিকে এক্ষেত্রে বনভোজনের তারিখ, স্থান, যাওয়ার উপায়, খাবারের মেন্যু, চাঁদার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রিম . সিদ্ধান্ত নিতে হবে । এর সবটাই পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য ।
২. সংগঠন (Organizing) : গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপকরণাদিকে সংগঠিত ও কাজে লাগানোর উপযোগী করাকেই সংগঠন বলে। ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি যখন আলাদা থাকে তখন তা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না । এই উপকরণগুলোকে যখন একত্রিত করে নির্মাণের কাজে লাগানো হয় তখন তা
থেকে বিল্ডিং, সেতু ইত্যাদি নির্মিত হয় । মানুষগুলো যখন আলাদা-আলাদা থাকে তখন তাদের দ্বারাও কিছু সৃষ্টি হয় না । কিন্তু যখন কাজ ভাগ করে তা মানুষগুলোকে বুঝিয়ে দেয়া হয়, দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, একের সাথে অন্যের সম্পর্ক বলে দেয়া হয় তখন এই মানুষগুলো একটা সংগঠনে রূপায়িত ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে । তাই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজকে বিভাজন, প্রতিটা কাজের জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দিষ্টকরণ এবং সে অনুযায়ী
উপায়-উপকরণকে সংহত করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার কাজকে সংগঠন বলা হয়ে থাকে ।
৩. কর্মীসংস্থান (Staffing) : প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য ও দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ ও উন্নয়নের কাজকেই কর্মীসংস্থান বলে । সংগঠন প্রক্রিয়ায় কাজ এবং প্রতিটা কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণের পর ঐ কাজ সম্পাদনের জন্য যোগ্য জনবল সংস্থানের প্রয়োজন পড়ে । এই জনবলের যোগ্যতা, আগ্রহ ও আন্তরিকতার ওপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। তাই কর্মী নিয়োগে ভুল করলে প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদে তার কুফল ভোগ করতে হয়। ধরা যাক, কলেজের গেটের জন্য যোগ্য নিরাপত্তা রক্ষীর প্রয়োজন । এক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মীর উচ্চতা, বয়স, বুকের মাপ, সুস্থতা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, সাহস ইত্যাদি বিষয় দেখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যদি দুর্বল ও রোগগ্রস্ত লোক নিয়োগ দেয়া হয় তবে তার নিকট থেকে উপযুক্ত সার্ভিস কখনই প্রত্যাশা করা উচিত নয় । তাই কোথায়, কোন মানের, কি সংখ্যক লোকের প্রয়োজন সে অনুযায়ী যোগ্য কর্মী নিয়োগ করতে হয় ।
৪. নেতৃত্ব / নেতৃত্বদান (Leading) : কোনো দল বা গোষ্ঠীর আচরণ ও কাজকে লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেয়ার কৌশলকেই নেতৃত্ব বলে । যিনি বা যারা এরূপ প্রয়াস চালান তাকে বা তাদেরকে নেতা বলা হয়ে থাকে । নেতৃত্ব দানের বিষয়টি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ । প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য আদেশ দেয়া, পরিচালনা করা, প্রভাবিত করা, উৎসাহিত করা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত করা, দলগত প্রচেষ্টা জোরদার করা ইত্যাদি বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত । তাই ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা, প্রেষণা ও সমন্বয় কাজ নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হয় । সেজন্য আমেরিকান বইগুলোতে ব্যবস্থাপনার কাজ উল্লেখ করতে যেয়ে পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ- এভাবে কাজের পরম্পরা উল্লেখ করা হয়ে থাকে । অবশ্য এখন অনেকেই পরিকল্পনা সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ— এ পাঁচটি কাজকে ব্যবস্থাপনার কাজ হিসেবে গণ্য করেন। নিম্নে নেতৃত্বের আওতাধীন ব্যবস্থাপনার কাজসমূহ উল্লেখ করা হলো :
ক. নির্দেশনা (Directing) : অধস্তন জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান, তত্ত্বাবধান, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান এবং অনুসরণ (Follow-up) কার্যকে নির্দেশনা বলে। যোগ্য জনবল কোথাও থাকলেই তারা কাজ করবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না । কী কাজ করবে এ বিষয়ে সময়ে সময়ে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করতে হয় । তারা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না বা করতে পারছে কি না তা তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণ (Follow) করতে হয় । একটা কারখানায় সপ্তাহে ১০০ একক পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা নেয়া হলো । এখন যদি এক সপ্তাহ পর খোঁজ-খবর নেয়া হয় কাজ কী হয়েছে? তবে দেখা যাবে কাজ পুরোটা হয়নি। অধস্তনরা নানান সমস্যার কথা বলবে, কারণ দর্শাবে। এক্ষেত্রে যদি উর্ধ্বতন প্রতিদিনের কাজের খোজ-খবর নিতেন, সমস্যা দেখা দিলে সেভাবে পরামর্শ বা নির্দেশনা দিতেন, পুরো সপ্তাহের কাজ সেভাবে দেখা হতো তবে কার্যফল আরও আশাব্যঞ্জক হতে পারতো ।
খ. প্রেষণা (Motivation): অধস্তন কর্মীদের কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত করার কাজকে প্রেষণা বলে । কর্মীদের কোনো কাজ করতে বললেই তারা সবসময় আন্তরিকতা নিয়ে সম্পাদন করবে এটা আশা করা যায় না। যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য বস্তুগত উপকরণের সাথে জনশক্তির এখানেই বড় পার্থক্য বিরাজমান । জনশক্তি যদি কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয় তবে তাদের যতই আদেশ-নির্দেশ প্রদান করা হোক, তত্ত্বাবধান করা হোক তা কখনই কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না। ভীতি প্রদর্শন বা কাজে চাপ সৃষ্টি করলে স্বল্প সময়ের জন্য কখনও কিছুটা ভাল ফল লক্ষ করা গেলেও বাস্তবে তা কার্যকর নয়। তাই ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে কর্মীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে কাজ আদায় এবং প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখার কাজ বর্তমানকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য আর্থিক ও অনার্থিক বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে ।
গ. সমন্বয়সাধন (Coordination) : বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের কাজকে একসূত্রে গ্রথিত ও সংযুক্ত করার কাজকে সমন্বয় বলে । একটা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগ কাজ করে । প্রতিটা ব্যক্তি ও বিভাগ যদি নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে, অন্যের সাথে নিজের কাজের সমন্বয় বা সংযুক্তির বিষয়টি না ভাবে তবে দেখা যাবে এক পর্যায়ে সামগ্রিক কাজে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তাই সম্মিলিত যে কোন কাজে সকল ব্যক্তি ও বিভাগকে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য অর্জন বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজন পড়ে। এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব উর্ধ্বতন নেতৃত্বের । উৎপাদন বিভাগ যদি ইচ্ছামতো উৎপাদন করে এবং বিক্রয় বিভাগ তার সাথে তাল মিলিয়ে বিক্রয় করতে ব্যর্থ হয় তবে এক পর্যায়ে মজুত পণ্য অবিক্রিত থাকবে এবং তা সকল ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করবে ।
৫. নিয়ন্ত্রণ (Controlling): পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে কি না তা পরিমাপ, বিচ্যুতি ঘটলে তার কারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে। প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে পরিকল্পনা প্রণীত হয় । তার আলোকে উপায়-উপকরণাদিকে সংহত করা হয়ে থাকে । এরপর অধস্তনদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রেষণা দেয়া হয়। কার্য চলাকালে বিভিন্ন বিভাগের কাজে সমন্বয়সাধন করা হয়। এরপর সময় শেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কতটা সম্পন্ন হয়েছে তা মূল্যায়নের প্রয়োজন পড়ে । এতে ব্যবস্থাপনা কার্য কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়েছে তার প্রমাণ মেলে । ধরা যাক, একটা প্রতিষ্ঠান তিন মাসে ১০,০০০ একক পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিকল্পনা নিয়েছিল। সে অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ পরিচালিত হয় । তিন মাস পর অবশ্যই দেখতে হবে যে, কতটা ফল অর্জিত হয়েছে এবং বিচ্যুতি হলে কেন তা ঘটেছে। যাতে পরবর্তী পরিকল্পনার মাধ্যমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এতে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা ও কার্যদক্ষতার মান বৃদ্ধি পায় । উল্লেখ্য, এ সময়কাল দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরও হতে পারে ।
সাধারণ অর্থে, ব্যবস্থাপনার কাজ হলো অন্যের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা । প্রাচীনকালে মানুষ যখন নিজের অভাব নিজেই পূরণ করত তখন ব্যবস্থাপনার বিষয় চিন্তায় আসেনি। যখন মানুষ সমাজবদ্ধ হলো, উৎপাদন বাড়তে লাগলো কার্যত সভ্যতা যতই এগুলো মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাও তত সম্প্রসারিত হলো এবং সেই সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবস্থাপনাও গুরুত্ব লাভ করলো । এই গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থাপনার আওতা বা পরিধি বেড়ে গেলো । বর্তমানে ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যেই কেন্দ্রীভূত নয়; সরকারি-বেসরকারি, বাণিজ্যিক- অবাণিজ্যিক সকল প্রতিষ্ঠানেই এটি একটি প্রধান কার্য হিসেবেই বিবেচিত । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনার আওতা নিম্নে তুলে ধরা হলো :
১. প্রতিষ্ঠানভেদে ব্যবস্থাপনার আওতা (Scope of management from institutional point of view) : গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে বলেছিলেন, “ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন” (Management is universal)। যেখানেই একের অধিক মানুষ একত্রে বাস করে সেখানেই কোনো না কোনোভাবে একটা ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব লাভ ঘটে । তাই পরিবারে যেমনি একটি ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব বিরাজমান তেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্রই ব্যবস্থাপনা ক্রিয়াশীল । পরিবারে পিতা বা মাতা যেমনি একজন ব্যবস্থাপক তেমনি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীও একজন ব্যবস্থাপক । তাই যেখানে যে উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় সেখানেই ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব লক্ষণীয় । নিম্নে প্রতিষ্ঠানভেদে ব্যবস্থাপনার আওতা তুলে ধরা হলো :
ক) সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : এর আওতাভুক্ত হলো পরিবার, সমাজ, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ক্লাব, লাইব্রেরি, সামাজিক সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ।
খ) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : এর অধীন হলো ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ প্রশাসন, শিক্ষা প্রশাসন, ডাক, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ, রেল, বিমান, বাংলাদেশ ব্যাংক, ওয়াসা, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা, মন্ত্রণালয় ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ।
গ) ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন ধরনের বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, খুচরা, পাইকারি, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপনি সংস্থা, হোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এর অধীন । ঘ) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : জাতিসংঘ ও এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক আদালত, শ্রম সংস্থা, এডিবি, আইডিবি, সার্ক, আসিয়ান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা এর মধ্যে পড়ে ।
২. কাজের দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনার আওতা (Scope of management from functional point of view) : একজন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করেন। স্বনামধন্য ব্যবস্থাপনাবিদ পিটার এফ. ড্রাকারের মতে, ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত তিন ধরনের কাজ সম্পাদন করে যা ব্যবস্থাপনার আওতাধীন :
ক) প্রতিষ্ঠান পরিচালনা : প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বলতে একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপায়-উপাদানের সুষ্ঠু পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদানকে বুঝায় । তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত ।
খ) ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা : প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকগণ কর্মরত থাকেন। তাই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তর হতে একেবারে নিচের স্তরে নিয়োজিত ফোরম্যান বা সুপারভাইজার পর্যায়ের সব লোকেরাই ব্যবস্থাপনার আওতাধীন । যাদের ব্যবস্থাপনাও এর অধিনে গড়ে ।
গ) শ্রমিক-কর্মী পরিচালনা : শ্রমিক-কর্মীরাই হলো প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত পক্ষ । তাই তাদের নিকট হতে যথাযথ কাজ আদায়ের নিমিত্তে পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, কর্মী পরিচালনা, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের মতো সর্ববিধ কার্যাবলি গ্রহণ করতে হয় । এগুলো ব্যবস্থাপনা কার্যের অধীন।
৩. কৌশল প্রয়োগের ভিত্তিতে আওতা (Scope of management from strategic point of view) : একজন ব্যবস্থাপককে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয় । প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে সফলতার সাথে টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের রণকৌশল গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ কৌশল গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। তাও ব্যবস্থাপনা কাজের আওতাধীন ।
৪. কার্যবিভাগের দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনার আওতা (Scope of manangement from the view point of division of work) : প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার জন্য একে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয় । এ সকল বিভাগ পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাদিও ব্যবস্থাপনার আওতাধীন। কার্য বিভাগের দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে নানান ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় বা বিপণন ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ।
৫. স্তরভেদে ব্যবস্থাপনার আওতা (Scope of manangement from the view point of levels) : ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তর হতে শ্রমিক-কর্মী তত্ত্বাবধানের স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত । স্তরভেদে ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ স্তর, মধ্যস্তর ও নিম্নস্তর এ সকল ভাগে ভাগ করা হয় । একটা বড় উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার উপরিস্তরে থাকেন পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ ব্যবস্থাপক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । মধ্যস্তরে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, জোনাল ব্যবস্থাপক, কারখানা ব্যবস্থাপক পদবির ব্যক্তিবর্গ কাজ করেন। নিম্নস্তরে, সুপারভাইজার, মাঠ কর্মকর্তা, ফোরম্যান ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ সরাসরি কাজ তত্ত্বাবধান করেন। যাদের প্রত্যেকের কাজ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন।
ব্যবস্থাপনা চক্র বলতে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অধীন কার্যসমূহের চক্রাকারে আবর্তিত হওয়াকে বুঝায় । ব্যবস্থাপনা হলো কতিপয় কার্যের সমষ্টি। এরূপ কার্যাদি একটি ধারাবাহিক কর্মপ্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে । প্রতিষ্ঠান যতদিন চলে ততদিন তা অবিরাম আবর্তিত হতে থাকে। ফলে এরূপ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ কাজ আবার পরবর্তী প্রথম কাজের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়। ব্যবস্থাপনার এরূপ ধারাবাহিক কর্মপ্রক্রিয়া ও অবিরাম আবর্তনকে ব্যবস্থাপনা চক্র নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে ।
ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া । ফলে তা ধারাবাহিক ও পরস্পর নির্ভরশীল কতিপয় কাজের সমষ্টি । পরিকল্পনা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেয়া হয় । এর আলোকে সংগঠন প্রতিষ্ঠা, কর্মীসংস্থান, নির্দেশ প্রদান, যোগাযোগ ও তত্ত্বাবধান, উৎসাহ প্রদান, বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং কাজ বা সময় শেষে নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে । নিয়ন্ত্রণ কাজের মধ্য দিয়ে যে নির্দেশনা বা সুপারিশমালা পাওয়া যায় তার আলোকে আবার নতুন পরিকল্পনা নেয়া হয় । এভাবে প্রতিষ্ঠান যতদিন চলে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বা কার্যচক্রও ততদিন স্বাভাবিক নিয়মেই আবর্তিত হতে থাকে ।
নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপনা কার্যচক্র প্রদর্শিত হলো :
বিষয়টিকে একটা উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে :
ধরা যাক, মি. খান তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুন একটা পণ্য তৈরির চিন্তা করছেন। এজন্য লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক করণীয় নির্ধারণ করা হলো । চিন্তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কী কী কাজ করতে হবে এবং প্রতিটা কাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কী হবে তা নির্ধারণ করলেন। প্রতিটা কাজের জন্য কোন কোন মানের জনশক্তির প্রয়োজন হবে তাও নির্ধারিত হলো । যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি কী লাগবে তাও ঠিক করে প্রথমেই মি. খান প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দিলেন। অতঃপর বস্তুগত উপকরণাদি জোগাড় করে দ্রুত উৎপাদনের কাজে মনোযোগী হলেন । জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া, কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না তা দেখা ইত্যাদি. কাজে মি. খান ও ব্যবস্থাপকগণ ব্যস্ত সময় কাটালেন । নতুন কাজে সাফল্য আসলে জনশক্তিকে নানান সুযোগ- সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো । নতুন কাজে উত্তম কর্মপরিবেশ ধরে রাখতে মি. খান খুবই যত্নবান । কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণকে নিয়ে তিনি মাঝে-মধ্যেই বসেন । প্রত্যেকের কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন । সবাই যাতে একতালে চলে ও সম্মিলিত প্রয়াস জোরদার হয় এজন্য সবাইকে উপদেশ দেন । বছর শেষ- এখন হিসাব করার পালা । যে সকল পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তার কতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। দেখা গেল ৮০% বাস্তবায়িত হয়েছে । ২০% কেন বাস্তবায়িত হয়নি তার পর্যালোচনায় কতকগুলো সমস্যা চিহ্নিত হলো । এ সকল সমস্যা দূর করে কাজকে আরও সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য নতুন পরিকল্পনা নিলেন মি. খান।
প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং উপায়-উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকে ব্যবস্থাপনা বলে । এ সকল কাজ প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল স্তরেই কম বেশি সম্পাদন করা হয়। তাই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি মাত্র স্তরেই সীমাবদ্ধ এ কথা বলা যায় না । নিম্নে ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ আলোচনা করা হলো :
১. উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা (Top level management) : প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাপনাকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বলে । প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য, কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায় সম্পৃক্ত থাকে । কোনো কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী, পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সচিব ও ক্ষেত্রবিশেষে জেনারেল ম্যানেজার এ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত।
২. মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা (Mid-level management) : উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও নীতি- নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণকে কাজে লাগাতে ব্যবস্থাপনার যে পর্যায় কাজ করে তাকে মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বলে । এরূপ পর্যায় উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সেতুবন্ধকের ভূমিকা পালন করে । এরূপ পর্যায় উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত লক্ষ্য, নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, উপায়-উপকরণাদি সংগঠিতকরণ, পরিচালনা, নেতৃত্ব প্রদান, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালনা করে ।
৩. নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা (Lower level or first line management) : মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতি-কৌশল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনাকে নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বলে । এ পর্যায়ের ওপরে থাকে মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ ও নিচের দিকে থাকে ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কর্মী বা শ্রমিক। নিচের দিক থেকে ওপর দিকে চিন্তা করলে একেবারে প্রথম সারির ব্যবস্থাপকগণ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়কে তত্ত্বাবধায়ন পর্যায় (Supervisory level) নামেও আখ্যায়িত করা হয়।
নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তর প্রদর্শিত হলো :
ব্যবস্থাপনার কাজকে প্রকৃতিগতভাবে চিন্তা করা (Thinking) ও কাজ করা (Doing) এ দু'ভাগে ভাগ করা . হলে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা অধিক মাত্রায় চিন্তনীয় কাজ এবং নিম্নপর্যায়ের ব্যবস্থাপনা অধিক মাত্রায় সরাসরি কাজের তত্ত্বাবধানের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। অন্যদিকে মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নির্বাহীগণ মোটামুটিভাবে উভয় ধরনের কর্ম সম্পাদন করে ।
আমাদের সমাজে পেশা বিষয়ে সাধারণ ধারণা খুবই সাদামাটা ধরনের। আমাদের ভোটার তালিকা বা নাগরিকত্ব সনদের ফর্ম পূরণকালে পেশা হিসেবে কৃষিকাজ, চাকরি এমনকি ছাত্র পর্যন্ত লেখা হয়ে থাকে । তাই পেশা কী এ নিয়ে ভুল ধারণা যেমনি রয়েছে তেমনি ব্যবস্থাপনাকে ভিন্ন পেশা হিসেবে দেখা উচিত কি না তা নিয়েও শিক্ষিত মহলে দ্বন্দ্ব বর্তমান। তবে এক কথায় বলা যায়, ব্যবস্থাপনা এখনও পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে গণ্য নয় ।
বিশেষায়িত জ্ঞান সম্বলিত কোনো কাজ বা বৃত্তিকে সাধারণ অর্থে পেশা বলে । বিশেষায়িত জ্ঞান বলতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানকে বুঝায় । একজন সাধারণ কৃষকের কৃষি বিষয়ক তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকে না । কৃষিকাজ করতে করতে তিনি যা শিখেছেন তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান কিন্তু তাকে পেশার মানদণ্ডে ফেলা যাবে না । কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রাজ্যুয়েট কৃষি বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানসমৃদ্ধ । এই জ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ে তিনি পড়াকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ! তাই তাকে একজন কৃষিবিদ বলা হয়। একজন হাতুড়ে ডাক্তারকেও গ্রাম-গঞ্জের মানুষ ডাক্তার বলে। কিন্তু যখন কারও পেশা ডাক্তারি বলা হবে তখন ডাক্তারি বিদ্যার ওপর তাত্ত্বিক জ্ঞান বা ডিগ্রি আছে কি না তা দেখতে হবে । এক্ষেত্রে কৃষিবিদ ও ডাক্তারের জ্ঞানকে বিশেষায়িত জ্ঞান বলা হবে । কারণ তাঁরা এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন । এভাবে ইঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ, চাটার্ড একাউন্টেন্ট ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গও স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী । এরূপ ব্যক্তিবর্গের রাষ্ট্রস্বীকৃত সংঘ বা সমিতি রয়েছে এবং এর সকল সদস্যদের এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয় । তাদের পেশাগত আচরণ বিধি ও নিয়ম-নির্দেশিকা থাকে এবং যার প্রতি সদস্যগণ দায়বদ্ধ থাকেন । তাই এরূপ জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের কাজকে পেশা হিসেবে গণ্য করা হয় ।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কাজ বা বৃত্তিকে পেশা হতে হলে তার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য:
১. পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট বিশেষায়িত জ্ঞান;
২. পেশাগত বিষয় দেখার জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত প্রতিনিধিমূলক সংঘ বা সংস্থা;
৩. পেশার প্রমাণ হিসেবে উক্ত সংঘ বা সংস্থার সদস্য পদ লাভ ;
৪. পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সংঘ বা সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত বিধি-বিধানের উপস্থিতি;
৫. উক্ত বিধি-বিধান মেনে চলার প্রতি সদস্যদের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং
৬. সদস্যবৃন্দের পরামর্শ প্রদানের সক্ষমতা ও ক্ষেত্র বিশেষে পরামর্শক শ্রেণির আবির্ভাব ।
ব্যবস্থাপনা একটি পেশা কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির বিদ্যমানত মূল্যায়ন প্রয়োজন । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার মিল থাকলেও কতকগুলো ক্ষেত্রে অমিল বিদ্যমান । নিম্নে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :
১. সুসংবদ্ধ জ্ঞানের প্রসার (Expansion of organized knowledge) : বর্তমানকালে বিশ্বজুড়েই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সনদ দেওয়া হচ্ছে । সারা বিশ্বেই B.B.A ও M.B.A কোর্স এখন খুবই জনপ্রিয় । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রদান করছে । এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম চলছে সারা বিশ্বজুড়েই । তাই ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে বর্তমানে সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ।
২. বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সংঘ ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা (Establishment of different management association) : উন্নত দেশসমূহে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সংঘ ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করছে । যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল অফিস ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন, আমেরিকান ব্যাংকার
এসোসিয়েশনের মতো প্রতিষ্ঠানের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । শুধুমাত্র ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীগণই এর সদস্য হতে পারেন ।
৩. ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শক শ্রেণির আবির্ভাব (Emergence of management consultants) : শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শক সংস্থা ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ নির্বাহী পদে কর্মরত ছিলেন এমন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ অনেকেই ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। এ ধরনের নিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের বিশেষত্ব বা মর্যাদাই তুলে ধরেছে ।
উপরোক্ত যুক্তিসমূহের মধ্যে অনেকটা সারবত্তা থাকলেও পরিশেষে বলা যায়, ব্যবস্থাপনা এখনও ডাক্তারি বা প্রকৌশলী পেশার ন্যায় বিশেষ পেশার মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়নি । ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থাপনাকে পেশার মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার সক্রিয় প্রয়াস লক্ষণীয় হলেও বাস্তব অর্থে এখনও ব্যবস্থাপনা সে মর্যাদা লাভ করতে পারেনি । তবে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও প্রভাব যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে একদিন তা পেশার মর্যাদা লাভে সমর্থ হবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় ।
ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা বলতে সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার আবশ্যকতা বা ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের প্রয়োগযোগ্যতাকে বুঝানো হয়ে থাকে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার আবশ্যকতা যেমনি দৃশ্যমান ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কাজ করলে উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানই লাভবান হতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ছোট-বড় সব প্রতিষ্ঠানকেই উপায়-উপকরণাদি সংহতকরণ, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে হয় । এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, ‘ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন' ।
গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস এর নাম সুবিদিত। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক সভ্যতাকালে তিনি ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন (Management is universal) এ বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। এ নিয়ে চমৎকার একটা ঘটনার বর্ণনা রয়েছে । তিনি একদিন তাঁর ছাত্র ও ভক্তদের আসরে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, 'সাবান কারখানার একজন দক্ষ ম্যানেজারকে সেনাধ্যক্ষ বা সামরিক সচিবের দায়িত্ব দেয়া হলে সে দক্ষতার সাথে তা পালন করতে পারবে ।' তখনকার দিনে গ্রীক সমাজে সৈন্যদের ব্যাপক প্রভাব। সেনাকর্মকর্তাগণ সক্রেটিসের এ বক্তব্যকে তাঁদের জন্য অপমানকর মনে করলেন । কারণ তখনকার দিনে সাবান কারখানা নেহায়েতই ছোট ছিল । তার ম্যানেজারের সাথে তাদের তুলনাকে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না । অভিযোগ রাজার দরবারে উত্থাপিত হলো । রাজা সক্রেটিসকে ডেকে তার এরূপ বক্তব্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সক্রেটিস সবার সামনে বললেন, ‘একজন সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন, সৈন্য ও রসদপত্র জোগাড় করে তাকে সংহত করেন, যুদ্ধের নির্দেশ দেন, সৈন্যদের উৎসাহ দেন, যুদ্ধ শেষে জয়-পরাজয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন, ভুলভ্রান্তি থাকলে তা সংশোধন করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেন । একজন সাবান কারখানার ম্যানেজার সাবান উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করেন, কর্মীদের কাজের নির্দেশ দেন, তাদের উৎসাহিত করেন এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না তা দেখে ভুলভ্রান্তি থাকলে তা সংশোধন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তাই ক্ষেত্রগত পার্থক্য থাকলেও ব্যবস্থাপনা একটা সর্বজনীন বিষয় যা সকল সমাজে সর্বকালে সবধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে কারণে সাবান কারখানার একজন দক্ষ ম্যানেজারও প্রতিরক্ষা সচিবের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম।' তাঁর বক্তব্যে রাজা সন্তুষ্ট হলেন ।
এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যা ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী ভিন্ন চলতে পারে । তাই ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান । একজন পরিবার প্রধান যেমনি ব্যবস্থাপক তেমনি একজন রাষ্ট্রপ্রধানও এক অর্থে ব্যবস্থাপক । পরিবার প্রধান যদি পরিকল্পিতভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও উপকরণাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন তবে তার পক্ষে লক্ষ্যার্জন সম্ভব হয় । অন্যদিকে একজন রাষ্ট্রপ্রধানকেও তাঁর জনগণ ও সহায়-সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজন পড়ে ।
ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সকল কাজ; যেমন- পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ যেমনি বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য তেমনি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানেও লক্ষ্যার্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার এ সকল কাজ সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দেয় ।
উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, দলবদ্ধ যেকোনো কাজ বা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা একটি অতি অপরিহার্য উপাদান। সকল সমাজেই ব্যবস্থাপনার কাজের ধরন ও প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরনের। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠান ও সমাজভেদে কিছুটা পার্থক্য হলেও যতোই দিন যাচ্ছে এ পার্থক্য ততোই হ্রাস পাচ্ছে । তাই ব্যবস্থাপনা একটি সর্বজনীন বিষয় তা বলা যেতে পারে । এ কারণেই Koontz, "Effective managing is the concern of the corporation president, the hospital Weihrich administrator, the government, first-line superviser, the Boy - Scout leader, the bishop in the church, the baseball manager and the university president.” অর্থাৎ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বড় কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট, হাসপাতালের পরিচালক, সরকারি প্রথম সারির তত্ত্বাবধায়ক, বয়স্কাউট লিডার, গীর্জার পাদ্রী, বেসবল দলের ম্যানেজার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট সবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ।
“নীতি-নৈতিকতা মেনে চলা উচিত'- এ আপ্তবাক্য সকল সমাজেই প্রচলিত । তাই নিঃসন্দেহে নীতি এমন ইতিবাচক বিষয় যা মেনে চললে এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হতে পারে । নীতি হলো কাজের সাধারণ নির্দেশিকা । প্রতিটা ক্ষেত্রে কিভাবে করলে কাজটা সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যাবে দীর্ঘদিনে এ ধরনের প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে কিছু উপায়-পদ্ধতি বেরিয়ে এসেছে যাকে নীতি হিসেবে দেখা হয়ে থাকে । ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো কী হতে পারে অনেকেই এ নিয়ে দীর্ঘদিনে প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন । হেনরি ফেওল প্রদত্ত ১৪টি মূলনীতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের কী কী গুণ থাকা উচিত তাও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আগামী দিনে যারা যোগ্য ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে চায় নিঃসন্দেহে এ সকল জ্ঞান তাদের যোগ্য ব্যবস্থাপক হতে সহায়তা করবে ।
এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা (শিখন ফল)
১. ব্যবস্থাপনা নীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
২. ব্যবস্থাপনার নীতি বা আদর্শসমূহ বর্ণনা করতে পারবে ।
৩. এফ. ডব্লিউ, টেলর ও হেনরি ফেয়লের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. আদর্শ ব্যবস্থাপকের দক্ষতা ও গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে ।
৫. আদর্শ ব্যবস্থাপকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৬. ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে ।
৭. সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৮. বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে ।
৭টি
৯টি
১২টি
১৪টি
আমরা কোঁনো কাজ নানানভাবেই করতে পারি । বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে নানানভাবেই খাওয়া যায় । কিন্তু মানুষ শুরু থেকেই বুঝেছে শুয়ে খাওয়ার চেয়ে বসে খাওয়া সহজ ও উত্তম । সুষম খাদ্য খাওয়া ভালো, অতিভক্ষণ স্বাস্থ্য ও কাজের জন্য ক্ষতিকর- এ বিষয়গুলো মানুষ আপনা-আপনি বুঝেছে, শিখেছে ও তা রপ্ত করেছে। এভাবেই চিন্তা ও কাজ করতে করতে মানুষ ঐ চিন্তা ও কাজ করার সাধারণ নির্দেশিকা বা করণীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট করে তা পালন করে এগিয়ে গেছে । এই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত ও সকলের নিকট গ্রহণীয় নিয়ম-পদ্ধতিকেই নীতি বলে । যখনই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে চলা শুরু করেছে তখন থেকেই তারা তাদের মধ্য থেকে কাউকে নেতা বা প্রধান হিসেবে মেনেছে ও তার আনুগত্য করেছে । অন্যদিকে নেতা বা প্রধান তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় উদ্দেশ্য অর্জন বা স্বার্থরক্ষার চেষ্টা চালিয়েছেন। এভাবে সমাজ বড় হয়েছে, নানান সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে ও সেই সাথে ব্যবস্থাপনা কার্যও ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নেতা, প্রধান বা ব্যবস্থাপকগণ কিভাবে তাদের কাজগুলোকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করবেন সে বিষয়ে নানান নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । সকলের নিকট গ্রহণীয় ও উত্তম বলে প্রতিষ্ঠিত এরূপ নিয়ম-পদ্ধতিই পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনার নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।
ব্যবস্থাপনা নীতি হলো ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদনের সাধারণ পথ নির্দেশনা (Guidance for action)। দীর্ঘদিনে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করতে যেয়ে ব্যবস্থাপকগণ যে সকল নিয়ম-নীতি পালন করে এসেছেন তার মধ্য হতে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নির্দেশিকাই ব্যবস্থাপনার নীতি হিসেবে গণ্য । একজন ব্যবস্থাপক যখন কিছু লোক নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালায় তখন অধস্তনদের মাঝে কাজকে ভাগ করে দিতে হয় । তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে । এতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে । এভাবে কে কাকে নির্দেশ দেবে, কে কার নির্দেশ পালন করবে তা যদি ঠিক করে দেয়া না হয়, একজন কর্মীর একাধিক আদেশদাতা যাতে না থাকে এটা যদি নিশ্চিত করা না হয় তবে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক । এভাবে অনেক নিয়ম-পদ্ধতির কথা বলা যাবে যেগুলো মেনে চললে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ব্যবস্থাপক বা পরিচালকগণই ভালো ফল পেতে পারেন । তাই এ সংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতি বা নির্দেশনাকেই ব্যবস্থাপনার নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় ।
ব্যবস্থাপনার কাজ বলতে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজকে বুঝায় । এর প্রতিটা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে পূর্ব নির্ধারিত কিছু সাধারণ নির্দেশিকা রয়েছে। যা পালন করা হলে প্রতিটা কাজে উত্তম ফললাভ সম্ভব । একইভাবে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কার্যের ক্ষেত্রেও এরূপ পালনীয় নির্দেশিকা বা নীতিমালা থাকে। এরূপ নীতিমালা এমন নিয়ম-নীতিসমূহের নির্দেশ করে যা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পথনির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরূপ নীতিসমূহ দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে যা সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য ।
ব্যবস্থাপনা নীতি হলো ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদনে দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা কতিপয় সাধারণ নির্দেশিকা বা নিয়ম-পদ্ধতি । এরূপ নির্দেশিকা মেনে চললে ব্যবস্থাপনা কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই এরূপ নির্দেশিকা কী হতে পারে তা নির্ধারণের জন্য ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়কে নীতি হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এফ. ডব্লিউ. টেলর, এল. উরউইক, হেনরি ফেয়ল ইত্যাদি মনীষীবর্গের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক হেনরি ফেয়ল ফরাসী ভাষায় তাঁর লেখা Administration Industrielle et General গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার ১৪টি মূলনীতির নির্দেশ করেছেন যা অদ্যাবধি বিশ্বের সকল মহলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। নিম্নে তার প্রদত্ত মূলনীতিসমূহ আলোচনা করা হলো:
১. কর্ম বিভাজন বা কার্য বিভাগের নীতি (Principle of division of work) : প্রতিষ্ঠানের কাজকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করার নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় কার্য বিভাজনের নীতি বলে । যে কোনো ব্যবস্থাপনা কার্যে কর্ম বিভাজন বা কার্য বিভাগ এর প্রথম ও প্রধান পালনীয় নীতি । একজন ব্যবস্থাপক অধস্তন জনশক্তি নিয়ে কাজ করেন। এদের কাজ যদি ভাগ করে সেভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া না হয় তবে কার্যক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেবে। প্রত্যেকেই সহজ বা মর্যাদাসম্পন্ন কাজটি করতে চাইবে। অন্যদিকে প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট না থাকায় কাউকে জবাবদিহি করাও যাবে না। তাই একজন ব্যবস্থাপককে সবসময়ই সতর্কতার সাথে কাজকে ভাগ করে প্রত্যেক কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। যাতে কর্মী তার কাজ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বুঝে নিয়ে সেভাবে কাজ করতে পারে। এতে একই ধরনের কাজ করতে যেয়ে কর্মীর কার্যদক্ষতা যেমনি বাড়ে তেমনি ব্যবস্থাপকের পক্ষে অধস্তনদের কাজ তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহিতা করা সহজ হয়।
২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে সমতা রক্ষণের নীতি (Principle of balancing authority and responsibility): কর্তৃত্ব হলো আদেশ দানের অধিকার। অন্যদিকে দায়িত্ব হলো জবাবদিহি করার বাধ্য-বাধকতা । এই অধিকার ও বাধ্য-বাধকতায় সমতা রক্ষার নীতিকেই কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে সমতা রক্ষণ বলে। কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে সঠিকভাবে কাজ পেতে চাইলে তাকে যেমনি কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হয় তেমনি উভয়ের মধ্যে যাতে সমতা বজায় থাকে সেটিও নিশ্চিত করা আবশ্যক। একজনকে হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব দিলে তাকে প্রয়োজনীয় খাতা-পত্র ও হিসাব তলব করার কর্তৃত্বও প্রদান করা উচিত । অন্যথায় তার পক্ষে হিসাব নিরীক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। একইভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যদি অনেক বেশি থাকে কিন্তু সেই পরিমাণে কারও নিকট তাকে জবাবদিহি করতে না হয় তবে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হতে বাধ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ এখানেই ।
৩. কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি (Principle of centralization and decentralization): প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে এ বিষয়ক নীতিকেই কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বলে । যদি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতা ব্যবস্থাপনার উপরিপর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয় তাকে কেন্দ্রীকরণ বলে। অন্যদিকে এরূপ ক্ষমতা নিচের পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের হাতে ছেড়ে দেয়া হলে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে । একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ ও সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ কোনোটিই লাভজনক নয়। সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ অধস্তনদের গুরুত্ব হ্রাস করে। ফলে তাদের দক্ষতা ও আগ্রহ হ্রাস পায়। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে ঊর্ধ্বতন অধস্তনদের ওপর কর্তৃত্ব হারায় । তাই প্রতিষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের উপরিস্তরে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপনার নিচের স্তরে প্রদান আবশ্যক ।
৪. আদেশের ঐক্য নীত (Principle of unity of command): একজন কর্মীর আদেশকর্তা হবেন একজন মাত্র ব্যক্তি-এরূপ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় আদেশের ঐক্য নীতি বলে। অর্থাৎ কোনো অধস্তন (Subordinate) একজন ঊর্ধ্বতন (Boss) এর নিকট থেকেই সরাসরি আদেশ লাভ করবে এবং তার কাজের জন্য ঐ ঊর্ধ্বতনের নিকট জবাবদিহি করবে। কখনই একাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে আদেশ লাভ বা এভাবে জবাবদিহি করবে না । ধরা যাক, প্রতিষ্ঠানে ৫ জন ফোরম্যান ক নামক একজন সুপারভাইজারের অধীন। এক্ষেত্রে উক্ত ৫ জন ফোরম্যানের প্রত্যেকের একক আদেশদাতা হলেন ক। এক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যেক ফোরম্যান তাদের অধস্তন শ্রমিকদের কাজের জন্য ক এর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। যদি উক্ত ফোরম্যানদের দু'জন আদেশকর্তা থাকে এবং দু'জন দু'ধরনের আদেশ দেন তবে অধস্তনদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। একজন অফিস পিয়ন যদি একাধিক বিভাগীয় প্রধানের অধীনে কাজ করে তবে সেক্ষেত্রেও দ্বৈত অধীনতার কারণে তার কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক ।
৫. নির্দেশনার ঐক্য নীতি (Principle of unity of direction): উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পূর্ব নির্দেশনার সাথে মিল রেখে পরবর্তী নির্দেশনা প্রদানের কাজকেই ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনার ঐক্য নীতি বলে । একটা সামগ্রিক উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি মাথায় রেখে তার আলোকে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে । ধরা যাক, প্রতিষ্ঠানে কিছু যোগ্য বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে। এ জন্য বিজ্ঞপ্তি তৈরি, পত্রিকায় প্রেরণ, আবেদনপত্র জমা গ্রহণ, আবেদন পত্র বাছাই, নিয়োগ পরীক্ষার কার্ড ইস্যু, পরীক্ষা অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপককে সংশ্লিষ্ট অধস্তনদের ধারাবাহিক নির্দেশনা দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি তিনি একবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার নির্দেশ দিয়ে পরে আবার সেখান থেকে সরে এসে বিজ্ঞপ্তি লিখে দেয়ালে দেয়ালে টাঙানোর নির্দেশ দেন, পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী নির্দেশনার সাথে মিল না রেখেই পরবর্তী নির্দেশ প্রদান করেন তবে স্বভাবতই উদ্দেশ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে এবং এতে ঊর্ধ্বতন সম্পর্কে অধস্তনদের মনে খারাপ ধারণা জন্মাবে।
৬. সাধারণ স্বার্থে নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগের নীতি (Principle of subordination of individual interest to general interest): ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রাতিষ্ঠানিক বা সাধারণ স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় সাধারণ স্বার্থে নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগ এর নীতি বলে। একটা ব্যবসায়ে কর্মরত প্রতিটা ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগ যদি প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে বড় করে দেখে তবে সেক্ষেত্রে দলীয় চেতনা (Team spirit) বৃদ্ধি পায় ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তারা ছোটখাটো বিভেদ এড়িয়ে চলে। এতে প্রতিষ্ঠান অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে । এতে জনশক্তির বেতন ও সুযোগ-সুবিধাও বাড়ে। অন্যদিকে যদি কর্মরত প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে তবে প্রাতিষ্ঠানিক বা সাধারণ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । একটা দেশের ক্ষেত্রেও এ নীতি প্রযোজ্য । সরকার, সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সবাই যদি দেশপ্রেম নিয়ে দেশের স্বার্থকে বড় মনে করে কাজ করে তবে দেশ ও দেশের মানুষ সবাই উপকৃত হয় । কিন্তু যখন প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাকে অগ্রাধিকার দেয় তখন এক পর্যায়ে দেশ ও জনগণ সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।
৭. জোড়া-মই-শিকলের নীতি (Principle of scalar chain) : প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে শুরু করে একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক নিয়মে প্রতিটা ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগকে একে অন্যের সাথে যুক্ত করে দেয়ার বা একই শিকলের অধীনে সবাইকে আবদ্ধ করার নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় জোড়া মই-শিকল নীতি বলে । এতে শিকলের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পারস্পরিক আবদ্ধতা কর্তৃত্ত্বের প্রবাহ ও যোগাযোগের পথ নির্দেশ করে। কে কার অধীন, কে কার অধস্তন সহজে বোঝা যায়। ফলে সংঘবদ্ধতা জোরদার হয় । প্রতিষ্ঠানের যে কোনো পর্যায়ে সমস্যা দেখা দিলে তা উর্ধ্বতন সহজে জানতে পারে ও দ্রুত তার সমাধা সম্ভব হয়ে থাকে। উল্লেখ্য কোনো ব্যক্তি দলছাড়া হয়ে গেলে বা দলের বাইরে থাকলে তা তার জন্য যেমনি সমূহ ক্ষতি বয়ে আনতে পারে তেমনি দলের জন্যও তা ক্ষতির কারণ হয়। একটা প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি, বিভাগ বা উপবিভাগ যদি এই শিকলের বাইরে থাকে তবে তাকে বা তাদের কাজে লাগানো বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। ফলে ঐ ব্যক্তি বা বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হয় এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য তা মন্দ উদাহরণ সৃষ্টি করে ।
৮. নিয়মানুবর্তিতার নীতি (Principle of discipline): প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্তম নিয়ম-নীতি নির্ধারণ এবং তা মেনে চলার নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় নিয়মানুবর্তিতার নীতি বলে । প্রতিষ্ঠানে যথোপযুক্ত নিয়ম-নীতি না থাকলে এবং তা সংশ্লিষ্ট সবাই মান্য না করলে প্রতিষ্ঠান কখনই ভালো চলতে পারে না । এই নীতি অনুযায়ী মনে করা হয়। যে, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও নিয়মের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ ও তা মান্য করার ঐকান্তিক আগ্রহ সফলতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে লক্ষণীয় যে, সেখানে নিয়ম-নীতি থাকলেও অনেকেই তা পরোয়া করে না । ফলে সেখানকার কার্যপরিবেশ ও সংশ্লিষ্টদের কার্যদক্ষতার মান খুবই হতাশাব্যঞ্জক । অন্যদিকে বেসরকারি বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহে সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও তা মান্য করার বিষয়ে খুবই জোর দেয়া হয়। ফলে সেখানে কার্য পরিবেশ ও কার্যমান উন্নত হয়ে থাকে । হেনরি ফেওল এক্ষেত্রে মনে করেছেন যে, ঊর্ধ্বতনগণ যদি নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন তবে প্রতিষ্ঠানে নিয়মানুবর্তিতার নীতি অনুসরণ সহজ হয়।
৯. শৃঙ্খলার নীতি (Principle of order): যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে এবং সঠিক বস্তুকে সঠিক স্থানে স্থাপনের নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলার নীতি বলে। এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বলতে উপায়-উপকরণাদির শৃঙ্খলাকে বুঝানো হয় । যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে বসানো না গেলে কখনই তার নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব হয় না । আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রায়শই লক্ষণীয় যে, ব্যক্তির যোগ্যতা বা মেধার চাইতেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক, রেফারেন্স, ব্যক্তিগত লাভালাভ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে মানবীয় শৃঙ্খলা বলতে সেখানে কিছুই থাকে না । কার্যত অদক্ষতা-অযোগ্যতাকেই সেখানে লালন করা হয়। যা কখনই প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো ফল দেয় না। অন্যদিকে যেই প্রতিষ্ঠান যোগ্য লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে আন্তরিক থাকে সেখানে কখনই অদক্ষতা, অনিয়ম ইত্যাদি ভর করতে পারে না । বস্তুগত শৃঙ্খলার বিষয়টাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । যে যন্ত্রটি যেখানে থাকা দরকার, যাকে যে ধরনের টেবিল-চেয়ার দেয়া দরকার, কারখানা বিন্যাস, অফিস বিন্যাস ইত্যাদি যেভাবে হওয়া প্রয়োজন তা সেভাবে করলেই তদ্বারা উপযুক্ত ফললাভ সম্ভব।
১০. পারিশ্রমিকের নীতি (Principle of remuneration): প্রতিষ্ঠানের প্রতিটা কর্মীর কাজের প্রকৃতি, মেধা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় উপযুক্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় পারিশ্রমিকের নীতি বলে । যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত জনশক্তি তার মেধা, যোগ্যতা ও কাজ অনুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করে । মালিক পক্ষও তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের বিপক্ষে উপযুক্ত মুনাফা পেতে চায়। তাই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদেরকে উভয় পক্ষের প্রত্যাশা পূরণে যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনবল ধরে রেখে দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনায় এ নীতির যথাযথ অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই ।
১১. সাম্যের নীতি (Principle of equity): অধস্তনদের সবার প্রতি সমান আচরণ বা স্নেহ প্রদর্শনের নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় সাম্যের নীতি বলে । এটি ন্যায়পরায়ণতার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। একজন ঊর্ধ্বতন যদি তার সকল অধস্তনকে সমান চোখে দেখেন, সমান আচরণ ও স্নেহ প্রদর্শন করেন তবে অধস্তনদের মাঝে ঊর্ধ্বতন সম্পর্কে সুধারণা গড়ে ওঠে। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় । প্রতিষ্ঠানে আনুগত্য, মান্যতা ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায় । অন্যদিকে ঊর্ধ্বতন যদি তার অধস্তনদের সমান চোখে না দেখেন, বেতন, পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি প্রদানে বৈষম্য করেন তবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঊর্ধ্বতনের প্রতিই খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয় না কর্মীদের নিজেদের মধ্যেও বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। একজন কর্মী অন্যায় করলেও ঊর্ধ্বতন যদি তার অন্যায় বিবেচনায় শাস্তি প্রদানে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধস্তন হিসেবে তার সাথে আর পাঁচজনের মতই ব্যবহার করেন তবে উক্ত অধস্তনের মনে ঊর্ধ্বতনের প্রতি শ্রদ্ধা কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।
১২. চাকরির স্থায়িত্বের নীতি (Principle of stabilization of service) : এই নীতি অনুযায়ী মনে করা হয়। যে, কর্মীদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা হলে তা কর্মীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে । সাধারণভাবে একজন যুবক লেখাপড়া শেষে ভালো চাকরি পাওয়াটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যখন সে চাকরি পায় তখন চাকরিটা স্থায়ী হোক এটাই তার প্রত্যাশার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ পর্যায়ে চাকরি স্থায়ী করা হলে সে তা নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করে। এ সময় থেকেই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠানের একজন প্রকৃত সদস্য গণ্য করে যা তার কাজের গতি বাড়িয়ে দেয় । কিন্তু প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের চাকরি যদি স্থায়ী করা না হয় তবে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনে যে কোনো সময় চাকরি চলে যাওয়ার ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাসা বাঁধে। সে অন্যত্র চাকরি খুঁজতে বাধ্য হয় । একসময় সে কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে । তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যোগ্য কর্মীদের চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা নেয়া উচিত ।
১৩. উদ্যোগের নীতি (Principle of initiative) : প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যাতে উদ্যোগী হতে পারে বা নিজের কাজের উন্নয়ন বিষয়ে ভাবতে পারে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার সুযোগ, সৃষ্টিকেই ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগের নীতি বলে। ঊর্ধ্বতনদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কাজের মান উন্নয়ন বা বিদ্যমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার বিষয়ে কার্যকর চিন্তা করা সম্ভব হয় না । তাই প্রতিষ্ঠানে যদি এমন পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয় যাতে প্রত্যেক অধস্তন স্ব স্ব স্থানে তাদের কাজের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে ও ঊর্ধ্বতনদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে তবে স্বভাবতই অধস্তনরা উদ্যোমী ও উদ্যোগী হয়ে ওঠে । যা অধস্তনদের প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজকে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহ যোগায়। অন্যদিকে যদি এ ধরনের পরিবেশকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং এ ধরনের চিন্তাকে অধস্তনদের বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করা হয় তবে নিঃসন্দেহে তা স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করে।
১৪. একতাই বল নীতি (Principle of unity is strength) : প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগকে সর্বাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থেকে পারস্পরিক সহযোগিতায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় একতাই বল নীতি বলে । প্রতিটা বিভাগ ও উপবিভাগের অধীন ব্যক্তিবর্গ যদি বিভাগীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং প্রতিটা বিভাগ ও উপবিভাগ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেকের কাজকে অন্যের সাথে সমন্বিত করে একতালে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তবে প্রতিষ্ঠান সহজেই তার মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে । কিন্তু সর্বত্র ঐক্য, সমঝোতা ও সহযোগিতা যদি না থাকে তবে পারস্পরিক বিরোধ, অনৈক্য ও অসহযোগিতা সেখানে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। যেখানে প্রতিষ্ঠান কখনই সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই ঊর্ধ্বতনদেরকে এরূপ নীতি বাস্তবায়নে সদা তৎপর থাকতে হয় ।
H. Fayol বর্ণিত উপরোক্ত মূলনীতিসমূহ ছাড়াও বর্তমানে আরও কিছু নীতি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনায় সাধারণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারে বলে মনে করা হয় :
১. নমনীয়তার নীতি (Principle of flexibility) : চিন্তা, কাজ ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনে পরিবর্তন এনে প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যাভিমুখী করার নীতিকেই নমনীয়তার নীতি বলে। ব্যবস্থাপনা সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা। তাই সামাজিক বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনাকে তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয়। তাই এরূপ নীতির মূল বক্তব্য হলো পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানে ব্যবস্থাপনার সমর্থ থাকা উচিত । এজন্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে ব্যবস্থাপনাকে সঙ্গতি বিধান করে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে ।
২. ভারসাম্যের নীতি (Principle of balancing) : ভারসাম্যের নীতি বলতে প্রতিটা ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগীয় কাজের মধ্যে সমন্বয় বিধান এবং সমতালে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য সৃষ্টিকে বুঝায়। কোনো বিভাগের কাজের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব বুঝে লোকবল ও সামর্থ্য নিয়োজিত করা উচিত; যাতে কোন বিভাগ অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে না পড়ে । সকল বিভাগ, উপবিভাগ ও ব্যক্তির কাজ ভারসাম্যপূর্ণ হলে তা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কাজে ভারসাম্যাবস্থার সৃষ্টি করে ।
৩. ব্যতিক্রমের নীতি (Principle of exceptions) : ব্যবস্থাপক কোন ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ করবে এরূপ নীতিতে তার প্রতি আলোকপাত করা হয়ে থাকে। একজন ব্যবস্থাপকের পক্ষে তার সবগুলো কাজ সমান গুরুত্ব দিয়ে করা সম্ভব হয় না। এজন্য কোন্ কাজটি উদ্দেশ্য অর্জনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ ক্ষেত্রে অধিক বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা বিদ্যমান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সেভাবে দৃষ্টি প্রদান এবং ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করা আবশ্যক।
সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবস্থাপনার যে উন্নয়ন ঘটেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক সময় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল খুবই সাদামাটা ধরনের। তাই তার ব্যবস্থাপনা ছিল সহজ। ব্যবস্থাপনা একটা বিষয়-এটাই ভাবনাতে আসেনি। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মনীষীবৃন্দের উন্নয়নচিন্তা প্রাচীনকালে মূলত বিভিন্ন সভ্যতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। ব্যবিলনীয় সভ্যতাকালে রাজা হাম্মুরাবি, চৈনিক সভ্যতাকালে সানজু, ভারতীয় সভ্যতাকালে কৌটিল্য, গ্রীক সভ্যতাকালে সক্রেটিস, এরিস্টটল ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছেন তা ইতিহাস থেকে জানা যায়। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালে আলফারাবি, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ লেখক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কিভাবে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের গুণাবলি কী থাকা উচিত-এ নিয়ে লেখালেখি করেছেন। মধ্যযুগের শেষ দিকে এসে লুকা প্যাসিওলী, স্যার থমাস মুর, নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী, স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট, এ্যাডাম স্মীথ এবং আরও পরে রবার্ট ওয়েন, চার্লস ব্যাবেজ ইত্যাদি মনীষীবর্গ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় এবং একত্রে হাজার হাজার শ্রমিক পরিচালনা ও কাজ আদায় করতে যেয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যে কারণে বেশ কিছু ব্যবস্থাপনা বিশারদ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখেন। এর মধ্যে হেনরি ফেয়ল, এফ ডব্লিউ, টেলর, এইচ. এল. প্যান্ট, ফ্রাঙ্ক বি. গিলব্রেথ, লিলিয়ান এম. গিলব্রেথ, হুগো মুনস্টারবার্গ, অলিভার শেলডন, এলটন মেয়ো, চেস্টার আই. বার্নার্ড প্রমুখ মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য । তাঁদের পবেষণা, চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থাপনাকে একটা সমৃদ্ধ ও গৌরবময় শাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত করে। বর্তমানকালে এটি এতটাই সমৃদ্ধ শাস্ত্র যে, এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নিয়ে লেখা-লেখি ও গবেষণার অন্ত নেই । আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় এখন আলাদা শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে আরও বিকশিত ও সুষমামণ্ডিত করেছে।
জীবন বৃত্তান্ত (Bio-data) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে ফ্রেডারিক উইন্সলো টেলর ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও খারাপ দৃষ্টিশক্তির কারণে। তার পক্ষে লেখাপড়া চালানো সম্ভব হয়নি। ১৮৭৫ সালে তিনি একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্যাটার্ন প্রস্তুতকারী মেকানিকের কাজ শেখার জন্য শিক্ষানবীস হিসেবে যোগ দেন। ১৮৭৮ সালে টেলর মিডডেল স্টীল কোম্পানিতে মেকানিক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। কার্যক্ষেত্রে স্বীয় দক্ষতা, প্রতিভা ও প্রজ্ঞার বলে ১৮৮৪ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে মিডভেল কোম্পানিতে প্রধান প্রকৌশলী পদে উন্নীত হন। উল্লেখ্য বৈকালিন সময়ে লেখাপড়া করে ইতোমধ্যে তিনি ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি মিডভেল কোম্পানি থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৯০০ সাল পর্যন্ত Consulting Engineer হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন । জীবনের বাকি সময়টা তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উদ্ভাবন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর নতুন চিন্তাধারার প্রয়োগে অবৈতনিক পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও নতুন ধারণার প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। যা পরিণামে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে অনেক গবেষক ও ব্যবস্থাপনা বিশারদ তার প্রদত্ত ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ ও এর উন্নয়ন সাধন করলেও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক (Father of Scientific Management) হিসেবে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন । ১৯১৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।
অবদান (Contributions) : ফ্রেডারিক উইন্সলো টেলর সাধারণ শিক্ষানবীস থেকে প্রধান প্রকৌশলী পর্যন্ত বিভিন্ন পদে দীর্ঘ দু'যুগ দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে তাঁর কাছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা ধরা পড়ে। তিনি এ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পর তা সমাধানের পন্থা কী হতে পারে এ নিয়ে দীর্ঘ দুই দশক বিভিন্ন গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। এভাবেই তিনি তাঁর গবেষণাকর্মের ফলাফলকে একটা দর্শনে রূপ দেন । যা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) নামে পরিচিত। এরূপ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে তাঁর অবদানসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :
ক) গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা (Writing books and articles): টেলর গবেষণাকর্ম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভাবনাকে সাধারণ্যে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। যার মধ্যে The Principles of Scientific Management অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও Shop Management, A Piece Rate System. The Gospel of Efficiency ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । যা তাঁর দর্শনকে পরবর্তী গবেষণার বিষয়বস্তু হতে ও স্থায়ী রূপ পরিগ্রহে সহায়তা করেছে। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপকে একটা মানসিক বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যা গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা ধারণা থেকে ব্যবস্থাপনাকে বেরিয়ে আসতে সুযোগ করে। দিয়েছে।
খ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আদর্শ উপস্থাপন (Introducing scientific management principle) : টেলর তাঁর গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দু'টি দিক; মানবীয় দিক (উত্তম কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ও বস্তুগত দিক (পরিকল্পনা, কারখানা পরিবেশ ইত্যাদি) নির্দেশ করেন ও তার উন্নয়নের উপায় নির্দেশ করেন । সেই সাথে তিনি এরূপ ব্যবস্থাপনার কতিপয় আদর্শ তুলে ধরেন; যা নিম্নরূপঃ
১. টিপসহির পদ্ধতি (গতানুগতিক হাতুড়ে পদ্ধতি) পরিহারপূর্বক মানুষের প্রতিটা কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করা;
২. বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণদান ও তাদের উন্নয়ন সাধন করা;
৩. সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা; ও
৪. ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষ্ঠু বণ্টন ।
গ) গবেষণা ও কর্ম পদ্ধতির উন্নয়ন (Research and developing working procedure) : টেলর তাঁর বাস্তব উপলব্ধি ও গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্ম সম্পাদনের অনেকগুলো সহায়ক উপাদান (Elements) বা পদ্ধতি (Mechanism)-এর উদ্ভাবন করেছেন। যা ব্যবস্থাপনা কাজকে অধিক কর্মক্ষম ও ফলদায়ক করতে সমর্থ হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ উল্লেখযোগ্য :
১. সময় নিরীক্ষা;
২. গতি নিরীক্ষা;
৩. শ্রান্তি নিরীক্ষা;
৪. কার্যভিত্তিক ফোরম্যানশীপ বা সংগঠন;
৫. পরিকল্পনার জন্য পৃথক কক্ষ বা বিভাগ;
৬. ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রম আদর্শের অনুসরণ;
৭. কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির বিনির্দিষ্ট মান প্রতিষ্ঠা;
৮. স্লাইড রুল এবং সমজাতীয় শ্রম-সংক্ষেপ যন্ত্রপাতির ব্যবহার;
৯. শ্রমিকদের জন্য নির্দেশ কার্ড প্রণয়ন;
১০. পার্থক্যমূলক ঠিকা মজুরি হার ব্যবস্থার প্রবর্তন;
১১. সকল কার্যের জন্য বোনাস পদ্ধতির প্রবর্তন এবং
১২. উৎপাদনে ব্যবহৃত কলকব্জা ও উৎপাদিত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসে নিমোনিক (Mnemonic) পদ্ধতির উদ্ভাবন ।
ঘ) মানব সম্পদের উপর গুরুত্বারোপ (Providing importance on human resources) : টেলর যদিও তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে কার্যক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন তবে তিনি কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠানে মানবশক্তির গুরুত্বকে ছোট করে দেখেননি । তিনি অকপটে বিশ্বাস করতেন বস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মূলেই রয়েছে মানুষের মানবিক প্রচেষ্টার প্রয়োগ । তিনি আরো লক্ষ করেন যে, মানুষের প্রচেষ্টা যতো বাড়ে সম্পদও ততোই বৃদ্ধি পায়। এ জন্যই তিনি সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মানসিক বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত । আর এটি হলো কাজের প্রতি, সহকর্মীদের প্রতি এবং কর্মকর্তাদের প্রতি তাদের মনোভঙ্গির আমূল পরিবর্তন।" আর এভাবেই নতুন চিন্তাগত ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে টেলর ব্যবস্থপনার জগতে নতুন এক দিগন্তের সৃষ্টি করেছেন । যা তৎকালীন সময়েই শুধু নয় বর্তমানকাল অবধি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে।
জীবন বৃত্তান্ত (Bio-data) : ব্যবস্থাপনা চিন্তার জগতে সবচেয়ে খ্যাতিমান ইউরোপীয় পণ্ডিত হলেন হেনরি ফেয়ল। ১৮৪১ সালে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালে ছয় বৎসর বয়সে বাবা-মার সাথে তিনি ফ্রান্সে চলে আসেন এবং সেখানেই তাঁর পরিবার স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। ১৮৬০ সালে তিনি এস.এ. কমেনট্রি ফোরচ্যামবোল্ট (S.A. Commentary Fourchambault)-এর একটি খনিতে প্রকৌশলী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ সালে তাঁকে এ খনি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এরূপ দায়িত্ব গ্রহণকালে এ প্রতিষ্ঠানটি অনেকটা দেউলিয়ার পর্যায়ে ছিল। ১৯১৮ সালে তিনি যখন এ দায়িত্ব থেকে অবসর নেন তখন তার স্বীয় যোগ্যতাবলে এ প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে ছিল যথেষ্ট সচ্ছল ।
ফেয়ল প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব হলো সর্বপ্রথম ও পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপিত তত্ত্ব। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্ব প্রমাণসিদ্ধ উপাদান, কার্যক্রম এবং যাবতীয় কলা-কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে । আধুনিক ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার মূল স্থপতি হিসেবে তাঁর অবদান ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ জন্যই তাঁকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক (Father of Modern Management Thougts) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । ১৯২৫ সাথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।
অবদান (Contributions) : ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিংশ শতকের শুরুতে যে ক'জন ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হেনরি ফেয়লের নাম তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ফ্রান্সের অধিবাসী এ খনি প্রকৌশলী ব্যবস্থাপনাকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কাজ সম্বলিত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য ও পাঠযোগ্য শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এজন্য তিনি গবেষণা করেছেন, গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং লেখনীর মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন, তত্ত্বের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে তত্ত্বকে তুলে ধরতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । তাঁর এই ভূমিকা তাকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকারী এই প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের অবদান নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো :
১. শাস্ত্র হিসেবে ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠা; ২. সর্বজনীন প্রয়োগযোগ্য বিষয় হিসেবে শাস্ত্রের উপস্থাপনা; ৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ নির্দিষ্টকরণ; ৪. ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কাজ নির্দিষ্টকরণ; ৫. ব্যবস্থাপনার নীতিমালা নির্দেশ; ৬. প্রতিটা কাজে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত; ৭. ব্যবস্থাপকীয় যোগ্যতা সম্পর্কে নির্দেশ ও ৮. গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন ও তত্ত্বের স্বীকৃতি আদায় |
উপরের ছকে উল্লেখ অবদানসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:
১. শাস্ত্র হিসেবে ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠা (Establishing management as a subject): ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির ন্যায় ব্যবস্থাপনাও একটা শাস্ত্র বা বিষয়-এ বিষয়টি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেন হেনরি ফেয়ল । ১৯১৬ সালে ফ্রেন্স ভাষায় লিখিত তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ Administration industriélé ét général ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে General and Industrial Management নামে প্রকাশিত হয় । যা মার্কিনমুলুকে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে । এতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে, ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের একটা পৃথক শাখা, সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদান সম্ভব । এ জন্যই তিনি ব্যবস্থাপনার কাজ, মূলনীতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরবর্তী আলোচনা ও গবেষণার দুয়ার খুলে দিয়েছেন । যার পথ ধরে ব্যবস্থাপনা আজ একটা সমৃদ্ধ শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে ।
২. সর্বজনীন প্রয়োগযোগ্য বিষয় হিসেবে শাস্ত্রের উপস্থাপন (Presenting the subject as an universal application): হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপনাকে শুধুমাত্র ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র হিসেবে নয়, এটাকে সর্বজনীন বিষয় হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি বলেছেন, গৃহস্থালী থেকে শুরু করে সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়সহ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে এরূপ শাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োগ সম্ভব এবং সবাই এ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উপকৃত হতে পারে । দু'হাজার বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ব্যবস্থাপনাকে যে সর্বজনীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন হেনরি ফেয়ল তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সেই বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন ।
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ নির্দিষ্টকরণ (Specifying the activities of industrial establishment): একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ কী হতে পারে তা তিনি নির্দিষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। এথেকে কাজের বিভাগীয়করণ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার প্রমাণ মিলে । তিনি মনে করেছেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজকে ছয়টা স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করা যেতে পারে । সেই সঙ্গে তিনি উক্ত বিভাগের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হতে পারে তারও দিক- নির্দেশ করেছেন । এজন্য তাঁকে ব্যবস্থাপনার কার্যভিত্তিক মতবাদের উদ্ভাবক বলা হয়ে থাকে । তাঁর নির্দেশিত কাজসমূহ নিম্নরূপ :
১. কারিগরি কার্যাবলি (উৎপাদন, নির্মাণ, সংযোজন);
২. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (ক্রয়, বিক্রয়, বিনিময়);
৩. অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি (মূলধনের অনুসন্ধান ও এর কাম্য ব্যবহার);
৪. নিরাপত্তা কার্যক্রম (সম্পত্তি ও ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ);
৫. হিসাবরক্ষণ; (জমা-খরচ, মূল্য, পরিসংখ্যান) ও ৬. ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ) ।
৪. ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কাজ বা উপাদানসমূহ নির্দিষ্টকরণ (Specifying the functions or elements of management process): ব্যবস্থাপনার কাজ কি এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ের ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ ব্যাপক চিন্তা-গবেষণা করলেও সর্ব প্রথম হেনরি ফেয়ল এর পাঁচটি কাজ নির্দিষ্ট করেন; যা অদ্যাবধি ব্যবস্থাপনার মূল কাজ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, "To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and to control." অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশদান, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা ।
৫. ব্যবস্থাপনার নীতিমালা নির্দেশ (Indicating the principles of management): প্রতিটা বিষয় সংশ্লিষ্ট কতকগুলো মূলনীতি থাকে । যে নীতির আলোকে শাস্ত্র সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বিকশিত হয় । ফেয়ল সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যবস্থাপনার ১৪টি মূলনীতি উপস্থাপন করেছিলেন- যা অদ্যাবধি ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায় পরীক্ষিত সত্য হিসেবে প্রয়োগযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে । এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনার নীতি বা আদর্শ শিরোনামে তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।
৬. প্রতিটা কাজে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত (Focusing the responsibility management in every organisational function) : ফেওল ব্যবস্থাপনার কাজই শুধু নির্দিষ্ট করেননি এ সকল কাজে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কী সেই নিয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি একজন সংগঠক বা ব্যবস্থাপকের ১৬টি ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্বের কথা বলেছেন; যা নিম্নরূপ:
১. বিচক্ষণভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
২. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, সম্পদ ও প্রয়োজনের সঙ্গে নিয়োজিত জনশক্তি ও উপকরণ সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা দেখা;
৩. একটি একক, দক্ষ ও শক্তিশালী কর্তৃত্বকাঠামো স্থাপন করা;
৪. বিভিন্ন কাজ এবং প্রচেষ্টার সমন্বয়সাধন করা;
৫. পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা;
৬. দক্ষ কর্মী নির্বাচন এবং সঠিক স্থানে নিয়োগের ব্যবস্থা করা;
৭. দায়িত্ব স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়ন করা;
৮. উদ্যোগ গ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করা;
৯. প্রদত্ত সেবার জন্য ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা;
১০. দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান প্রয়োগ করা;
১১. শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে কি না তা দেখা;
১২. সাধারণ স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান প্রদান নিশ্চিত করা;
১৩. আদেশের ঐক্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া;
১৪. বৈষয়িক এবং মানবিক দু'ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন তত্ত্বাবধান করা;
১৫. প্রত্যেক কাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা; ও
১৬. নিয়মকানুনের বাড়াবাড়ি বা লালফিতার দৌরাত্ম্য এবং কাগুজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করা ।
৭. ব্যবস্থাপকীয় গুণ সম্পর্কে নির্দেশ (Indicating the managerial quality): হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপকদের কাজ ও দায়িত্ব ছাড়াও ব্যবস্থাপকদের যোগ্যতা ও জ্ঞান সম্পর্কেও দিক-নির্দেশ করেছেন । তাঁর মতানুসারে একজন ব্যবস্থাপকের নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক :
ক) স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতা;
খ) বুদ্ধিমত্তা ও মানবিক শক্তি;
গ) নৈতিক গুণাবলি;
ঘ) সাধারণ শিক্ষা;
ঙ) বাণিজ্যিক, কারিগরি ও অন্যান্য কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান এবং
চ) প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিশেষ জ্ঞান ।
৮. গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন ও তত্ত্বের স্বীকৃতি আদায় (Forming research organisation and acquiring the acceptance of concept) : হেনরি ফেয়ল তাঁর প্রশাসনিক তত্ত্বের উন্নয়ন ও জনপ্রিয় করার জন্য দু'টি বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করেন । যা তত্ত্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে পরবর্তীতে ভূমিকা রেখেছে । যা নিম্নরূপ :
ক) প্রশাসনিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (Establishing centre for administrative studies): তিনি তাঁর প্রশাসনিক তত্ত্বের উন্নয়নের জন্য Centre of Administrative Studies প্রতিষ্ঠা করেন । সেখানে তিনি লেখক, দার্শনিক, প্রকৌশলী, শিল্পপতিসহ বিভিন্ন পেশার লোকদের নিয়ে সাপ্তাহিক সভার ব্যবস্থা করতেন । এসব সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতেন। এই কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় ফেয়লবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
খ) তত্ত্বের প্রসারে ব্যবস্থা গ্রহণ (Taking steps for widening concept): তিনি তাঁর নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য ফ্রান্সের সরকারকে উৎসাহিত করার চেষ্টা চালান । ১৯২৩ খিস্টাব্দে ব্রাসেসে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন । ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের অধিবেশনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক তত্ত্বের গুরুত্বের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন । এভাবেই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রসার ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন ।
উপসংহারে বলা যায়, ব্যবস্থাপনা বিষয়কে হেনরি ফেয়ল যেভাবে বুঝেছিলেন, যেভাবে একে শাস্ত্র হিসেবে চিন্তা ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সবার জন্য উপযোগী শাস্ত্র ও পাঠ্য বিষয় হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন সেজন্য ইতিহাসে তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উদগাতা হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন । আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন হেনরি ফেয়লের নাম ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ইতিহাসে উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে থাকবে ।
মি. সাইফুল সানমুন গ্রুপের একটা শিল্প ইউনিটের ব্যবস্থাপক । ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু বিষয়ে সমস্যা থাকলেও বিভাগগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন । ফলে তার শিল্প ইউনিটটি ভালো মুনাফা করছে । অন্যদিকে মি. শরিফুল আরেকটি শিল্প ইউনিটের ব্যবস্থাপক । তিনি সৎ ও উত্তম স্বভাবের মানুষ। কিন্তু তার অধীনস্ত বিভাগগুলো তিনি সঠিকভাবে চালাতে ব্যর্থ হচ্ছেন । অধস্তনরা সন্তুষ্ট থাকলেও শিল্প ইউনিটটি প্রত্যাশিত মুনাফা করতে পারছে না । মাঝে মধ্যে মি. সাইফুল সম্পর্কে কিছু অভিযোগ হেড অফিসে আসলেও মালিক পক্ষ তার ওপর সন্তুষ্ট । এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক হিসেবে কে দক্ষ এ বিচারে মি. সাইফুল নিশ্চয়ই এগিয়ে থাকবেন । কারণ ব্যক্তি হিসেবে কিছু দুর্বলতা থাকলেও ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতার পরিচয় দিতে পারছেন । তাই যাকে যেখানে যে উদ্দেশ্যে কাজ দেয়া হয়েছে তিনি সেটা কতটা সাফল্যের সাথে পালন করতে পারছেন তার ওপরই ব্যবস্থাপকের কার্যদক্ষতা নির্ভরশীল ।
সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে ও কম খরচে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারাই হলো দক্ষতা । ব্যবস্থাপকের দক্ষতা বলতে একজন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে যোগ্যতার সঙ্গে এবং স্বল্প ব্যয়ে সম্পাদন করার সামর্থ্যকে বুঝায় । ন্যূনতম শক্তি, অর্থ, সামর্থ্য ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি তাই একজন ব্যবস্থাপকের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল । ব্যবস্থাপকের এরূপ দক্ষতা তার কতিপয় জ্ঞান, গুণ ও সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যার বিবেচনায় একজন ব্যবস্থাপকের কতিপয় গুণ বা দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেই ব্যবস্থাপক যতবেশি সবগুলো দক্ষতা অর্জন করতে পারেন ততই তিনি আদর্শ ও দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে গণ্য হন । একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের যে সকল দক্ষতা থাকতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :
১. কারিগরি দক্ষতা (Technical skill) : প্রতিটা কাজ সম্পাদনে যে পদ্ধতি, কৌশল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারা কারিগরি দক্ষতা হিসেবে গণ্য। প্রতিটা কাজের সাথেই কমবেশি কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে । কম্পিউটারে একজন কর্মী কাজ করছে । এর সংশ্লিষ্ট প্রতিটা বিষয় কর্মীর জানা থাকলে সে যেভাবে দ্রুত কাজটা করতে পারবে আরেকজন কম জানা কর্মীর পক্ষে তা সম্ভব হবে না । এক্ষেত্রে পার্থক্যই হলো কারিগরি দক্ষতা । একজন উকিল একটা কেস যেভাবে সুন্দর করে সাজান ও বক্তব্য তুলে ধরেন আরেকজন সেভাবে পারে না । এক্ষেত্রে পার্থক্য কারিগরি দক্ষতার । কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জ্ঞান যেমনি কারিগরি দক্ষতা তেমনি কোম্পানির হিসাব সংরক্ষণ, উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) তৈরি, হিসাব নিরীক্ষার জ্ঞানও কারিগরি দক্ষতার আওতাধীন ।
২. মানবীয় বা আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (Human or Interpersonal skill) : মানুষের সাথে মিশতে পারার এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে কাজ আদায় করতে পারার দক্ষতাকেই মানবীয় বা আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বলে । এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দলকে বুঝে সেভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, নিজস্ব চিন্তার প্রতি তাদের সমর্থন আদায় এবং প্ররোচিত ও উৎসাহিত করার সামর্থ্য গুরুত্বপূর্ণ । ব্যবস্থাপনার কাজ মূলত মানুষ চালানো। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন মানুষের সাথে ব্যবস্থাপককে মিশতে হয়, মতবিনিময় করতে হয় । তাদের প্রত্যাশা ও সমস্যা বুঝতে হয়, তাদের মনের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে নিজের কাজটা করিয়ে নিতে হয় । তাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানবীয় দক্ষতা খুবই আবশ্যক বিবেচিত হয়ে থাকে ।
৩. ধারণাগত বা কল্পনা সংক্রান্ত দক্ষতা (Conceptual skill) : ভবিষ্যৎ অবস্থা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম ধারণা করতে পারার সামর্থ্যকেই ব্যবস্থাপকের কল্পনা সংক্রান্ত দক্ষতা বলে । একজন ব্যবস্থাপকের প্রথম কাজই হলো পরিকল্পনা গ্রহণ । এই পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বানুমানের সাথে সম্পৃক্ত। সঠিকভাবে পূর্বানুমান করে পরিকল্পনা গ্রহণ, সিদ্ধান্ত প্রদান ইত্যাদি তাই ব্যবস্থাপকের কল্পনা সংক্রান্ত দক্ষতার সাথে সম্পৃক্ত । আগাম কোনো বিষয়ে ধারণা করতে পারাই শুধু নয় উদ্ভূত অবস্থায় কী ধরনের কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সর্বোচ্চ সুফল লাভ করা যাবে এ বিষয়ে ধারণা করতে পারাও এরূপ দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত । প্রয়োজনীয় নীতি-কৌশল নির্ধারণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় বিধায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহীদের এ ধরনের দক্ষতার অধিক প্রয়োজন পড়ে ।
৪. সমস্যা অনুধাবনের দক্ষতা (Diagnostic skill) : কোনো সমস্যা ও এর প্রকৃতি দ্রুত আঁচ করতে পারার সামর্থ্যকেই সমস্যা অনুধাবনের দক্ষতা বলে। একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে যেয়ে ব্যবস্থাপকদেরকে প্রতিনিয়তই ছোট বড় নানান ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। সমস্যার প্রকৃতি এমন যে, এটাকে বুঝে শুরুতেই তা সমাধা করা গেলে ভবিষ্যতে সেটি বড় বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে না। একজন ডাক্তার যদি রোগীর রোগকে শুরুতেই সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেন তবে রোগ নিরাময়ে তা যেমনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে একজন ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রেও সেভাবে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো দ্রুত শনাক্ত করতে পারার দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় । এরূপ সমস্যা বোঝার সাথে সমাধানের পন্থা বা করণীয় নির্ধারণের বিষয়ও এরূপ দক্ষতার অধীন। প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের জন্য এরূপ দক্ষতার অধিক প্রয়োজন পড়ে ।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন পরিমাণের কারিগরি, মানবীয় ও ধারণাগত জ্ঞান বা দক্ষতা থাকতে হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা কতটা থাকা আবশ্যক তা নিম্নের রেখাচিত্রে প্রদর্শিত হলো :
বর্তমানকালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপায়-উপাদানের মধ্যে দক্ষ ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সকল মহলেই স্বীকৃত । একই স্থানে একই পরিমাণে অর্থ ও উপাদান বিনিয়োগের পরও দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে সফলতা অর্জনে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায় তার মধ্যে মূল পার্থক্য নির্ধারণকারী উপাদান হলো ব্যবস্থাপকের গুণাবলির ভিন্নতা । ব্যবসায়ের সফলতার জন্য একজন ব্যবস্থাপকের যে সকল গুণ কম-বেশি থাকা উচিত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :
১. সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান (General education and knowledge) : বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের একজন ব্যবস্থাপককে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হলে তার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া উচিত । সাংগঠনিক পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান একজন ব্যবস্থাপককে তার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে ।
২. অভিজ্ঞতা (Experience) : অভিজ্ঞতা বলতে কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে অর্জিত ও লব্ধ জ্ঞানকে বুঝায় । ব্যবস্থাপনা একদিকে কলা ও অন্যদিকে বিজ্ঞান। তাই কলা হিসেবে একজন ব্যবস্থাপকের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য। বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও কার্যকলাপের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা একজন ব্যবস্থাপককে পূর্ণতা দান করে । শিক্ষিত কম হওয়ার পরও যারা ব্যবসায়ে ভালো করছেন, এটা সম্ভব হয়েছে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণেই ।
৩. শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য (Physical and mental abilities) : শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, শক্তি ও দৃঢ়তাকে এ ধরনের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় । একজন ব্যবস্থাপককে বিশেষত শীর্ষ নির্বাহীদের ক্ষেত্রবিশেষে ২৪ ঘন্টা কাজ করতে হয় । তাই কর্তব্য কাজে তাদের যথেষ্ট পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক । সেই সাথে নানা প্রতিকূল অবস্থা ও ঝামেলার মধ্যে তাকে চলার জন্য যথেষ্ট মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ ও দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন পড়ে । অন্যথায় দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা তার পক্ষে সম্ভব হয় না ।
৪. আন্তরিকতা ও সংকল্পবদ্ধতা (Sincerity and determination) : কোনো কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্য-কাজে একাগ্র ও মনোযোগী হলে তাকে আন্তরিকতা বলে । একজন ব্যবস্থাপক যদি তার কর্তব্য কাজে আন্তরিক না হয় এবং কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে না পারে তবে তার পক্ষে ভালো ব্যবস্থাপক হওয়া সম্ভব নয় । সেই সাথে একজন ব্যবস্থাপক এ পেশায় ব্যক্তিক উন্নয়নের ব্যপারে সংকল্পবদ্ধ না হলে তার পক্ষে ভালো ব্যবস্থাপক হওয়া সম্ভব হয় না । এরূপ গুণ থাকলে অনেক কম যোগ্য ব্যক্তিও নিজস্ব পেশায় ভালো করতে পারে ।
৫. যোগাযোগ দক্ষতা (Communicative skill) : অন্যের বা অন্যদের নিকট সঠিক সময়ে সঠিক উপায় বা পদ্ধতিতে নিজের বক্তব্য কার্যকরভাবে তুলে ধরে উদ্দেশ্য অর্জনের সামর্থ্যকে যোগাযোগ দক্ষতা বলে । বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও কাজ আদায়ে একজন ব্যবস্থাপকের যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হয় । যে ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে যতবেশি যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন কার্যক্ষেত্রে তার পক্ষেই ততবেশি কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়ে থাকে । তাই সকল অবস্থায় যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সঠিক তথ্য জানা ও জানানো এবং সহজে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ্যার্জনের গুণ ব্যবস্থাপকের থাকা উচিত ।
৬. অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা (Power to motivate) : অনুপ্রাণিত করা বলতে অন্যদেরকে উৎসাহিত, শক্তি সঞ্চারিত ও কাজে উদ্দীপ্ত করাকে বুঝায় । ব্যবস্থাপনার কাজ হলো অন্যদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করিয়ে নেয়া । এরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে সংশ্লিষ্টদের অনুপ্রাণিত করা অপরিহার্য । তাই সহজে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে অনুপ্রাণিত ও প্ররোচিত করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপকের একটি অন্যতম গুণ হিসেবে বিবেচিত ।
৭. প্রজ্ঞা বা দূরদর্শী (Fore-sight) : জ্ঞানচক্ষু বা বিশেষ জ্ঞান দ্বারা ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি বা বুঝতে পারার সামর্থ্যকে প্রজ্ঞা বা দূরদর্শী বলে । একজন ব্যবস্থাপককে সব সময়ই পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় । তাই ব্যবস্থাপক যদি বর্তমান অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক অনুমান করতে ব্যর্থ হয় তবে তার পক্ষে কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না । একজন দূরদর্শী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যোগ্য ও সফল ব্যবস্থাপক হিসেবে সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে ।
৮. তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা (Sharp intelligence) : বোধশক্তি, বিচারশক্তি, জ্ঞান ও মেধাশক্তির সম্মিলিত রূপকে বুদ্ধিমত্তা বলে । একজন ব্যবস্থাপককে সকল অবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে যেতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন । সকল পক্ষের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রেখে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাই প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া ব্যবস্থাপকের একটি অন্যতম গুণ ।
৯. সাহসিকতা (Courage) : যে কোনো পরিস্থিতিতে ভীত না হয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে সামনে এগিয়ে যাওয়ার গুণকেই সাহসিকতা বলে । ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকি সব সময়ই জড়িত । যে কোনো নতুন উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে । তারপরও ব্যবসায় পরিচালনায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানারূপ বিপত্তি লক্ষ করা যায় । সকল অবস্থায় দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সাহসী হতে হয় ।
১০. সংযত ব্যক্তিত্ব (Pleasant personality) : চিন্তা, কথা, কাজ ও আচরণে কোনো ব্যক্তি ভদ্র, মার্জিত, বিনয়ী, দৃঢ় ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হলে অন্যের নিকট ব্যক্তির যে আকর্ষণীয় রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে ব্যক্তিত্ব বলে । বিচিত্র মনের কর্মী ও বিচিত্র পরিবেশের মধ্যেও সবদিক বজায় রেখে চলতে হলে ব্যবস্থাপককে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে । যা অন্যদের নিকট ব্যবস্থাপককে আকর্ষণীয় করে তোলে ।
উপসংহারে বলা যায়, অন্যকে দিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে কাজ করাতে হলে একজন ব্যবস্থাপকের উপরোক্ত গুণাবলি থাকা আবশ্যক । যে ব্যবস্থাপকের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলির সমাহার বেশি ঘটে কার্যক্ষেত্রে তার পক্ষেই তত বেশি সফলতা অর্জন সম্ভব হয়।
যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল জনশক্তি ও উপায়-উপকরণকে লক্ষ্যপানে পরিচালিত করেন বা নেতৃত্ব দেন। তাদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা বা ভূমিকা প্রতিষ্ঠানকে সবসময় গতিশীল রাখে । পরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্যে ব্যবস্থাপকগণ সবসময় ব্যাপৃত থাকেন। সীমিত সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় ও বস্তুগত উপকরণাদিকে কাজে লাগানোর জন্য একজন ব্যবস্থাপক সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালান । তাই একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের ভূমিকা বা প্রাত্যহিক কাজ প্রতিষ্ঠানে কি হওয়া উচিত এ নিয়ে বিভিন্ন মনীষী গবেষণা চালিয়েছেন । এতে একজন ব্যবস্থাপকের প্রতিদিন তিন ধরনের ভূমিকা মুখ্য বিবেচিত হয়েছে । নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:
১. আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা (Interpersonal roles): অন্যের সাথে কথা বলা ও আলাপ-আলোচনা করার কাজকে একজন ব্যবস্থাপকের আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা বলে। একজন ব্যবস্থাপককে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে অফিসে যাওয়া বা ঢোকা থেকে শুরু করে বেরিয়ে আসা এমনকি ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ভিতরের ও বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে হয় । নির্দেশ-উপদেশ ও পরামর্শ দিতে হয়,তাদের স্বমতে নিয়ে আসতে হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয় । মাঝে মধ্যেই অধস্তনদের নিয়ে সভা করতে হয় । সমস্যা নিয়ে আলোচনা, পরামর্শ ও সমাধান দেয়ার প্রয়োজন পড়ে । বাইরের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কথা শুনতে হয়, প্রয়োজনে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয় । এর সবই একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা হিসেবে গণ্য । এরূপ ভূমিকা ব্যবস্থাপকের মানবীয় দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে । যদি একজন ব্যবস্থাপক মানুষের সাথে কথা বলতে বিরক্তবোধ করেন, কারও সাথে যোগাযোগ রক্ষায় অনীহায় ভোগেন, বিভিন্ন জনের মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগে নিরুৎসাহী হন তবে তার পক্ষে এ ধরনের ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না ।
২. তথ্য সংশ্লিষ্ট ভূমিকা (Informational roles): প্রতিদিন তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপকের কাজকেই তথ্য সংশ্লিষ্ট ভূমিকা বলে । বর্তমান যুগকে তথ্যের যুগ বলা হয় । কারণ যার কাছে যত তথ্য থাকে ততই তিনি সমৃদ্ধ বিবেচিত হন । প্রতিষ্ঠানে সমপদে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যিনি যত তথ্যসমৃদ্ধ কার্যক্ষেত্রে তার পক্ষেই তত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব । সাধারণ একজন ব্যবস্থাপকের কথাই যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে তাকে সকালে প্রতিষ্ঠানে ঢুকেই সকল কর্মী প্রতিষ্ঠানে এসেছে কি না সে বিষয়ে তথ্য নিতে হয় । কাঁচামাল আসলো কি না, উৎপাদন ঠিকমত হচ্ছে কি না, সমস্যা থাকলে সমস্যার কারণ কী, মাল বিক্রয় হচ্ছে কি না, মজুত কী রয়েছে, গ্রাহকদের প্রত্যাশা কী, তারা কেমন আচরণ করছে, প্রতিযোগীরা কী ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে ইত্যাদি নানান তথ্য তার কাছে থাকতে হয় । এরপর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ বা মালিককে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিতে হয় । বাইরের বিভিন্ন পক্ষও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে চায় । তাদেরকেও প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে । এভাবে তথ্য সংগ্রাহক, সংরক্ষক ও প্রচারক হিসেবে একটা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকের প্রাত্যহিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ।
৩. সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা (Decisional role) : প্রাত্যহিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় নির্ধারণের কাজকেই ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা বলে । একজন ব্যবস্থাপককে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা করণীয় নির্ধারণ করতে হয়, সিদ্ধান্ত দিতে হয়, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি দেখতে হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে সহযোগিতা করতে হয়, সম্পৃক্ত থাকতে হয়— যার সব কিছুই ব্যবস্থাপকের প্রাত্যহিক সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকার মধ্যে পড়ে । একজন উৎপাদন ব্যবস্থাপক সকালে অফিসে যেয়েই শুনলেন তাদের একটা মেশিন কাজ করছে না । মেরামত বিভাগকে জানিয়ে দ্রুত টেকনিশিয়ান আনতে হবে । কাঁচামাল যেটা সরবরাহ করা হয়েছে তা মানসম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনের মান খারাপ হচ্ছে । করণীয় কী তাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। প্রয়োজনে সাধারণ ব্যবস্থাপক থেকে সিদ্ধান্ত জেনে নিতে হবে । বিভাগীয় একজন ফোরম্যান অসদাচরণ করেছে তার বিষয়েও সিদ্ধান্ত দেয়া দরকার । ঊর্ধ্বতনদের দেয়া সিদ্ধান্ত অধস্তনদের জানানো ছাড়াও প্রতিদিন প্রতিনিয়ত একজন ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নমূলক নানান কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। তাই দ্রুত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারার সামর্থ্য একজন ব্যবস্থাপকের অন্যতম গুণ বিবেচিত হয়ে থাকে ।
উপায়-উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার করে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকে ব্যবস্থাপনা বলে । এ ধরনের কাজ যারা সম্পাদন করেন তাদেরকে ব্যবস্থাপক বলা হয়ে থাকে । অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার উপরিপর্যায়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে প্রশাসন বলা হয়ে থাকে । একটা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপক কার্য পরিচালনা করেন । স্তরভেদে তাদেরকে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন পর্যায়-এ তিনভাগে ভাগ করা হয় । স্তরীয় পার্থক থাকায় কার্য প্রকৃতিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও সকল পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণকেই পরিকল্পনা প্রণয়নসহ সকল ব্যবস্থাপনা কাজ কমবেশি সম্পাদনের প্রয়োজন পড়ে । পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি কৌশল নির্ধারণ করেন । অন্যদিকে তা বাস্তবায়নের জন্য মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ বিভাগীয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নিচের স্তরের ব্যবস্থাপকদের নিকট থেকে কাজ আদায়ে মুখ্য ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকেন। স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণের সুবিধার্থে ব্যবস্থাপনার উচ্চ বা শীর্ষ পর্যায়কে প্রশাসন নামে অভিহিত করা হয় । প্রশাসন হলো একটা দেহের মস্তিস্ক স্বরূপ । কারণ মস্তিস্ক করণীয় নির্ধারণ করে । আর তা বাস্তবায়িত হয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে । সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রশাসন মুখ্য করণীয় বা পকিল্পনা ও নীতি কৌশল নির্ধারণ করে আর ব্যবস্থাপনা (মধ্য ও নিম্ন পর্যায়) তা বাস্তবায়ন করে থাকে । এরূপ বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা প্রশাসনের অধীন । প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অধিক মাত্রায় প্রশাসন ভোগ করে এবং সেখান থেকে তা নিচের পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্রমান্বয়ে ন্যস্ত হয় । একটা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পর্যায়ে শীর্ষ নির্বাহীর সংখ্যা কম থাকে কিন্তু ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে ব্যবস্থাপকের সংখ্যা বেশি হয় । প্রশাসনে চিন্তনীয় বা মানসিক শ্রম সম্বলিত কাজ বেশি থাকে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার পর্যায় অনুযায়ী করণীয় (Doing) অর্থাৎ শারিরীক শ্রম নিচের পর্যায়ে বাড়তে থাকে । নিম্নে ব্যবস্থাপনার স্তর ভেদে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপস্থিতি রেখাচিত্রে তুলে ধরা হলো :
সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। সংগঠন না থাকলে যেমনি ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না তেমনি ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন ছাড়া সংগঠন কখনই অস্তিত্ব লাভ করে না । তাই অনেকে এদের সবাইকে সমার্থক গণ্য করেন । পরিভাষার দিক বিবেচনা করলে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে । প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে ব্যবস্থাপনা পর্যায় বিবেচনায় পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হলে সেক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে পৃথক রূপ প্রতিভাত হয় । সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রতিটা বিষয়ে পৃথক ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হলো :
১. সংগঠন (Organization) : প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদি সংহত ও সমন্বিত করার কৌশলকে সংগঠন বলে । সংগঠনকে প্রতিষ্ঠান অর্থে ধরা হলে-এটি হলো কতিপয় ব্যক্তির সংঘবদ্ধ সম্পর্কের কাঠামো । তাই প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে কতিপয় ব্যক্তি লক্ষ্যার্জনের জন্য একত্রে কাজ করে । ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেউ ঊর্ধ্বতন ও কেউ অধস্তন হিসেবে সম্পর্কযুক্ত থাকে । প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড যত বাড়ে ব্যবস্থাপনার পর্যায় বা স্তরও ততই বৃদ্ধি পায় । সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তরে কর্মরত নির্বাহীদের কার্যকে প্রশাসন এবং মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ে কর্মরত ব্যবস্থাপকদের কার্যকে ব্যবস্থাপনা নামে আখ্যায়িত করা হয় ।
২. ব্যবস্থাপনা (Management) : উপকরণাদিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নেতৃত্ব দান ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকে ব্যবস্থাপনা বলে । মানবীয় ও বস্তুগত উপকরণ যতোই উন্নত হোক না কেন ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা না হলে তা কার্যক্ষেত্রে কোনোই ফল দিতে পারে না । এরূপ উপকরণাদি কোথাও একত্রে থাকলেই তা সংগঠন হয় না তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে সাজিয়ে তাদের প্রত্যেকের করণীয় নির্ধারণ করে দিতে হয় । আর এভাবেই ব্যবস্থাপনা সংগঠন পরিচালনায় কার্যকর শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে ।
৩. প্রশাসন (Administration) : ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রশাসক এবং তাদের কর্মপ্রয়াস বা প্রচেষ্টাকে প্রশাসন বলে। J. W. Sheultz (শিউলজ) তাই বলেছেন, ‘যারা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন এবং যাদের অধীনে সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে তাই প্রশাসন' । প্রশাসন হলো মানব দেহের মস্তিষ্কস্বরূপ । কারণ মস্তিষ্ক করণীয় নির্দেশ করে; যা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় । প্রশাসন প্রতিষ্ঠানে নীতি ও উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের সহায়তা গ্রহণ করে ।
সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণে অলিভার শেল্ডন বিশেষভাবে প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “শিল্পের অংশ হিসেবে ব্যবস্থাপনা মূলধন ও শ্রম থেকে আলাদা এবং এটি তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত । অংশগুলো হলো-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন ।'
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রশাসনের কাজ মস্তিষ্কের ন্যায় যা নীতি-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে। সংগঠন কিভাবে চলবে ব্যবস্থাপনা তার পথ প্রদর্শন করে বা উপায়-উপকরণ কিভাবে কার্যকররূপে ব্যবহৃত হবে তার উপায় নির্দেশ করে । অন্যদিকে সংগঠন হলো উপকরণাদিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার উপায় । তাই বলা হয়ে থাকে সংগঠন বাহু, ব্যবস্থাপনা চক্ষু এবং প্রশাসন মস্তিষ্ক ।
বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে । এ দেশের ব্যবসায়ের প্রায় ৮৫% ক্ষুদ্র একমালিকানা ব্যবসায়। যেখানে ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা থাকে এক ও অভিন্ন। তাই ব্যবস্থাপনার মান এবং তা উন্নয়নের বিষয়টি সেখানে কখনই তেমন গুরুত্ব পায় না । অবশিষ্ট যা বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানেও ব্যবস্থাপক নিয়োগে তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। তাই যে কোনো বিষয় থেকে ডিগ্রি নিয়েই কোনো ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সীমাবদ্ধতায় ভোগেন । আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবস্থাপনার মান দুঃখজনক । সরকারি কর্তা ব্যক্তিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা দোষে দুষ্ট থাকেন । ক্ষমতা ভোগ ও তা প্রদর্শনেই তারা স্বাচ্ছন্দবোধ করেন । তাই ব্যবস্থাপনার মান উন্নত করে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন ও জনগণকে সেবা করার বিষয়টি কখনই গুরুত্ব পায় না। তদুপরি দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দলীয় লেজুড়বৃত্তি, নির্লজ্জ দলীয়করণ, বিভিন্নমুখী চাপ ব্যবস্থাপনাকে সবসময়ই অসহায়ত্বের সম্মুখীন করে । এর বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যা রয়েছে তাদের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের মান উন্নয়নে কিছু কর্মসূচি নিলেও দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নানান সমস্যার নিগড়ে বন্দী । নিম্নে কতিপয় সমস্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :
১. প্রতিযোগী ব্যবসায় পরিবেশের অভাব (Lack of competitive business environment) : আমাদের দেশের ব্যবসায় জগতে এখনও কার্যত একচেটিয়া ব্যবসায় পরিবেশ বিরাজমান। অদক্ষ ব্যবস্থাপনাও এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায় চালায় । নতুন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও প্রতিযোগী পরিবেশ গড়ে না ওঠার কারণেই এখানে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন চিন্তা প্রবল নয় ।
২. পেশা হিসেবে মর্যাদার অভাব (Non professionalisation of managers) : উন্নত বিশ্বে ব্যবস্থাপনা পেশা হিসেবে অনেকটা মর্যাদা পেলেও আমাদের দেশে এটি এখনও পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে এ. পেশায় এমন লোকেরা সহজেই প্রবেশ করে যাদের এ বিষয়ে কোনো প্রাথমিক জ্ঞানও নেই । তাদের পরিচালিত ব্যবস্থাপনা প্রায় ক্ষেত্রেই 'হাতুড়ে' বিষয়ে পরিণত হয় । যেটাও এ দেশে ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে একটি বড় সমস্যা।
৩. সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব (Lack of associate institution) : আমাদের দেশে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন কেন্দ্র (IBA), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPTAC)-এর মতো দু'একটা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তার কার্যক্রম তেমন বিস্তৃত নয় । বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানদানের যে পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে তাও যথেষ্ট বলা যায় না ।
৪. দক্ষ ব্যবস্থাপকের অভাব (Lack of efficient managers) : বাংলাদেশে দক্ষ ব্যবস্থাপকের তীব্র অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । ভালো উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক যারা রয়েছেন তাদের ভালো দিকগুলোও যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় না । বরং বিরূপ প্রচারণা হয় বেশি। তাই দোষ-ত্রুটিমুক্ত একদল সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপক যদি জনসমক্ষে প্রচারণা লাভের সুযোগ পেত তাহলে অনেকেই তা দেখে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষতা অর্জনে তৎপর হতো ।
৫. আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব (Absence of modern approaches) : আমাদের দেশের মালিক, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক-কর্মচারী সবাই কার্যত গতানুগতিক মানসিকতার অধিকারী। আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে তারা সচেতন নন । যে কারণে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্যম, উৎসাহ, দলীয় প্রচেষ্টা, নতুন চিন্তা-গবেষণা বাস্তব অর্থেই অনুপস্থিত । ফলে স্থবিরতা ও অদক্ষতা ব্যবস্থাপনার সর্বস্তরে বিরাজমান ।
৬. প্রশিক্ষণের অভাব (Lack of training) : আমাদের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য কোনো কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি । ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও তা কার্যত তেমন ফলপ্রদ নয় । তাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উন্নতির কথা কেউ ভাবলেও প্রশিক্ষণের অভাবে তাদের পক্ষে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয় না ।
৭. শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের অভাব (Lack of labour-management relations) : আমাদের দেশে শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক কাম্য মানের নয় । অদক্ষ ও অশিক্ষিত শ্রমিক-কর্মীরা নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে অসচেতন। ট্রেড ইউনিয়নের নামে এ দেশে যা চলছে তা ভালো কিছু নয় । বেসরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সাথে যে আচরণ করা হয় তাও অত্যন্ত দুঃখজনক । এরূপ অবস্থায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে পারে না ।
৮. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (Political instability) : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আমাদের দেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগে আরেকটি বড় বাধা। আর এরূপ অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হলো শিক্ষাঙ্গন ও শিল্প এলাকা । এ ধরনের অবস্থায় মূলত ব্যবস্থাপকদের করার তেমন কিছু থাকে না । ফলে ব্যবস্থাপনা উৎসাহ হারায় এবং স্থবির ও অদক্ষ হয়ে পড়ে ।
উপসংহারে বলা যায়, ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু প্রয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । তাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে এ দেশের সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে ।
ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো পরিকল্পনা। এটি হলো ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের ভিত্তি । ভবিষ্যতে আমরা কী চাই, কখন ও কিভাবে চাই ইত্যাদি বিষয়গুলো পূর্বে নির্ধারণ করাকেই পরিকল্পনা বলে । তাই পরিকল্পনা একটা চিন্তনীয় কাজ। চিন্তায় ভুল হলে পরিকল্পনায় তার যেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ঠিক একইভাবে পরিকল্পনায় ভুল হলে বাস্তবায়নমূলক কাজেও ভুল হয় । ফলে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব হয় না । আমরা ব্যক্তিগত কাজ করার ক্ষেত্রে যদি সারাদিনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং সে অনুযায়ী কাজ করি, তবে দেখা যাবে কাজগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে । তাই প্রতিটা কাজের পূর্বেই ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক। পরিকল্পনার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত । পরিকল্পনা নিতে গেলে বিকল্প নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও উত্তম বিকল্প গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে । এই উত্তম বিকল্প গ্রহণের কাজকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে । বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠানে ও ব্যক্তি জীবনে প্রায়শই সিদ্ধান্ত নিতে হয় । তাই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত জ্ঞান যে কোনো ব্যক্তিকেই চলার পথে কার্যকরী সহায়তা প্রদান করতে পারে ।
এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা (শিখন ফল)
১. পরিকল্পনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
২. আদর্শ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে ।
৩. পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৪. পরিকল্পনার প্রণয়নের ধাপসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
৫. পরিকল্পনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৬. পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
৭. উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবে ।
৮. একার্থক ও স্থায়ী পরিকল্পনার পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে ।
৯. উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
১১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
১২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকারী উপাদানগুলো শনাক্ত করতে পারবে ।
১৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
১৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে ।
১৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে এবং সমাধানকল্পে সুপারিশ করতে পারবে ।
কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষার্থীদের বনভোজন হবে । স্থান ঠিক হলো কুমিল্লার ময়নামতি । তারিখ ও চাঁদার হার ঠিক করে অফিসে ছাত্রছাত্রীদের টাকা জমা দিতে বলা হলো । পরবর্তী করণীয় কিছুই ঠিক না করে অধ্যক্ষ স্যার ক'দিন কলেজের বাইরে থাকলেন । টাকা কিছু জমা হলো ঠিকই কিন্তু গাড়ি, বাবুর্চী, খাবার মেন্যু কিছুই ঠিক হলো না । শেষ দিকে এসে তড়িঘড়ি করে তা ঠিক হলো কিন্তু শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হয়নি । শেষদিনেও অনেকে টাকা জমা দিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছে। ফলে প্রথমে সীট নিয়ে ঝামেলা । অনেকে রাগ করে যাবেই না । কোনোভাবে ম্যানেজ হলো । পরে দেরি করে যেয়ে সুবিধামতো স্পট পাওয়া গেল না । যাও বা মিললো খাবার দিতে দেরি হলো । মূল বিপদটা হলো যখন অনেকে খাবারই পেল না । অধ্যক্ষ স্যার ও শিক্ষকগণ খুবই মানসিক কষ্ট নিয়ে কলেজে ফিরলেন । যথাযথ পরিকল্পনার অভাবই ভোগান্তির কারণ এটা সবাই স্বীকার করছেন ।
ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্বনির্ধারিত নক্শা বা চিত্রকে পরিকল্পনা বলে । এটি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান কাজ । এটি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের ভিত্তিস্বরূপ। তাই যে কোনো কাজ শুরুর আগেই ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ ঠিক করতে হয় । তাই ভবিষ্যতে কী করা হবে এ সম্পর্কে আগাম চিন্তা-ভাবনা করে করণীয় ঠিক করাকেই পরিকল্পনা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । কী করা হবে এটি ঠিক করা যেমনি পরিকল্পনা তেমনি কখন, কোথায়, কার দ্বারা, কিভাবে, কত সময়ে কাজটি করা হবে তাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। উপরের উদাহরণটি বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, পিকনিকের স্থান, চাঁদার হার এবং কোথায় টাকা জমা হবে তা ঠিক করা হয়েছিল । কিন্তু অবশিষ্ট কাজগুলো আগে ঠিক করা, দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া, যথাসময়ে যথা উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি বিষয় না হওয়ায় পিকনিক নিয়ে এরূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।
পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্বনির্ধারিত প্রতিচ্ছবি। ব্যবস্থাপনা কার্য প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্য হতে একে স্বতন্ত্র রূপ প্রদান করেছে । নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :
১. পরিকল্পনার প্রাথমিকতা ও মুখ্যতা (Primacy of planning) : পরিকল্পনা হলো ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কাজ । এটি অন্যান্য সকল কাজের ভিত্তিস্বরূপ। কী করা হবে শুধুমাত্র এতটুকু ঠিক করাই পরিকল্পনা নয় । বরং কখন, কিভাবে, কার দ্বারা, কত সময়ে, কোন কাজ করানো হবে ইত্যাদি বিষয়ও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত । তাই সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সকল কাজেই পরিকল্পনার অনুসরণ করা হয় ।
২. চিন্তন-মনন প্রক্রিয়া (Mental-thinking process) : পরিকল্পনার বিষয়টি চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত । যদিও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয় তথাপিও এর মূল উদ্দেশ্যই থাকে চিন্তাকে অধিক কার্যকর করা। এজন্য বলা হয়, “পরিকল্পনা হলো কাজ শুরুর পূর্বে চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়া” (Process of thinking before doing)। তাই পরিকল্পনা কোনো শারীরিক বা বাহ্যিক (Physical) কাজ নয় । এটি চিন্তন-মনন প্রক্রিয়া ।
৩. ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অনুমান (Assumptions regarding future course of action): পরিকল্পনা সব সময়ই ভবিষ্যৎ অনুমানের সাথে জড়িত । এ অনুমান শুধুমাত্র কী করা উচিত বা কি করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । বরং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ বা পরিকল্পনা অঙ্গন কেমন থাকবে এবং গৃহীত পরিকল্পনা সে সকল পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তাও অনুমান করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে । অর্থাৎ সঠিক পূর্বানুমান ভবিষ্যৎ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর করতে সহায়তা করে ।
৪. পরিকল্পনার উদ্দেশ্যমুখিতা (Goal-orientation of planning) : পরিকল্পনা সবসময়ই একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরূপিত হয় । যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ১০% উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় তবে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিক্রয় বৃদ্ধি, মেশিনের শ্রমঘণ্টার অপচয় হ্রাস বা যন্ত্রপাতি উন্নয়ন, প্রয়োজনে শ্রমিক-নতুন কর্মী নিয়োগ, অতিরিক্ত কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত পরিকল্পনা নেয়ার প্রয়োজন পড়ে ।
৫. পরিকল্পনার তথ্য নির্ভরশীলতা (Dependency of information of planning) : অতীতকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা করা যায় না। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে সব সময়ই অতীতে কী ঘটেছে তার মূল্যায়ন করতে হয়। এজন্য বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দেয় । শুধু প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ই নয় বাইরের বিভিন্ন বিষয়ও বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনে বিভিন্ন পক্ষের নিকট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে হয় । এতে পরিকল্পনার মান বৃদ্ধি পায়।
৬. উত্তম বিকল্প (Best alternative) : বিকল্পসমূহের মধ্য থেকে বাস্তবতা বিবেচনায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্পটিকেই উত্তম বিকল্প বলে । পরিকল্পনা বলতে কার্যত উত্তম বিকল্প গ্রহণকে বুঝায় । উদ্দেশ্যার্জনে একাধিক বিকল্প পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে । বিকল্পসমূহের মধ্য হতে সবদিক বিচারে উত্তম বিকল্প গ্রহণই পরিকল্পনা হিসেবে গৃহীত হয় । ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে একজন ব্যক্তি যে রুট ঠিক করবে তাই পরিকল্পনার আওতায় আসবে ।
মি. হক একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপক । প্রতিষ্ঠানের প্রতিটা কাজে তিনি হিসাব করে চলেন । নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই তিনি চলতি বছরের সর্বশেষ হিসাব বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ও পূর্ববর্তী বছরগুলোর হিসাব বিবেচনায় নিয়ে তার ওপর একটা ভাবনা দাঁড় করান । অতঃপর বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের মূল প্রতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন । ধরা যাক, নির্ধারিত হলো সামনের বছরে চলতি বছরের তুলনায় ২০% বিক্রয় বৃদ্ধি করতে হবে । সে অনুযায়ী তিনি উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপকদের স্ব স্ব বিভাগীয় পরিকল্পনায় ৩০% বৃদ্ধির টার্গেট ধরে ত্রৈমাসিক বিভাজনসহ বিভাগীয় পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দিলেন । বিভাগসমূহের লিখিত পরিকল্পনা তার নিকট জমা হলে তিনি ত্রুটি- বিচ্যুতি সংশোধন করে পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন । অতঃপর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও বিভাগীয় পরিকল্পনাসমূহ লিখিত আকারে বিভাগগুলোতে পাঠানো হলো । প্রয়োজনে তিনি স্ব-স্ব বিভাগে যেয়ে বসে তাদের টার্গেট ও করণীয় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন । সমস্যা থাকলে তার সমাধানের পন্থাও নির্দেশ করলেন । বছর শেষে দেখা গেল প্রতিষ্ঠানটি তার টার্গেট পূরণে সফল হয়েছে ।
মি. হকের প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পরিকল্পনাকে উত্তম পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হলে তার যে সকল বৈশিষ্ট্য আলোচনার দাবি রাখে তা নিম্নরূপ:
১. সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য (Specific objective) : কাঙ্ক্ষিত ফল যাকে ঘিরে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকেই প্রতিষ্ঠানের বা কাজের উদ্দেশ্য বলে । পরিকল্পনা প্রণয়নে এর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রথমেই নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক । উদ্দেশ্যবিহীন পরিকল্পনা কখনই কার্যকর ফল দিতে পারে না । তাই একটি আদর্শ পরিকল্পনা অবশ্যই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক হয়ে থাকে । প্রতিষ্ঠানে সামগ্রিক একটা উদ্দেশ্য যেমনি থাকে তার আলোকে প্রত্যেক বিভাগ-উপবিভাগেরও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ।
২. বাস্তবমুখিতা (Reality oriented) : পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী হতে হয়। বাস্তবমুখিতা বলতে ভবিষ্যৎ অবস্থা বিবেচনায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নযোগ্য হওয়াকে বুঝায় । বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং তার আলোকে একটি বড় ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই তা সুফল দিতে পারে না। অবাস্তব পরিকল্পনা সবার মাঝে তাৎক্ষণিক কিছুটা আশাবাদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও কার্যক্ষেত্রে তা কখনই কাঙিক্ষত ফল দেয় না। বরং পরবর্তীতে তা হতাশা ও নানান ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে ।
৩. গ্রহণযোগ্যতা / পালনযোগ্যতা (Acceptability) : পরিকল্পনা যারা বাস্তবায়ন করবে তাদের কর্তৃক উক্ত পরিকল্পনা পালনযোগ্য মনে করে সাদরে গ্রহণ করাকেই পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা বলে । পরিকল্পনা যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে তাদের নিকট এটি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কর্মীরা যদি পরিকল্পনাকে কোনো কারণে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে না পারে তবে তার সঠিক বাস্তবায়ন আশা করা যায় না । এজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বা অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা (Participative management)-এর প্রতি আজকাল গুরুত্বারোপ করা হয় ।
৪. সঠিক পথ-নির্দেশনা (Proper guidance) : বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করণীয় বিষয়ে পরিকল্পনা থেকে যেন নির্দেশনা পাওয়ার সম্ভব হয় এটা নিশ্চিত করাকেই পরিকল্পনার সঠিক পথনির্দেশনা বলে । একটা প্রণীত পরিকল্পনা অবশ্যই সঠিক পথ নির্দেশক হওয়া উচিত। যাতে তা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সঠিক পথ-নির্দেশ করতে পারে। এজন্যই Koontz & O. Donnell পরিকল্পনাকে দর্পন (Looking glass) এর সাথে তুলনা করেছেন । কী কী কাজ করা হবে পরিকল্পনা তার দিক নির্দেশে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক । এজন্য যতদূর সম্ভব পরিকল্পনা বিশদ বর্ণিত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া উত্তম ।
৫. সমন্বয় ও যোগসূত্র (Co-ordination and linkage) : বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনাকে মূল লক্ষ্যের আলোকে একসূত্রে সংযুক্ত করার কাজই হলো পরিকল্পনায় সমন্বয় ও যোগসূত্র স্থাপন । প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরেই যেহেতু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তাই একটি আদর্শ পরিকল্পনায় সকল স্তর বা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও যোগসূত্র রক্ষা করা হয়ে থাকে । প্রতিষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা-পূর্ব সময়ে গৃহীত পরিকল্পনার সাথে এবং বিভিন্ন স্তরে গৃহীত পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত হওয়া আবশ্যক। বিক্রয় বিভাগ ও উৎপাদন বিভাগের পরিকল্পনায় যোগসূত্রিতা না থাকলে উভয় পরিকল্পনায় যে অকার্যকর-তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।
৬. নমনীয়তা (Flexibility) : পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানের সামর্থ্যকে নমনীয়তা বলে। একটি উত্তম পরিকল্পনায় নমনীয়তার সুযোগ থাকা আবশ্যক । সম্ভাব্য যে সকল আবস্থার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে ধরে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তা সবসময় মিলবে এমন আশা করা যায় না । তাই অবস্থার পরিবর্তন হলে যতটা সম্ভব দ্রুততার সাথে পরিকল্পনা সংশোধন করতে হয়। পরিকল্পনা প্রণেতাগণ যদি আগে থেকে বিকল্প অবস্থায় করণীয় ঠিক করে রাখেন সেক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন সহজ হয়ে থাকে। যাকে পরিস্থিতিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে । নমনীয় বাজেট (Flexible budget) তৈরি এর একটি উত্তম উদাহরণ ।
শুভ খেলাধুলায় খুবই ভালো । ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন সবই ভালো খেলে । তার সতীর্থ ইমন শুধু ক্রিকেট খেলে । শুভ কোনো খেলাতেই স্থানীয় পর্যায়ের গণ্ডি পেরুতে পারেনি । কিন্তু ইমন এখন জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলছে । ইমনের ভালো করার কারণ সে লক্ষ্য ঠিক করে সেভাবে পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে । যা শুভর পক্ষে সম্ভব হয়নি । ব্যবস্থাপনা বিষয়ের অন্যতম লেখক অধ্যাপক নিউম্যান তাঁর Administrative Action গ্রন্থে একটা উদাহরণ দিয়ে লক্ষ্য ও পরিকল্পনার মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ‘একটা বিমান সংস্থা তার কার্যক্রম নির্ধারণ, এয়ারক্রাফট সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচন, কর্মী সংগ্রহ ইত্যাদি যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে অবশ্যই স্থির করবে যে, তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য যাত্রী পরিবহন না মালামাল পরিবহন ।' এটা ঠিক না। হলে কখনই পরিকল্পনা গ্রহণ ও লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না ।
পরিকল্পনার অভিপ্রেত ফলকে লক্ষ্য বলে । পরিকল্পনা সবসময়ই লক্ষ্যাভিমুখী । লক্ষ্য নির্ধারণ যেমনি একটি পরিকল্পনা তেমনি এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কর্মপন্থা ঠিক করা হয় তাও পরিকল্পনা । মানুষ ভাল-মন্দ যা-ই করুক না কেন তার একটা লক্ষ্য থাকে । কারণ সচেতন মানুষ লক্ষ্যহীন উদভ্রান্তের মতো কোনো কাজ করতে পারে না । কাজ শুরুর পূর্বেই তার লক্ষ্য কী অর্থাৎ এ কাজ থেকে কী পাওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা বুঝে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে । অতঃপর তার আলোকে পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে থাকে ।
ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া যার অধীনে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্য পারস্পরিক ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন হয় এবং তা নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে । তাই ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূলে থাকে একটা লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নেওয়া হয় ও ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় । ধরা যাক, একটা প্রতিষ্ঠান আগামী বছরে তাদের বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫% বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে । এখন সেভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ প্রসার কর্মসূচি তৈরি, বাজার সম্প্রসারণ, অর্থসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা নেবে । প্রত্যেকটা বিভাগ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে অধিলক্ষ্য (Sub-goal) নির্ধারণ করবে ও সে অনুযায়ী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে । এভাবে লক্ষ্য সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে । বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে :
লক্ষ্যের প্রকারভেদ (Types of goal in plan)
লক্ষ্য একটা সাধারণ পরিভাষা । পরিকল্পনার ভিন্নতা থাকায় লক্ষ্যকেও নানানভাবে নানান অভিধায় নামকরণ করতে দেখা যায় । প্রতিষ্ঠান ভেদেও একেক স্থানে লক্ষ্যকে একেক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিচারে বিষয়টিকে নিম্নে আলোচনা করা হলো :
ক) প্রকৃতি বিচারে:
১. উদ্দেশ্য (Objectives) : উদ্দেশ্য হলো অভিপ্রেত লক্ষ্য যাকে ঘিরে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় । যে কোনো কার্য সম্পাদনের পিছনে সম্পাদনকারীর একটা উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পিছনে ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা। একটা ক্লাব, পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে । যাকে ঘিরেই তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় । প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, দূরকল্পনা বা সাধারণ উদ্দেশ্যকে (Vision) বলে ।
২. মিশন (Mission): মিশন লক্ষ্যের আরেকটি রূপ । ইংরেজি Mission শব্দের বাংলা অর্থ হলো ব্রত, সাধনা বা প্রচেষ্টা । পূর্বে মিশন শব্দটি ধর্মীয় ব্রত বা সাধনার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হলেও এখন সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানেই মিশন শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্নত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রয়াসকে মিশন হিসেবে দেখা যায়। একটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে ‘উত্তম ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন'কে মিশন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে । তাই মিশন কর্মলক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত ।
৩. সময় লক্ষ্য (Time Goal): সময় লক্ষ্যও লক্ষ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । একটা কাজ কত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এটা নির্ধারণকেই সময় লক্ষ্য বলে । অনেক সময় এরূপ লক্ষ্য সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যবিন্দু বিবেচিত হয় । যেমন- একটা নির্মাণ কোম্পানি বিল্ডিং নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছে । তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে দু'বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে অন্যথায় নির্মাণ চুক্তি বাতিল হবে এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে । এক্ষেত্রে দু'বছর সময়কে সময় লক্ষ্য বলা হবে ।
৪. বাজেট লক্ষ্য (Budget goal): প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত ফলাফল যখন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় তাকে বাজেট লক্ষ্য বলে । প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়, প্রাপ্তি-প্রদান ইত্যাদি আর্থিক অংককে সাধারণভাবে বাজেট মনে করা হয় । তবে সেক্ষেত্রে ঐ বাজেটের একটা লক্ষ্য থাকতে পারে যাকে বাজেট লক্ষ্য বা টার্গেট বলা হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বিগত বছরের তুলনায় ২৫% বৃদ্ধির লক্ষ্যকে বাজেট লক্ষ্য বলা যায়। এভাবে উৎপাদন বিভাগের এক লক্ষ একক পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ৫০০ শিক্ষার্থী ভর্তির পরিকল্পনাকে বাজেট লক্ষ্য বা টার্গেট হিসেবে গণ্য করা যায় । যা লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে ।
খ) সাংগঠনিক স্তর বিচারে:
১. স্ট্র্যাটিজিক লক্ষ্য (Strategic goal): প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন তাকে স্ট্র্যাটিজিক লক্ষ্য বলে । দশ বছরের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের মুনাফার হার ২০% এ উন্নীতকরণ, পাঁচ বছরের মধ্যে ঢাকায় বিভিন্ন মার্কেটে আরও নতুন তিনটি শাখা দোকান প্রতিষ্ঠা, পাঁচ বছরের মধ্যে বিক্রয়ের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা তিন গুণ বৃদ্ধি ইত্যাদি এরূপ লক্ষ্যের উদাহরণ ।
২. বিভাগীয় বা কৌশলগত লক্ষ্য (Departmental or tactical goal): প্রতিষ্ঠানের মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ স্ট্র্যাটিজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন তাকে বিভাগীয় বা কৌশলগত লক্ষ্য বলে । বিক্রয় বৃদ্ধির স্ট্র্যাটিজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বিভাগ এক বছরে ২৫% উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । এটিকে উৎপাদন বিভাগের বিভাগীয় বা কৌশলগত লক্ষ্য বলা হবে ।
৩. কার্যসম্বন্ধীয় লক্ষ্য (Operational goal): প্রতিষ্ঠানের নিচের পর্যায়ের উপবিভাগ বা কর্মকেন্দ্রগুলোতে বিভাগীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় তাকে কার্যসম্বন্ধীয় লক্ষ্য বলে । শ্রম ঘন্টার অপচয় রোধের জন্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যে, যে কোনো মেশিনে ত্রুটি দেখা দেয়ার তিন ঘন্টার মধ্যে তা অবশ্যই মেরামত করা হবে- এটি কার্যসম্বন্ধীয় লক্ষ্যের উদাহরণ ।
পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এটি একটি চিন্তন-মনন প্রক্রিয়া; যা প্রণয়নকালে ভবিষ্যৎ নানান বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে। এটি কোনো আবেগ বা শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর কার্য নয়, বরং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচিত হয় । পরিকল্পনার ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত হওয়ায় এর উপরিস্তরে দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ে ঐ পরিকল্পনার আলোকে বিভাগীয় ও কার্যভিত্তিক যে সব পরিকল্পনা নেয়া হয় সেখানে বিচার-বিশ্লেষণের আবশ্যকতা স্বভাবতই কমে আসে । তথাপিও কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সকল ধারাবাহিক পদক্ষেপ অনুসৃত হয় তা নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হলো :
রেখাচিত্রে প্রদর্শিত পদক্ষেপসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :
১. ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন (Evaluating future) : প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি (Strength) ও দুর্বলতা (Weakness) এবং বাহ্যিক সুযোগ (Opportunity) ও বাধা (Threat) চিন্তায় নিয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থা কেমন হতে পারে তার আগাম মূল্যায়নকে পরিকল্পনা প্রণয়নে ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন বলে । এক্ষেত্রে বাইরের বিভিন্ন পক্ষ; যেমন- গ্রাহক, প্রতিযোগী, সরবরাহকারী ইত্যাদি পক্ষের প্রতিক্রিয়া গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে । অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়; যেমন- আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতির মান, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের দক্ষতা ইত্যাদিও এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয় । যার আলোকেই ভবিষ্যৎ মূল্যায়নে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় ।
২. লক্ষ্য নির্ধারণ (Establishing goal) : পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে কোন ফল অর্জনের জন্য তা প্রণীত হবে পূর্বেই তা নির্ধারণকে পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ বলে । বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণপূর্বক তার আলোকে প্রতিষ্ঠানের মৌলিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী বিভাগ ও উপ-বিভাগের লক্ষ্য ও অধি- লক্ষ্য (Sub-goal) নির্ধারণ পরিকল্পনার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । ধরা যাক, একটা প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন বিগত বছরের তুলনায় ১০% ভাগ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তবে তার আলোকে বিভিন্ন বিভাগের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে । এ সকল লক্ষ্য অবশ্যই সুস্পষ্ট এবং সমন্বিত হওয়া উচিত ।
৩. বিকল্প স্থিরকরণ (Determining the alternatives) : অনুমিত অবস্থার মধ্য দিয়ে কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে এ জন্য বিভিন্ন বিকল্প কার্যপদ্ধতি দাঁড় করানোর কাজকেই পরিকল্পনায় বিকল্প স্থিরকরণ বলে । ধরা যাক, ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে । এখন এই বর্ধিত বাজারে কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিক্রয় বাড়াবে এজন্য বিভিন্ন বিকল্প; যেমন-মূল্য কমানো, বিজ্ঞাপন বাড়ানো, পণ্যের মান উন্নয়ন ইত্যাদি যেকোনো এক বা একাধিক বিষয় বিবেচনা করতে পারে । বিকল্পের সংখ্যা বেশি হলে তার মধ্য হতে একেবারে দুর্বল বিকল্প বাদ দিয়ে শক্তিশালী বিকল্পসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে ।
৪. বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন (Evaluation of alternatives) : দাঁড় করানো প্রতিটা বিকল্প তার সুবিধা- অসুবিধার আলোকে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করার কাজকেই বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন বলে । এক্ষেত্রে বিকল্পসমূহ অনুমিত অবস্থা ও লক্ষ্যের আলোকে বিবেচনা করতে হয় । সাধারণ বিচারে কোনো বিকল্প সর্বোত্তম মনে হলেও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় ঐ বিকল্প গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে । প্রয়োজনে প্রতিটা বিকল্পকে একেকটি প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করে তাতে সম্ভাব্য ব্যয়, প্রাপ্তব্য সুবিধা ও অসুবিধা পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হয় ।
৫. সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ (Selecting the best alternative) : বিকল্পসমূহ মূল্যায়নের পর প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতার আলোকে কার্যকর বিকল্পটি খুঁজে বের করাকেই সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ বলে । ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার একাধিক বিকল্প পথ রয়েছে । এখন কোনো ব্যক্তি কোন্ পথে সেখানে যাবে তা তার প্রয়োজন, সময় ও বাস্তব অবস্থার আলোকেই নির্ধারণ করতে হয় । বিজ্ঞাপন না বাড়িয়ে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের কমিশনের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি লাভজনক বিবেচিত হতে পারে । বাছাইকৃত বিকল্পটি কার্যকরী মৌলিক পরিকল্পনা হিসেবে গৃহীত হয় এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা হিসেবে রূপায়িত করা হয়ে থাকে ।
৬. সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন (Preparing derivative plans ) : মৌলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কোনো সহায়ক বা সহযোগী ভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হলে তাকে সহায়ক পরিকল্পনা বলে। মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনেই অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে । ধরা যাক, একটা বিমান কোম্পানি কয়েকটা নতুন বিমান ক্রয়ের পরিকল্পনা নিচ্ছে। এখন এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতকগুলো সহায়ক পরিকল্পনা নিতে হবে; যেমন-ক্রু সংগ্রহ, তাদের প্রশিক্ষণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি ।
সবশেষে বলা যায়, নিয়মতান্ত্রিক ও স্থায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারাবাহিক পদক্ষেপ খুবই ফলপ্রদ হলেও একার্থক বা জরুরিভাবে গৃহীত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সবসময় অনুসরণ করা যায় না । তবে যতদূর সম্ভব উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণে এক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে ।
পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার শুধুমাত্র প্রথম কাজই নয় এটি অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় কাজেরও ভিত্তিস্বরূপ । তাই যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের ফলপ্রদতা নির্ভরশীল । একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় বিবেচ্য তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :
১. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য (Organizational objects): প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ পরিকল্পনার একটা অংশ হলেও এরূপ উদ্দেশ্যের আলোকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হয় । তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে অবশ্যই এর প্রণেতাগণকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে সামনে রাখার প্রয়োজন পড়ে ।
২. অধস্তনদের মান ও অবস্থা (Qualities and conditions of subordinates): পরিকল্পনা প্রণয়নে অধস্তন জনশক্তির মান ও অবস্থাও বিবেচ্য। পরিকল্পনা অধস্তনদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় গৃহীত পরিকল্পনায় অধস্তনদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা আগাম বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে ।
৩. পূর্বে গৃহীত পরিকল্পনার কার্যকারিতা (Effectiveness of previous plan) : পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্ব সময়ে গৃহীত পরিকল্পনার ফলাফল অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় উঠে আসা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। পূর্ব সময়ের গৃহীত পরিকল্পনার সঙ্গে কার্যাকার্যে যদি ব্যাপক বিচ্যুতি ঘটে তবে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ কষ্টসাধ্য হয় । অন্যথায় পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজসাধ্য হয়ে থাকে ।
৪. প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা (Existing problems and prospects of the organization): পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য। প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সমস্যার পরিমাণ বেশি হলে একভাবে পরিকল্পনা নিতে হয়। অন্যদিকে সমস্যা বেশি না হলে পরিকল্পনা ভিন্নভাবে নেয়া হয়ে থাকে ।
৫. প্রতিযোগীদের অবস্থা (Competitors condition): বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিযোগীদের অবস্থা ও তাদের গৃহীত কৌশল বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে । তবে প্রতিযোগীরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলে সাধারণ নিয়মে পরিকল্পনা তৈরি করে অগ্রসর হওয়া যায় ।
৬. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও অন্যান্য সামর্থ্য (Financial and other abilities of organization): পরিকল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও অন্যান্য সামর্থ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে । প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য ভালো থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়নে যেমনি প্রয়োজনীয় ব্যয় করা যায় তেমনি গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়।
৭. দেশের অর্থনেতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা (Economic and political situation of a country): দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যদি ভালো থাকে তবে পরিকল্পনা নিতে অনেক সুবিধা হয়। অন্যথায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে ।
উপসংহারে বলা যায়, উপরোক্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা উত্তম পরিকল্পনা বিবেচিত হতে পারে । এজন্যই বর্তমানকালে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সোট বিশ্লেষণ (SWOT analysis) করা হয়ে থাকে । এতে 'S' ও 'W' অভ্যন্তরীণ শক্তি (Strength) ও দুর্বলতা (Weakness) এবং 'O' ও 'T' বাহ্যিক সুযোগ (Opportunity) ও বাধা বা হুমকি (Tareat) নির্দেশ করে । এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পরিকল্পনা নিলে উক্ত পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী হয়ে থাকে ।
পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্ব নির্ধারিত নক্শা বা চিত্র। এর ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠানের সকল স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত । একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতেও পরিকল্পনাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে । নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো :
রেখাচিত্রে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচিত হলো :
ক) প্রকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of nature)
পরিকল্পনাকে তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় । নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :
১. লক্ষ্য (Goals) : পরিকল্পনার অভিপ্রেত ফলকে লক্ষ্য বলে । এরূপ অভিপ্রেত ফল বা লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল উপায়-উপাদান ও কর্মপ্রচেষ্টাকে কাজে লাগানো হয় । কোনো প্রতিষ্ঠানে ১০% উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা এরূপ লক্ষ্যের একটি উদাহরণ। সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি লক্ষ্য ঠিক করা হয় এবং তার আলোকে বিভিন্ন বিভাগ বা স্তরে অধি-লক্ষ্য (Sub-Goal) নির্ধারণ করা হয় । পরিধি ও প্রকৃতি অনুযায়ী লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য, মিশন, সময় লক্ষ্য, বাজেট লক্ষ্য বা কোটা, টার্গেট ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। (পরিকল্পনার লক্ষ্য শিরোনামের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।
২. স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing plan) : যে পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে একবার গৃহীত হওয়ার পর নতুন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ বা নতুন কোনো অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা বারবার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে । একই ধরনের সমস্যা বা অবস্থা মোকাবেলার জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং বারে বারে তা ব্যবহৃত হয় । ফলে উর্ধ্বতনদের যেমনি নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা অধস্তনদের জানানোর প্রয়োজন পড়ে না তেমনি অধস্তনরা একই পরিকল্পনার আওতায় কাজ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস পায় । যা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে । এরূপ পরিকল্পনা নিম্নোক্ত কয়েক ধরনের হতে পারে :
i) নীতি (Policy) : একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বনির্ধারিত আদর্শ বা সাধারণ নির্দেশনাকেই নীতি বলে । সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও কার্যসম্পাদনে নীতি ব্যবস্থাপকদের বিশেষভাবে সহায়তা করে । কোনো প্রতিষ্ঠানে নগদ বিক্রয়ের নিয়ম বা জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান-এরূপ নীতির উদাহরণ ।
ii) প্রক্রিয়া (Process) : লক্ষ্যার্জনে পরস্পর নির্ভরশীল ধারাবাহিক কার্যসমষ্টিকে প্রক্রিয়া বলে । প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কার্যসমূহ একের পর এক নির্দিষ্ট থাকে । পরস্পর নির্ভরশীল থাকায় একের কাজ দ্বারা অন্যে প্রভাবিত হয় । সকল কাজের সফল সম্পাদন লক্ষ্যার্জন নিশ্চিত করে । কর্মী নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ হতে শুরু করে নিয়োগ দান পর্যন্ত কর্মসমষ্টিকে প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে ।
iii) পদ্ধতি (Procedure) : প্রক্রিয়ার অধীনে নির্ধারিত প্রত্যেকটি কার্য সম্পাদনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে পদ্ধতি বলে । কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ একটা অন্যতম উপায় বা পদ্ধতি । এই লিখিত পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে-এ সম্পর্কিত নিয়মকে পদ্ধতি বলা যায় ।
iv) কৌশল (Technique) : কৌশল হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিকল্পনা । প্রতিযোগী ফার্ম কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাকে কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তার জন্য পূর্বনির্ধারিত নীতিকে কৌশল বলে। উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সরবরাহের নীতি- কৌশলের একটি উদাহরণ ।
৩. একার্থক পরিকল্পনা (Single-use plan) : যে পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র একবার ব্যবহারের জন্য বা একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণয়ন করা হয় তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে । যে সকল কার্যক্ষেত্রে অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হয় বা ফরমায়েশ অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেখানে একার্থক পরিকল্পনা উত্তম বিবেচিত হয়ে থাকে । প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশেষ অবস্থা মোকাবেলার জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতে পারে । প্রতিষ্ঠানে কিছু যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন মেরামত না করার কারণে নষ্ট হওয়ায় যথেষ্ট শ্রম ঘণ্টার অপচয় হচ্ছে এরূপ অপচয় একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য গৃহীত বিশেষ কর্মসূচি এরূপ পরিকল্পনার উদাহরণ । সময়ের অভাবে এরূপ পরিকল্পনার পরিবর্তন আনা অনেকসময়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । এ ধরনের পরিকল্পনাকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়; যা নিম্নরূপ :
i) কর্মসূচি (Programme) : কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে বড় ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাকে কর্মসূচি বলে । বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণ রোধ করার জন্য গৃহীত বড় ধরনের পরিকল্পনা এর উদাহরণ । পোলিও রোগ নিরূপণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠানের পুরনো সকল যন্ত্রপাতি সরিয়ে নতুন যন্ত্রপাতি বসানোর পরিকল্পনাকে কর্মসূচি বলা যায় ।
ii) প্রকল্প (Project) : কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের প্রতিটা পরিকল্পনাকে প্রকল্প বলে । আর্সেনিক দূষণ রোধে অনেকগুলো পরিকল্পনার সাথে দূষণযুক্ত টিউবওয়েল শনাক্তকরণের পরিকল্পনাকে একটা প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যায়। একাধিক শ্রেণিবিন্যস্ত তালিকার মধ্য থেকে ক তালিকাভুক্ত যন্ত্রপাতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃসংস্থাপনের কার্যক্রমকে প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে ।
খ) মেয়াদভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of time period)
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেয়াদের ভিত্তিতেও পরিকল্পনা গৃহীত হতে দেখা যায়। এরূপ ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় :
১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (Short-term plan) : সাধারণত এক বৎসর বা তার কম সময়ের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে । প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় পর্যায়ে যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদাহরণ । বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ত্রৈমাসিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক পরিকল্পনার সবগুলোকেই এ ধরনের পরিকল্পনা গণ্য করা যায় ।
২. মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা (Mid-term plan) : এক বৎসরের অধিক ও সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর সময়ের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট লেভেলে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ ধরনের মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হতে দেখা যায় । সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এর একটি উদাহরণ ।
৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long-term plan) : পাঁচ বৎসরের অধিক যেকোনো সময়ের জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে স্ট্র্যাটিজি নির্দিষ্ট করা হয় তা এ ধরনের পরিকল্পনার উদাহরণ । কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল স্ট্রাটিজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে- তা এর মধ্যে পড়ে । বাংলাদেশ সরকারের Vision 2021 এর ঘোষণা এর অন্তর্ভুক্ত ।
গ) সংগঠন কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis or organization structure)
প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোর কোন পর্যায়ে কোন পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে তা অনুসারেও পরিকল্পনাকে ভাগ করা যায়; যেগুলো নিম্নরূপ :
১. স্ট্র্যাটিজিক বা কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic plan) : তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তমূলক কোনো পরিকল্পনা গ্রহণকে স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা বলে । স্বাভাবিকভাবেই এরূপ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহীদের কর্তৃক দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা সহযোগে প্রণীত হয় । এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নিচের স্তরে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে । প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পণ্যসারিতে নতুন ১০টি আইটেম অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে-এটি স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনার উদাহরণ ।
২. কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা (Functional plan) : প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাটিজিক বা কৌশলমূলক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিষ্ঠানের মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ে স্বল্প সময়ের জন্য বাস্তবায়নমূলক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা বলে । এরূপ পরিকল্পনা সাধারণত নিম্নরূপ হয়ে থাকে:
ক. বিভাগীয় পরিকল্পনা (Departmental plan) : প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক বিভাগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তাকে বিভাগীয় পরিকল্পনা বলে । কার্যভিত্তিক বিভাগ খোলা হলে সেক্ষেত্রে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি বিভাগের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা এর মধ্যে পড়বে। এরূপ বিভাগের অধীন উপবিভাগ ও কর্মকেন্দ্রের পরিকল্পনাও এর অধীন । দ্রব্যভিত্তিক বিভাগ খোলা হলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যভিত্তিক বিভাগের গৃহীত পরিকল্পনা-এ ধরনের পরিকল্পনা বিবেচিত হবে ।
খ. আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional plan) : যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত থাকে সেক্ষেত্রে আঞ্চলিকভাবেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় । বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা নিলে তা আঞ্চলিক পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য হয়। একটা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বিভাগ বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য জোনাল পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে ।
গ. মাস্টার বা সামগ্রিক পরিকল্পনা (Master plan) : কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ বা অঞ্চলের পরিকল্পনাকে একত্রিত করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে সামগ্রিক বা মাস্টার পরিকল্পনা বলে। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগীয় বাজেট সমন্বয়ে ‘মাস্টার বাজেট' তৈরি এরূপ সামগ্রিক পরিকল্পনার উদাহরণ ।
সদ্য পাসকরা মি. হাবীব বাবার গড়া নতুন শিল্প ইউনিটের দায়িত্ব নিয়েছেন । বাবাকে রাতদিন ব্যবসায় নিয়ে যেভাবে ভাবতে দেখেছেন তা তার নিকট পছন্দের মনে হয়নি । তার ভাবনা, এত সিরিয়াস হওয়ার কী আছে । নতুন জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে । বাবাকে বললেন, কী কী পদে লোক নিয়োগ দিতে হবে- এটা ঠিক করে দাও । এরপর আমি আমার পছন্দমতো লোক নিয়ে নেবো । বাবা বললেন, আগে ভাবো কী মানের, কোন ধরনের লোক, কোত্থেকে, কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে । পরিকল্পনা নিয়ে কাজ না করলে সমস্যায় পড়বে । মি. হাবীবের ভাবনা, মানুষ তো সব শিখে আসে না । করতে করতে শিখবে । তিনি অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের বিষয়টি মাথায় না নিয়ে সদ্য পাস করা ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছেন । নিয়োগ দিতে যেয়ে প্রতিষ্ঠানের যে সু-নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি ছিল তা না মেনে বন্ধু-বান্ধবদের সুপারিশ আমলে নিয়েছেন । প্রতিষ্ঠান চালাতে যেয়ে এখন তিনি হাড়ে হাড়ে সমস্যা অনুভব করছেন। না নিজে তেমন কিছু বুঝছেন না কারও সহযোগিতা পাচ্ছেন । তাই প্রতিষ্ঠান আর ঠিকমতো চলছে না । তিনি বুঝতে পারছেন আবেগ দিয়ে ব্যবসায় চলে না । ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসায় চালাতে না পারলে বিপদে পড়তেই হয় । পরিকল্পনার গুরুত্ব এখন তার নজরে এসেছে ।
উপরের উদ্দীপক বিবেচনায় নিলে এটা স্পষ্ট যে, পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় । যা প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনকে ব্যাহত করে । বিভিন্ন দিক থেকে পরিকল্পনার গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হলো :
১. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন (Accomplishment of organisational objectives) : পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো কার্যক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হ্রাসপূর্বক সহজতম পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করা । পূর্ব পরিকল্পনা থাকায় নির্বাহী ও তত্ত্বাবধায়কগণ এর আলোকে সহজেই করণীয় নির্ধারণ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে । তাই কার্যকর পরিকল্পনা উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি প্রথম ও প্রধান কার্য ব্যবস্থা ।
২. ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (Development and expansion of business) : পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের ও বাইরের যে সকল সমস্যা ভবিষ্যতে মোকাবিলা করতে হতে পারে তা সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তদনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । যা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস ও অনিশ্চয়তা দূর করে এর কার্যকলাপ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সহজতর করে ।
৩. ব্যয় ও অপচয় হ্রাস (Minimization of cost and wastage) : আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ শুরু করা হলে সেক্ষেত্রে বাহুল্য ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পায় । এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে যদি বাজেট থাকে এবং বাজেটের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তবে মিতব্যয়িতা অর্জন সহজ হয় । এ ছাড়া জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের অপচয় হ্রাস করতেও পরিকল্পনা সাহায্য করে ।
৪. উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার (Effective utilization of resources) : যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা অর্জনে এতে নিয়োজিত মানবীয় ও বস্তুগত উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কাজ করা হলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেকটি উপায়-উপকরণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় । এর ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকটি উপায়-উপকরণের কার্যদক্ষতা বাড়ে । আর দক্ষতার উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও লক্ষ্যার্জন নিশ্চিত করতে পারে ।
৫. সঠিক কার্যধারা অনুসরণ (Following proper course of action) : পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করে । প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি, বিভাগ ও উপ- বিভাগ পরিকল্পনার অধীনে কাজ করায় প্রত্যেকে তাদের করণীয় সম্পর্কে আগাম জানতে পারে । এতে মানসিক প্রস্তুতি সহকারে কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় ।
৬. ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন (Implementation of other managerial functions) : পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার সমুদয় কাজের ভিত্তিস্বরূপ । পরিকল্পনা ছাড়া ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ; যেমন-সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্য সঠিকভাবে সম্পাদন করা যায় না । তাই পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের সঠিক বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে ।
পরিকল্পনা হতে খুবই আশাপ্রদ ফল লাভ করা গেলেও এটি অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে এ কথা বলা যায় না । সাধারণভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় এরূপ সমস্যা দেখা দেয় । এরূপ সীমাবদ্ধতাসমূহ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :
১. পটভূমি বা অঙ্গন নির্ধারণে সমস্যা (Problems in premising) : যে অবস্থার মধ্য দিয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তাকে পরিকল্পনার পটভূমি বা অঙ্গন বলে । ভবিষ্যৎ অবস্থা কী দাঁড়াবে তা সম্পূর্ণ অনুমান করা কষ্টসাধ্য । এজন্য পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় । কিন্তু অনেক সময় প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয় না । সে কারণে সঠিক পটভূমি নির্ধারণ কঠিন হয় ।
২. সময়সাপেক্ষ (Time consuming) : সাধারণত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক জটিলতা ও কার্যকলাপের আধিক্যহেতু পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যধিক সময় বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, বিকল্প নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় বেশি লাগে । যা অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর হয় ।
৩. ব্যয়সাপেক্ষ (Costly) : পরিকল্পনা অনেক সময় ব্যয়সাপেক্ষ হয় । অনেক সময় পরিকল্পনার খরচ অপেক্ষা এ হতে অর্জিত ফলাফল কম হয় । অনেক সময় পরিকল্পনা দক্ষতা অর্জনে কোনো ভূমিকা রাখে না ফলে ব্যবসায়ে মিতব্যয়িতা অর্জিত হয় না । সরকারি পর্যায়ে ক্ষেত্রে বিশেষে এমন অনেক পরিকল্পনা নেয়া হয় যা ব্যয় বাড়ায় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সুফল দেখতে পাওয়া যায় না ।
৪. মানসিক সমস্যা (Mental hazard) : সংগঠনের কর্মীরা সহজাতভাবে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, রীতি- নীতিতে বিশ্বাসী । তারা ভবিষ্যতের চাইতে বর্তমানকেই উত্তম বলে মনে করে । তাই নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে জনশক্তির মধ্যে নিরুৎসাহ দেখা দেয়। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও সমস্যার সৃষ্টি করে ।
৫. উদ্যোগ গ্রহণে বাধাদান (Obstacle to initiative) : পরিকল্পনাকে সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, পরিকল্পনা ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়স্বরূপ এবং এটি ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মননশীলতায় ও ব্যক্তিগত চিন্তার পরিসরে কাজ করতে দেয় না । ফলে তা কর্মীকে উদ্যমহীন করে তুলতে পারে ।
৬. সংশোধনজনিত সমস্যা (Problem in correction) : পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রজ্ঞার অভাব, দক্ষতার অভাব, ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে সমস্যা ইত্যাদি কারণে পরিকল্পনা ত্রুটিযুক্ত থেকে যায় । এ ত্রুটি সংশোধনে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয় ।
৭. আতিশয্যের প্রতি ঝোঁক (Tendency toward excessiveness) : পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে আতিশয্যের প্রতি বা বাড়তি কিছু করা যাবে এমন আশাবাদের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অতীতে কী হয়েছে তার বিবেচনার চাইতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিরিক্ত আশাবাদ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণে পরিকল্পনাবিদদের অনেক সময়ই উৎসাহিত করে । যা কার্যক্ষেত্রে সঠিক দিক- নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয় ।
৮. বাহ্যিক সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা (Inability to resolve external problems) : কিছু কিছু বাহ্যিক সমস্যা সমাধানে একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা ফলপ্রদ হয় না। কারণ, বাহ্যিক সমস্যা বাহ্যিক পরিবেশ হতে উদ্ভূত হয়। যেমন- সরকারি আমদানি ও রপ্তানি নীতি, কর নীতি, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রভাব ইত্যাদি ।
পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনার অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপকদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞানের অভাব, যথাসময়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্নমুখী জটিলতার কারণে পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকর ফল দিতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হয় ।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল অনেকদিন টেস্ট ক্রিকেট বিশ্ব র্যাংকিং-এ দশম স্থানে । কোনোভাবেই নবম অবস্থানে উঠে আসতে পারছে না। সামনে জিম্বাবুয়ে সফর। জিম্বাবুয়ে নবম অবস্থানে থাকলেও বাংলাদেশ থেকে তাদের পয়েন্ট পার্থক্য তেমন বেশি নয় । তাই বাংলাদেশ দল এবারের সফরের উদ্দেশ্য ঠিক করেছে যেভাবেই হোক জয় নিয়ে ফিরতে হবে । কোচ, খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাগণ সবাই সেভাবে ছক কাটছেন । তিন মাস আগে থেকেই খেলোয়াড়গণ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে কোচের অধীনে নিবিড় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। জিম্বাবুয়ের মাঠ বিবেচনায় একজন স্পিন বোলিং এর কোচ নিয়োগ দেয়া হয়েছে । জিম্বাবুয়ের প্রতিটা খেলোয়াড়ের বিভিন্ন খেলার ভিডিও ফুটেজ ধরে ধরে তাদের দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে । কোন খেলোয়াড়কে পরাস্ত করতে কোন বোলার উত্তম হবে ও কোন বোলারকে কিভাবে মোকাবেলা করা হবে তাও ঠিক করা হচ্ছে । দলের ফিল্ডিং-এর দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তার উন্নয়নের প্রতিও নজর দেয়া হচ্ছে । এ সকল পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কারণে সফর শেষে মূল্যায়ন হলো জিম্বাবুয়ে সফরে দল ভালো খেলেছে ও জয় নিশ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ঠিক করে সেভাবে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিতে পারাকেই জয়লাভের কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে
সম্পর্কযুক্ত।
উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্ত ফল যাকে ঘিরে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় । লক্ষ্য হলো পরিকল্পনার অভিপ্রেত ফল । অর্থাৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে কী করা হবে, কখন ও কিভাবে করা হবে, ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। আর এরূপ লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্যকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে থাকে ।
উদ্দেশ্য নির্ধারণ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীন। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর আবার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হতে পারে। আবার সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভাগ ও উপ-বিভাগের পরিকল্পনা প্রণীত হয় । অর্থাৎ সকল পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন করা । অধ্যাপক নিউম্যান প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার মধ্যকার সম্পর্ককে একটা সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; যা হলো-একটা বিমান সংস্থা এর কার্যক্রম নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, কর্মী সংগ্রহ এবং কোনো কিছু যথাযথভাবে শুরুর পূর্বে অবশ্যই স্থির করবে যে, তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে যাত্রী বহন না মালামাল বহন করা । উদ্দেশ্য ঠিক হলেই তখন উদ্দেশ্যার্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ছাড়া কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয় । পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাই উদ্দেশ্য নির্ধারণকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অনেকেই উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন । উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও কৌশলগত দীর্ঘ বা মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যকার সম্পর্ককে নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্য তুলে ধরা হলো :
প্রতিনিয়ত আমরা নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি । প্রতিষ্ঠানেও নানান প্রয়োজনেই প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । এই সিদ্ধান্তে ভুল হলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে । যথাসময়ে যথাসিদ্ধান্ত নেয়া না গেলে তার ফল শুভ হয় না । মি. আরিফ অফিসের কাজে চট্টগ্রাম যাবেন । বিমানে, বাসে, ট্রেনে- নানানভাবেই যাওয়া যায়। তিনি কোন পথে যাবেন- এটা সিদ্ধান্তের বিষয়। বাসে গেলেও নানান বাস, তাই সেখানেও সিদ্ধান্তের প্রশ্ন। মিসেস নার্গিস দুপুরের রান্না করবেন। মেন্যু কী করবেন এখানেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে । মিস সামন্তার বেতন থেকে বেশ কিছু টাকা জমেছে । তিনি এই টাকা কী করবেন- এটাও সিদ্ধান্তের বিষয় । প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় বৃদ্ধির চিন্তা করা হচ্ছে। বাজারজাতকরণ প্রসার কার্যসূচি বাড়ানো হবে না দ্রব্যমূল্য কমানো হবে- এটাও সিদ্ধান্তের প্রশ্ন। বাজারজাতকরণ কার্যসূচি বাড়ানো হলে বিজ্ঞাপন বেশি দেয়া হবে, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের কমিশন বাড়ানো হবে না স্বল্পমেয়াদি বিক্রয় বৃদ্ধির কার্যসূচি; যেমন- পণ্যের সাথে কোনো কিছু ফ্রি, সাময়িক মূল্য হ্রাস ইত্যাদির মতো স্বল্পমেয়াদি কোনো কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে - এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তের প্রশ্ন এসে যায় । তাই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সব সময়ই নানান উপায়, পন্থা বা বিকল্প থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তম বিকল্পকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করে পথ চলে ।
যে কোনো সমস্যা সমাধান বা কর্মপন্থা গ্রহণে একাধিক উপায় বা বিকল্প থেকে সর্বোত্তম বিকল্প বাছাইকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। যেক্ষেত্রে কোনো বিকল্প থাকে না সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন আসে না। মোটর গাড়ির টায়ার নষ্ট হয়েছে বদলাতে হবে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আসছে না । কিন্তু বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের টায়ার - রয়েছে- কোনটি কেনা হবে এটা সিদ্ধান্তের বিষয়। একজনের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তাই খেতে হবে- এটাও সিদ্ধান্তের বিষয় নয় । কিন্তু যখনই খাওয়ার প্রশ্ন এলো তখন কী খাওয়া হবে এখানে নানান বিকল্প থাকতে পারে । তাই এখানে সিদ্ধান্তের বিষয়টি এসে দাঁড়াচ্ছে । ব্যবস্থাপনা কার্য চালাতে যেয়ে ব্যবস্থাপকদের প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় । পরিকল্পনা গ্রহণও সবসময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত । কারণ পরিকল্পনা গ্রহণেও বিকল্প নির্ধারণ করে তার মধ্য থেকে উত্তম বিকল্পকে পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে । একইভাবে সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা ইত্যাদি কাজেও নানান সিদ্ধান্ত নিতে হয় । একজন ব্যবস্থাপককে প্রতিনিয়ত তার কাজেও নানান সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। সেজন্য বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনার মৌল কাজই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।
টেলিভিশনে মোবাইল ফোন কোম্পানির একটা বিজ্ঞাপন । হঠাৎ করে কেউ কোনো কথা বলছে না । সবাই নির্বাক । ফ্যাল ফ্যাল করে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে । প্রাণের উচ্ছ্বাস নেই । হঠাৎ করে কথা শুরু হলো । যেনো দম ফেলে বাঁচলো মানুষগুলো । এখন কথা আর কথা । প্রাণের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ ভাগাভাগি করার পালা । যদি ধরি একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না, সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না, তাহলে কেমন হবে । বস (Boss) অফিসের চেয়ারে বসা। কাঁচামাল নেই । সরবরাহকারীদের সাথে আলাপ করে কাউকে সরবরাহের আদেশ দিতে হবে । বস সিদ্ধান্ত নেবেন না- তাই কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ । গুদামে মজুত মাল জমে আছে । কিছু দাম কমালে বা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের একটু কমিশন বাড়ালে মালগুলো বিক্রয় হয়ে যায় । কিন্তু সংশ্লিষ্টরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না । কী অবস্থা হবে? শ্রমিকে-শ্রমিকে মারামারি করে উৎপাদন বন্ধ । করণীয় কী? সিদ্ধান্ত দিতে হবে । কিন্তু কেউ সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না । এভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানে যে নানান সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠান কখনই চলতে পারবে না ।
একটা প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে এর কাজকে গতিশীল রাখা হয়। করণীয় নির্দেশের ফলে অধীনস্থরা স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে। সমস্যার দ্রুত সমাধান নির্দেশ করায় শুরুতেই তা সমাধান করা সম্ভব হয় । এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজনীয় সকল মূহুর্তে প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে । ব্যবস্থাপনার প্রতিটা কাজ পরিচালনায় সিদ্ধান্ত নিতে হয় । পরিকল্পনা গ্রহণে উত্তম বিকল্প বাছাইয়ের কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কীত । সংগঠনের ক্ষেত্রে কাজকে কিভাবে ভাগ করা হবে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কিভাবে বন্টিত হবে- ইত্যাদি বিষয়েও শীর্ষ নির্বাহীদের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন পড়ে । কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন উৎস থেকে জনশক্তি সংগ্রহ করা হবে, কর্মী বাছাই প্রক্রিয়া কী হবে, কোন ক্ষেত্রে কোন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে ইত্যাদি বিষয়ও সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত । নির্দেশের বিষয় কী হবে, তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে- এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্টদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় । এভাবে প্রেষণা দানে, সমন্বয় সাধনে এবং নিয়ন্ত্রণে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নির্দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। একটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বিপণন, অর্থসংস্থান, জনশক্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা অপরিহার্য কাজ । অর্থনীতির মৌলিক প্রশ্নসমূহ - কী উৎপাদন করতে হবে, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে, কী মূল্য নির্ধারিত হবে ইত্যাদি বিষয়গুলোর উত্তরের মূলে রয়েছে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়া । অর্থাৎ ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যে কোনো কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত আবশ্যক ।
যথাসময়ে যথাসিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর ব্যক্তিক ও প্রতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভরশীল । তাই যেনোতেনোভাবে সিদ্ধান্ত নিলে তার ফল উল্টো হতে বাধ্য। সে কারণেই সিদ্ধান্ত নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে অবশ্যই অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সুবিধা-অসুবিধাসহ নানান বিষয় বিবেচনা করতে হয়। একজন চাকরিজীবীর কিছু টাকা জমেছে । সে এই টাকা দিয়ে সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে তার পিছনে অর্থ ব্যয় করতে পারে অথবা আরও কিছু টাকা আত্মীয়-স্বজন থেকে ঋণ করে একটা সস্তা ফ্ল্যাট বুকিং দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কিস্তি বহনের ভার মাথায় নিতে পারে । এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে । ব্যক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতেই যেখানে নানান বিষয় বিবেচ্য সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবশ্যই আরও গভীরভাবে নানান বিষয় ভাবতে হয় । অবশ্য সবক্ষেত্রেই এমন কিছু সিদ্ধান্ত থাকে যা সাধারণমানের এবং যেগুলো বিষয়ে প্রায়শই সিদ্ধান্ত দিতে হয় । এমন সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়াটা কিছুটা সহজ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সিদ্ধান্ত দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে অবশ্যই অনেক বিষয় ভাবতে হয় এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপ বিবেচনার বা প্রক্রিয়ার অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে । সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হলো:
১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ (Identifying and defining problems): জটিল বা অসুবিধাজনক কোনো বিষয় যা উত্তরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক এমন কোনো বিষয়কে সমস্যা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে । কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটি যদি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা না যায় তবে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না । সমস্যা সামনে আসলে তাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার অর্থাৎ সমস্যার প্রকৃতি, করণীয় নির্ধারণের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ও ভেবে দেখতে হয় । এভাবে সমস্যা ও করণীয়কে যদি সঠিকভাবে চিহ্নিত ও অনুধাবন করা সম্ভব হয় তবে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হয়ে থাকে ।
২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Determination of priority): সমস্যার পরিমাণ একাধিক হলে এবং সবগুলো একসাথে সমাধান সম্ভব না হলে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে করা হবে এ বিষয় নির্ধারণকেই অগ্রাধিকার নির্ধারণ বলে । এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রথমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা করণীয় নির্ধারণ করতে হবে এবং এরপর পরম্পরা কী হবে তাও ঠিক করার প্রয়োজন পড়ে । ধরা যাক, মেশিন আর কাজ করছে না তাই তা পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন, বিল্ডিং সম্প্রসারণের কাজ চলছে তাও চালানো দরকার এবং কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অগ্রিম দিতে হবে- এই তিনটা বিষয়কে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার । এক্ষেত্রে যেহেতু কোনোটিই বাদ দেয়া যাচ্ছে না, তাই ফান্ড বিবেচনায় সিদ্ধান্তের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে । অন্যথায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেলে পরে তা সমস্যার কারণ হতে পারে ।
৩. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ (Collection of data and information): কোনো বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা, জ্ঞান, বিষয় বা সংবাদকে তথ্য বলে । এরূপ অবস্থা জানা বা সংবাদ সংগ্রহকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ বলা হয়ে থাকে । এরূপ তথ্য ও উপাত্ত হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুখ্য অবলম্বন । সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যতবেশি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে সমর্থ হন তত বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন । এরূপ তথ্য সংগ্রহ চিহ্নিত সমস্যা বা করণীয় বুঝতে যেমনি সহায়তা করে তেমনি সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধানেও সহায়তা দেয় । উল্লেখ্য, নতুন নতুন প্রযুক্তি, উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে তথ্য লাভ অনেক সহজ হয়েছে; যা সংগ্রহ ও বিবেচনা করা না গেলে সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি এবং সমস্যা সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ।
৪. বিকল্পসমূহ উদ্ভাবন (Generation of alternatives): অনুমিত অবস্থার আলোকে সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য উপায়সমূহ দাঁড় করানোর কাজকেই বিকল্প উদ্ভাবন বলে । সিদ্ধান্ত গ্রহণে একজন ব্যবস্থাপককে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ কি হতে পারে তা উদ্ভাবন বা নির্দিষ্ট করতে হয় । ধরা যাক, একটা মেশিন পুনঃস্থাপন করতে হবে । তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মেশিনের দাম কেমন তা জানা গেছে । এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এজন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে রাজি আছে সে সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হয় । এরপর উদ্ভাবিত বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে প্রয়োজনে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা (Short list) তৈরি করা হয় । একজন ব্যক্তি অফিসের কাজে চট্টগ্রাম যাবেন । যাওয়ার বিকল্প কি হতে পারে তা প্রথমে জানা থাকলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়ে থাকে ।
৫. বিকল্পসমূহের মূল্যায়ন (Evaluation of alternatives): দাঁড় করানো প্রতিটা বিকল্প উপায় সুবিধা- অসুবিধার আলোকে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করার কাজকেই বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন বলে । এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা, দুর্বলতা ও ঝুঁকির দিকগুলো বিবেচনা করতে হয়। নতুন একটা শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত, নতুন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় মূলধন সংস্থানের সিদ্ধান্ত, নতুন বাজারজাতকরণ প্রসার কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিকল্পসমূহকে নানান বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন পড়ে । চট্টগ্রামে বিভিন্ন পথে যাওয়ার বিকল্প মূল্যায়নে ব্যয় করার সামর্থ্যই শুধু নয় চট্টগ্রামে কাজের ধরন, যাত্রায় ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করার প্রয়োজন পড়ে ।
৬. উত্তম বিকল্প গ্রহণ (Choosing proper alternative): মূল্যায়নকৃত বিকল্প হতে প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতা বিবেচনায় উত্তম বিকল্প বাছাইয়ের কাজকেই উত্তম বিকল্প গ্রহণ বলে । এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বিকল্পগুলোকে দেখতে হয়। মূল্যায়নে কোনো বিকল্প উত্তম মনে হলেও সামগ্রিক বিচারে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক নাও হতে পারে। সাময়িকভাবে কোনো বিকল্প গ্রহণ লাভজনক মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । বাংলাদেশে বিদ্যুত সমস্যা নিরসনে কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুত উৎপাদন, গ্যাস ও কয়লা থেকে বিদ্যুত উৎপাদন এবং পারমাণবিক বিদ্যুত প্রকল্পে বিদ্যুত উৎপাদনের বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে। সরকার কুইক রেন্টাল পদ্ধতিকে সাময়িকভাবে উৎসাহিত করলেও সেই সাথে স্থায়ী বিদ্যুত প্লান্ট স্থাপনের বিষয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে । কারণ সাময়িক ব্যবস্থা দেশের জন্য মারাত্মক সংকট ডেকে আনতে পারে । এরূপ বিকল্প গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত আকারে তা অধস্তনদের জানানো ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে ।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা যৌক্তিক প্রক্রিয়া । যেক্ষেত্রে একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সমস্যা চিহ্নিতকরণ বা করণীয় কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জনের পর সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারাবাহিক কতকগুলো পদক্ষেপ অনুসরণ করেন । এরূপ পদক্ষেপ অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কতকগুলি বিষয় তাকে সহায়তা প্রদান করে । নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:
১. বিচার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা (Judgment power and intuition): বিচার ক্ষমতা হলো কোনো পরিস্থিতি অনুধাবনপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞা হলো ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারার সামর্থ্য । বিভিন্ন বিকল্প থেকে উত্তম বিকল্প বাছাইয়ে সিদ্ধান্তগ্রহীতার বিচার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে । সাধারণ বিচারে কোনো বিকল্প লাভজনক মনে হলেও প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় তা লাভজনক নাও হতে পারে । তাই সিদ্ধান্তগ্রহীতা কতটা বিচক্ষণতার সাথে ও দূরদৃষ্টি সহকারে উত্তম বিকল্প বাছাই করতে সক্ষম তা এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় ।
২. সুসংবদ্ধ চিন্তা (Systematic thought) : সুসংবদ্ধ চিন্তা বলতে একজন সিদ্ধান্তগ্রহীতা কতটা ঠাণ্ডা মাথায় নিয়ম মেনে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন তার সামর্থ্যকে বুঝায় । অনেকেই থাকেন যারা কোনো বিষয়কে গুছিয়ে চিন্তা করতে পারেন না। অনেকে বিষয় বুঝে উঠার আগেই মতামত দিয়ে ফেলেন । প্রতিষ্ঠানের নিয়ম- কানুনও অনেকে বুঝে উঠতে পারে না । সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দেয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না । তাই সুসংবদ্ধ চিন্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিকে সহায়তা করে ।
৩. অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য (Experience and skill): সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য একটা বড় সহায়ক উপাদান । অভিজ্ঞতা এমন এক শক্তি যা ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচার ক্ষমতা সবকিছুকেই সংহত ও শক্তিশালী করে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি সাহসী হয় এবং পরিস্থিতি ও প্রয়োজন দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিক নৈপুণ্য, দক্ষতা বা কুশলতা যথাসময়ে যথাসিদ্ধান্ত দিতে ও অন্যদের নিকট থেকে নিজ মতামতের পক্ষে সমর্থন আদায়ে ব্যক্তিকে সহযোগিতা করে ।
৪. তথ্য (Information): বর্তমান যুগ হলো তথ্যের যুগ । যে যত বেশি তথ্য ধারণ করেন তার পক্ষে তত কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাল এখন আর নেই । একজন শিল্পমালিক উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তা বিবেচনা করেন। প্রতিযোগীরা কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে, গ্রাহকদের রুচি-পছন্দ কোন দিকে যাচ্ছে, উৎপাদন বাড়ালে তা বিক্রয়ে বিক্রয় বিভাগ কতটা সমর্থ, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা কেমন সাড়া দেবে- এ সকল বিষয়ে তথ্য থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে থাকে ।
৫. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (Power and authority): ক্ষমতা হলো অন্যদের প্রভাবিত করার সামর্থ্য । অন্যদিকে কর্তৃত্ব হলো অন্যদের বাধ্য করার ক্ষমতা । একজন ব্যবস্থাপক যদি অন্যদেরকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখেন তবে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয় । সাংগঠনিক নিয়মে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই অধস্তনদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী থাকেন। ফলে তার দেয়া সিদ্ধান্ত মানতে অধস্তনরা বাধ্য থাকে। তদুপরি যদি তিনি অধস্তনদের প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখেন তবে তার এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখে ।
৬. প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য (Capacity of organization) : অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন সহযোগী উপায়- উপকরণসমূহের কার্যকর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের যে সক্ষমতার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বলে । যোগ্য জনশক্তি, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা, উত্তম কার্য পরিবেশ, আর্থিক ও কারিগরি সামর্থ্য, বাজার সামর্থ্য, ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য, প্রতিষ্ঠানের সুনাম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাম্য মাত্রায় বজায় থাকলে নির্বাহীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন সহজ হয় । অন্যথায় সিদ্ধান্ত দিতে ব্যবস্থাপকদের নানান বিষয় ভাবতে হয় । ফলে সিদ্ধান্তহীনতার প্রতি এক ধরনের ঝোঁকের সৃষ্টি হয়ে থাকে ।
৭. অংশগ্রহণের সুযোগ (Opportunity of participation): সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধস্তনদের অংশগ্রহণের সুযোগ সিদ্ধান্তের মানকে উন্নত করে । সেই সাথে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেও সহায়তা দেয় । একটা প্রতিষ্ঠানে যদি গণতান্ত্রিক বা অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা যায় তবে অধস্তনদের মধ্যে উচ্চ মনোবল বিরাজ করে । ফলে তারা পরামর্শ প্রদানে যেমনি স্বতঃস্ফূর্ত থাকে তেমনি গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে । তাই প্রতিষ্ঠানে অধস্তনদের কার্যকর অংশগ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা গেলে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহায়তা দেয় ।
সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সফলতা অর্জন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল । ব্যক্তিক সিদ্ধান্তে যদি ভুল হয় তাহলে ব্যক্তি ও তার পরিবার এর কুফল ভোগ করে । প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যদি ভুল করেন তবে প্রতিষ্ঠানকে এ ভুলের মাশুল দিতে হয় । একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় লাভজনক ব্যবসায়ের সন্ধান পেয়ে লেখাপড়া শেষ না করেই তাতে ঢুকে পড়লো । এক পর্যায়ে ব্যবসায় বন্ধ । অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিটাও নেয়া হলো না । জীবনটাই মাটি হওয়ার পালা । একটা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিগণ কাজ বাড়বে চিন্তা করে বেশি লোক নিয়োগ দিলেন । কাজ বাড়লো না কিন্তু বেশি লোক নিয়োগের কারণে ব্যয়সহ নানান জটিলতা প্রতিনিয়তই ভোগ করতে হচ্ছে । সমস্যা নিরসনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে নতুন নতুন সমস্যা মোকাবেলার নজীর প্রায়শই লক্ষণীয় । শ্রমিকদের দু'টি দল গন্ডগোল করেছে । কর্তৃপক্ষ দু'দলের দু'জনকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন । পরে দেখা গেল সব শ্রমিক একত্রিত হয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে । তাই নানান বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেই প্রতিষ্ঠান সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় । এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:
১. সমস্যার প্রকৃতি (Nature of problem): যে সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে তা সমস্যা হিসেবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সমস্যার প্রকৃতি ও গভীরতা কেমন ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হয় । অনেক সময় প্রতিষ্ঠান ছোট বিষয়কে বড় করে দেখে সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু পরে দেখা যায়, নতুন সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্যভাবে ম্যানেজ করা যেতো । অনেক সিদ্ধান্ত থাকে যেগুলো পৌনঃপুনিক প্রকৃতির; যেমন- কাঁচামাল ক্রয়, মজুত পণ্য বিক্রয়, কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি । যেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ । কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত থাকে যেগুলির প্রভাব ও ফলাফল ব্যাপক হয়ে থাকে; যেমন- শ্রমিক অসন্তোষ, কারখানা পুড়ে যাওয়া, অন্য কোম্পানির সাথে একত্রীভূত হওয়া ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক ভেবে-চিন্তে সমস্যা মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। পড়ে ।
২. ভবিষ্যৎ অবস্থা (Future condition): সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ভবিষ্যৎ অবস্থা কী দাঁড়াবে তাও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয় । কাঁচামালের দাম কমেছে বিবেচনায় একটা প্রতিষ্ঠান বেশি কাঁচামাল কিনে তা মজুদ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে । কিন্তু যদি দেখা যায়, বাজারে পণ্যের চাহিদা এ সময়ে কম থাকবে বিধায় বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কিনলে তা অব্যবহৃত অবস্থায় গুদামে পড়ে থাকবে । এতে পুঁজি আটকে থাকার এবং কাঁচামাল নষ্ট হওয়ার ঝুঁকির সৃষ্টি হবে। তা হলে কর্তৃপক্ষ এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বিরত থাকবে । ভবিষ্যৎ অবস্থা নিশ্চিত হলে একভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কিন্তু যদি এরূপ অবস্থা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার নির্দেশ করে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন পড়ে ।
৩. প্রাপ্ত তথ্য (Received information) : সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমবেশি তথ্য বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে । ধারণা বা অনুমানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিলে অনেক সময়ই তা ক্ষতির কারণ হয় । একজন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল সরবরাহ করেন। বাজার সম্পর্কে পর্যাপ্ত খোঁজ-খবর না নিয়ে তাকেই মাল সরবরাহের ফরমায়েশ দেয়া হচ্ছে। বাজারে কাঁচামালের মূল্য কমলেও সঠিক তথ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট থাকায় পুরনো দামে মাল কেনার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর । তথ্য পেলেও সেই তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেটাও দেখা দরকার । সবমিলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকার ও তার বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে ।
৪. সিদ্ধান্ত লক্ষ্য (Decision goal): অনেক সময় বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের লক্ষ্যকে যথার্থরূপে বুঝে নিয়ে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এগুনোর প্রয়োজন পড়ে । ধরা যাক, শ্রমিক-কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল দেয়া হবে । এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য হতে পারে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের মধ্যে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হবে এবং জনশক্তিও তাতে সন্তুষ্ট থাকবে । এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে শ্রমিক- কর্মচারীদের সাথে ঊর্ধ্বতন মত বিনিময় করতে পারেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটিতে কর্মচারীদের প্রতিনিধি রাখতে পারেন । এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে যেভাবেই হোক নতুন বেতন কাঠামো যেনো সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। শ্রমিক-কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নিতে যেন তা নতুন অভিযোগের সৃষ্টি না করে সে বিষয়টিও মনে রাখা আবশ্যক ।
৫. সহযোগিতার মাত্রা (Degree of co-operation): সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী পক্ষসমূহের সহযোগিতা কেমন পাওয়া যাবে সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা আবশ্যক । প্রতিষ্ঠানে অধস্তনরা যোগ্য ও আন্তরিক হলে উর্ধ্বতন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ভালো না হলে বা অধস্তনরা যোগ্য না হলে তাদের নিকট থেকে যথোপযুক্ত সহযোগিতা পাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠানে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা, শিল্পীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে এরূপ সহযোগিতার মাত্রা বেশি হয় ।
৬. প্রাপ্তব্য সময় (Receivable time): সিদ্ধান্তের সাথে সময়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । ভালো সিদ্ধান্ত নিলেই চলে না- যথাসময়ে ঐ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন । সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটা সময়ের পার্থক্য থাকে । যদি এমন সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, তা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ঐ সিদ্ধান্ত উত্তম সিদ্ধান্ত নয় । সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা, পরামর্শ ইত্যাদি কাজে সময়ের দরকার হয় । মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সেখানেও সময়ের প্রয়োজন। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগও যথাসময়ে নেয়া আবশ্যক ।
বর্তমানকালে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সো'ট (SWOT) বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয় । SWOT বিশ্লেষণ বলতে শক্তি (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ভীতি (Threat)- এ চারটা ও উপাদান বা বিষয়কে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করাকে বুঝায়। যার প্রথম দু'টি অভ্যন্তরীণ উপাদান এবং পরের দু'টি বাহ্যিক উপাদান বিবেচনা করা হয়ে থাকে। শক্তি (Strength) এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, জনশক্তির উচ্চ মান ইত্যাদি বিষয় পড়ে । দুর্বলতা (Weakness ) এর মধ্যে মূলধনের অভাব, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, সুনামের অভাব ইত্যাদিকে বুঝায়। অন্যদিকে সুযোগ (Opportunity) বলতে বাজার সম্ভাবনা, প্রতিযোগীদের দুর্বল অবস্থা, অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি বুঝানো হয় । ভীতি (Treat) এর মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগী পরিবেশ, অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা, শক্তি-সম্পদের অভাব ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ।
ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপকীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকগুলো বাধার সম্মুখীন হন, সেগুলো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে । এসব প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলোর অধিকাংশই সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অক্ষমতা বা অযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত থাকে । নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথে সৃষ্ট প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ করা হলো:
১. অপূর্ণাঙ্গ বা অসম্পূর্ণ তথ্য (Imperfect or incomplete information) : অনেক সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ব্যবস্থাপকগণ পান না এবং সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হলে পর্যাপ্ত সময় ও অর্থ ব্যয়ের যে প্রয়োজন পড়ে তারও সুযোগ সর্বত্র থাকে না । ফলে অপূর্ণাঙ্গ বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় । এতে সিদ্ধান্ত সঠিকতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না ।
২. সমস্যা ও বিকল্পসমূহের অসঠিক শনাক্তকরণ (Inaccurate identification of prablem or alternatives): অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ যথাযথভাবে সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারেন না কিংবা কার্যকর বিকল্পসমূহের সন্ধান পান না । সমস্যার লক্ষণকেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করায় প্রকৃত সমস্যা অনাবিষ্কৃত থাকে । তাই ভুল বা অসঠিক সমস্যার চিহ্নিতকরণ থেকে সঠিক সমাধান পাওয়া সম্ভব নয় । যে কারণে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবস্থাপকদের সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সতর্কতার সাথে বিকল্পসমূহ নির্ধারণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন ।
৩. পক্ষপাতমূলক ঝোঁক (Biasness): সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না । তার বা তাদের মধ্যে পক্ষপাতমূলক ঝোঁক সৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়। শ্রমিকদের মধ্যকার গণ্ডগোল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন নিজেই যদি একটা পক্ষ নিয়ে ফেলেন তখন সিদ্ধান্ত যেমনি যথার্থ হয় না তেমনি বাস্তবায়নে আরেকটা পক্ষ ঐ সিদ্ধান্ত মানতে চায় না । তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ ধরনের প্রবণতা পরিহার করা উচিত।
৪.সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা (Timidity): অনেক নির্বাহী থাকেন যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাজটি চালিয়ে নেয়াটাকেই তারা প্রাধান্য দেন। নিজে সিদ্ধান্ত না দিয়ে অনেক সময় কোনো অধস্তনের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেন। এক্ষেত্রে এরূপ অধস্তনের দেয়া সিদ্ধান্ত তার সহকর্মীগণ মানতে চায় না। অনেক সময় ঊর্ধ্বতন সিদ্ধান্ত দিলেও যতটা আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক তার ঘাটতি থাকে । ফলে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয় । ফলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ থেকেই সিদ্ধান্ত আসা উচিত ।
৫. আবেগের প্রভাব (Effect of emotion): আবেগের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীতমুখী সম্পর্ক লক্ষণীয় আবেগ যত প্রবল হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ততই কার্যকারিতা হারায়। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিকল্প উদ্ভাবন, মূল্যায়ন ও উত্তম বিকল্প গ্রহণ আর সেক্ষেত্রে মূল্যবান বিবেচিত হয় না। ব্যক্তি আবেগনির্ভর হয়ে পড়লে যত না ক্ষতি হয় তার চেয়ে একটা দল যখন আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তখন গৃহীত সিদ্ধান্তের মান নিঃসন্দেহে দুর্বল হয় এবং তার বাস্তবায়নে নানান জটিলতা দেখা দেয় । তাই আবেগমুক্ত থেকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ।
৬. উপকরণের অপ্রতুলতা (Inadequacy of input factors) : সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ, মানবীয় সম্পদ ও ভৌত সম্পদের অভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না । প্রয়োজনীয় মূলধন, জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের অপর্যাপ্ততাই অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার প্রধান কারণ । তাই যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা যেনো যথাযথভাবেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং উপকরণের অপ্রতুলতার অভাবে যেনো তা অবাস্তবায়িত না থাকে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সতর্ক থাকা উচিত ।
৭. সহযোগিতার অভাব (Lack of co-operation) : সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনেক ক্ষেত্রেই অধস্তনরা ঊর্ধ্বতনদের সহযোগিতা করে না । অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদির অভাবেই সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় না। তাই অধস্তনদের সহযোগিতার অভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে যতটা সম্ভব অধস্তনদের পরামর্শ গ্রহণ বা সম্পৃক্ত করা গেলে এরূপ সহযোগিতা লাভ সহজ হয় ।
যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না বা নেয়া যায় না। আবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও যথাসময়ে ও যথনিয়মে তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পরবর্তীতে ঐ সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা থাকে না । ক্ষেত্রবিশেষে তা বাস্তবায়নকালে নতুন নতুন বিপত্তি দেখা দেয় । তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকালে যে সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে- তা কিভাবে সমাধা করা যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পক্ষের পূর্বধারণা থাকা আবশ্যক । নিম্নে এরূপ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:
১. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ (Collecting necessary informations): সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথার্থতা উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের ভিতর ও বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা গেলে তার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমনি সহজ হয় তেমনি বাস্তবায়নকালে যে সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে তাও আগাম অনুধাবন করা যায় । ফলে সমস্যাগুলো সমাধানে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় ।
২. সঠিক বিকল্প নির্বাচন (Selecting proper alternatives): সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সঠিক বিকল্পই সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচ্য। তাই কার্যকর বিকল্পগুলো যদি সঠিকভাবে দাঁড় করানো যায় এবং বাস্তবতা বিবেচনায় সেগুলো যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় তবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়ে থাকে । এভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে তার বাস্তবায়নও সহজ হয় । তাই কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে সঠিক বিকল্প নির্বাচন করা উচিত ।
৩. যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Taking decision in time): সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়ন যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল । সময় পরিবর্তনের সাথে অবস্থা বদলায় । যে পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার ছিল বিলম্ব হলে সেই পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে। ফলে সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ধরা যাক, প্রতিষ্ঠানের একটা মেশিনে কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্রুত মেরামত প্রয়োজন । সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হওয়ায় মেরামতে যেয়ে দেখা গেল মেশিনটি আর মেরামতের অবস্থায় নেই, বদলাতে হবে ।
৪. প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ গ্রহণ (Consulting with concerned persons if necessary): যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা উত্তম ফল দেয় । সিদ্ধান্ত যদি কোনো পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয় তবে তাদের সাথে আলোচনা করলে ক্ষেত্রবিশেষে অনেক ভালো ফল পাওয়া সম্ভব । সিদ্ধান্ত যারা বাস্তবায়ন করবে তাদের সাথে পরামর্শ করলে তাতে যেমনি সিদ্ধান্তের মান বাড়ে সেই সাথে বাস্তবায়নে তাদের কার্যকর সহযোগিতা লাভও সম্ভব হয়ে থাকে ।
৫. যথাসময়ে সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ (Informing decision in time): যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই চলে না যারা ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে তাদেরকে যথাসময়ে ও যথানিয়মে সিদ্ধান্ত অবহিত করাও আবশ্যক । অনেক সময় দেখা যায় তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা নিচের পর্যায়ে ঠিক সময় পৌছুলো কি না সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেয় না । অনেক সময় সিদ্ধান্ত যে প্রক্রিয়ায় জানালে উত্তম ফললাভ সম্ভব তা না করে শুধুমাত্র একটা সার্কুলার দিয়েই দায়িত্ব শেষ করা হয় । ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয় ।
৬. প্রয়োজনীয় সহায়তা দান (Providing necessary assistance): সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকালে বাস্তবায়নকারী পক্ষের বিভিন্ন উপকরণগত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে । তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণগত সহায়তা কখন, কতটা লাগবে এবং তা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে তাও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পক্ষকে ভাবতে হয় এবং সে অনুযায়ী তা সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে । বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্টদের যদি প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি, অর্থ, মালামাল ইত্যাদির জন্য ঊর্ধ্বতনের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় তবে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না ।
৭. কার্যকর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ (Effective supervision and control): সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইলে কার্যকর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ । সিদ্ধান্ত জানানোর পর উর্ধ্বতন যদি তার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ-খবর না নেয়, বাস্তবায়নকালে কোনো ভুল হচ্ছে কি না তা না দেখে- তবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যে সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ সেখানে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়কাল নির্ধারণপূর্বক প্রতিটা পর্যায় শেষে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা উচিত।
ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সংগঠন। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদিকে সঠিকভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন পড়ে । ভূমি, শ্রম ও মূলধন - এ তিনটি উপাদান উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা আলাদা আলাদাভাবে কোনো উৎপাদন করতে অক্ষম। একটা প্রতিষ্ঠানেও মানুষ, যন্ত্রপাতিসহ নিয়োজিত উপকরণাদি পৃথকভাবে কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না । যখন এগুলোকে সংঘবদ্ধ করে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগ করে দেয়া হয় ও একের সাথে অন্যের সম্পর্ক নির্ণীত হয় তখন তা একটা কাঠামোর সৃষ্টি করে ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। এভাবে সংঘবদ্ধ করার কাজকেই সংগঠিতকরণ বা সংগঠন বলে । একটা ছোট প্রতিষ্ঠানে যেভাবে সংগঠন কাঠামো গড়ে তোলা হয় একটা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে সেভাবে সংগঠন কাঠামো গড়ে তুললে চলে না । একটা উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং বিক্রয়ধর্মী প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোতেও ভিন্নতা লক্ষণীয় । প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বা চালাতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিরই সংগঠন ও সংগঠন কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক ।
এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা (শিখন ফল)
১. সংগঠিতকরণ ও সংগঠনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
২. আদর্শ সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৩. সংগঠিতকরণ ও সংগঠনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ।
৪. উত্তম সংগঠনের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবে ।
৫. সংগঠন কাঠামোর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৬. বিভিন্ন ধরনের সংগঠন কাঠামোর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৭. সরলরৈখিক, সরলরৈখিক ও পদস্থ, কার্যভিত্তিক, কমিটি ও মেট্রিক্স সংগঠনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৮. সংগঠন কাঠামো প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
সংগঠিতকরণের সমার্থক শব্দ হলো সুসংবদ্ধকরণ, গঠনকরণ, নির্মাণ, সংগঠন ইত্যাদি । অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদানকে বা আলাদা আলাদা কোনোকিছুকে যখন একত্রে সুসংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত করা হয় তখন তাকে সংগঠিতকরণ বলে । কাজ বিবেচনায় সংগঠন ও সংগঠিতকরণ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় । অন্যদিকে গুণ বা ভাব অর্থে কিছু লোক মিলে গড়ে তোলা দল বা প্রতিষ্ঠানকে সংগঠন বলে । কিছু লোক যখন একই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় তখন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। সেখানে কেউ নেতা ও কেউ অনুসারী বা কেউ ঊর্ধ্বতন (Boss) ও কেউ অধস্তন (Subordinate) হিসেবে কাজ করে । এক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় । কে কার নিকট থেকে কাজের নির্দেশ লাভ করবে ও কার নিকট জবাবদিহি করবে তাও বলে দেয়া হয় । এভাবে সংঘবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটা সম্পর্কের কাঠামো গড়ে ওঠে । সংঘবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার এরূপ সম্পর্কের কাঠামোকে তাই সংগঠন নামে অভিহিত করা হয় ।
'Organising' শব্দটি 'Organism' হতে এসেছে। যার অর্থ হলো কোনো পৃথক সত্তাবিশিষ্ট অংশগুলোকে এতখানি সমন্বিত করা যার ফলে প্রত্যেক অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক (Whole) কোনো কিছুর সৃষ্টি হয় । শিশুরা যেমন কতকগুলো প্লাস্টিকের বিল্ডিং তৈরির উপযোগী ছোট ছোট অংশকে একত্রে জুড়ে দিয়ে খেলনা বাড়ি তৈরি করে, একজন সংগঠকও তেমনি বিভিন্ন উপায়-উপকরণকে একত্রিত করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে । খেলনার ছোট ছোট অংশ হতে কার্যত কোনো কিছুই অনুমান করা যায় না, কিন্তু যখন এগুলোকে একত্রে জুড়ে দিয়ে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তখনই তা একটা বাড়ির রূপ ধারণ করে । ঠিক একইভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে উপায়-উপকরণ যা থাকে তা আলাদাভাবে কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। যখন এগুলোকে কাজ অনুযায়ী আলাদা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কাজের জন্য উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট করা হয় এবং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তখন তা লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযোগী একটা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের রূপলাভ করে । তাই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজকে বিভাজন, প্রতিটা বিভাগের দায়িত্ব-কর্তৃত্ব নির্দিষ্টকরণ ও অর্পণ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার কাজকেই সংগঠন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে ।
সংগঠন হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় ও বস্তুগত উপকরণাদিকে সংহত ও সঠিকভাবে কাজে লাগানোর একটি প্রক্রিয়া। L. A. Allen বলেছেন, 'সংগঠন হলো একটি প্রক্রিয়া যা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় কার্যাদি শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িতকরণ ও বণ্টন এবং কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত।” উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সংগঠন প্রক্রিয়ার যে সকল পদক্ষেপ লক্ষণীয় তা নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হলো :
ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :
১. কার্য বিভাজন বা বিভাগীয়করণ (Departmentation of jobs) : ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ বা পদক্ষেপ হলো কার্যাদি সঠিকভাবে শনাক্ত বা নির্দিষ্ট করে তা প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা । কাজ সঠিকভাবে চিহ্নিত ও ভাগ করা না হলে উপযুক্ত কর্মীসংস্থান ও দায়িত্ব অর্পণ সম্ভব হয় না । ধরা যাক, সজীবকে একটি ক্লাব সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । তাহলে সজীবের প্রথম কাজ হবে ক্লাবের উদ্দেশ্য বুঝে কী কী কাজ করতে হবে তা নির্দিষ্টপূর্বক কাজগুলোকে প্রধান প্রধান কতকগুলো ভাগে ভাগ করা; যেমন -অফিস বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ, সংস্কৃতি বিভাগ ইত্যাদি ।
২. দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িতকরণ (Defining authority and responsibility) : কাজ ভাগ করার পর সংগঠন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রত্যেক কাজের জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমারেখা নির্দিষ্ট করা । উৎপাদন বিভাগ এবং ক্রয় বিভাগ পাশাপাশি থাকলে যদি প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ঠিক করে দেয়া না হয়, কোন মালামাল কোন বিভাগ ক্রয় করবে এ বিষয়ে যদি সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব ভাগ না থাকে তবে কার্যক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়া স্বাভাবিক । প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট থাকলে সে অনুযায়ী প্রত্যেককে জবাবদিহি করা সহজ হয় । ফলে ফাঁকিবাজী, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো ইত্যাদির সুযোগ থাকে না ।
৩. দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ (Delegation of authority and responsibility) : দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমারেখা নিরূপণের পর সংগঠন প্রক্রিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো প্রত্যেক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, বিভাগ বা উপবিভাগকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দেয়া । এক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সব সময়ই সমান হওয়া উচিত । প্রত্যেক ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় । সেই সাথে প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝে নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে কার্যক্ষেত্রে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় ।
৪. পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ (Determining interpersonal relation) : সংগঠন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। এক্ষেত্রে কে কার ঊর্ধ্বতন এবং কে কার অধস্তন তা ঠিক করা হয় । কে কার নিকট থেকে নির্দেশ লাভ করবে ও কার নিকট জবাবদিহি করবে তা বলে দেয়া হয় । তবে এক্ষেত্রে যাতে কখনই দ্বৈত অধীনতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন ।
উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলা হয় । সংগঠন কাঠামো মজবুত ও শক্তিশালী হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উপায়-উপকরণের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হয়ে থাকে ।
মিসেস নাসরীন বড় চাকরি করেন । বাসা-বাড়ির কাজে তেমন সময় দিতে পারেন না । তাই তিনটা কাজের মেয়ে রেখেছেন । তারা কাজ নিয়ে প্রায়শই ঝগড়া করে । কোনো কাজ কেন হয়নি জিজ্ঞাসা করলে একজন আরেকজনের ওপর দোষ চাপায় । সারাদিন পর অফিস থেকে ফিরে কাজের মেয়েদের ঝগড়া মিটাতেই তার নাভিশ্বাস । তিনি এ সমস্যাটা তার বান্ধবী মিসেস চৌধুরীকে বললেন । বান্ধবীর পরামর্শ, প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা করে ভাগ করে দাও। কে ঘর-দোর, হাড়ি-পাতিল পরিষ্কার করবে, কে কাপড়-চোপড় ধোয়া ও ঘর-দোর গুছানোর কাজ করবে এবং কে রান্নাবান্না করবে- এটা ঠিক করে দিলে দেখবে কাজও ভালো হচ্ছে, ঝগড়াও কমে গেছে । সম্ভব হলে তিনজনের মধ্যে যে একটু বয়স্ক ও অন্যদের চালাতে পারবে- তাকে অন্য দু'জনের ওপর দায়িত্বশীল করে দাও । সেক্ষেত্রে তুমি যাকে দায়িত্ব দিয়েছো তার সাথে যোগাযোগ করে কাজ সম্পর্কে খোঁজ- খবর নিতে পারবে । মিসেস চৌধুরীর কথামতো কাজ করে মিসেস নাসরীন ভালো ফল পাচ্ছেন। একটা বাসা- বাড়িতে তিনজনের কাজ ভাগ করে তাদের সংগঠিত না করলে যদি সমস্যা হয় তবে যেখানে নানান মানের শত শত কর্মী কাজ করে তাদেরকে সঠিকভাবে সংগঠিত করে কাজ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিতে না পারলে সঠিকভাবে কাজ বুঝে নেয়া বা শৃঙ্খলার সাথে কাজ পরিচালনা করা কখনই সম্ভব নয় । তাই সংগঠিত করার বা সংগঠনের বেশ কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তাকে আদর্শ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা যায় । এরূপ সংগঠনের কতিপয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
১. উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতা (Objects oriented) : প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যকে ঘিরে কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হওয়াকেই উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতা বলে । একটি উত্তম সংগঠনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি এমনভাবে বিন্যস্ত ও সংহত করা হয় যাতে তা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। উৎপাদনধর্মী একটি প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে সংগঠিত করা হয় একটি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সেভাবে সংগঠিত করলে চলে না । একটি সামরিক ও একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে একইভাবে সাজানো হয় না । তাই একটি ভালো সংগঠনে এর কার্য বিভাজন, দায়িত্ব-কর্তৃত্ব নির্ধারণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণে এর উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে ।
২. সহজবোধ্যতা (Easy understanding) : সহজে চেনা যায়, বোঝা যায় বা ধারণা লাভ করা যায় কোনো বিষয়ের এমন গুণকেই সহজবোধ্যতা বলে । একটি উত্তম সংগঠনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য হতে হয় । একটি সংগঠন চার্ট দেখে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরের যে কেউ যাতে এর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন পদ, পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তৃত্ব শৃঙ্খল (Chain of command) ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পেতে পারে-একটি উত্তম সংগঠনে তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। সংগঠন জটিল হলে সেখানে আদেশ দান, যোগাযোগ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে সব সময়ই সমস্যা দেখা দেয় এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক কার্যধারা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।
৩. বিশেষায়ণের সুযোগ (Opportunity of specialization): বিশেষ কাজে কর্মীর বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের সুযোগকেই বিশেষায়ণের সুযোগ বলে । একটা উত্তম সংগঠনে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে এমনভাবে বিভাজন করা হয় যাতে বিশেষায়ণের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী যদি একটা কাজ করে তবে সে ঐ একক কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে । কিন্তু তাকে যদি একই সাথে একাধিক কাজ দেয়া হয় তবে তার পক্ষে কোনো কাজেই যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় না । তাই সংগঠনে কার্য বিভাজন এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণকালে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে ।
৪. সুসংজ্ঞায়িত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব (Well-defined responsibility and authority) : কর্তৃত্ব হলো আদেশ দানের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব হলো জবাবদিহি করার বাধ্য-বাধকতা । কোনো ব্যক্তি বা বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কতটা— তার সুস্পষ্ট বর্ণনা ও যথাযথ অনুসরণ একটি ভালো সংগঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । প্রতিষ্ঠান যতো বড় হয় বা এর কাজ যতো জটিল হয় ততোই সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের দায়িত্ব-কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা না হলে ভুল বোঝাবুঝি ও জটিলতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা থাকে । তাই একজন ভালো সংগঠক তার প্রতিষ্ঠানের ওপর হতে নিচ পর্যন্ত সকল পদে কর্মরত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন ।
৫. ভারসাম্যপূর্ণ (Well-balancing) : কাজের ভারে এবং দায়িত্ব-কর্তৃত্বের মাত্রায় সামঞ্জস্য বিধানের গুণকেই ভারসাম্যপূর্ণ বলে। একটি উত্তম সংগঠনকে অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হয়। এক্ষেত্রে বিভাগ ও উপবিভাগ এমনভাবে খোলা হয় যাতে প্রত্যেকটি বিভাগই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও একে অন্যের সহযোগী হয়ে উঠতে পারে । প্রত্যেকেই পরিমিত কাজ পায় । কোনো ব্যক্তি বা বিভাগ কর্মভারগ্রস্ত আবার কারও তেমন কোনো কাজ নেই এমন অবস্থার সুযোগ উত্তম সংগঠনে থাকে না। এ ছাড়া একটি উত্তম সংগঠনে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যেও ভারসাম্য বজায় থাকে। অধিক কেন্দ্রীকরণ যেনো কাউকে স্বেচ্ছাচারী না করে এবং অধিক বিকেন্দ্রীকরণ শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করা হয়ে থাকে ।
৬. আনুগত্য ও শৃঙ্খলা (Loyalty and discipline) : অন্যের বশ্যতা স্বীকার বা বাধ্যতার গুণকে আনুগত্য বলে । অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মান্য করে চলা শৃঙ্খলা হিসেবে গণ্য । একটি কার্যকর সংগঠনে আনুগত্য ও শৃঙ্খলার ভাবধারা সব সময়ই বজায় থাকে । প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট থাকায় প্রত্যেকেই যার যার কাজ সম্পাদন করে । কেউ কোনোরূপ ফাঁকি দিলে সাংগঠনিক নিয়মের কারণে তা সহজেই ধরা পড়ে যায় । জবাবদিহিতা করাও দ্রুত ও সহজ হয় । ফলে কার্যক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার কোনোই সুযোগ থাকে না । প্রতিষ্ঠানে 'জোড়া-মই-শিকল' নীতি অনুসরণ করায় প্রত্যেকেই অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করে । উপর হতে নিচের দিকে পর্যায়ক্রমে কর্তৃত্বরেখা প্রবাহিত হওয়ায় প্রত্যেকেই তার ঊর্ধ্বতনের নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য থাকে । ফলে আনুগত্যহীনতার সুযোগ থাকে না ।
সংগঠন হলো ইঞ্জিন সদৃশ । ইঞ্জিন অচল হলে ড্রাইভার, বডি বা বগির যেমন কার্যকারিতা থাকে না তেমনি একটা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন বা সংগঠিতকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে না হলে তা চলতে পারে না। মনে করি একটা উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বিভাগ খোলা হয়েছে কিন্তু বিক্রয় বিভাগ খোলা হয়নি বা বিক্রয় বিভাগ খোলা হয়েছে কিন্তু তার অধীনে জেলা বা আঞ্চলিক বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি । তাহলে প্রধান অফিসের পক্ষে ৬৪টি জেলার বিক্রয় কাজ সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান ও বিক্রয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না । প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া যেমনি জরুরি তেমনি একের সাথে অন্যের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেয়ারও প্রয়োজন পড়ে। এতে কে কার নিকট জবাবদিহি করবে, আদেশ লাভ করবে-এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এতে সংগঠনে কর্তৃত্ব রেখা ও যোগাযোগ প্রবাহ সম্পর্কে প্রত্যেকে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে । অতঃপর কোনো নির্দেশ দিলে তা যথানিয়মে সংশ্লিষ্টদের নিকট পৌঁছে ও তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় । এভাবে নির্দেশ দান ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটা প্রতিষ্ঠান সচল থাকে ও গতিশীলতা লাভ করে। তাই একটি প্রতিষ্ঠানে যদি উদ্দেশ্য অর্জনের উপযোগী করে একটা সংগঠন কাঠামো তৈরি এবং সে অনুযায়ী কাজ ও উপায়-উপকরণ সংহত করা সম্ভব না হয় তবে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য সকল কাজ কখনই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না । নিম্নে বিভিন্ন দিক হতে সংগঠনের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:
১. উদ্দেশ্যার্জনে সহযোগিতা (Aid to accomplishment of objective ) : ব্যবস্থাপনা সংগঠনে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি এর প্রকৃতি বা অন্য কোনো সুবিধাজনকভাবে ভাগ করে এর প্রত্যক ভাগের দায়িত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর অর্পণ করা হয় । কার্যকর শ্রমবিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে নির্বাহীগণ স্ব-স্ব কার্যক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে । প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট থাকায় প্রত্যেকেই স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে উদ্বুব্ধ হয় । ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন সহজতর হয়ে থাকে ।
২. উপকরণের যথাযথ ব্যবহার (Effective utilization of resources) : একটি কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় ও বস্তুগত সকল উপকরণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় । এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজকে সঠিকভাবে ভাগ করে প্রত্যেকটি কাজ বা বিভাগের জন্য কোন্ মানের জনশক্তি ও উপায়-উপাদানের প্রয়োজন হবে তা নির্ণীত হয়। এ ছাড়া প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণপূর্বক কে কার নিকট জবাবদিহি করবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়। এর ফলে জনশক্তিসহ সকল উপকরণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
৩. বিশেষীকরণে সহায়তা (Aid to specialization) : প্রতিষ্ঠানে একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিশেষায়ণ ও শ্রম বিভাগের নীতির মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়। একজন কর্মীর জন্য একই ধরনের কাজ নির্দিষ্ট করার প্রয়াস চালানো হয় । এতে কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় । ফলে মিতব্যয়িতা ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ সম্পাদন সম্ভব হয় । এভাবে কার্য সম্পাদনের ফলে প্রত্যেক বিভাগ ও উপবিভাগের কার্যদক্ষতা বাড়ে, নির্বাহীর পক্ষে তত্ত্বাবধান সহজ হয় এবং কাজের মানও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ।
৪. সহজ সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ (Smooth co-ordination and control) : সংগঠন কাঠামো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উপর হতে নিচ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিভাগ ও উপবিভাগের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্টের পাশাপাশি এদের মধ্যকার সম্পর্কও নির্ণীত হয়। এ ছাড়া কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠায় 'জোড়া-মই-শিকলের' নীতি অনুসৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি ও উপায়-উপাদানকে একে অন্যের সহযোগী করে তোলার চেষ্টাও করা হয়ে থাকে । ফলে প্রত্যেক বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্য স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং সর্বস্তরে সমন্বিত কার্যব্যবস্থা পরিচালিত হয় ।
৫. সৃজনশীলতার বিকাশ (Development of creativity) : উত্তম ও শক্তিশালী সংগঠন কাঠামো বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত নির্বাহী ও কর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে । যথোপযুক্ত কর্তৃত্ব লাভে যেমনি কর্মী বা নির্বাহী সন্তুষ্ট হয় তেমনি পূর্বে বর্ণিত দায়িত্ব তাকে নিজ যোগ্যতা অর্জনে উৎসাহিত করে । প্রত্যেকের কর্তৃত্ব সীমা নির্দিষ্ট থাকায় নিজ কর্তৃত্ব সীমার মধ্যে কিভাবে সুন্দররূপে দায়িত্ব পালন করা যায় নির্বাহী বা কর্মী তা চিন্তা করে । এ ছাড়া সংগঠন কাঠামোতে পদোন্নতির গতিপথ পূর্বনির্দিষ্ট থাকায় কর্মীও সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে । এতে তার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে ।
৬. কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা (Establishing effective leadership) : কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য । এরূপ নেতৃত্ব সৃষ্টি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির কার্যকর বিভাজন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট বর্ণনা, কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধান, আনুগত্যের ভাবধারা প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার মতো পরিবেশ সৃষ্টির ওপর। এ ছাড়া কাজের চাপকে একটা কাম্য মাত্রায় ধরে রাখার বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । উত্তম সংগঠনই মাত্র এ সকল সুযোগ নিশ্চিত করে কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে ।
৭. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা (Establishing discipline) : সাংগঠনিক শৃঙ্খলা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য । এরূপ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষণীয় । কার্য বিভাজন, দায়িত্ব-কর্তৃত্ব নিরূপণ, কে কার অধীন, কে কার ঊর্ধ্বতন, কে কার কাছ থেকে নির্দেশ পাবে এবং কার কাছে কাজের জন্য জবাবদিহি করবে ইত্যাদি বিষয় যদি সঠিকভাবে পূর্বেই নির্ধারণ করা না হয়, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে যদি সমস্যা থাকে তবে কার্যক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় । কার্যকর সংগঠনের মাধ্যমেই এরূপ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায় ।
নীতি হলো কোনো কাজ সম্পাদনের সাধারণ নির্দেশিকা (Guidance for action)। দীর্ঘ দিনের কার্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সকল ক্ষেত্রেই এমন কিছু নিয়ম-নীতি গড়ে ওঠে বা গৃহীত হয় যা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে ঐ কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায়। এ ধরনের নিয়ম বা দিক-নির্দেশনাকেই নীতি বলা হয়ে থাকে। কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এমন কিছু নিয়ম-রীতি বা নীতিমালা লক্ষণীয় । নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :
১. লক্ষ্যের নীতি (Principle of goals) : প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সামনে রেখে সংগঠন গড়ে তোলার নীতিকেই লক্ষ্যের নীতি বলে । কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠায় একজন সংগঠককে প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হয়। লক্ষ্য যেমন হবে সংগঠনকেও সেভাবেই গড়ে তোলা আবশ্যক । এলাকার উন্নয়নে একটা ক্লাব গড়তে যেয়ে সংগঠনকে যেভাবে তৈরি করার প্রয়োজন হয় একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকে সেভাবে গঠন করলে চলে না। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ কারণেই সংগঠন কাঠামোতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় ।
২. দক্ষতার নীতি (Principle of efficiency) : কমশক্তি ও উপায়-উপকরণ ব্যয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নীতিই হলো দক্ষতার নীতি। ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠায় দক্ষতার বিষয়টি সবসময়ই সামনে রাখতে হয়। সংগঠনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্য প্রবাহের গতিপথ রচিত হয়ে থাকে । যেখানে যে বিভাগ খোলা প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রত্যেকের জন্য যেভাবে নির্ধারণ করা উচিত, সম্পর্ককে যেভাবে ঠিক করে দেওয়া আবশ্যক তা যদি করা না যায় তাহলে পরবর্তী সময়ে যতো নিষ্ঠা সহকারে কাজ করা হোক না কেন দক্ষতাসহকারে তা সম্পাদন ও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হয় না ।
৩. কাম্য পরিসর নির্ণয়ের নীতি (Principle of determining optimum span of supervision) : একজন নির্বাহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাম্য সংখ্যক অধস্তন ন্যস্ত করার নীতিকেই কাম্য পরিসর নির্ণয়ের নীতি বলে । প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত প্রত্যেক নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকগণ প্রত্যক্ষভাবে কতজন অধস্তনের কাজ তত্ত্বাবধান করবেন তা সংগঠন কাঠামোতে নির্দিষ্ট করা হয় । এক্ষেত্রে একজন নির্বাহীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এমন পরিমাণ নির্বাহীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে তার পক্ষে অধস্তনদের কাজ সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা যায় । এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের উপরিস্তরে তত্ত্বাবধান পরিসর ছোট এবং নিচের দিকে তত্ত্বাবধান পরিসর কিছুটা বড় রাখতে হয় ।
৪. জোড়া-মই-শিকলের নীতি (Principle of scalar-chain) : প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল ব্যক্তি ও বিভাগকে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত করার নীতিকেই জোড়া-মাই-শিকলের নীতি বলে । একটি মজবুত ব্যবস্থাপনা সংগঠনে জোড়া মই-শিকলের নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ উপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত প্রত্যেক বিভাগ, উপবিভাগ ও ব্যক্তির কাজকে এমনভাবে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে কেউই এর বাইরে না থাকে । এরূপ শিকল প্রতিষ্ঠার ফলে কর্তৃত্ব প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । এতে আদেশ দান ও এর বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং দলীয় প্রচেষ্টা জোরদার হয় ।
৫. দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণের নীতি (Principle of defining specific responsibility) : দায়িত্ব হলো কর্ম সম্পাদন বা কর্তব্য পালনের দায়। ব্যক্তি ও বিভাগের কর্ম বা কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে দায় পালনযোগ্য ও জবাবদিহিতামূলক করার নীতিকেই দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণের নীতি বলে। ব্যবস্থাপনা সংগঠনে কর্মরত প্রত্যেক বিভাগ, উপবিভাগ ও কর্মীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক । প্রত্যেকেই যেনো জানতে পারে তার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমা কতদূর । প্রতিষ্ঠানের উপরিস্তরের নির্বাহীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বেশি হয় এবং ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে তা কম হতে থাকে । এতে ঊর্ধ্বতন অধিক কর্তৃত্বশালী হয়। ফলে সে যেমনি অধস্তনদেরকে জবাবদিহি করাতে পারে তেমনি নিজেও জবাবদিহির সম্মুখীন হবে বাধ্য থাকে । এছাড়া কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সবসময়ই সমতা বিধান অপরিহার্য ।
৬. আদেশের ঐক্য নীতি (Principle of unity of command) : একজন কর্মীর আদেশদাতা হবে একজন মাত্র ব্যক্তি - এটা নিশ্চিত করার নীতিকেই আদেশের ঐক্য নীতি বলে । সংগঠন প্রতিষ্ঠাকালে এমনভাবে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বণ্টন করা উচিত যেনো কোনো ক্ষেত্রেই দ্বৈত অধীনতার সৃষ্টি না হয় । অর্থাৎ একজন অধস্তনের যাতে প্রত্যক্ষভাবে একজন মাত্র আদেশকর্তা (Boss) থাকে এবং কোনো কর্মীকেই যেনো তার কাজের রিপোর্ট একাধিক ঊর্ধ্বতনের নিকট পেশ বা জবাবদিহি করতে না হয়। একাধিক আদেশদাতা থাকলে দ্বৈত অধীনতার সৃষ্টি হয় এবং সে অবস্থায় অধস্তনের পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না ।
৭. সারল্য ও সুস্পষ্টতার নীতি (Principle of simplicity and clarity) : সংগঠন কাঠামোচিত্র দেখেই যেন এর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ, কর্তৃত্ব প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে সহজে বোঝা যায় এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যেনো সবাই সহজে বুঝে নিতে পারে- এটা নিশ্চিত করার নীতিকেই সারল্য ও সুস্পষ্টতার নীতি বলে । ব্যবস্থাপনা সংগঠন এমন হওয়া আবশ্যক যাতে তা সহজ ও সরল হয় । এরূপ সংগঠন কাঠামো দেখে সংগঠনের ভিতরে ও বাইরের যে কেউ যেন এর স্তর বিন্যাস, কর্তৃত্বরেখা এবং জনশক্তি ও বিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। প্রত্যেকেই যেন তার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সম্পর্কে এবং নিজস্ব দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয় ।
৮. বিশেষায়ণের নীতি (Principle of specialization) : বিশেষ কাজে কর্মীর বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্ম বিভাজন ও দায়িত্ব অর্পণের নীতিকেই বিশেষায়ণের নীতি বলে । বিশেষায়ণ বলতে কাজকে সুষ্ঠুভাবে বিভাজন করে একজন কর্মীর জন্য একটি কাজ নির্দিষ্ট করাকে বুঝায় যাতে সে একই ধরনের কাজ করতে গিয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় । এতে কর্মীর কার্যদক্ষতা বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে কাজের গতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হয় । কার্য বিভাজনকালে এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা উচিত ।
মি. রায়হান রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করেননি । প্রথমে কয়েকজন কর্মী সাথে নিয়ে তিনি একটা ছোট কসমেটিক্স সামগ্রী তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। প্রথমে নিজেই কর্মীদের কাজ দেখেছেন । উৎপাদিত পণ্য দোকানে ঘুরে ঘুরে বিক্রয় করেছেন। তার উৎপাদিত পণ্যের মান ও এর সুগন্ধ দ্রুতই ক্রেতাদের নজর কাড়ায় তার ব্যবসায় দ্রুত বাড়তে থাকে । এক পর্যায়ে উৎপাদনের কাজ দেখার জন্য তিনি একজন জুনিয়র কেমিস্ট নিয়োগ করেন। বিক্রয় দেখার জন্য বিবিএ পাস করা একজন গ্রাজুয়েটকে দায়িত্ব দেয়া হয় । পরে উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার এবং বিক্রয় কার্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কেটিং বিভাগ খুলে তার অধীনে সেলস প্রমোশন অফিসার নিয়োগ করেন । এখন তার কারখানা অনেক বড় হয়েছে । নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্র বসেছে। সারা দেশে পরিবেশক নিয়োগ দিয়েছেন । প্রশাসনিক বিভাগ, মানবসম্পদ বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, অর্থ বিভাগ ইত্যাদি খুলে বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । এখন তিনি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) । এভাবে তার প্রতিষ্ঠানে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপক ও কর্মী মিলে একটা শক্তিশালী ও দৃশ্যমান সম্পর্কের রূপরেখা গড়ে উঠেছে । যেই সম্পর্কের মূলকেন্দ্রে আছেন তিনি। আর তা ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ হয়ে নিচের দিকে বিস্তৃত হয়েছে । মি. রায়হান ভাবেন, একটা বিল্ডিং যেভাবে ধীরে ধীরে নির্মিত হয়ে একটা বৃহৎ অবকাঠামোতে রূপ নেয় আজ তার শিল্পও ধীরে ধীরে এ ধরনের একটা কাঠামোর রূপ নিয়েছে । প্রথমে তিনি স্বল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে যেই প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন সেখানেও একটা কাঠামো ছিল । কিন্তু আজ তা সত্যিই দৃশ্যমান । মি. রায়হানের প্রতিষ্ঠানে যে সম্পর্কের কাঠামো আমরা অনুমান করতে পারি তাকেই সংগঠন কাঠামো বলে । যদি তা একটা চিত্রে তুলে ধরা হয় তবে তাকে সংগঠন কাঠামো চিত্র (Organogram) বলা হয়ে থাকে ।
সংগঠন কাঠামো হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও কর্মীবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি কাঠামো চিত্র । সংগঠন কাঠামোকে যখন একটি চিত্রে উপস্থাপন করা হয় তখন ঐ চিত্রকে সংগঠন চার্ট নামে অভিহিত করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তর, বিভাগ, উপবিভাগ এবং ক্ষমতা প্রবাহের চিত্র প্রদর্শিত হয় ।
সংগঠন কাঠামোর আয়তন-এর কাজ ও কর্মীর সংখ্যা এবং এর স্তর বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল । স্তর বিন্যাস যত বৃদ্ধি পায় সংগঠন কাঠামোর আয়তনও ততো বাড়ে। সংগঠন চিত্র ততোই ওপরের একক কেন্দ্র হতে নিচের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে । ফলে এটি অনেকটা পিরামিডের আকৃতি পায় । নিম্নে একটা সংগঠন কাঠামো চিত্র তুলে ধরা হলো:
মি. মজুমদার একটা ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ব্যবস্থাপক বা মুখ্য নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন বিশ বছর আগে । তখন তার অধীনে উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের দু'জন ব্যবস্থাপক অধীনস্থ নির্বাহী হিসেবে কাজ করতেন । উৎপাদন ব্যবস্থাপকের অধীনে ছিল দু'জন কর্মী তত্ত্বাবধায়ক ও তাদের অধীনে মোট বিশ জন শ্রমিক । বিক্রয় ব্যবস্থাপকের অধীনে তিনজন বিক্রয় তত্ত্বাবধায়ক এবং তাদের অধীনে মোট ত্রিশ জন বিক্রয়কর্মী । ছোট প্রতিষ্ঠান তাই সহজ সংগঠন কাঠামো ছিল । পরে উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়লো । উৎপাদন বিভাগে নতুন নতুন প্লান্ট বসায় প্রতিটা প্লান্টে আলাদা ম্যানেজার নিয়োগ করা হলো । সেভাবে নিচের স্তরগুলোতে তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রমিক- কর্মীর সংখ্যা বাড়লো। বিক্রয় বিভাগে এরিয়া সেলস ম্যানেজার, সেলস সুপারভাইজার ও বিক্রয় কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো । তাই উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় ব্যবস্থাপককে সহযোগিতার জন্য প্রত্যেককে একজন করে সহকারী দেয়া হলো। তিনি নিজের অধীনেও একজন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছেন। পরবর্তীতে কাজের চাপ ও জটিলতা বাড়ায় এবং ক্ষেত্রেবিশেষে উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপকের মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করে মি. মজুমদার উৎপাদন বিভাগের কাজকে প্রকৃতি অনুযায়ী ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সীমিত কর্তৃত্ব সহযোগে সেখানে আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন । উৎপাদন ব্যবস্থাপককে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (উৎপাদন) হিসেবে পদোন্নতি দেন । উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে সমান গুরুত্ব না পাওয়ায় ব্যবসায় দু-একটা পণ্য নির্ভর হয়ে পড়েছিল । তাই তিনি প্রতিটা পণ্যকে আলাদা প্রজেক্ট ধরে নিয়ে প্রতিটা পণ্যের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছেন । অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণ কার্যিক ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রজেক্ট ম্যানেজারকে সহায়তা করেন । এতে প্রতিটা পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ে মি. মজুমদারকে ভাবতে হয় না। তিনি কোনো সমস্যা হলে সেখানেই শুধু হস্তক্ষেপ করেন। প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানের জন্য অথবা সমন্বয়ের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ঊর্ধ্বতনকে দায়িত্ব দেন । যারা সামষ্টিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন । ফলে প্রতিষ্ঠান বড় হলেও মি. মজুমদার অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন । আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোতে পরিবর্তন আনার কারণেই । তিনি যদি শুরুতে যে সংগঠন কাঠামো পেয়েছিলেন তার ওপর নির্ভর করতেন তবে কোনোভাবেই এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না ।
সংগঠন কাঠামো হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের কাঠামো । এরূপ সম্পর্ক সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তি ও বিভাগের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক অবস্থান ও পদমর্যাদা থেকে সৃষ্ট হলে তাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলে । এর বাইরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মিল- মহব্বত, পছন্দ-অপছন্দ সামাজিক, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন কারণে সম্পর্কের সৃষ্টি হলে তাকে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়ে থাকে। ছোট হতে বড় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান সমাজে কর্মরত রয়েছে। এদের প্রত্যেকের কাজের প্রকৃতিও নানান রকমের। কর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রবাহের ধারণাও এক নয় । তাই প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে নানান ধরনের সংগঠন কাঠামো আমরা দেখতে পাই । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :
১. সরলরৈখিক সংগঠন (Line organization) : যে সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব রেখা ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর হতে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে সরলরেখার আকারে নেমে আসে তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে। সামরিক সংগঠনে আদেশদানের সরলরৈখিক গতিরেখার প্রতি যে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ঊর্ধ্বতনের আদেশ অধস্তনরা যেভাবে বিনা দ্বিধায় মানতে বাধ্য থাকে, এক্ষেত্রে অনুরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় বলে একে সামরিক সংগঠনও বলা হয়ে থাকে ।
২. সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন (Line and staff organization) : যে সংগঠন কাঠামোতে সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মীর ব্যবহার করা হয় তাকে সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন বলে । এরূপ সংগঠন কাঠামোতে দু'ধরনের কর্মী থাকে - একদল সরলরৈখিক নির্বাহী ও অন্যদল উপদেষ্টা কৰ্মী । এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সরলরৈখিক নির্বাহী ভোগ করেন । অপরপক্ষে উপদেষ্টা কর্মীর কাজ হলো সরলরৈখিক নির্বাহীর কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা ।
৩. কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional organization) : কার্যভিত্তিক সংগঠন বলতে এমন এক ধরনের সংগঠনকে বুঝায় যেখানে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এদের এক একটিকে এক একজন বিশেষজ্ঞের ওপর ন্যস্ত করা হয় । এরূপ সংগঠনে বিশেষজ্ঞদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ করা হয়ে থাকে । বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক এফ. ডব্লিউ. টেইলর এ ধরনের সংগঠন কাঠামোর উদ্ভাবক ।
৪. মেট্রিক্স সংগঠন (Matrix Organization) : ব্যবস্থাপনা সংগঠনের আধুনিক রূপ হলো মেট্রিক্স সংগঠন । এটি হলো মূলত বিভাগীয়করণের একাধিক পদ্ধতির মিশ্র রূপ । দ্রব্য ও কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ ও ক্ষেত্রেবিশেষে অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীয়করণের সমন্বয়ে দ্বৈত কর্তৃত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক সম্বলিত যে সংগঠন কাঠামো বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোতে গড়ে তোলা হয় তাকেই মেট্রিক্স সংগঠন বলে । এ ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হলো-এক্ষেত্রে কার্যিক ব্যবস্থাপক ও প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক- দু'ধরনের কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে কাজ করে ।
৫. কমিটি সংগঠন (Committee organization) : কমিটি হলো একদল লোকের সমষ্টি যাদের ওপর বিশেষভাবে কোনো নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কার্য সমাধা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সাধারণত সরলরৈখিক বা সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনে বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ প্রয়োজনে এ ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কমিটি, পরীক্ষা কমিটি ইত্যাদি এরূপ সংগঠনের উদাহরণ ।
পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগঠন কাঠামো ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন ধরনের সংগঠন কাঠামো ব্যবহৃত হবে তা বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে ।
যে সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব রেখা সরলরেখার আকারে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসে এবং বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত সরলরৈখিক নির্বাহীগণ কোনো সহযোগীর সহায়তা ছাড়াই স্বীয় বিভাগের সর্বময় দায়িত্ব পালন করেন তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে । এক্ষত্রে কর্তৃত্ব রেখার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধস্তন ব্যক্তিবর্গের ওপর অতিমাত্রায় কর্তৃত্বশালী থাকে। সামরিক সংগঠনে আদেশদানের সরলরৈখিক গতিরেখার প্রতি যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং উর্ধ্বতনের আদেশ অধস্তনরা বিনা দ্বিধায় মানতে বাধ্য থাকে, এরূপ সংগঠন কাঠামোতে আদেশ দান ও তা পালনে অনুরূপ নীতিমালার অনুসরণ করা হয় বলে একে সরলরৈখিক সংগঠনের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এটি সবচেয়ে পুরনো ধরনের সহজ প্রকৃতির সংগঠন কাঠামো । জটিলতামুক্ত ও সীমিত আয়তন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এরূপ সংগঠন কাঠামো অধিক ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এরূপ সংগঠন কাঠামো রেখাচিত্রে প্রদর্শিত হলো:
উল্লেখ্য উপব্যবস্থাপক, সহব্যবস্থাপক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে সাধারণভাবে পদস্থ কর্মী বিবেচনা করা হলেও তা সবসময় নাও হতে পারে । কর্তৃত্ব রেখা কিভাবে ব্যক্তিবর্গকে সমন্বিত করেছে তাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য ।
বৃহদায়তন ও জটিল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য সরলরৈখিক সংগঠন খুব উপযুক্ত নয় । তথাপি প্রাচীনতম সংগঠন পদ্ধতি হিসেবে এরূপ সংগঠন কাঠামো এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যার ফলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত এটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন কাঠামো হিসেবেই বিবেচিত । নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :
১. সরল ও সহজবোধ্য সংগঠন (Simple and easily comprehend organization): সরলরৈখিক সংগঠন একটি সরল ও সহজবোধ্য সংগঠন । এরূপ কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের অবস্থান, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় । এ ছাড়া এরূপ সংগঠনে সহযোগী বা পদস্থ কর্মী (Staff assistant) না থাকায় কার্যক্ষেত্রে কোনো জটিলতা থাকে না ।
২. কর্তৃত্বের প্রকৃতি (Nature of authority): এরূপ সংগঠনে ঊর্ধ্বতন তার অব্যবহিত অধস্তনের ওপর অধিকমাত্রায় কর্তৃত্বশালী থাকে । ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ ঊর্ধ্বতন তার অধীনস্থ কর্মী বা নির্বাহীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে গণ্য হয় । আর যে কারণে অধস্তনরা বিনা দ্বিধায় ঊর্ধ্বতনের নির্দেশ মান্য করে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে ।
৩. কর্তৃত্বের প্রবাহ (Flow of authority): এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্বরেখা ওপর থেকে নিচের দিকে আড়াআড়ি বা সরলরেখার আকারে নেমে আসে । এতে কর্তৃত্বরেখার নিচের দিকে কর্মরত নির্বাহীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং প্রতিটা উপরিস্তরে তা ক্রমানুযায়ী বাড়তে থাকে ।
৪. স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ (Self-sufficient department): এরূপ সংগঠন কাঠামোতে সংগঠনের কাজকে প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটা বিভাগের জন্য একজন বিভগীয় প্রধান নিয়োজিত থাকে । উক্ত প্রধান তার বিভাগের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন । এরূপ প্রতিটা বিভাগ অন্য বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে ।
৫. আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ (Inter-departmental communication): এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে বিভাগগুলো একজন সাধারণ ব্যবস্থাপক বা মহাব্যবস্থাপকের অধীনে এবং উপবিভাগগুলো বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের অধীনে কর্মরত থাকে । ফলে আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ ঊর্ধ্বতনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় ।
৬. ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Individuality): এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগীয় নির্বাহী তার বিভাগে একক কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ায় বিভাগের সকল দায়িত্বও তার ওপরই বর্তে। তার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষে দায়িত্ব পালনের মতো কোনো সহযোগী না থাকায় পুরো বিভাগের ভালো-মন্দ একক ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ।
৭. প্রয়োগ ক্ষেত্র (Field of application): সহজ ও সরল প্রকৃতির এরূপ সংগঠন জটিল ও বৃহদায়তন কার্য পরিবেশে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা যায় না । তাই জটিলতামুক্ত ও সীমাবদ্ধ আয়তন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এরূপ সংগঠন অধিক উপযোগী ।
সরলরৈখিক সংগঠন সবচেয়ে সহজ ও প্রাচীন সংগঠন কাঠামো। এরূপ সংগঠন কাঠামো সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপযোগী এবং ছোট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে এরূপ সংগঠন কাঠামোর সংখ্যায় সর্বাধিক । নিম্নে এরূপ সংগঠনের সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো:
১. কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট বণ্টন (Explicit distribution of responsibility and authority) : এরূপ সংগঠনে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব স্পষ্টরূপে বর্ণিত ও বণ্টিত হয়। ফলে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে কর্মীদের মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না ।
২. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (Prompt decision making and execution) : এক্ষেত্রে প্রত্যেক নির্বাহী তার আপন পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । কোনো উপদেষ্টা কৰ্মী না থাকায় আপন চিন্তার আলোকে ঊর্ধ্বতন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজ দায়িত্বে তা বাস্তবায়ন করতে পারে ।
৩. সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা (Establishing maximum discipline) : সামরিক সংগঠনের ন্যায় এরূপ সংগঠনে অধিক মাত্রায় শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব হয়। দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়ায় এবং প্রত্যেকেই তার কার্যের জন্য সর্বোতভাবে তার ঊর্ধ্বতনের নিকট দায়ী হওয়ায় সকলক্ষেত্রে সহজেই শৃঙ্খলা বজায় থাকে ।
৪. নির্বাহীর দক্ষতা বৃদ্ধি (Development of efficiency of executives) : এরূপ সংগঠন কাঠামোতে একজন নির্বাহী তার পরিসরে সকল কার্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকে বিধায় তাকে সফল কাজ তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে হয়; যা বিভিন্ন বিষয়ে তাকে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে ।
৫. পদোন্নতির স্পষ্ট পথনির্দেশক (Specific indicator of promotion) : এরূপ সংগঠনে ধাপে ধাপে পদোন্নতি হয় বিধায় কর্মীরা পদোন্নতির ব্যাপারে পূর্বে জ্ঞাত থাকে এবং নিজেকে সেই অনুযায়ী গঠনে সচেষ্ট হতে পারে । যেমন-একজন ফোরম্যান তার অব্যবহিত উচ্চতর পদ সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি পাবে এটাই এরূপ সংগঠনের সাধারণ নিয়ম ।
৬. স্থায়ী ও শক্তিশালী সংগঠন (Permanent and strong organization) : এরূপ সংগঠনে কে কার ঊর্ধ্বতন এবং কে কার অধস্তন তা সহজেই বোঝা যায়। প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তৃত্ব সংগঠন কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকে । যোগাযোগ ব্যবস্থাও থাকে প্রত্যক্ষ ও সহজ। দ্বৈত অধীনতা ও সাংগঠনিক জটিলতা না থাকায় এর কাঠামো যথেষ্ট মজবুত ও শক্তিশালী হয় ।
সরলরৈখিক সংগঠন সহজ ও সরল প্রকৃতির সংগঠন হওয়ায় সাধারণ মানের প্রাতিষ্ঠানে এরূপ সংগঠন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও প্রতিষ্ঠানের কাজ যতই বিস্তৃত হতে থাকে ততই এ সংগঠনের সমস্যাগুলো সামনে, এসে ধরা দেয় । নিম্নে এর অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো :
১. বিশেষায়ণের অভাব (Lack of specialisation) : এরূপ সংগঠন কাঠামোতে একজন নির্বাহীকে তার গণ্ডিতে সকল ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হয় । যা সকল অবস্থায় দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা একজন নির্বাহীর পক্ষে সম্ভব হয় না । ফলে কোনো কার্যে বিশেষজ্ঞতা বা বিশেষায়ণের রীতিও কার্যকর করা যায় না।
২. স্বৈরতন্ত্রের প্রতি ঝোঁক (Tendency towards autocracy) : এক্ষেত্রে প্রত্যেক নির্বাহী নিজস্ব গণ্ডিতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও অধস্তনদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বিবেচিত হয়। যে কারণে স্বৈরতন্ত্রের প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতা এরূপ সংগঠন কাঠামোতে লক্ষ করা যায় । ফলে একদল মোসাহেব বা তোষামোদকারীর সৃষ্টি হওয়া এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক ।
৩. নির্বাহীদের কার্যভার বৃদ্ধি (Increase in workload of executives) : এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত স্বল্পসংখ্যক নির্বাহীকে তার গণ্ডিতে কোনো সহযোগীর সহযোগিতা ছাড়াই সকল কাজ সম্পাদন ও তার জন্য ঊর্ধ্বতনের নিকট দায়ী থাকতে হয়। ফলে নির্বাহীগণ সব সময়ই অতিরিক্ত কাজের চাপের মধ্যে থাকে এবং যা ফলপ্রদ কাজে বাধার সৃষ্টি করে ।
৪. নির্বাহীর অনুপস্থিতিতে ক্ষতি (Loss due to the absence of executive) : এরূপ সংগঠন কাঠামোতে বিভাগীয় নির্বাহীকে সহযোগিতা করার বা তার অনুপস্থিতিতে কার্য সম্পাদনের মতো কোনো উপদেষ্টা কৰ্মী না থাকায় কোনো কারণে তার অনুপস্থিতি ঐ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।
৫. সমন্বয়ে সমস্যা (Problems in co-ordination) : প্রত্যেকটি বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে বিধায় এরূপ সংগঠনে একমাত্র সাধারণ বা মহাব্যবস্থাপকের মাধ্যমে কার্যে সমন্বয় বিধান করতে হয়। যা অনেক ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ ও জটিল হয়ে দাঁড়ায় । এ ছাড়াও সকল বিভাগ স্বাধীন হওয়ায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোতা সৃষ্টি হয় না ।
৬. জটিল ও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অনুপযোগী (Unsuitable in case of complex and large scale enterprise): বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই । অথচ সরলরৈখিক সংগঠনের মাধ্যমে কখনই জটিল ও বড় ধরনের সংগঠন পরিচালনা করা সম্ভব নয় ।
জনাব তালুকদার পারিবারিক সদস্যদের নিয়ে একটা কোম্পানি গঠনপূর্বক নিজেই এম.ডির দায়িত্ব নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন । তার অধীনে উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় ব্যবস্থাপক স্ব-স্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা হিসেবে বিভাগ চালিয়েছেন । কিন্তু প্রতিষ্ঠান বড় হওয়ায় এখন আরও কিছু বিভাগ খুলেছেন । উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় ব্যবস্থাপকদ্বয়ের একার পক্ষে বিভাগের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কষ্টসাধ্য মনে করে প্রত্যেকের অধীনে একজন করে সহকারী ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছেন । এতে উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় ব্যবস্থাপকের কাজের ভার কিছুটা কম হওয়ায় তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন । এক্ষেত্রে জনাব তালুকদারের প্রথম গড়া সংগঠন কাঠামো ছিল সরলরৈখিক সংগঠন কিন্তু পরে সহকারী নিয়োগ দেয়ায় সংগঠন কাঠামোর প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং তা সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনে রূপায়িত হয়েছে ।
যে সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব রেখা ওপর থেকে নিচের দিকে সরলরেখার আকারে নেমে আসে এবং সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য সহযোগী বা পদস্থ কর্মী নিয়োগ করা হয় তাকে সরলরৈখিক ও পদস্থকর্মী সংগঠন বলে । উৎপাদন ব্যবস্থাপককে সহযোগিতা করার জন্য সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপক নিয়োগ বা এরূপ পদ সৃষ্টি এ ধরনের সংগঠনের উদাহরণ । কলেজগুলোতে প্রিন্সিপ্যালকে সহযোগিতা করার জন্য ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গণ্য । মূলত সরলরৈখিক সংগঠনের মধ্যদিয়ে সংগঠন কাঠামোর অগ্রযাত্রা শুরু । পরবর্তীতে কাজের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় দেখা যায় যে, একজন উৎপাদন ব্যবস্থাপক বা বিক্রয় ব্যবস্থাপকের পক্ষে বিভাগীয় সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে না । আবার একই সাথে দু'জন উৎপাদন ব্যবস্থাপকও নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয় । তাই কর্মভারগ্রস্ত এরূপ ব্যবস্থাপকদের সহযোগিতার জন্য সহযোগী, সহকারী বা পদস্থকর্মী নিয়োগ দান শুরু হয় । এতে যে নতুন সংগঠন কাঠামো রূপলাভ করে তাই সরলরৈখিক ও পদন্তকর্মী সংগঠন নামে অভিহিত। তুলনামূলকভাবে বড় ও বিস্তৃত কার্যক্ষেত্রে এরূপ সংগঠন কাঠামো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । পদস্থ কর্মী (Staff) এর সহযোগিতার ওপর এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেয়ার কারণে একে অনেকেই পদস্থকর্মী সংগঠন (Staff organization) নামে অভিহিত করেন। নিম্নে এরূপ সংগঠন কাঠামো রেখাচিত্রে প্রদর্শিত হলো :
সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনের বৈশিষ্ট্য :
১. এরূপ সংগঠনে দু'ধরনের কর্মী থাকে; একদল সরলরৈখিক কর্মী বা নির্বাহী ও অন্যদল উপদেষ্টা কর্মী;
২. দু'ধরনের কর্মী থাকায় এক্ষেত্রে দু'ধরনের কর্তৃত্ব বিরাজ করে; যথা- সরলরৈখিক কর্তৃত্ব ও সহযোগী কর্তত্ব;
৩. এক্ষেত্রে সংগঠনের কর্তৃত্বরেখা ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর হতে ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তরে নেমে আসে;
৪. এক্ষেত্রে সরলরৈখিক কর্মকর্তার পাশে উপদেষ্টা কর্মীগণ প্রয়োজনীয় অবস্থান গ্রহণ করে;
৫. দু'ধরনের কর্মী থাকলেও সরলরৈখিক কর্মকর্তাগণই এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে এবং
৬. পদস্থ বা সহযোগী কর্মীদের কাজ হলো সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান এবং কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা করা ।
উল্লেখ্য উপরের চিত্রে যদি মহা-ব্যবস্থাপকের অধীনে সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক এবং তার অধীনে বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ থাকতেন তবে সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক সরলরৈখিক নির্বাহী গণ্য হতেন ।
সরলরৈখিক কর্মকর্তা ও পদস্থ কর্মী সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন কাঠামোকেই সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন বলে । সরলরৈখিক সংগঠনের ত্রুটিসমূহ দূরপূর্বক অতিরিক্ত সুবিধা অর্জনের জন্যই মূলত এরূপ সংগঠনের উদ্ভব ঘটে । আমাদের দেশে বৃহদায়তন সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান; যেমন- ব্যাংক, বিমা, সরকারি প্রশাসন ইত্যাদি সর্বত্রই আমরা এ ধরনের সংগঠন কাঠামোর ব্যবহার দেখাতে পায় । যে সকল সুবিধার কারণে সর্বত্র এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :
১. নির্বাহীর কর্মভার লাঘব (Relieving burden of executives) : এরূপ সংগঠনে সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বা সহযোগী কর্মী নিয়োগ করায় নির্বাহীর কর্মভার অনেকাংশে লাঘব হয় । ফলে সে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে । এতে নির্বাহীর কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটে ।
২. স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ হ্রাস (Reducing the chance of whims) : এ ধরনের সংগঠনে স্বাভাবিকভাবেই একজন নির্বাহী তার দায়-দায়িত্বের অংশ বিশেষ সহযোগী বা উপদেষ্টা কর্মীর ওপর অর্পণ করে । এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞ কর্মীর উপস্থিতি থাকায় প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ এক্ষেত্রে সরলরৈখিক নির্বাহীর নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় । ফলে তার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায় ।
৩. সমস্যার দ্রুত সমাধান (Prompt solution of problems) : সরলরৈখিক সংগঠনে নির্বাহী নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় তার পক্ষে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন সম্ভব হয় না । কিন্তু এক্ষেত্রে উপদেষ্টা কর্মীর উপস্থিতি থাকায় তারা সমস্যা সমাধানে নির্বাহীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে। ফলে সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়।
৪. শ্রম বিভাগের সুফল অর্জন (Achieving the merits of division of labour) : এ ধরনের সংগঠনে একজন নির্বাহী তার কাজের অংশবিশেষ সহযোগীর ওপর অর্পণ করতে পারে । ইচ্ছে করলে একজন নির্বাহী তার কাজ সহযোগীর সাথে ভাগ করে যে যে কাজের যোগ্য সে সেই কাজ সম্পাদন করে। এতে প্রত্যেকের পক্ষে একই ধরনের কাজ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয় । ফলে কার্যক্ষেত্রে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে ।
৫. নমনীয়তা অর্জন (Achieving flexibility) : সরলরৈখিক সংগঠনে নির্বাহীগণ অনেক সময় কার্যক্ষেত্রে এত ব্যস্ত থাকে যাতে প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না । কিন্তু পদস্থ কর্মী কর্মরত থাকায় নির্বাহী যেমনি নতুন চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায় তেমনি প্রয়োজনে একাধিক সহযোগী নিয়োগ করে কর্মক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারে ।
৬. সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে সুবিধা (Advantages of co-ordination & control) : এরূপ সংগঠনে পদস্থ কর্মীগণ অন্য বিভাগের খোঁজখবর গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রদান ইত্যাদি কাজ করতে পারায় অন্য বিভাগের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন সহজ হয়। এ ছাড়া অধস্তনের কাজের খোঁজখবর গ্রহণ, কার্যফল মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপও অনেক সহজ হয়ে থাকে ।
বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহে সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও এরূপ সংগঠন ত্রুটিমুক্ত এ কথা বলা যায় না। প্রকৃতিগত কারণেই এক্ষেত্রে যেমনি কিছু সমস্যা লক্ষণীয় তেমনি দু- ধরনের নির্বাহীদের কর্তৃত্ব প্রয়োগে ব্যক্তিগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অনেক সময়ই এক্ষেত্রে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় । নিম্নে এরূপ সংগঠনের অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:
১. ব্যয় বৃদ্ধি-(Increase in expenditure) : এ ধরনের সংগঠনে সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক পদস্থ কর্মী নিয়োগ করা হয়। অনেক সময় পদস্থ কর্মী নিয়োগকে নির্বাহী নিজের জন্য অধিক মর্যাদাকর গণ্য করে । ফলে প্রয়োজনের বাইরেও পদস্থ কর্মী নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ করা যায় । এতে প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ।
২. সহযোগীদের কর্তৃত্ব ও কার্য বিষয়ে অস্পষ্টতা (Lack of clarity in delegation of authority and responsibility) : এক্ষেত্রে সরলরৈখিক নির্বাহীদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে সংগঠন কাঠামোতে বর্ণিত হলেও পদস্থ কর্মীদের ক্ষেত্রে তা থাকে না। পদস্থ কর্মীর কাজ হয় নির্বাহীর ইচ্ছা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা । ফলে তার কাজে অস্পষ্টতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সমস্যা দেখা দেয়।
৩. বিশেষজ্ঞ কর্মীদের উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা (Chance of being neglected of the expertise) : এরূপ সংগঠনে সরলরৈখিক নির্বাহীরা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী থাকে। পদস্থ বা বিশেষজ্ঞ কর্মীদের কার্যত কোনো কর্তৃত্ব এতে থাকে না। সরলরৈখিক নির্বাহীদের দেয়া কাজ বা দায়-দায়িত্ব তারা পালন করে এবং উক্ত নির্বাহীর নিকটই কাজের জন্য জবাবদিহি করে। বিশেষজ্ঞ কর্মী কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দিলেও তা মানতে নির্বাহী বাধ্য থাকে না । ফলে বিশেষজ্ঞ কর্মী বা উপদেষ্টারা অনেক সময়ই উপেক্ষিত হয় ।
৪. কর্মকর্তাদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি (Generating conflict among the executives) : এরূপ সংগঠনে অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী নির্বাহী ও উপেক্ষিত বিশেষজ্ঞ কর্মীর মধ্যে মনোমালিন্য লক্ষ করা যায় । যা সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে ও জটিল পরিবেশের জন্ম দেয়। আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেই গ্রুপিং-লবিং এর বড় কারণ হলো উভয় ধরনের কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা মনোমালিন্য ।
৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব (Delay in decision making) : এরূপ সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নির্বাহীগণ অনেক সময়ই উপদেষ্টা কর্মীদের সাথে শলা-পরামর্শে অধিক সময় ব্যয় করে বা তাদের ওপর নির্ভর করে যা ক্ষেত্রবিশেষে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্বের কারণ হয় ।
৬. বিশেষজ্ঞ কর্মীদের যোগ্যতার বিকাশে বাধা (Barrier to the flourish of the quality of expertise) : এরূপ সংগঠনে বিশেষজ্ঞ কর্মীগণ দায়িত্ব-কর্তৃত্ব ছাড়াই নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সহায়তাকারী হিসেবে কার্যে নিয়োজিত থাকায় অধিক দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তারা নিরুৎসাহবোধ করে । ফলে তাদের যোগ্যতার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।
মি. কবীরের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের বিস্তৃতি বাড়ায় উৎপাদন ব্যবস্থাপককে সহযোগিতা করার জন্য একজন যন্ত্র প্রকৌশলী ও একজন কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞকে সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে । বিভাগীয় কর্তৃত্ব এককভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাপকের থাকায় তার দ্বারা এ দু'জন সহকারী উপেক্ষিত হন।
ফলে তাদের যোগ্যতা কোনো কাজে আসছে না । এখন উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব একজন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (উৎপাদন) বা সহসভাপতি (উৎপাদন)এর অধীনে রেখে উৎপাদন বিভাগের কাজকে যন্ত্র প্রকৌশল, কাঁচামাল ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ, মেরামত ও সংরক্ষণ এ চারটা বিভাগে ভাগ করে পদস্থ বা বিশেষজ্ঞ কর্মীদের সীমিত সরলরৈখিক কর্তৃত্ব সহযোগে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে কারও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আর নেই । বরং প্রত্যেকেই নিজস্ব পরিসরে যোগ্যতা প্রদর্শন করে দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারছে । এক্ষেত্রে মি. কবীরের উৎপাদন বিভাগের জন্য গড়া নতুন সংগঠন কাঠামো হলো কার্যভিত্তিক সংগঠন ।
যে সংগঠন কাঠামোতে কাজকে প্রকৃতি অনুযায়ী ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ কর্মীদের ওপর সীমিত সরলরৈখিক কর্তৃত্ব সহযোগে অর্পণ করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে । সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনে লক্ষণীয় যে, সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক পদস্থ, সহযোগী বা বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। উদ্দেশ্য থাকে উভয় ধরনের কর্মী বা নির্বাহীগণ মিলে-মিশে দায়িত্ব পালন করবেন । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উভয় ধরনের নির্বাহীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কারণ হয় । সকল কর্তৃত্ব সরলরৈখিক নির্বাহীর থাকায় অনেক সময় যোগ্য বিশেষজ্ঞ সহকারী তার দ্বারা উপেক্ষিত হয়। এতে বিশেষজ্ঞ কর্মী হতাশ থাকেন এবং তার নিয়োগের উদ্দেশ্যই অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই কার্যভিত্তিক সংগঠন কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে । এফ. ডব্লিউ. টেইলর এরূপ সংগঠন কাঠামোর উদ্ভাবক ।
বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিপণনের মত বিভাগগুলোর জন্য এ ধরনের সংগঠন কাঠামো খুবই কার্যকর । নিম্নে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো রেখাচিত্রে প্রদর্শিত হলো:
কার্যভিত্তিক সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :
১. কাজের ধরন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল কাজকে এক্ষেত্রে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়;
২. এর প্রতিটি বিভাগ একযোগে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে সেবা প্রদান করে;
৩. এর প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব একজন বিশেষজ্ঞের ওপর ন্যস্ত করা হয়;
৪. যিনি উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত সরলরৈখিক নির্বাহীর অনুমোদনক্রমে সীমিত কর্তৃত্ব ভোগ করেন এবং
৫. বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বিভাগে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো অধিক ব্যবহৃত হয় ।
সুদীর্ঘ কর্মজীবনে শিক্ষানবিস কর্মী হতে শুরু করে বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে F. W. Taylor তার অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে যে নতুন ধরনের সংগঠন কাঠামোর রূপরেখা প্রদান করেন তাই কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional Foremanship) নামে অভিহিত । এরূপ সংগঠনের যে সকল সুবিধা লক্ষণীয় তা নিম্নরূপ :
১. কার্যক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান প্রয়োগ (Application of specialised knowledge) : সংগঠনে বিশেষজ্ঞদেরকে শুধুমাত্র উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের ওপর সরাসরি নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এতে বিশেষজ্ঞগণ স্বাধীনভাবে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারে। ফলে প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় ।
২. স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস (Reduction of autocracy) :কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন এরূপ সংগঠনে নিশ্চিত করা যায় । ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে তারা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। অন্যদিকে কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করায় বিশেষজ্ঞ কর্মীগণও কর্মক্ষেত্রে স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ পায় না ।
৩. বিশেষায়ণ ও কর্মী উন্নয়ন (Specialization and employee development ) : এক্ষেত্রে কাজকে বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করায় কার্যক্ষেত্রে যেমনি বিশেষায়ণের সুযোগ নিশ্চিত হয় তেমনি বিশেষজ্ঞের অধীনে কাজ করতে গিয়ে অধস্তনরা সরাসরি তার নিকট হতে অনেক কিছুই শিখতে পারে । ফলে অধস্তনদের মান উন্নীত হয় ।
৬. নমনীয়তা বৃদ্ধি (Increase in flexibility) : বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ নির্বাহ হওয়ার কারণে তারা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সাথে সহজেই সঙ্গতি বিধান করতে পারে । ফলে নমনীয়তা অর্জন সহজ হয়। এ ছাড়া এক্ষেত্রে কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করায় প্রয়োজনে কোনো নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা বা কোনো বিভাগ বন্ধ করে দেয়া যায় ।
৫. নিয়ন্ত্রণে সহায়তা (Aid to controlling) : এরূপ সংগঠনে কাজগুলো ছোট ছোট বিভাগে ভাগ করায় একজন বিশেষজ্ঞ কর্মীর অধীন কাজের আওতা ছোট হয় । ফলে কার্যফল মূল্যায়ন সহজ হয় । প্রতিটি বিভাগের জন্য এমনকি ব্যক্তির জন্য কাজের পূর্ব নির্ধারিত মান নির্দিষ্ট থাকায় জবাবদিহিতাও সহজ হয়। যে কারণে প্রতিষ্ঠানে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় ।
কার্যভিত্তিক সংগঠনের বেশ কিছু সুবিধা থাকলেও এরূপ সংগঠনের অসুবিধার পরিমাণও কম নয় । নিম্নে এর অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো :
১. কর্মীদের কর্মভার বৃদ্ধি (Increase in workload of employees) : এরূপ সংগঠনে একটি বিভাগ প্রয়োজনে একাধিক বিভাগকে সেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকে । যে কারণে কোনো একটি বিভাগীয় কর্মীদের ওপর একই সময়ে অন্য একাধিক বিভাগ হতে সেবা সুবিধা প্রদানের নির্দেশ আসতে পারে । আর এরূপ অবস্থায় উক্ত বিভাগের কর্মীদের কর্মভার বৃদ্ধি পায় এবং তারা সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয় ।
২. সরলরৈখিক কর্মকর্তাদের প্রভাব হ্রাস (Reduction in influnce of line-authority) : এ ধরনের সংগঠনে কাজের মূল দায়িত্ব থাকে বিশেষজ্ঞ কর্মীদের ওপর। যারা স্ব-স্ব বিভাগে নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে । সরলরৈখিক নির্বাহী বলতে যা বুঝায় তা থাকে মূলত সংগঠন কাঠামোর একেবারে ওপর পর্যায়ে। বিশেষজ্ঞ কর্মীগণ মূল চালকের ভূমিকায় অবস্থান করায় সংখ্যালঘু সরলরৈখিক নির্বাহীদের কর্তৃত্ব এক্ষেত্রে হ্রাস পায়। যা প্রকারান্তরে সমস্যার সৃষ্টি করে ।
৩. দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ (Opportunity to avoid responsibility) : এক্ষেত্রে একটি বিভাগ বা বিভাগীয় কর্মীগণ একই সাথে একাধিক বিভাগের আদেশ-নির্দেশ পালন করায় কার্যক্ষেত্রে দ্বৈত অধীনতার সৃষ্টি হয় । ফলে কোনো কর্মী বা বিভাগ ইচ্ছা করলে অন্যের দোহাই দিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে পারে । দ্বৈত অধীনতার কারণে এক্ষেত্রে অধস্তনদের সঠিকভাবে জবাবদিহিও করা যায় না ।
৪. শৃঙ্খলার অভাব (Lack of discipline) : এ ধরনের সংগঠনে কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করায় এমনিতেই যথাযথ তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দেয় । তদুপরি কোনো অধস্তন কর্মী বা বিভাগ একাধিক ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের অধীনে কাজ করায় কার্যক্ষেত্রে মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । এরূপ সংগঠন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ না করার পিছনে এটাকে অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়ে থাকে ।
৫. প্রয়োগ ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitation of applicability) : কার্যভিত্তিক সংগঠন কাঠামো এমনিতেই যথেষ্ট জটিল । নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বৃহদায়তন উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বিভাগেই এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভব । ক্রয়, বিক্রয়, অর্থ, শ্রমিক-কর্মী ইত্যাদি বিভাগে কার্যভিত্তিক সংগঠন কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার কার্যত সম্ভব নয় ।
কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি । প্রিন্সিপ্যালের একার পক্ষে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বিধায় তিনি কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষককে দিয়ে ভর্তি কমিটি করে দিয়েছেন। যাদের কাজ হবে ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রশাসনকে সহায়তা করা । মি. ইসলামের কারখানায় দু'টি বিভাগের শ্রমিকেরা মারামারি করেছে। মি. ইসলাম দুই বিভাগের প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহযোগে পাঁচ সদস্যের কমিটি করে দিয়েছেন । এক সপ্তাহের মধ্যে গণ্ডগোলের কারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে । এই ব্যক্তিবর্গও তাদের স্ব-স্ব কাজের বাইরে একত্রে বসে সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন । এভাবেই দেখা যায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রয় কমিটি, ভর্তি কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, মসজিদে মসজিদ কমিটি, হাটে হাট কমিটি, মার্কেটে মার্কেট কমিটি, খেলার জন্য টুর্নামেন্ট কমিটি ইত্যাদি নানান কমিটি গঠন করা হয় । প্রশাসন পরিচালনার সর্বস্তরে নানান প্রয়োজনেই কমিটি গঠন করতে দেখা যায় । এভাবেই কমিটি বা কমিটি সংগঠন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানে একটা সহযোগী অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে ।
প্রতিষ্ঠান বা ঊর্ধ্বতনের পক্ষ থেকে অথবা আইন, বিধি বা গঠনতন্ত্রবলে বিশেষ কোনো কার্য সম্পাদনের ভার একাধিক ব্যক্তির ওপর অর্পিত হলে ঐ ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে কমিটি বলে । এরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্কের কাঠামোর সৃষ্টি হয় তাকে কমিটি সংগঠন বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান বা আহবায়ক থাকেন । যিনি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন ও দায়িত্ব পালনে সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকে জোরদার করেন । প্রয়োজনে কমিটির একজন সদস্য সচিবও করা হতে পারে। যিনি সভাপতির নির্দেশমত প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে কমিটির সকল সদস্য কমিটির কাজে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমঅধিকার ভোগ করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অবাঞ্চিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণ্ডগোল ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে । চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে । ভিসি মহোদয়, বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য প্রক্টরকে আহবায়ক করে বিভিন্ন দায়িত্বশীল শিক্ষক সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যের কমিটি করে দিয়েছেন । এটি ঊর্ধ্বতনের পক্ষ থেকে গঠিত কমিটি । বেসরকারি স্কুল ও কলেজ পরিচালনার জন্য আইনে পরিচালনা কমিটি বা গভর্নিং বডি নিয়োগের বিধান রয়েছে । এর সদস্যগণ যথানিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হন । এটি নিয়ম বা বিধি বলে গঠিত কমিটির উদাহরণ । দু'টি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবর্গ কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই সম্মিলিতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন । কমিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনো ধরনের হতে পারে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি, শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় কমিটি, মার্কেট কমিটি, মসজিদ বা মন্দির পরিচালনা কমিটি ইত্যাদি স্থায়ী প্রকৃতির । অন্যদিকে তদন্ত কমিটি, ভর্তি কমিটি, সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি ইত্যাদি অস্থায়ী কমিটির উদাহরণ । কমিটিকে বোর্ড, কমিশন, কাউন্সিল, টাস্কফোর্স ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয় ।
কমিটি বর্তমানকালে একটি বহুল ব্যবহৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু কাজ থাকে যা সরলরৈখিক নির্বাহী বা উপদেষ্টা কৰ্মী নিয়োগ বা কোনো বিশেষ বিভাগ খুলে সম্পাদন করা যায় না । অথচ উক্ত কাজ সম্পাদন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় । তাই উক্ত বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষ সাংগঠনিক ব্যবস্থা হিসেবেই কমিটির ব্যবহার করা হয়ে থাকে । নিম্নে কমিটির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :
১. একাধিক ব্যক্তির সম্মিলন (Association of a group of people) : কমিটি হলো কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি । এখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তির সম্মিলন ঘটে। এর সদস্যদের দায়িত্বও থাকে যৌথ । এক সদস্যের কমিটি গঠনের কথা কখনও বলা হলেও কার্যত তাকে কমিটি বলার কোনো সুযোগ নেই । কমিটিকে যদি একটি সংগঠন ধরা হয় তবে একক সদস্যের সমন্বয়ে কখনই কমিটি সংগঠন গড়ে উঠে না ।
২. নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য (Elected or nominated member) : কমিটির সদস্যগণ সাংগঠনিক নিয়মে নির্বাচিত বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকে । কোনো কোম্পানিতে পরিচালনা বোর্ডের সদস্যগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত নিয়মে নির্বাচিত হন। কলেজ গভর্নিং বডিও নির্দিষ্ট নিয়মে নির্বাচিত হয়ে থাকে । আবার কোনো বিষয়ে তদন্ত কমিটি, সুপারিশ কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কমিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃক মনোনীত হন ।
৩. স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রকৃতি (Permanent or temporary in nature) : কমিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে । কোনো প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ কমিটি, অর্থ কমিটি, সমন্বয় কমিটি ইত্যাদি স্থায়ী প্রকৃতির কমিটি । অন্যদিকে তদন্ত কমিটি, সাক্ষাৎকার বোর্ড, প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি ইত্যাদি অস্থায়ী প্রকৃতির কমিটি ।
৪. খণ্ডকালীন বা অস্থায়ী কর্ম (Part-time or temporary function) : কমিটির সদস্যপদ কোনো স্থায়ী বা সার্বক্ষণিক কর্ম নয় । কমিটি সদস্যদের সাধারণত একটি পৃথক নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র বা পরিমণ্ডল থাকে । কমিটির সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার কারণে এটা তাদের একটা অতিরিক্ত কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় । এজন্য তারা কোনো বেতন পান না । মিটিং-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদেরকে সাধারণত সম্মানী বা ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে ।
৫. বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার (Use for multiple purposes) : বর্তমানকালে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করা হয় । প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে সরলরৈখিক কর্তৃত্ব সহযোগে যেমনি কমিটি গঠন করা হয় তেমনি অনেক সময় ঊর্ধ্বতনকে সহযোগিতা করার জন্যও কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে । পরামর্শ প্রদান, বিশেষ প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন, বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কোনো জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা ইত্যাদি নানান প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে ।
৬. সদস্যদের সমমর্যাদা (Equal status of members) : কমিটির সদস্যরা প্রত্যেকই সমান মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ভোগ করে । কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কাউকে কমিটির আহ্বায়ক, চেয়ারম্যান বা সদস্য সচিব মনোনীত করা হলেও কমিটির সভায় প্রত্যেক সদস্যই সমান মর্যাদা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয় । এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিমালার অনুসরণ করা হয়ে থাকে । সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ী এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।
৭. সহযোগী ব্যবস্থা (Subsidiary arrangement) : প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সংগঠন কাঠামোর বাইরে কমিটি বা কমিটি সংগঠন একটি বিশেষ সহযোগী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে । কমিটি গঠন করে প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ পরিচালনা সম্ভব নয় । অথচ এমন কিছু কাজ রয়েছে যা সরলরৈখিক নির্বাহী বা পদস্থ কর্মী দিয়েও সম্পাদন সম্ভব হয় না। সেখানে সংগঠনের অভ্যন্তরে কমিটি একটি সহযোগী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে ।
যে কোন ধরনের বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে কমিটি একটি অতি পরিচিতি নাম এবং বহুল ব্যবহৃত সাংগঠনিক বিষয় । অনেকেই নানানভাবে কমিটিকে সমালোচনা করলেও প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ব্যাপক ব্যবহার এর উপযোগিতাই প্রমাণ করে । যে সকল সুবিধার কারণে কমিটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয় তা নিম্নরূপ :
১. দলগত বিচার-বিবেচনার সুযোগ (Opportunity to group-decision) : কথায় আছে 'Two heads are better than one' বাস্তবেও কোনো জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত চিন্তা বা বিচার-বিবেচনা অধিক ফলপ্রসূ হতে দেখা যায়। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক জ্ঞানী-গুণী ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকে । ফলে দলগত বিচার-বিবেচনার সুযোগে প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় ।
৪. যোগাযোগের সুবিধা (Advantage in communication) : কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় সকল স্তরে জ্ঞাত করানোর ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা অর্জন করা যায়। বিভাগীয় প্রধানদের দ্বারা বা প্রয়োজনীয় পক্ষসমূহের সদস্যদের দ্বারা সৃষ্ট কমিটি, গৃহীত সিদ্ধান্ত নিজ দায়িত্বেই অধস্তনদের জ্ঞাত করে বিধায় এতে সময় ও খরচ উভয়ই বাঁচানো যায়।
৩. স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতিনিধিত্ব (Representation of group-interest) : একটি প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক নিয়মেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব থাকে সরলরৈখিক নির্বাহীদের ওপর । অথচ প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে । তাই সেখানে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন সবচেয়ে কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে পারে ।
২. সহযোগিতা বৃদ্ধি (Increase of co-operation) : কমিটি প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । যেহেতু কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনায় সকল সদস্যের কম-বেশি অবদান থাকে, তাই এটি বাস্তবায়নে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভ করা যায় ।
৫. ব্যক্তিগত দায় এড়ানোর সুযোগ (Opportunity to avoid personal liability) : কমিটি একজন দক্ষ প্রশাসককে অনেক বিষয়ে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ প্রদান করে । কমিটির মাধ্যমে তিনি নিজ চিন্তা কার্যে রূপায়িত করেন যা হয়তোবা নিজ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ।
৬. অবাঞ্ছিত সমস্যা এড়ানো (Avoidance of unwanted situation) : অনেক ক্ষেত্রে নির্বাহী এমন সমস্যার সম্মুখীন হন যেক্ষেত্রে ত্বরিত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমনি যুক্তিযুক্ত হয় না তেমনিভাবে নির্লিপ্ততাও মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে। এমন অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়ানোর জন্য কমিটি গঠন অব্যর্থ মহৌষধের ভূমিকা পালন করে ।
কমিটি কতিপয় সুবিধার কারণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও এর অসুবিধার পরিমাণও কম নয় । আজকাল সাধারণভাবেই মনে করা হয়, কোনো কাজে বা সিদ্ধান্তে বিলম্ব করতে চাইলে এর সহজ উপায় হলো একটা কমিটি করে দেয়া । এ ছাড়া নানানভাবেই কমিটিকে সমালোচনা করা হয়ে থাকে । যে সকল অসুবিধার কারণে কমিটি সমালোচিত হয় তা নিম্নরূপ :
১. বিভক্ত দায়িত্ব (Divided responsibility) : দায়িত্ব এককভাবে কারও ওপর নির্দিষ্ট না করে একাধিক ব্যক্তির ওপর তা অর্পিত হলে একে বিভক্ত দায়িত্ব বলে । কমিটির ক্ষেত্রে কার্যকরণের দায়-দায়িত্ব সকল সদস্যের সমান । তাই এতে “সকলের দায়িত্ব অর্থ কারও দায়িত্ব নয়” (Everybody's responsibility is nobody's responsibility)- প্রবাদ এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কমিটির কাজের বাইরে এর সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকায় তারা সেই কাজের ব্যাপারে যতটুকু আন্তরিক হয় সামষ্টিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে তা হয় না । যার কারণে লক্ষ্যার্জন ব্যাহত হয় ।
২. ধীরগতিসম্পন্ন (Slowness) : নির্বাহীগণ কাজের ফাঁকে মিটিং-এ বসাকে কষ্টকর বাড়তি কাজ মনে করে । ফলে মিটিং ডাকার পরও তা হয় না বা দেরিতে শুরু হয় । নানা কথাবার্তা, বাক-বিতণ্ডা, দ্বিমত, সভা মুলতবি ইত্যাদি কারণে কমিটির কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলে । ফলশ্রুতিতে ফলাফল শুভ হয় না ।
৩. সিদ্ধান্তহীনতার প্রতি ঝোঁক (Tendency towards indecision) : সিদ্ধান্তহীনতার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা কমিটির কাজে আরেকটি বড় বাধা । একদিকে কমিটির মিটিং-এ বসায় এক সমস্যা অন্যদিকে মিটিং-এ “নানা মুনির নানা মত” তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অনেকক্ষেত্রেই জটিল হয়ে পড়ে । বিভক্ত দায়িত্বের কারণে এরূপ অবস্থা সবার জন্য তেমন মাথাব্যথার কারণ হয় না। ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব হয় ।
৪. আপসমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশঙ্কা (Danger of compromising decision) : কমিটির আলোচনায় মতামতের ভিন্নতা, সংখ্যালঘু সদস্যদের বাড়াবাড়ি এবং এ ছাড়া সিদ্ধান্তের পক্ষে সকল সদস্যের মত লাভের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই আপসমূলক সিদ্ধান্তের জন্ম দেয় । আর এরূপ আপসমূলক সিদ্ধান্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো ফল দেয় না ।
৫. নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার প্রবণতা (Tendency to establish own opinion) : কমিটির সভায় সকল সদস্যের সমান অধিকার থাকায় সদস্যদের মতামত প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সভায় প্রত্যেক সদস্যের অধিকার সমান হওয়ায় কেউ কথা বলতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া যায় না । কমিটির সভাপতির মধ্যে এরূপ প্রবণতা সুদৃঢ় হলে কমিটির কাজে আরো মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয় ।
মি. সরকার বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক । তার প্রতিষ্ঠানে A, B ও C তিন ধরনের পণ্য প্রস্তুত হয় । প্রতি বছরে মোট উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাথে মিলিয়ে মুনাফাও বাড়ছে । উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের কাজে মি. সরকার খুশী । কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, A পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় যেভাবে বাড়ছে B ও C পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সেভাবে বাড়ছে না । তিনি B ও C পণ্যের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন, A পণ্য যথেষ্ট চলার কারণে উৎপাদন বিভাগ ও বিক্রয় বিভাগ একটা পণ্য নিয়েই বেশি ব্যতিব্যস্ত রয়েছে । তিনি ভাবলেন, যদি কোনো কারণে A পণ্যের বাজার পড়ে যায় তবে তিনি বিপদে পড়বেন। তাই B ও C পণ্যের বিক্রয় অবশ্যই বাড়াতে হবে । তিনি চিন্তা করলেন A, B ও C পণ্য তিনটাকে আলাদা আলাদা প্রজেক্ট ধরে নিয়ে যদি প্রতিটা প্রজেক্টের জন্য একজন করে ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হয় তবে প্রত্যেক প্রজেক্ট ম্যানেজার তার পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিষয়ে দায়িত্বশীল থাকবেন। এতে প্রতিটা পণ্য সমান গুরুত্ব পাওয়ায় লক্ষে পৌঁছানো সহজ হবে । তাই তিনি সংগঠন কাঠামোতে পরিবর্তন আনলেন । উৎপাদন, বিক্রয়সহ আগে যে বিভাগগুলো ছিল তাদের ব্যবস্থাপকদের কার্যিক (Functional) ব্যবস্থাপক ঘোষণা করলেন। যাদের কাজ হবে প্রজেক্ট ম্যানেজারগণের ফরমায়েশ ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা। এতে তিনি লক্ষ করছেন যে, প্রজেক্ট ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে B ও C পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এক্ষেত্রে মি. সরকার যে নতুন সংগঠন কাঠামো গড়ে তুলেছেন তা-ই মেট্রিক্স সংগঠন ।
দ্রব্য ও কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন কাঠামোকে মেট্রিক্স সংগঠন বলে । দ্রব্যভিত্তিক বিভাগীয়করণের ক্ষেত্রে প্রতিটা দ্রব্য ও সেবার জন্য যেভাবে আলাদা বিভাগ ও বিভাগীয় ম্যানেজার কর্মরত থাকে এক্ষেত্রেও প্রতিটা দ্রব্য বা সেবাকে আলাদা প্রজেক্ট ধরে তার জন্য একেকজন প্রজেক্ট ম্যানেজার নিয়োগ করা হয় । অন্যদিকে উৎপাদন, বিপণন, ক্রয়, মানবসম্পদ ইত্যাদি কার্যভিত্তিক বিভাগগুলো একইভাবে কর্মরত থাকে। এক্ষেত্রে কার্যভিত্তিক বিভাগগুলোর ব্যবস্থাপকদেরকে কার্যিক (Functional) ব্যবস্থাপক বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপকগণ তাদের স্ব স্ব দ্রব্য বা প্রজেক্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন । কার্যিক ব্যবস্থাপকগণের কাজ হয় প্রজেক্ট ব্যবস্থাপকগণের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন, বন্টন ও আনুষঙ্গিক কাজে সহায়তা করা । এ ধরনের সংগঠনে সাধারণ বা মহাব্যবস্থাপক কার্যত মেট্রিক্স ব্যবস্থাপক হিসেবে গণ্য হন। তার অধীনে একদিকে থাকে বিভিন্ন কার্যিক ব্যবস্থাপক ও অন্যদিকে প্রজেক্ট বা দ্রব্য ব্যবস্থাপকগণ । এ কারণে একে Two Boss Employees পদ্ধতির সংগঠন কাঠামোও বলা হয়ে থাকে । উভয় ধরনের ব্যবস্থাপকই মহা-ব্যবস্থাপকের নিকট দায়ী থাকেন। উভয়ের পারস্পরিক চেষ্টা, সমন্বয় ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আপনা-আপনি কাজের মধ্যে এক ধরনের গতির সঞ্চার হয় । কার্যক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা মেট্রিক্স ব্যবস্থাপকের কাছে যায় এবং তিনি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে মেট্রিক্স ম্যানেজারকে অবশ্যই যোগ্য ও অধস্তনদের ওপর যথেষ্ট প্রভাবশালী হতে হয় । ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের এ্যারোস্পেস কোম্পানিতে সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এ সংগঠন যাত্রা শুরু করে । নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে এরূপ সংগঠন কাঠামো তুলে ধরা হলো:
মেট্রিক্স সংগঠনের বৈশিষ্ট্য :
১. এটি হলো কার্যভিত্তিক ও দ্রব্যভিত্তিক বিভাগীয়করণের মিশ্রণ;
২. এক্ষেত্রে দু'ধরনের ব্যবস্থাপক একই সঙ্গে কাজ করে; যথা- কার্যিক ব্যবস্থাপক ও প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক;
৩. কার্যিক ব্যবস্থাপকের কাজ হলো প্রজেক্ট ব্যবস্থাপকের চাহিদামতো জনশক্তি, উপায়-উপকরণ ও সেবা সরবরাহ করা;
৪. প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক বিশেষ দ্রব্য বা প্রজেক্টের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং যার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে;
৫. উভয় ধরনের ব্যবস্থাপকদের চেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর এরূপ সংগঠনের সফলতা নির্ভর করে এবং
৬. উভয় ধরনের ব্যবস্থাপক একযোগে প্রজেক্ট ম্যানেজার বা সাধারণ ব্যবস্থাপকের নিকট দায়ী থাকে ।
আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন ব্যবসায় পরিমণ্ডলে প্রচলিত সাংগঠনিক কাঠামোসমূহের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ১৯৬০ সালের পর থেকে মেট্রিক্স সংগঠন কাঠামোর ব্যবহার শুরু হয় । এর পর থেকে আধুনিক বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে । এ ধরনের জনপ্রিয়তার পরও মেট্রিক্স সংগঠন সর্বত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে তা নয় । এছাড়া বেশ কিছু অসুবিধাও এর কার্যকারিতাকে ক্ষেত্রবিশেষে বাধাগ্রস্ত করে । নিম্নে এরূপ সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো :
সুবিধাসমূহ (Advantages) :
১. নির্বাহীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing efficiency of the executives) : এক্ষেত্রে প্রজেক্ট পর্যায়ে ও কার্যক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকগণ যথেষ্ট কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করেন এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণের অনুমোদনসাপেক্ষে নিজেরাই অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । ফলে নির্দিষ্ট প্রজেক্ট বা ব্যবসায় পর্যায়ের (Business level) নির্বাহীরা অধিক দক্ষতা অর্জন ও যোগ্যতা প্রদর্শনের সূযোগ পায় ।
২. সহযোগিতার উন্নয়ন (Developing co-operation) : এক্ষেত্রে অঞ্চল, প্রজেক্ট, দ্রব্য বা ব্যবসায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত নির্বাহী যেমনি তার প্রজেক্টের জন্য উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহীর (CEO) কাছে দায়ী থাকেন তেমনি উক্ত প্রজেক্টের প্রতিটা কাজ সম্পাদনের জন্য কার্যভিত্তিক নির্বাহীগণ প্রজেক্ট নির্বাহীকে সহযোগিতা প্রদান করেন । ফলে ব্যবসায় পর্যায়ে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠে ।
৩. কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা (Establishing effective co-ordination) : মেট্রিক্স সংগঠন প্রতিষ্ঠানে সমান্তরাল সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একটা প্রজেক্টকে কার্যিক ব্যবস্থাপকগণ পাশাপাশি থেকে সহযোগিতা করেন । উৎপাদন বিভাগের নির্বাহী সফল হলেও যদি বিপণন বিভাগের নির্বাহী সফল না হয় তবে সামগ্রিকভাবে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক দায়ী হয় এবং তার সাথে অন্যরাও সেজন্য ঊর্ধ্বতনের (CEO) নিকট দায়ী থাকে । ফলে বাধ্য হয়েই একে অন্যের সাথে কাজের সমন্বয় করে ।
৪. উচ্চ নির্বাহীগণকে সহায়তা দান (Providing assistance to chief executives) : এরূপ সংগঠনে উপরিস্তরের (Corporate level) নির্বাহীগণকে প্রজেক্ট লেভেল দেখার জন্য তেমন সময় ব্যয় করতে হয় না। উন্নত তথ্য প্রযুক্তির কারণে তার নিকট সকল প্রজেক্টের সর্বশেষ তথ্য থাকে । প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র তাকে প্রজেক্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান বা হস্তক্ষেপ করতে হয় । ফলে তাঁর বা তাঁদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও নতুন নতুন উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয় ।
৫. প্রতিভা ও দক্ষতার সমন্বয় (Co-ordination between intelligence and efficiency) : এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে বহুমুখী প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা একত্রিত হয় । উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানো সহজ হয় । এতে যে কোন জটিল সমস্যা সহজে সমাধান করে এগিয়ে যাওয়া যায় ।
অসুবিধাসমূহ (Disadvantages ) :
১. প্রশাসনিক খরচ বৃদ্ধি (Increasing administrative cost) : এরূপ সংগঠন কাঠামোতে কার্যভিত্তিক বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণের সাথে প্রতিটা প্রজেক্টের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মী কর্মরত থাকায় প্রশাসনিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ।
২. দ্বৈত কর্তৃত্বের বিপদ (Danger of dual authority) : এরূপ সংগঠনে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক, কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপক এবং ক্ষেত্রবিশেষে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ পাশাপাশি কর্মরত থাকেন । এতে কোনো সমস্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রদানে দ্বৈত কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয় । যা ক্ষেত্রবিশেষে সমস্যার সৃষ্টি করে ।
৩. দ্বন্দ্ব সৃষ্টি (Making conflict) : এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে একই সমান্তরালে কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপক ও প্রজেক্ট ব্যবস্থাপকগণ কাজ করায় একে অন্যকে কোনো নির্দেশ দিতে বা বাধ্য করতে পারে না । তাই কোনো কারণে একবার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে তা দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এমন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয় ।
৪. দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যা (Problem in taking group decision) : এ ধরনের সংগঠনে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও সমান্তরাল পর্যায়ে কর্মরত ব্যবস্থাপকগণ দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেন । প্রতিটা বিষয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে যেয়ে ঝামেলার পাশাপাশি সময় নষ্ট ও নানান ধরনের জটিলতা লক্ষ করা যায় ।
৫. পরিবর্তনে সমস্যা (Problem in change) : এরূপ সংগঠনে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে হলে সে ধরনের সিদ্ধান্ত কর্পোরেট লেভেল বা উচ্চ পর্যায় থেকে নিতে হয় । সেক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো দুর্বলতা বা নিচের পর্যায়ের নির্বাহীগণের দক্ষতায় অভাব থাকলে এরূপ পরিবর্তনের সাথে দ্রুত সাড়াদান তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না ।
একটা প্রতিষ্ঠানের কাজকে সুষ্ঠুভাবে বিভাজন করে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ সৃষ্টি, প্রতিটা বিভাগ ও উপবিভাগের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ এবং ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত একের সাথে অন্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজ সংগঠন নামে পরিচিত । এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টির ফলে তা নিঃসন্দেহে একটা কাঠামোর রূপ লাভ করে । যেখানে শীর্ষ পর্যায়ে একজন মুখ্য নির্বাহী থাকেন এবং তা যতই নিচের দিকে বিস্তৃত হয় ততই তা একটা পিরামিডের রূপ লাভ করে । এরূপ কার্য বিভাজন, দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভুল হলে বাহ্যিক দিক থেকে তা অনেক সময় বোঝা না গেলেও কার্য পরিচালনায় যেয়ে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে। যা সংশোধন কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় । বিষয়টি ইঞ্জিন তৈরি বা সংযোজনের মত । স্টার্ট দিলেই ধরা পড়ে তা কতটা যথার্থ । ক্লাব সংগঠনের কাঠামো দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলে না । ছোট প্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে বড় প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না । উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠান চালাতে সংগঠন কাঠমোকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হয়। তাই এরূপ কাঠামো গড়তে এর উদ্যোক্তা বা শীর্ষ নির্বাহীদের নানান বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে । নিম্নে এরূপ বিবেচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো:
১. উদ্দেশ্য (Objectives) : সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন করার পূর্বে প্রতিষ্ঠানকে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয় অতঃপর উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে কার্যবিভাজন এবং প্রয়োজনীয় বিভাগ ও উপবিভাগ খুলতে হয় । একটি ক্লাবের সংগঠন কাঠামো তার উদ্দেশ্যের কারণেই এক ধরনের হয় । উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোও উদ্দেশ্য বিবেচনায় ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে ।
২. দক্ষতা (Efficiency) : সংগঠন কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা আবশ্যক যাতে ন্যূনতম সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয়ে পূর্ব পরিকল্পিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদান যাতে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে সংগঠন কাঠামো প্রণয়নে তা নিশ্চিত করারও প্রয়োজন পড়ে। একজন উর্ধ্বতনের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন এমন সংখ্যক অধস্তন রাখা উচিত যাদের কাজকে তিনি সুষ্ঠুভাবে তদারক করে নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন ।
৩. নির্দিষ্টতা (Specification) : সংগঠনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মচারীর স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত । এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু তাও স্পষ্ট থাকতে হবে। এজন্য প্রত্যেকটি বিভাগ, উপবিভাগ ও ব্যক্তির কাজকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন । প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তৃত্বও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা দরকার। সংগঠন কাঠামো প্রণয়নের সময় এ বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে রাখা একজন সংগঠকের কর্তব্য ।
৪. বিশেষজ্ঞতা (Specialization) : সংগঠন কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে এর প্রত্যেক ব্যক্তি, বিভাগ ও উপবিভাগ বিশেষজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায় । এ জন্য কার্যাদি এমনভাবে ভাগ করা প্রয়োজন যাতে একজন কর্মীকে একটিমাত্র কাজই করতে হয় বা একটি বিভাগ একই ধরনের কার্য সম্পাদন করে । আর এটা সম্ভব হলে ব্যক্তি বা বিভাগের পক্ষে ঐ কাজে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়ে থাকে ।
৫. ভারসাম্য (Balancing) : সংগঠনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ ও উপবিভাগের কার্যাবলির মধ্যে যতদূর সম্ভব সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। কোনো বিভাগের কাজ বেশি হলে সেখানে বেশি জনশক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন । আবার কাজের পরিমাণ কম হলে জনশক্তিও কম রাখা দরকার । এমন যেনো না হয় যে কোনো বিভাগ বা এর কর্মীদের কাজ নেই আবার কোনো বিভাগের কর্মীরা কার্যভারগ্রস্ত ।
আরও দেখুন...
Promotion