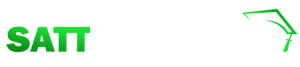পরিবেশের সাথে জীবের মানিয়ে চলার বিশেষ গুণকে অভিযোজন (adaptation) বলে।
প্রজাতিঃ
Job Ray খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম species শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রজাতি জীবের শ্রেণিবিন্যাস স্তরের
সর্বনিম্ন মৌলিক স্তর একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত, দৈহিক ও জনন সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সাদৃশ্যযুক্ত একদল জীব যারা নিজেদের মধ্যে মিলনে উর্বর (জননক্ষম) প্রজন্ম সৃষ্টিতে সক্ষম তাদের প্রজাতি বলে।
প্রত্যেক প্রজাতির নিজস্ব সুস্পষ্ট গাঠনিক, আচরণগত ও বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রজাতি হচ্ছে জীবের ক্ষুদ্রতম সুস্পষ্ট গোষ্ঠীকরণ (smallest distinct grouping of organisms)। পরিবেশের সঙ্গে একটি প্রজাতির অনন্য ও বহুমাত্রিক সম্পর্ককে নীশ বলেএকটি প্রজাতি এমন সব সদস্য নিয়ে গঠিত যারা কেবল নিজেদের মধ্যেই জনন ঘটাতে সক্ষম।
প্রজাতি শনাক্তকরণ এর জন্য বৈশিষ্ট্য (Characteristics for Indentification of Species)
প্রজাতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করার বিষয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও প্রজাতি শনাক্তকরণের জন্য বৈশিষ্ট্য:
১. অভিন্ন উৎপত্তি (Common descent) : একটি প্রজাতির সদস্যদের উৎপত্তি অবশ্যই প্রাকৃতিকভাবে অভিন্ন পুর্বপুরুষ থেকে হবে। বস্তুত তাদের ঐতিহাসিক স্বত্ত্বা (historical entities) থাকবে।
২. সুনির্দিষ্ট ক্ষুদ্রতম জীবগোষ্ঠী (Smallest distinct grouping of plants and animals) : অঙ্গসংস্থানিক ও ক্রোমোজোমীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে এই জীবগোষ্ঠীকে বংশলতিকা বা পেডিগ্রি (pedigre) তে অবশ্যই ক্ষুদ্রতম ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে ।
৩. প্রজননিক সম্প্রদায় (Reproductive community) : প্রজাতি গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে। যৌন জননে সক্ষম কিন্তু অন্য এরূপ জনগোষ্ঠী থেকে অবশ্যই পৃথক।
৪. বাস্তুতান্ত্রিক একক (Ecological unit) : বাস্তুতান্ত্রিকভাবে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা একই পরিবেশে একক জনগোষ্ঠী হিসেবে বাস করে এবং ঐ পরিবেশে বসবাসকারী অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর সাথে আন্ত:বিক্রিয়াগতভাবে অবশ্যই পৃথক । অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজাতির সুনির্দিষ্ট বাস্তুতান্ত্রিক নীশ (ecological niche) রয়েছে ।
৫. জেনেটিক একক (Genetic unit): প্রজাতি এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানযোগ্য এক বিশাল জিন ভান্ডার রয়েছে। তবে তা অন্য জীবগোষ্ঠী হতে পৃথক।
জীবগোষ্ঠীঃ
একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে দলবদ্ধ বসবাসকারী এবং পারস্পরিক মিথক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের বংশধর সৃষ্টিকারী তথা জেনেটিক তথা বিনিময়কারী একই প্রজাতির জীবসমষ্টিকে জীবগোষ্ঠী বলে। যেমন - ধানক্ষেতে পঙ্গপাল, একটি পুকুরে কটকটি ব্যাঙ, একটি জমিতে আবাদকৃত নির্দিষ্ট ফসল (যেমন-ধান, গম, সরিষা) বা একটি গর্জন বন ইত্যাদি একেকটি জীবগোষ্ঠী। একটি জীবসম্প্রদায়ে (community) শক্তির সঞ্চারণে ও পুষ্ঠির চক্রাকার আবর্তনে জীবগোষ্ঠী গতিশীল একক হিসেবে কাজ করে। এটি স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি এবং এর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়।
জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্টঃ
পরিবেশের একক হিসেবে জীবগোষ্ঠীর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারিত ও চক্রাকারে আবর্তিত হয়। সুস্থ, স্বনিয়ন্ত্রিত, গতিশীল জীবগোষ্ঠীর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব অটুট থাকে। জীবগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।
১. ঘনত্ব (Density) কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক স্থানে বসবাসকারী কোন প্রজাতির মোট সংখ্যাকে জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব বলে । জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব সর্বদা পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে জীবগোষ্ঠীর ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে । জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব নির্ভর করে জীবের জন্মহার, মৃত্যুহার, অভিপ্রয়ান (migration) ইত্যাদির উপর।
২. জন্মহার বা ন্যাটালিটি (Birth rate or Natality) : (একক সময়ে একটি পপুলেশনে যে হারে নতুন সদস্যের
সংযোজন ঘটে তাকে জন্মহার বা ন্যাটালিটি বা পোটেনসিয়াল ন্যাটালিটি (potential natality) বলে) ৩. মৃত্যুহার বা মর্টালিটি (Death rate or Mortality) : (একক সময়ে একটি পপুলেসনের সদস্যদের যে হারে মৃত্যু ঘটে তাকে মৃত্যুহার বলে। জন্মহারের মতো মৃত্যুহারও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (যথা-ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি) দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৪. বয়সের বন্টন (Age Distribution) ((একটি জীবগোষ্ঠীতে নানা বয়স-শ্রেণিতে (age-class) জীবসদস্যের সংখ্যা বা শতকরা হারকে বয়সের বন্টন বলে। কোন জীবগোষ্ঠীতে জীবসদস্যদের বয়সের বন্টন গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এটি জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়কেই প্রভাবিত করে। মৃত্যুহার সাধারণত বয়সের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং জীবনের প্রথম ও শেষ দিকে মৃত্যুর হার হয় সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণির জীবের ক্ষেত্রে মধ্য বয়সেই তাদের জন্ম দানের হার সবচেয়ে "বেশি। জীবগোষ্ঠীর একক সদস্যদেরকে প্রজননপূর্ব, প্রজননক্ষম ও প্রজননউত্তর এ তিনভাগে ভাগ করা যায়। —৫. জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি (Population Growth) : জীবগোষ্ঠীর হ্রাস-বৃদ্ধি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জীবগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সদস্য সংখ্যা বাড়লে ( জন্মগ্রহণ ও বাইরে থেকে আগমন ঘটলে) জীবগোষ্ঠীর আকারও বড় হয়। পরিবেশে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান সদস্যসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবগোষ্ঠীরও বৃদ্ধি ঘটে।
৬. জীবগোষ্ঠীর ভারসাম্য (Population Equilibrium) : একটি জীবগোষ্ঠী বৃদ্ধির সময় প্রথম দিকে দ্রুত বাড়ে। প্রারম্ভিকভাবে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ বৃদ্ধি একই মাত্রায় দীর্ঘকাল ধরে রাখতে জীবগোষ্ঠী সচেষ্ট থাকে। এলাকার বহনক্ষমতা (carrying capacity) যদি ঠিক থাকে, জীবের জন্যে ক্ষতিকারক উপাদান যদি অপসারিত হয় তাহলে জীবগোষ্ঠীর ভারসাম্য রক্ষিত হবে। তখন জন্ম ও মৃত্যুহার সমান হবে। এ অবস্থায় জননহার কম-বেশি হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিহার যতদিন পর্যন্ত মৃত্যুহারের সমান থাকবে জীবগোষ্ঠীর ভারসাম্যও ততদিন সুরক্ষিত থাকবে।
৭. জীবগোষ্ঠীর বিস্তারণ (Population Dispersal) : যখন একটি জীবগোষ্ঠীর সদস্যরা জীবগোষ্ঠী অধিকৃত এলাকার ভেতরে প্রবেশ করে কিংবা ঐ এলাকা ছেড়ে অন্য জীবগোষ্ঠীর এলাকায় একক জীব হিসেবে বা জননশীল অংশ (যেমন জীব, রেণু, লার্ভা ইত্যাদি) হিসেবে অনুপ্রবেশিত হয় তখন এ চলনকে জীবগোষ্ঠীর বিস্তারণ বলে। জীবগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আহার-আলো-পানিজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে, শারীরবৃত্তিক কারণে, জনন বৈশিষ্ট্যের জন্য, শিকারী জীবের হাত থেকে বাঁচার জন্য জীবগোষ্ঠীর সদস্যরা সবসময় অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে থাকে। এভাবে নতুন নতুন এলাকা জীববৈচিত্রের সমাহারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।
৮. সীমিতকরণ (Growth Regulation) : প্রত্যেক জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধির নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে ঐ জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি থেমে যায় এবং বৃদ্ধির হারও কমতে থাকে। পরিবেশিক বিভিন্ন উপাদান এ বৃদ্ধির হারকে সীমিত রাখতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আবার কোন জীবগোষ্ঠী অন্য একটি জীবগোষ্ঠী দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।
পপুলেশন বণ্টনে প্রভাবকসমূহঃ
১. জলবায়ু : পানি, আর্দ্রতা, সূর্যালোক, তাপমাত্রা, বায়ুর গতিবেগ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি পপুলেশনের সার্বিক গঠনে, ভূমিকা রাখে ।
২. ভূ-সংস্থান : ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, অক্ষাংশ বিভিন্ন অরণ্যের পপুলেশন তৈরি করে। যেমন-হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মে।
৩. মৃত্তিকা : মাটির প্রকৃতি, মাটির পানি, তাপমাত্রা, মৃত্তিকার বায়ু, খনিজ লবণ উদ্ভিদ পপুলেশন গঠনে ভূমিকা রাখে ।
৪. জীবজ প্রভাবক : বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, পরজীবী, পরাশ্রয়ী জীব পরস্পর সহাবস্থান করে এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট পপুলেশন তৈরিতে মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করে।
জীবসম্প্রদায় (Community)
একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াশীল (interacting) সকল জীবগোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে জীবসম্প্রদায় বলে। অর্থাৎ জীব সম্প্রদায় বলতে একটি বাস্তুতন্ত্রের সম্পূর্ণ জীবন্ত অংশকে সব উদ্ভিদ, সব প্রাণী ও সব অণুজীব) বোঝায়। তবে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে কোনো এলাকার জীবগোষ্ঠীকে শৈবাল সম্প্রদায়, ফার্ণ সম্প্রদায়, ব্যাঙ সম্প্রদায়, পতঙ্গভুক বা পাখি সম্প্রদায় প্রভৃতি উপায়েও ভাগ করা যায় ।
জীবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যঃ
১. প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species diversity) : একটি জীবসম্প্রদায়ে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব বাস করে। এবং প্রজাতি বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। জীবসম্প্রদায়ে প্রজাতির সংখ্যা ও জীবগোষ্ঠীর প্রাচুর্যেও ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়।
২. জীবের আকার ও গঠন (Growth form and structure) : একটি জীবসম্প্রদায়ের প্রধান জীবগোষ্ঠীগুলোকে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন-শৈবাল, তৃণ, গুলা, বৃক্ষ ইত্যাদি। এ ধরনের প্রত্যেক জীবগোষ্ঠী বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত। যেমন-বৃক্ষ, এক্ষেত্রে উদ্ভিদগুলো চিরসবুজ, পাতাঝরা, চওড়া পাতাধর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের হতে পারে। এভাবে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী একটি জীবসম্প্রদায়ের গাঠনিক ধরনকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. প্রাধান্য (Dominance) : কোনো জীবসম্প্রদায়েই সকল প্রজাতি সমান প্রাধান্য বিস্তার করে না। কয়েকটি মাত্র প্রজাতি আকৃতি, সংখ্যা বা কর্মকান্ডের মাধ্যমে জীবসম্প্রদায়ের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করে ।
৪. ক্রমাগমন (Succession) : প্রত্যেক জীবসম্প্রদায়ের নিজস্ব ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দিকমুখী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি জীবসম্প্রদায় গড়ে উঠে।
৫. আপেক্ষিক প্রাচুর্য (Relative abundance) : একটি জীবসম্প্রদায়ে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী আপেক্ষিক অনুপাত অনুযায়ী উপস্থিত থাকে।
৬. খাদ্যস্তরীয় গঠন (Tropic structure) : জীবসম্প্রদায় প্রজাতিগুলোর মধ্যে খাদ্য গ্রহণজনিত সম্পর্কের ফলে উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী, তৃণভোজী থেকে মাংসাশী খাদকে শক্তি প্রবাহ নির্ধারিত হয়।
জীবের অভিযোজন (Adaptations of Organism):
যে দৈহিক বা শারীরবৃত্তিক আচরণগত বৈশিষ্ট্যাবলী কোনো জীবকে তার পরিবেশের অস্তিত্ব রক্ষায় ও বংশবিস্তারে আরও সুরক্ষিত করে তোলে তাকে অভিযোজন বলে। বিবর্তন, জিন মিউটেশন কিংবা দ্বৈবাৎ পরিবেশ পরিবর্তনে অভিযোজন সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয় । এসব বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এবং অনেক প্রজন্ম শেষে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অভিযোজন জীবগোষ্ঠীতে সঞ্চিত হয়ে সুস্পষ্ট হয়। এভাবে জীবসম্প্রদায়ে যে অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে উঠে তা থেকে জীব স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ে এবং প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়।
উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Plants)
আবাসস্থলে পানির উপস্থিতির উপর উদ্ভিদের গঠন ও প্রকৃতি নির্ভর করে। যেখানে পানির পরিমাণ সীমিত সেখানে উদ্ভিদের পরিমিত পানি ব্যবহারের কৌশলও রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদ পানির প্রাপ্যতা ও ঘাটতি এ দুটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। পানির এই ভারসাম্য অবস্থা উদ্ভিদের দৈহিক গঠনে নানা বৈচিত্র্য আনে। মাটির পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারমিং সব উদ্ভিদকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন । যথা-
১. জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট (Hydrophytes);
২. মরুজ উদ্ভিদ বা জেরোফাইট (Xerophytes);
৩. সাধারণ উদ্ভিদ বা মেসোফাইট (Mesophytes); .
৪. লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophytes)।
জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট (Hydrophytes): যে সব উদ্ভিদ সম্পূর্ণ আর্দ্রস্থান অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় পানিতে জন্মায় সেগুলোকে জলজ উদ্ভিদ (hydrophytes; hydro = পানি + phyte = উদ্ভিদ) বলে । জীবনচক্র সম্পন্ন করতে এরূপ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়াকে জলজ অভিযোজন বলা হয়। কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে জলজ উদ্ভিদ পরস্পর থেকে পৃথক হলেও তাদের অধিকাংশ বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে একই রকম। জলজ উদ্ভিদকে তার পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে নিচেবর্ণিত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।
ক. মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Free floating hydrophytes) : মাটির সাথে এসব উদ্ভিদের কোন যোগাযোগ নেই এবং পানির উপরিতলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। উদাহরণ- ক্ষুদিপানা (Lemna minor),কচুরীপানা (Eichhornia crassipes), টোপাপানা (Pistia stratiotes) ইত্যাদি।
খ. মূলাবদ্ধ ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Rooted Floating hydrophytes) : এ ধরনের জলজ উদ্ভিদের মূলগুলো পানির নিচে কাদায় আবদ্ধ থাকে কিন্তু দীর্ঘ পত্রবৃন্তযুক্ত পাতাগুলো পানির উপরিতলে ভাসমান থাকে। উদাহরণ- শাপলা (Nymphaea nouchali), পদ্ম (Nelumbium speciosum) ইত্যাদি।
গ. মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Rooted submerged hydrophytes) : এসব জলজ উদ্ভিদেরা সর্বক্ষণ পানির নিচে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় কর্দমাক্ত মাটিতে মূল দিয়ে আবদ্ধ থাকে। যেমন- হাইড্রিলা (Hydrilla verticillata), পাতা শেওলা (Vallisneria spiralis), পাতা ঝাঁঝি (Poramogeton nodosus) ইত্যাদি।.
ঘ. উভচর উদ্ভিদ (Amphibious Plants) : এসব উদ্ভিদের কিছু অংশ মাটিতে এবং কিছু অংশ পানিতে অবস্থান করে। উদাহরণ- হেলেঞ্চা (Enhydra fluctuans), কলমি লতা (Ipomoea aquatica) ইত্যাদি ।কলমি লতা (Ipomoea aquatica) ইত্যাদি ।
জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Hydrophytes):
ক. অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological adaptation):
১. এদের মূল সংক্ষিপ্ত, দুর্বল এবং সুগঠিত হয় না। মূলে মূলরোম থাকে না কারণ পানি শোষণের জন্য মূলরোমের প্রয়োজন হয় না। অনেক উদ্ভিদের (গুঁড়িপানা-Wolffia) আবার মূলই থাকেনা। ছোট উদ্ভিদ
২. কিছু উদ্ভিদের অস্থানিক ভাসমান (কেশরদাম-Jussiaea repens) থাকে যা উদ্ভিদকে
বায়ুকুঠুরী অ্যারেনকাইমা ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৩. জলজ উদ্ভিদের কাজ নমনীয় ও স্পঞ্জী ।
৪. প্রচুর বায়ুকুঠুরীর উপস্থিতি এদের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।
৫. পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম থাকে। তাই পানির টানে ছিড়ে যায় না। অনেক উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত স্ফীত (যেমন-কচুরিপানা) যা উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৬. প্রজাতিভেদে পাতা বিভিন্ন আকৃতির হয়। অনেক সময় মোমাবৃত। কখনো অতিশয় বৃহৎ। যেমন আমাজন লিলির পাতা এতো চওড়া যে একটি ছোট শিশুকে ধারণ করতে পারে। পাতা মোমাবৃত,চওড়া হলে পানির চাপ নিয়ন্ত্রিত থাকে।
খ. অন্তর্গঠনগত অভিযোজন (Anatomical adaptation) (ক) বাহ্যিক গঠন, (খ) কাণ্ডের অন্তর্গঠন
১. ত্বকে কিউটিকল হয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, নয় তো খুবই পাতলা থাকে। কারণ পানির অপচয় রোধ করা প্রয়োজন হয় না।
২. কান্ড ও পাতার অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে। এরা বায়ু (O). CO,) ধরে রাখে। তাছাড়া কুঠুরীগুলো।
৩. নিমজ্জিত উদ্ভিদে যান্ত্রিক টিস্যু সাধারণত থাকেনা। তাই সহজে পানির টানে ভেঙ্গে যায় না।
৪. উদ্ভিদের নিমজ্জিত অংশে স্টোমাটা থাকে না। কারণ কোষপ্রাচীর দিয়ে গ্যাসের বিনিময় ঘটে।
৫. পরিবহন টিস্যু থাকে না বা সুগঠিত নয়। কারণ নিমজ্জিত সকল অংশ দ্বারা পানি ও খনিজ শোষিত হয়। উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।
নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে ।
গ.শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptation): সব অঙ্গ দিয়ে পানি শোষণ করতে পারে (তুকে কিউটিকল না থাকায়), পানি শোষণের জন্য মূল ও মূলরোমের কাজ ও পাতার ত্বকেও ক্লোরোফিল থাকে, তাই পানির নিচে কম আলোতে ও কম CO-যুক্ত পরিবেশে জন হয় না। প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।
অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে (কারণ পরাগায়ন অনিশ্চিত)। প্রস্বেদন হার কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রস্বেদনের টান দরকার হয়না। প্রাণীর জলজ অভিযোজন (Aquatic adaptation of animals) কিনিতে বসবাসকারী প্রাণিদের জলজ প্রাণী বলে। জলজ পরিবেশে বসবাস করার জন্য প্রাণীর যে গঠনগত শারীরবীয় ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটে, তাদের সামগ্রিকভাবে জলজ অভিযোজন বলা হয়। মুধরনের হতে পারে-প্রাথমিক বা মুখ্য এবং সেকেন্ডারি বা গৌণ। জলজ অভিযোজন কাজ ও পাতার বায়ু কুঠুরীতে বায়ু জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণের অসুবিধা হয় না।
যে সব প্রাণী জলচর পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হয়ে আজীবন পানিতেই রাস করেছে, কখনও ডাঙ্গায় বাস করেনি সে সব প্রাণীর অভিযোজন হচ্ছে মুখ্য জলজ অভিযোজন, যেমন- মাছ। অন্যদিকে যে সব প্রাণী ভূচর (অর্থাৎ স্থলচর, যেমন - ভূপান্তর, ভূগর্ভচর, বৃক্ষচর, খেচর প্রভৃতি)
পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তনের গতিপথে কোনো কারণে জলচর হতে বাধ্য হয়েছে সে সব প্রাণীর অভিযোজন হচ্ছে গৌণ জলজ অভিযোজন। যেমন - তিমি, কাছিম, কুমির, জলহস্তি প্রভৃতি ।
* মুখ্য জলজ অভিযোজন : মাছ হচ্ছে মুখ্য জলচর প্রাণীর প্রধানতম উদাহরণ। পানিতে দ্রুত সাঁতার কাটতে যেন অসুবিধা না হয়, সে কারণে মাছের দেহ মাকু আকৃতির। কিন্তু সামুদ্রিক মাছ ছাড়া অধিকাংশ মাছ দ্বিপার্শ্বীয় চাপা। দেহপেশির তরঙ্গায়িত আন্দোলনে মাছ সাতার কাটে। ভারসাম্য রক্ষা ও চলনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পাখনা সহযোগিতা করে। শ্বসনের জন্য দ্রবীভূত গ্যাসীয় বিনিময় ঘটাতে অপারকুলামে সুরক্ষিত ফুলকা অবস্থিত। অনেক মাছ দ্রুত উপরে উঠতে এবং ডুবে যেতে সহায়তা করতে বায়ুথলি (পটকা) বহন করে। পানির গুণাগুণ দূর থেকে বুঝতে দেহের দুপাশে পার্শ্বীয় রেখাতন্ত্র নামে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ও গ্রাহকইন্দ্রিয় রয়েছে।
* গৌণ জলজ অভিযোজন : স্থলচর প্রাণিদের কোনো ধারা বা সদস্য যখন বিবর্তনের গতিপথে পানিতে বংশপরম্পরায় জীবনযাপনে সক্ষম তখন ওদের অভিযোজনকে গৌণ জলচর অভিযোজন নামে অভিহিত করা হয়। কয়েক প্রজাতির ব্যাঙ, কাছিম, কুমির, সাপ, পাখি, তিমি, জলহস্তি, উট প্রভৃতি প্রাণী গৌণ জলজ অভিযোজন প্রদর্শন করে।
গৌণ জলজ অভিযোজনের মধ্যে রয়েছে : দেহের আকার ছিমছাম গড়নের। ঘাড়ের খাঁজ অনুপস্থিত, লেজ সুগঠিত, পিনা লুপ্তপ্রায়। গ্রীবাসঞ্চালন প্রায় অনুপস্থিত। ত্বক বহিঃকংকালবিহীন (লোম বা আঁইশবিহীন)। তুর্কীয় গ্ৰন্থি নেই বললেই চলে। পুরু চর্বিস্তর অবস্থিত। হাঁস, রাজহাঁস, ব্যাঙের পদগুলো লিপ্তপাদ। তিমি, ডলফিন-এ পশ্চাৎপদ লুপ্ত, অগ্রপদ জিপার বা প্যাডলে (flippers or paddle) রূপান্তরিত। তিমি সাঁতার ও ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের পাখনাবিশিষ্ট । পাচ্ছিক পাখনার আন্দোলনে দেহ সামনে এগিয়ে চলে। কয়েক প্রজাতির তিমি সদস্য দাঁতবিহীন, কয়েক প্রজাতি দাঁতযুক্ত দাঁতবিহীনদের ব্যালীন প্লেট থাকে।
মরুজ উদ্ভিদ (Xerophytes): বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক ও বালুকাময় অঞ্চলের উদ্ভিদকে মরুজ উদ্ভিদ বলা হয় যে অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হয় সে অঞ্চলেও মরুজ উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। মোট কথা, যেখানে পানির সরবরাহ কম কিন্তু প্রস্বেদনের হার বেশি সেখানে মরুজ উদ্ভিদ অধিক জন্মে ওপেনহিমার (Oppenheimer-1960) মরুজ উদ্ভিদ বলতে সেসব উদ্ভিদকে বুঝিয়েছেন যারা আবাসস্থলে পানির অভাব মেটানোর জন্য নিজেদের বহির্গঠন, অন্তর্গঠন ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম) মরুজ উদ্ভিদকে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা:
১. খরা এড়ানো উদ্ভিদ (Drought escaping plants).
২. কৌশলে খরা এড়ানো উদ্ভিদ (Drought evading plants)
৩. খরা সহ্যকারী উদ্ভিদ (Drought enduring plants)
৪. খরা প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ (Drought resistant plants)।
মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of xerophytes) মরুজ পরিবেশে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে এসব উদ্ভিদ গাঠনিক ও শারীরবৃত্তিক পর্যায়ে বেশ কিছু অভিযো প্রদর্শন করে । উদ্ভিদের মরুজ অভিযোজনগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।
ক. বাহ্যিক অভিযোজনঃ মরুজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত আকারে ছোট ও ঝোপযুক্ত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ বালির ঝাপটা ও বায়ুর ঝাপটা সহ্য করতে পারে, তাই ভেঙ্গে যায় না।
২. মূল মাটির উপরিতলের কাছাকাছি অথবা খুবই গভীরে প্রলম্বিত। তাই উপর থেকে সামান্য বৃষ্টির পানি যেমন শোষণ করতে পারে, দ্রুত মাটির গভীরে চলে যাওয়া পানিও শোষণ করতে পারে। অর্থাৎ এদের মূল সুগঠিত।
৩. অনেক উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড চ্যাপ্টা, রসালো ও সবুজ থাকে। তাই পানি ধরে রাখতে পারে।
৪. পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট, পুরু বা কাঁটায় রূপন্তরিত হয়।
খ. অন্তর্গাঠনিক অভিযোজনঃ
১. মূলের প্রাচীর পুরু ও দৃঢ়; কান্ডের কিউটিকল খুব পুরু।
২. এপিডার্মিস পুরু প্রাচীরযুক্ত; হাইপোডার্মিস বহুস্তরবিশিষ্ট এবং স্কেরেনকাইমা কোষে গঠিত।
৩. পরিবহন টিস্যু সুগঠিত এবং লিগনিনযুক্ত।
৪. ভাস্কুলার বান্ডল ও যান্ত্রিক টিস্যু এবং পাতার কিউটিকল সুগঠিত।
৫. মেসোফিল প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় Euphorbia সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত।
৬. পত্রবৃদ্ধ এপিডার্মিসের নিচের স্তরে থাকে, কখনওবা গর্তের ভিতর অবস্থান করে, অনেক সময় রোমে আবৃত থাকে
গ. শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনঃ
১. ত্বক পুরু হওয়ায় প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।
২. স্টোমাটা নিমজ্জিত হওয়ায় এবং রোম দিয়ে ঢাকা থাকায় প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।
৩. এদের পাতা কন্টককে পরিণত হওয়ায় প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায় ।
৪. উদ্ভিদকোষে পানির ঘাটতি ঘটায় এনজাইমের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়।
৫. কোষরসের উচ্চ ঘনত্বের কারণে পাতা সহজে শুকাতে পারে না।
উদাহরণ : শতমূলী (Asparagus racemosus), ফণিমনসা (Opuntia dillenit), ঘৃত কুমারী (Aloe vera), খেজুর (Phoenix sp.), করবী (Nerium odoratum), ইউফরবিয়া (Euphorbia) প্রভৃতি ।
মরুজ প্রাণীর অভিযোজনঃ
কম বৃষ্টিপাত, পানি স্বল্পতা, চরম তাপমাত্রা, ধূলিঝড় ও উদ্ভিদ স্বল্পতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মরুজভূমি এক অনন্য ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। এমন পরিবেশেও অনেক প্রাণী বাস করে এবং তারা সুঅভিযোজিত হয়েই বাস করে। নিচে মরুজ প্রাণীর কয়েকটি অভিযোজন উল্লেখ করা হলো।
১. মরুজ প্রাণী দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকতে পারে। এদের অধিকাংশই রসালো খাদ্যে বিদ্যমান পানি দ্বারা পানির অভাব পূরণ করে।
২. মরুজ কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপদের দেহে পানি প্রতিরোধ আবরণ থাকে ফলে উচ্চমাত্রায় দেহ হতে পানি বের হয়ে যেতে পারে না।
৩. এদের অনেকের দেহে চর্বি, শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চিত থাকে যেগুলো জারণের ফলে পানি সৃষ্টি হয়।
৪. মরুজ স্তন্যপায়ীদের দেহত্বকে ঘর্মগ্রন্থি খুব কম থাকে। এছাড়া অনেকের দেহে কাঁটা বা আঁশের আবরণ থাকে, ফলে পানির বাষ্পীভবন ও ঘাম নিঃসরণ কম হয়।
৫. মরুজ প্রাণী রেচনবর্জ্য থেকে অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করে রাখে ফলে এদের রেচনবর্জ্য শুষ্ক প্রকৃতির হয়।
৬. দিনের কড়া তাপ এড়ানোর জন্য অধিকাংশ মরুজ প্রাণী নিশাচর প্রকৃতির হয়।
৭. অনেক মরুজ প্রাণী খুব দ্রুত চলতে পারে এবং বালিতে লুকাতে পারে ।
৮. মরুজপ্রাণিদের বর্ণময়তা বালুময় পরিবেশের সাথে মিশে শত্রুর হাত থেকে রক্ষায় আরও অবদান রেখেছে।
লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophytes)
যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত মাটিতে জন্মায় তাদেরকে লোনামাটির উদ্ভিদ বলে। এরূপ আবাসস্থলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ (NaCl, MgCl,, Mg SO.) বেশি থাকায় সাধারণ উদ্ভিদ সেখান থেকে পানি শোষণ করতে পারে না। তাই, সেখানে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। মাটিতে প্রচুর পানি থাকা সত্ত্বেও লবণের আধিক্যের জন্য সাধারণ উদ্ভিদের পক্ষে ঐ পানি শোষণ করা সম্ভব হয় না অগ্রহণযোগ্য পানিযুক্ত এরূপ মাটিকে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক বা উষর মাটি (physiologically dry soil) বলা হয়। এ কারণে লবণাক্ত মাটির উদ্ভিদের ও মরু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী লোনামাটির উদ্ভিদকে মরুপ্রেমী (xerophilous) উদ্ভিদ নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।
লোনামাটির উদ্ভিদ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জন্মায় তাদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (mangrove plants) বলা যেসব হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যথা- সুন্দরবনে এই জাতীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায় ।
লোনামাটির উদ্ভিদ চারটি গ্রুপে বিভক্ত, যথা-
মিথোফিলাস (Lithophilous) : লবণাক্ত অঞ্চলের
নিউম্যাটোফোর শিলা ও পাথরের নুড়ির উপর জন্মায়।
স্যামোফিলাস (Psammophilous) : লোনাপানিতে বালি মাটির উপর জন্মায় ।
পেলোফিলাস (Pelophilous) : লোনাপানির কাদা
মাটিতে জন্মায়।
হেমোফিলাস (Helophilous) : লবণাক্ত জলাভূমিতে জন্মায়। লবণাক্ত মরু অঞ্চলেও জন্মাতে পারে।
লোনামাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যঃ
১. এসব উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রসালো।
২. কদমাক্ত মাটিতে খাড়া হয়ে থাকার জন্য স্তম্ভমূল ঠেসমূল থাকে যা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত থাকে ।
৩. এই বিশেষ ধরনের মূল যা অক্সিজেন গ্রহণের জন্য (উল্টো দিকে বর্ধিত হয়ে) মাটির উপরে উঠে আসে তাকে নিউম্যাটোফোর (pneumatophore) বলে।
৪. মূলের অভ্যন্তরে (কর্টেক্স-এ) বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।
৫. লোনামটির উদ্ভিদে প্রস্বেদন কম হয়।
৬. উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট হয় ।
৭. অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (viviparous germination) হয়।
লোনামাটির অভিযোজনঃ
১. মাটির গভীরতার সাথে সাথে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের মূলতন্ত্র মাটির খুব গভীরে না গিয়ে মাটির উপরের স্তরেই বিস্তৃত থাকে।
২. অধিক লবণাক্ত পানি শোষণ করতে অসুবিধা হয়, তাই বৃষ্টির সময় লবণাক্ততা কিছু কমে আসলে উদ্ভিদ দ্রুত পানি শোষণ করে তাদের প্যারেনকাইমা কোষে সঞ্চয় করে রাখে। এ কারণে এদের কাণ্ড, পাতা ও মূলকে কিছু রসালো দেখায়।
৩. জোয়ার-ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক উদ্ভিদে স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল থাকে।৪. শ্বাসমূলের ভেতরে বায়ুকুঠুরী থাকে এবং সে কুঠুরীতে বায়ু (O2) ধরে রাখতে পারে। শ্বাসমূলের কারণে মূল ও বাইরের সাথে গ্যাসের বিনিময় সহজ হয়।
৫. জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের (ম্যানগ্রোভ অঞ্চল) অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অংকুরোদগম হয় ফল মাতৃউদ্ভিদে থাকা অবস্থায় বীজের অংকুরোদগম শুরু হওয়াকে জরায়ুজ অংকুরোদগম বা vivipary বলে । এক্ষেত্রে বীজের ভ্রূণমূল বড় হয়ে কাদা মাটিতে খাড়াভাবে পড়ে, ফলে এরা জোয়ার-ভাটায় ভেসে না গিয়ে স্থায়ী হয়।
উদাহরণ : কেওড়া (Sonneratia apetala), পশুর (Carapa moluccansis), গোলপাতা ( Nipa fruticans), হারগোজা (Acanthus illicifolius), সুন্দরী (Heritiera fomes) প্রভৃতি।ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (Mangrove Vegetation)।
লবণাক্ত পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জুওপ্লাংক্টনসহ বিশাল আকৃতির তিমি পৃথিবীর লবণাক্ত পরিবেশে বাস করে। পৃথিবীর লবণাক্ত পরিবেশ বলতে সাগর-মহাসাগরীয় অঞ্চলকে বোঝায়। এটি পৃথিবীর বিশালতম ঝুয়োম। এখানে বসবাসকারী জীবের অভিযোজনগুলো নিচে আলোচিত হলোঃ
১. লবণ নিয়ন্ত্রণ : মাছ লোনাপানি পান করতে পারে, ফুলকার ভিতর দিয়ে ত্যাগও করতে পারে। সামুদ্রিক পাখিও লোনা পানি পান করে। কিন্তু নাসাগহ্বরে অবস্থিত নাসাগ্রন্থি বা লবণ গ্রন্থি (salt glands)-র মাধ্যমে পাখি সর্দি ঝড়ার মতো করে সে লবণ বের করে দেয়। তিমি কখনও লবণ পানি পান করে না বরং খাদ্য হিসেবে যে সব জীব গ্রহণ করে সেখান থেকে পানির প্রয়োজন মেটায়।
২. অক্সিজেন প্রাপ্তিঃ পানির নিচে বসবাসকারী মাছ ও অন্যান্য জীব হয় ফুলকা না হয় ত্বকের মাধ্যমে O2 গ্রহণ করে। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীরা পানিপৃষ্ঠে নাক উঠিয়ে শ্বসন সম্পন্ন করে। এ কারণে গভীর পানিতে বাসকারী তিমির মাথার চূড়ায় ব্রো-হোল (blowhole) নামে বিশেষভাবে নির্মিত একটি ছিদ্রপথ রয়েছে।
৩. পানির চাপজনিত সমস্যার মোকাবিলা : সমুদ্রে গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপও বেড়ে যায়। (প্রতি ৩৩ ফুট পানির জন্য প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড পর্যন্ত পানিচাপ বেড়ে যায় । কিছু সামুদ্রিক প্রাণী কখনও পানির গভীরতা পরিবর্তন করে না, কিন্তু যেসব প্রাণী (যেমন-তিমি, সামুদ্রিক কাছিম ও সীল) দৈনিক বেশ কয়েকবার অগভীর পানি থেকে গভীর পানিতে চলাচল করে তারা এ সমস্যা মোকাবিলায় যথেষ্ট পারদর্শী প্রমাণিত হয়েছে । স্পার্ম-তিমি (sperm whale) সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় মাইল সাগরতলে ডুব দিতে সক্ষম। এ সময় তিমির ফুসফুস ও বক্ষপিঞ্জর সংকুচিত হয়ে শরীরকে পানির গভীরে যেতে বিশেষভাবে অভিযোজিত করেছে।
৪. তাপমাত্রার উঠা-নামা প্রতিরোধ : অনেক সামুদ্রিক প্রাণী শীতল রক্তবিশিষ্ট। এদের দৈহিক তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার মতোই। কিন্তু স্তন্যপায়ীরা উষ্ণরক্তবিশিষ্ট হওয়ায় পরিপার্শ্বিক তাপমাত্রা যাইহোক দৈহিক তাপমাত্রা অর্থাৎ অন্তঃস্থ তাপ সব সময় স্থির রাখতে হয়। এ কারণে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর দেহে চর্বি ও যোজক টিস্যুনির্মিত তাপ অপরিবাহী স্তর থাকে ।
৫. বায়ু ও পানিতরঙ্গ : জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের অন্তর্বর্তী অংশে (intertidal zone) বসবাসকারী প্রাণিদের উচ্চ পানিচাপ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু উচ্চ বায়ুচাপ ও তরঙ্গের মোকাবিলা করতে হয়। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ পাথর ও অন্যান্য কঠিন বস্তুতে আটকে থাকার অভিযোজনে অভিযোজিত হওয়ায় পানির টানে ভেসে যায় না, অনেকে কঠিন খোলসে আবৃত থাকে ।
৬. আলো প্রাপ্তি : যে সব জীবের পর্যাপ্ত আলো দরকার (যেমন-গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রবাল ও তাদের সংশ্লিষ্ট শৈবাল) সে সব জীব অগভীর ও এমন পরিষ্কার পানিতে বাস করে যাতে পর্যাপ্ত আলো পৌঁছাতে পারে। গভীর পানিতে যেহেতু অপর্যাপ্ত আলো থাকে, কিংবা অন্ধকার থাকে সে কারণে তিমিরা শিকারের জন্যো ইকোলোকেশন বা শব্দের উপর। হরণশক্তির উপর) নির্ভর করে । অতল সাগরে কিছু প্রাণী নিজস্ব আলো বিচ্ছুরণকারী অঙ্গের সাহায্যে, কিছু প্রাণী আলো উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া ধরে রেখে আহার ও সঙ্গীকে খুঁজে নেয়।
বায়োম
ক. তুন্দ্রা বায়োমঃ
১। এ অঞ্চলে সারা বছর বরফ দ্বারা আবৃত থাকে ।
২। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৯°C এর বেশি হয় না এবং শীতকালে তাপমাত্রা 0°C এর নিচে নেমে আসে।
৩। এখানে বছরে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত থাকে।
৪ । সুমেরু ও কুমেরু নিয়ে এ মেরুমণ্ডল গঠিত
বসবাসকারী প্রাণি ও উদ্ভিদঃ ঘাস, মস, লাইেেকন, বল্লা, হরিণ, নেকড়ে, খরগোশ, পেচা, বাজপাখি প্রভৃতি।
খ. মরুভূমির বায়োমঃ
১। এই অঞ্চল অতি উষ্ণ।
২। এখানে স্থায়ী অথবা সাময়িকভাবে প্রবাহিত জলাশয় অনুপস্থিত।
৩। এ অঞ্চলে বাতাসে আর্দ্রতা না থাকায় সূর্যরশ্মি মাটিতে পড়ে ফলে তাপমাত্রা অনেক উচ্চতায় পৌঁছায় ।
৪। মরুভুমির প্রাণীরা রাতে চলাচল করে ।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ কাঁটা ঝোপ, রসালো ক্যাকটাস, খেজুর, ইঁদুর, গিরগিট, র্যাটল সাপ প্রভৃতি।
গ. তৃণভূমির বায়োমঃ
১। এ বায়োমের বার্ষিক গড় বৃষ্ণিপাত ২৫-৭৫ সে.মি. ।
২। এখানকার মাটি হিউমাস সমৃদ্ধ হওয়ায় ঘাস জাতীয়
উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী ।
৩। ঘাসের পাতা খাড়া ও সুরু হওয়ায় প্রস্বেদন কম হয় ।
৪ । বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় মাটির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ ঘাস, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, গম, যব, রাই, জেব্রা, নেকড়ে, এন্টিলোপ, ঘাসফড়িং, মৌমাছি, চড়ুই, পেচা প্রভৃতি।
ঘ. পর্ণমোচী অরণ্যের বায়মঃ
১। শীতকালে বনাঞ্চলের উদ্ভিদের পাত ঝারে যায়। যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় ।
২। এ অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ,
৩। এ অঞ্চলের প্রাণীদের অনেকেই গর্তে বাস করে।
৪ । এখানে ঋতুচক্র উপস্থিত।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ পর্ণমোচী উদ্ভিদ (সাধারণত ম্যাপল ও এক) হরিণ, কাঠবিড়ালী, বনবিড়ালী, সাপ, উদ প্রভৃতি।
ঙ. সাভানা বায়োমঃ
১। এ অঞ্চলে দাবানল, ভূমিধঊমি রূপ প্রকৃতির।
২। এখানে উচ্চ তাপমাত্রা বিদ্যমান ।
৩। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ কম।
৪ । বছরে ১০০-১৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ ঘাস, গুল্ম ও জোপঝাড় জাতীয় উদ্ভিদ, বাবলা, তাল জাতীয় উদ্ভিদ, ক্যাঙ্গারু, হাতি, সিংহ, সাপ, উইপোকা প্রভৃতি।
চ. ক্রান্তীয় বা প্রপিক্যাল বায়োমঃ
১। এখানে বৃষ্টিপাত প্রায় সারা বছরই হয়।
২। এ ধরনের বনাঞ্চল ঘন চিরহরিৎ এবং নানা প্রকার বড় বড় বৃক্ষ সমৃদ্ধ।
৩। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে থাকে ।
৪। উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় বছরব্যাপী।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, পরজীবী উদ্ভিদ, চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষ, বানর, বিভিন্ন প্রকার পাখি, উভচর, কীটপতঙ্গ, ঝোঁক, শামুক, পিপীলিকা উইপোকা, বিছা প্রভৃতি।
ছ. তৈগা বায়োমঃ
১। উপমেরু দেশীয়, সংক্ষিপ্ত ও শীতল গ্রীষ্মকাল ।
২। দীর্ঘ ও অতিশীতল শীতকাল ।
৩। শীতকালে বরফপাত হয়।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ সরলবর্গীয় চিরহরিৎ বৃক্ষ (পাইন, ফার, স্পুস ইদ্যাদি), শিয়াল, ভালুক প্রভৃতি।
জ. চ্যাপারাল বায়োমঃ
১। শীতলকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত।
২। দীর্ঘ উত্তপ্ত বা শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ।
বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ কাটা ঝোপ, শক্ত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিরহরিৎ বৃক্ষ।
মহাদেশগুলোর অতীত ও বর্তমান অবস্থা এবং প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলঃ
বিভাজনবিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে কার্বোনিফেরাস যুগে (Carboniferous Period) পৃথিবীর মহাদেশগুলো মিলে প্যানগিয়া (Pangaea, গ্রীক Pan = সব + gaia = স্থলভাগ) নামক একটিমাত্র বিশাল ভূখন্ড ছিল । সে সময় উত্তর আমেরিকা ইউরেশিয়ার সাথে, দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকার সাথে এবং অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের অবস্থান ছিল আফ্রিকা ও অ্যান্টার্কটিকার মাঝে। এ সময় প্যানগিয়ার চতুদিকে প্যানথালাসা নামে একমাত্র সাগর ছিল। প্রায় ১৮ কোটি বছর পূর্বে ক্রিটেশাস যুগে (Cretaceous Period) সংযুক্ত প্যানগিয়া বিষুবরেখার কিছুটা উপরে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর উত্তর ও দক্ষিণে দুভাগে বিভক্ত হয়। উত্তরাংশের ভূখন্ডটি লরেসিয়া (Laurasia) এবং দক্ষিণাংশের ভূখন্ডটি গন্ডোয়ানাল্যান্ড (Gondwanaland) নামে আত্নপ্রকাশ করে। বিশাল টেথিস সাগর (Tethy Sca) ভূখন্ডদুটিকে পৃথক করে রেখেছিল। আজকের উত্তর আমেরিকা, গ্রিনল্যান্ড ও ইউরেশিয়া লরেসিয়ার মধ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অ্যান্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া গন্ডোয়ানার অন্তর্ভুক্ত ছিল । এভাবে (পৃথিবীর বৃহৎ ভূখন্ডগুলো ভেঙে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়াকে মহাদেশীয় সঞ্চারণ (Continental drift), বলে।
লরেসিয়া বিভক্ত হওয়ার আগেই গন্ডোয়ানাল্যান্ড খন্ডিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা থেকে দূরে সরে যাওয়ার মধ্যবর্তীস্থানে আটলান্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ আদি অবস্থান থেকে দ্রুত সরে গিয়ে এশিয়ার নিম্নভাগে ধাক্কা খেলে টেথিস সাগরের স্থানে হিমালয়ের উদ্ভভ ঘটে। টেথিস সাগরের অংশবিশেষ লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগরে মিশে আছে। পরবর্তিতে অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা থেকে বিভিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে, লরেসিয়া খন্ডিত হয়ে উত্তর আমেরিকা, গ্রীনল্যান্ড ও ইউরেশিয়ার জন্ম দেয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রায় ৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সবকটি মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং বর্তমান রূপ লাভ করেছে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে।
প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলঃ
ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রাণিদের নির্দিষ্ট সন্নিবেশে এমন কিছু প্রজাতি বাস করে যা ঐ অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব তাকে প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল (Zoogeographical Region) বলে।
১৮৫৭ সালে পি. এল. স্ক্লেটার (P. L. Sclater) সর্বপ্রথম পক্ষীকূলের ভৌগোলিক বিস্তৃতির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র পৃথিবীকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করেন। পরবর্তীতে ১৮৭৬ সালে এ. আর. ওয়ালেস (A. R. Wallace) পক্ষীকূলের সাথে প্রধান প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণিদের যুক্ত করে সামগ্রিক প্রাণী বিস্তৃতির আলোকে স্ক্লেটার প্রদত্ত অঞ্চল বিভাজনে সামান্য পরিবর্তন এনে ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল নিচের মতো করে ভাগ করেন।প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর নাম
১. প্যালিআর্কটিক অঞ্চল : ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বাদে)।
এন্ডেমিক ও উল্লেখযোগ্য প্রাণীঃচোষক মাছ, ব্ল্যাক ফিশ, প্যাডল ফিশ, জায়ান্ট সালামান্ডার, চাইনিজ অ্যালিগেটর, ও ম্যান্ডারিন হাঁস, সাদা পেলিক্যান এবং স্প্যালাক্স ও সেলেভিনিয়া নামক স্তন্যপায়ী।
২. নিআর্কটিক অঞ্চল : উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ, গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড।
এন্ডেমিক ও উল্লেখযোগ্য প্রাণীঃ চ্যাগা, পাঙ্গাস, উডুক্কু ব্যাঙ, ঘড়িয়াল, কুমীর, ব্লুবার্ড, শ্বেত কোকীতু, সবুজ বুলবুলি, গিবন, এবং লজ্জাবতী বানর, বনরুই, কালো ভালুক, কৃষ্ণষাঁড় ইত্যাদি।
৩. নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল : সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা এবং অধিকাংশ মধ্য আমেরিকা।
এন্ডেমিক ও উল্লেখযোগ্য প্রাণীঃ লেপিডোসাইরেন, অ্যারাপাইমা, অ্যানাকোন্ডা, জায়ান্ট টরটয়েজ, কালো কাইমান, বোয়া, রিয়া, টুকান, ম্যাকাউ, পিপরেভুক, গিনিপিগ, কাঁটাময় ইঁদুর ইত্যাদি।
৪. ইথিওপিয়ান অঞ্চল : সাহারার দক্ষিণমুখী আফ্রিকা এবং সংলগ্ন মাদাগাস্কার দ্বীপ।
এন্ডেমিক ও উল্লেখযোগ্য প্রাণীঃ এলিফ্যান্ট ফিশ, ল্যাং ফিশ, আফ্রিকান সি মাডস্কিপার, নখরযুক্ত ব্যাঙ, রেইনবো লিজার্ড, ডেসার্ট লিজার্ড, উটপাখি, সেক্রেটারি বার্ড, জলহস্তী, জিরাফ, গরিলা, সিংহ ইত্যাদি।
৫. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল : বৃটিশ ইণ্ডিয়া (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ), আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, ইন্দোচীন, তাইওয়ান (ফরমোজা), এবং ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ।
এন্ডেমিক ও উল্লেখযোগ্য প্রাণীঃ চ্যাগা, পাঙ্গাস, উডুক্কু ব্যাঙ, ঘড়িয়াল, কুমীর, ীন, ব্লুবার্ড, শ্বেত কোকীতু, সবুজ বুলবুলি, গিবন, এবং লজ্জাবতী বানর, বনরুই, কালো ভালুক, কৃষ্ণষাঁড় ইত্যাদি।
৬. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল : অস্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি এবং পূর্বাংশীয় দ্বীপগুলো।
এন্ডেমিক ও উল্লেখযোগ্য প্রাণীঃ লাং ফিশ, টুয়াটারা, ক্যাসোয়ারি, কিউই, ক্লাস ইমু, বার্ড অব প্যারাডাইস, প্লাটিপাস, শান্ত ক্যাঙ্গারু, অপোসোম, বান্ডিকুট, ওমব্যাট ইত্যাদি।
বাংলাদেশের বনাঞ্চল ( Forests of Bangladesh)
বাংলাদেশ ২০°৩০ থেকে ২৬°৪৫ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° থেকে ৯২°৫৬ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি জনবহুল ছোট্ট দেশ। এর আয়তন ১.৪৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা উচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চল কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগের মতো। বনের অনুযায় বাংরাদেশের বনকে নিম্নলিখিত উপায়ে ভাগ করা যেতে পারে।
১। চিরসবুজ ও উপ-চিরসবুজ বনাঞ্চল, ২। পত্রঝরা বনাঞ্চল এবং ৩ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ।
চিরসবুজ ও উপ-চিরসবুজ বনাঞ্চল (Evergreen and semi-evergreen forest): চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চিরসবুজ ও উপ-চিরসবুজ বন অবস্থিত।
(i) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২৫ সেমি (চট্টগ্রামে) থেকে ৫০০ সেমি (সিলেট), তাই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে।
(ii) মাটিতে হিউমাস অধিক, মাটি অ্যাসিডিক (অম্লীয়)।
(iii) বন অপেক্ষাকৃত ঘন।
(iv) ভূমিরূপ : ছোট ছোট পাহাড় ও মাঝে মাঝে খাদ।
(v) অধিকাংশ উদ্ভিদ চরিসবুজ প্রকৃতির।
সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে সিভিট (Swintona floribunda), গর্জন (Dipterocarpus turbinatus), চন্দু (Tetrameles undiflora), দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর (Mesua ferrea), বাটনা (Quercus spp.), পিতরাজ, (Amoora wallichiti) প্রধান। পত্রঝরা বৃক্ষের মধ্যে কড়ই ( Albizia procera), গামার ( Gmelina arborea), ভাদি (Lannea coromandelica), চাপালিশ (Artocarpus chama), উদাল, (Sterculia vilosa) ইত্যাদি প্রধান।পার্বত্য চট্টগ্রামের অনিক দুর্গম ও বিস্তর এলাকা নিয়ে বাঁশবন অবস্থিত। অধিকাংশ বাঁশই মূলী বাঁশ (Melocanna haccifera), জুম চাষের পর দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এলাকায় ছনবন আছে। ছন বনের প্রধান উদ্ভিদ হন Imperata cylindrica) এবং খাগড় (Saccharum spontaneum), সিলেটের উত্তরাংশে জলাবদ্ধ বন (Swamp forest) আছে। এ বনের উদ্ভিদ নল (Phragmitis karka), খাগড় (Saccharum spontaneum) এবং ইকড় (Erianthus ravennae) বৃক্ষের মধ্যে হিজল (Barringtonia acutangula) এবং করচ গাছ (Pongamia pinnata) প্রধান। বাংলাদেশের একমাত্র বন্য গোলাপ (Rosa involucrata) এখানে পাওয়া যায়।
পত্রঝরা বনাঞ্চল (Deciduous forest) : এ বন ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কুমিল্লার ময়নামতি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। ময়নামতির বন শালবন বিহার নামে, শেরপুর জেলার একটি বন রাংটিয়া বন, আরেকটি বন গজনী বন নামে পরিচিত।
i) শীতকালে এ বনের বৃক্ষরাজির পাতা ঝরে যায়।
ii) বার্ষিক বৃষ্টিপাত কম, ১২৫ (বরেন্দ্র অঞ্চলে) থেকে ১৭৫ সেমি (ঢাকা), তাই বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত কম। iii) মাটির বর্ণ লাল, মাটি বেশ অ্যাসিডিক, বর্ষায় কর্দমাক্ত ও শীতে শুকনো।
iv) বন তুলনামূলকভাবে কম ঘন, তবে মধুপুর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ঘন।
v) উঁচু 'চালা' এবং ফাঁকে ফাঁকে সমতলভূমি 'বাইদ' অবস্থিত। চালায় বন এবং বাইদে ধান চাষ হয় ।
এ বনের প্রধান বৃক্ষ শাল। শাল বৃক্ষের পরিমাণ কোনো কোনো স্থানে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পর্যন্ত। তাই এই বনের অপর নাম শালবন। বর্তমানে অধিকাংশ মূল শালবৃক্ষেই কর্তিত। মূল বৃক্ষের গোড়া থেকে গজানো চারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বন, তাই এ বনের আরেক নাম গজারী বন।
প্রধান বৃক্ষ শাল (Shorea orbusta) ছাড়াও চালতা (Dillenia pentagyna), কড়ই ( Albizia procera), গাছিগজারী (Miliusa velutina), কু (Careya aborea), বহেড়া (Terminalia bellirica), কুরচি (Holarrheana antidysenterica) ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে থাকে। শতমূলী (Asparagus racemosus), উলট চণ্ডাল (Gloriosa superba), এবং সর্পগন্ধা (Rouvolfia serpentina) তিনিটি বিপদাপন্ন ভেষজ উদ্ভিদ এ বনে দেখা যায়।
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest) : লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বনের বড় অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে বৃহত্তর তুলনা পাড় হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাছে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া মাতামুহুরী নদীর মোহনায় চকোরিয়া সুন্দরবন এবং নাশ নদীর তীরে কিছু ম্যানগ্রোভ বন দেখা যায় ।
সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য :
১. সুন্দরবনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে
২. মাটি-কর্দমাক্ত, ভেজা
৩. শ্বাসমূল / নিউমেটাফোর তৈরি হয়
৪. পাতার আয়তন কম থাকেদৈনিক দু'বার জোয়ার ভাটার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে
৫. মাটিতে মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে
৬. জরায়ুজ অংকুরোদগম হয়
৭. পত্ররন্ধের সংখ্যা কম থাকে।
৮. এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং এদের অভিস্রবনিক চাপ বেশি থাকে।
৯. উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট হয়।
এ বন চিরসবুজ বন।সুন্দরবনকে তিনটি Ecological Zone এ ভাগ করা যায়।
১। অলবণাক্ত অঞ্চল ২। অনধিক লবণাক্ত অঞ্চল ৩। লবণাক্ত অঞ্চল
১.লবণাক্ত পরিবেশে জন্মিতে পারে এধরনের উদ্ভিদকে বলা হয় লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (halophytes)
২. Mangrove plant এ বিশেষ এক প্রকারের মূল আছে যা, ভূগর্ভস্থ মূল থেকে গম্বুজের মত মাটির উপরে উঠে আসে। এ মূলগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত থাকে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এ জাতীয় উদ্ভিদের ভূ-গর্ভস্থ মূল শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়।
৩. এই মূলকে শ্বাসমূল (Breathing root) অথবা Pneumatophore বলে। মূলের অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে। ঠেসমূল Mangrove plant এর বৈশিষ্ট্য ।
৪. Viviparous germination এই অঞ্চলের বৃক্ষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, তবে সুন্দরী ও গেওয়াতে Viviparous germination হয় না, হারগোজাতে হয়।
সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেক্স সাইট (বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা) : সুন্দরবনের তিনটি বন্যজীব অভয়ারণ্য নিয়ে ওয়ার্ল্ডে হেরিটেজ সাইট গঠিত। এর আয়তন ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৯১০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি আর ৪৯০ বর্গ কিলোমিটার জলাভূমি। অসাধারণ প্রাকৃতিক মূল্যের কারণে UNESCO-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি ১৯৯৭ সালে তাদের ২১তম সেশনে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকার একে ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে।
জীববৈচিত্র্যঃ প্রচলিত অর্থে জীববৈচিত্র্য বলতে বোঝায় বৈচিত্র্যময় জীব অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব, এদের জিন সমষ্টি এবং এদের সৃষ্ট বাস্তুতন্ত্রকে।
বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদঃ
১. তালিপাম । বৈজ্ঞানিক নাম: Corypha taliera Roxb. গোত্র: Palmac = Arecaceae. তালিপাম একটি বড় মনোকার্দিক (monocarpic) উদ্ভিদ যা জীবনে একবারমাত্র ফুল ও ফল দিয়ে মরে যায়। এর কাও ১০ মিটার উঁচু, ব্যাস প্রায় ৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত (গোড়ার দিকে)। পাতা লম্বা বৃত্তযুক্ত (প্রায় ৬ মিটার লম্বা) পাতা প্রায় গোল, পুষ্পমঞ্জুরী ৬ মিটার বা তার চেয়েও বড়, দেখতে পিরামিডের মতো। বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত একটি তালিপামকে পৃথিবীর সর্বশেষ বন্য তালিপাম সদস্য বলে অভিহিত করে উদ্ভিদবিজ্ঞানিরা এ প্রজাতিকে ২০০১ সালে অতিবিপন্ন [Critically Endangered, (CR)] হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ গাছটি ২০১০ সালে ফুল ও ফল দিয়ে মারা গেছে। বীজগুলো থেকে চারা সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ উদ্যান ও মিরপুর জাতীয় উদ্যানে রোপন করা হয়েছে। ভারতে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া উদ্ভিদউদ্যানে একটি রোপিত গাছের বীজ ও চারা সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যে ফেরারচাইল্ড ট্রপিকাল গার্ডেনে পাঠানো হয়েছে। এভাবে Ex situ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে তালিপামের বংশধারা অব্যাহত রাখায় IUCN 2013.2 তালিপামকে Extinct in the Wild (EW) o অভিহিত করেছে
২. মালাক্কা ঝাঁজি বা পাতা ঝাঁজি। বৈজ্ঞানিক নাম : Aldrovanda vesiculosa Linn. গোত্র: Droscraceae. শিকড়হীন নিমজ্জিত, রসাল ও ভাসমান উদ্ভিদ। কতকগুলো স্বচ্ছ পাতাসহ একটি সরু কাও থাকে। কাণ্ডের চারদিকে ৮টি পাতা স্পোকের মতো সাজানো থাকে। উদ্ভিদটি ১০-৩০ সেন্টিমিটার (৪-১২ ইঞ্চি) লম্বা হয়। বসন্তকালে ছোট সাদা ফুল ফোটে। শিকার ধরার ফাঁদ থাকে পানির নিচে। পাতাগুলোই ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। পাতাগুলো ৬ মিলিমিটার লম্বা। এসব ফাঁদে প্ল্যাংকটনজাতীয় আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও প্রাণী শিকার করে। বাংলাদেশে মালাক্কা ঝাঁজি মাত্র দুটি জায়গায় পাওয়া যেত... একটি হচ্ছে ঢাকা, অন্যটি রাজশাহী। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এ উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হয় ঢাকার কাছাকাছি কোনো জলাভূমি থেকে। পরে রাজশাহীর চলনবিলের পরিষ্কার ও গভীর পানিতে প্রথমে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, সর্বশেষে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যায়। অবশ্য বিজ্ঞানী Cohn (১৮৫০) তাঁর এক নিবন্ধে এ ঝাঁজির প্রাপ্তিস্থান হিসেবে বাংলাদেশর নির্দিষ্ট এলাকার নাম উল্লেখ না করলেও অন্য বিজ্ঞানীদের ধারণা, সে জায়গাটি সম্ভবত চলনবিল-ই হবে। বিজ্ঞানিদের ধারণা, জলাবসতি ধ্বংসের কারণে পরিবেশ থেকে এ উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটেছে কিনা জোর অনুসন্ধান প্রয়োজন। বাংলাদেশের Red Data Book (2001) এ উদ্ভিদকে বিপন্ন [Endangered (EN)] বলে চিহ্নিত করেছে।
IUCN 2013.2-এর তালিকা অনুযায়ী এটি আগে ৪৩ দেশে পাওয়া যেত। এখন ২২টি দেশে এ উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ তালিকায় বাংলাদেশ থেকে এটি বিলুপ্ত [ Extinct (Ex)] বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
৩. ক্ষুদে বড়লা। বৈজ্ঞানিক নাম : Knema bengalensis de Wilde. গোত্র : Myristicaceae. এটি মাঝারি আকারের উদ্ভিদ। বাকল রেজিনযুক্ত ও সূক্ষ্ম দাগবাহী। নতুন শাখা-প্রশাখাগুলো রোমযুক্ত। বাংলাদেশের এন্ডেমিক উদ্ভিদ। ১৯৫৭ সালে কক্সবাজারের দুলাহাজরা থেকে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। এরপর ১৯৯৯ সালে আরেকটি গাছ পাওয়া গেছে কক্সবাজারের রিজু বনে। Red Data Book (2001) অনুযায়ী ক্ষুদে বড়লা শংকাকুল (Vulnerable (VU)] উদ্ভিদ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে আর এ উদ্ভিদ আছে কিনা সে বিষয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা শংকা প্রকাশ করেছেন। ক্ষুদে বড়লা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বসতি ধ্বংসকে দায়ী করেছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, যে জায়গা থেকে গাছটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে স্ত্রী গাছ খুঁজে বের করে বীজ সংরক্ষণ, কলম লাগানো, সে সঙ্গে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে নতুন গাছ সৃষ্টি করে গাছ সংরক্ষণে জরুরী এগিয়ে আসতে হবে।
৪. কোরুদ। বৈজ্ঞানিক নাম : Licuala peltata Roxb. গোত্র : Arecaceae. কোরুদ হচ্ছে চিরসবুজ দলবদ্ধ পাম। লম্বায় ২-৩ মিটার, কান্ড ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। পত্রবৃন্ত প্রায় ১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা, পত্রফলক প্রায় গোলাকার। সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মিশ্র বনে অর্দ্র ছায়াঢাকা স্থানে এ পাম জন্মায় । এ গাছের পাতা ঝাপি বা ছাতা বানিয়ে ব্যবহার করা হয়, এবং ঘর ছাওয়ার কাজেও ব্যবহৃত হয়। অতি আহরণ এবং বসতি ধ্বংসের ফলে কোরুদ গাছ বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের উদ্ভিদবিজ্ঞানিদের Red Data Book (2001)-এর তথ্য অনুযায়ী কোরুদ গাছ অন্যতম শংকাকুল [Vulnerable (VU)] গাছ হিসেবে পরিচিত। জ্যান্ত জার্মপ্লাজম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সাফারি পার্ক ও ইকোপার্কগুলোতে Ex situ conservation প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। IUCN এর Red List তালিকায় এ উদ্ভিদের নাম এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
৫. রোট্যালা। বৈজ্ঞানিক নাম : Rotala simpliciuscula Kochne. গোত্র: Lythraceae সরু, উভচর, বর্ষজীবী তৃণ। পাতা অতিক্ষুদ্র, ২.৫-৫.০ × ০.৫-২.২ মিলিমিটার আকারবিশিষ্ট। ধানক্ষেতের সিক্ত কিনারা বরাবর জন্মায়। এটি বাংলাদেশের এন্ডেমিক উদ্ভিদ। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে। আবিষ্কারের পর থেকে এ তৃণ অন্য কোথাও বর্ণিত হয়নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বসতি ধ্বংসের ফলে এ তৃণও হয়তো ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 1997 IUCN Red List of Threatened Plants-এ এউদ্ভিদটি শংকাকুল হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেও সাম্প্রতিকতম IUCN 2013.2 তে উদ্ভিদ তালিকাভুক্ত হয়নি।
বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীঃ
১. ঘড়িয়াল। বৈজ্ঞানিক নাম: Gavialis gangeticus Gmelin, 1789 লম্বাটে ও সরু ভুন্ডবিশিষ্ট কুমিরজাতীয় সরিসৃপ। উভয় চোয়াল সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে তুন্ডের সৃষ্টি করেছে। তুন্ডের অগ্রপ্রান্ত মোটা ও ভোঁতা (পুরুষ ঘড়িয়ালের তুন্ডের শীর্ষভাগ কলাসাকৃতির। এটাকে 'ঘট' বা 'ঘড়া' বলে। ঘড়া থেকে এর নাম হয়েছে ঘড়িয়াল। তুন্ডের প্রতিপাশে এক ডজনের বেশি ধারালোও চোখা দাঁত থাকে। লেজ সুগঠিত ও দুপাশে চাপা। এদের অগ্র ও পশ্চাৎদের আঙ্গুল আংশিক লিপ্তপাদ । ঘড়িয়াল শান্ত প্রকৃতির প্রাণী। বিরক্ত না করলে সারাদিন নদীর পাড়ে বালিতে রোদ পোহায়। মাছখেকো, ভাল সাঁতারু, ডাঙ্গায় ভাল হাটতে পারে না। কিন্তু শুকনো মৌসুমে (ফাল্গুন-চৈত্র) নদীর পানি কমে গেলে বালিতে গর্ত খুঁড়ে ৪০-৫০টি ডিম পাড়ে। প্রায় ৩ মাস পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। মাছ সমৃদ্ধ নদ-নদীতে বিশেষ করে পদ্মা ও যমুনা নদীর অংশবিশেষে এরা বিস্তৃত।
২. মিঠাপানির কুমির। বৈজ্ঞানিক নাম : Crocodylus palustris Lesson, 1768 খাটো ও চওড়া তুন্ডবিশিষ্ট, শত্রু চর্মে আবৃত, মাঝারি আকৃতির (৩-৪ মিটার লম্বা) কুমির। শিশু বয়সে তামাটে বা বাদামী রঙের এবং গাঢ় আড়াআড়ি ব্যান্ডযুক্ত। লেজে কালো ব্যান্ড থাকে। পরিণত কুমিরে ব্যান্ড অদৃশ্য হয়ে যায়, গায়ের রং হয় ধুসর থেকে বাদামী, তলদেশ সাদাটে বা হলদে। বুকে ও পেটে বর্ম থাকে না। লেজে দুসারি খাড়া আঁইশ উপর দিকে একীভূত হয়ে একটি একক সারি নির্মাণ করে শীর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে। তরুণ কুমির কাঁকড়া, চিংড়ি, বিভিন্ন পোকা, শামুক-ঝিনুক, ছোট মাছ ইত্যাদি, এমনকি নিজ প্রজাতির সদস্যকেও alis ধরে খায়। পরিণত বয়সে বড় বড় মাছ, উভচর, সরিসৃপ (প্রধানত সাপ ও কচ্ছপ), জলচর পাখি, পানির কাছে পাওয়া যায় এমন স্তন্যপায়ী (যেমন- বানর, হরিণ, মোষ) শিকার করে। ছয় বছরেই জননক্ষম হয়ে উঠে। শীতকাল হচ্ছে জনন ঋতু। বসতির ঢালু তীরে গর্ত খুঁড়ে ২৫-৩০টি ডিম পাড়ে, ওগুলো পাহাড়া দেয় এবং ডিম ফুটলে শাবকগুলোকে মুখে নিয়ে পানিতে ছাড়ে। কুমির মিঠাপানির নদী, হ্রদ ও জলাশয়ে বাস করে। মানুষের নির্মিত জলাধার, নালা ও পুকুর-দিঘীতেও বাস করে। কখনওবা উপকূলীয় মোহনায়ও পাওয়া যায়। পাঁচ মিটারের বেশি গভীর নয় এমন অগভীর জলাশয় এদের পছন্দ,স্রোতস্বীনি নদীও অপছন্দ ।
৩. রাজশকুন, বৈজ্ঞানিক নাম: Sarcogyps calvus Scopoli, 1786 মাথা, গলা, উরু ও পা হলদে-লাল। পালকের রং কালো, তাই দেখতে কালো। ঘাড়ের নিচে ও উরুর উপর দিকে সাদা দাগ। ওড়ার সময় ডানার নিচে সুস্পষ্ট সাদা ফোঁটা দেখা যায়। ঠোঁট কালচে-বাদামি, নিচের ঠোঁটের গোড়া হলদে এবং ঘাড়ে লাল ঝুলন্ত লতিকা । রাজশকুন লম্বায় ৮৪ সেন্টিমিটার (২.৭৫ ফুট)। এরা একা কিংবা জোড়ায় থাকে উঁচুগাছে। শান্ত স্বভাবের শকুন। প্রধান খাবার গলিত শব। খরকুটো, লতাপাতা দিয়ে ছোট মাচার মতো বাসা বানিয়ে ডিসেম্বর এপ্রিলের মধ্যে একটি মাত্র সাদা রংয়ের ডিম পাড়ে। এদের বসতি মানববসতির কাছাকাছি আম, বট প্রভৃতি গাছে এক সময় গলিত শবকে ঘিরে থাকা অন্য প্রজাতির শকুনের সঙ্গে একটি করে রাজশকুন দেখা যেত। এখন প্রায় বিলুপ্ত বলা যেতে পারে। মাঝে-মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বাইরে এ শকুন ভুটান, কম্বোডিয়া, চায়না, ইন্ডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে পাওয়া যায়। এদের সংকটের প্রধানতম কারণ হচ্ছে গবাদিপশুর রোগ নিরাময়ে ডাইক্রোফেনাক জাতীয় একটি ওষুধের প্রয়োগ । ওসব পশু যখন মারা যায় আর সেখানে যেখানে ফেলা হয় সেগুলো খেয়ে শকুন বন্ধীয় জটিলতায় ভুগে মারা যায়।
৪. নীল গাই। বৈজ্ঞানিক নাম : Boselaphus tragocamelus Pallas, 1766 নীলগাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় এশীয় অ্যান্টিলোপ। পুরুষ সদস্যের উচ্চতা সাধারণত ১৩০-১৪০ সে.মি. (৫২-৫৬ইঞ্চি), স্ত্রী নীলগাই আকারে একটু ছোট হয়। দেখতে অনেকটা বিদঘুটে চেহারার ঘোড়ার মতো। লেজের দিক কাঁধ থেকে উঁচু, কারণ সামনের পা পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বা; ঘাড়ে কুঁচির মতো গাঢ় লোম, লেজের ডগায় একগোছা চুল; পুরুষ সদস্যের গায়ের রং ধুসর, খুরের উপরের লোম সাদা এবং প্রত্যেক গালে চোখের নিচে ও পেছনে দুটি সাদা চোপ, ঠোঁট, খুঁতনি, কানের ভেতরের দিক ও লেজের নিচের তল সাদাটে; পুরুষেরই শুধু শিং হয়, শিং দুটি মসৃণ ছোট কোণাকার ও সামনের দিকে সামান্য বাঁকানো; শিংয়ের গোড়া ত্রিকোণা, ডগা বৃত্তাকার; এবং স্ত্রী নীলগাই ও বাচ্চা লালচে-বাদামী রংয়ের কিন্তু বয়স্ক পুরুষ প্রায় কালো। নীলগাই ছোট ছোট পাহাড়ে এবং ঝুপী জঙ্গলপূর্ণ মাঠে চরতে ভালবাসে, ঘন জঙ্গল এড়িয়ে চলে। গাছে ঢাকা উঁচু- নিচু সমতলে বা তৃণভূমিতে যেমনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে তেমনি আবার হুট করে শস্যক্ষেতে নেমে ব্যাপক ক্ষতি করতেও পটু। সকাল আর বিকেলে খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিনের বাকি সময়টা গাছের ছায়ায় বসে কাটায়। মহুয়া গাছের রসালো ফুল নীলগাইয়ের দারুণ পছন্দ। এ ফুল যখন ফোটে তখন আকৃষ্ট হয়ে আরও অনেক জন্তুই গাছের নিচে এসে হাজির হয় পানি ছাড়া নীলগাই দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়, এমনকি গরমের দিনেও ওরা নিয়মিত পানি খায় না। আত্মরক্ষার প্রধান উপায় হচ্ছে দৌড়ে পালানো। দ্রুতগামী ও শক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে না চড়ে নীলগাই ধরা প্রায় অসম্ভব। গন্ডারের মতো নীলগাই ও এক নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করে, উঁচু ঢিবি বানিয়ে ফেলে। এ অভ্যাসের ফলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সদস্যদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের পর্বটাও সম্পন্ন হয়। চার থেকে দশ সদস্যের দল নিয়ে নীলগাই ঘুরে বেড়ায়। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সবাই এক সঙ্গে থাকে।
৫. শুশুক। বৈজ্ঞানিক নাম : Platanista gangetica Roxburgh, 1801
পূর্ণবয়স্ক শুশুকের দেহের দৈর্ঘ্য ১.৫-২.৫ মিটার পর্যন্ত, ওজন প্রায় ৭০-৯০ কেজি। দেহের আকৃতি টর্পেডোর মতো। স্ত্রী ডলফিন আকারে পুরুষের চেয়ে বড়। গাঙ্গেয় শুশুক একটি লম্বা চঞ্চু, স্থূল শরীর, গোল পেট ও বড় স্লিপার বিশিষ্ট জলচর স্তন্যপায়ী। চোখে লেন্স নেই বলে একে অন্ধ শুশুকও বলে। চোখ দর্শন কাজের চেয়ে দিক নির্ণয়ের কাজে লাগে। গায়ের রং ধূসর বাদামী, তলদেশ কখনওবা গোলাপী রংয়ের। এদের বসতি মিঠা পানির নদী ও হ্রদ। বাংলাদেশের সমতল জুড়ে প্রবাহিত নদীতে যেমনি পাওয়া যায়, তেমনি চট্টগ্রামের মতো পাহাড়ি অঞ্চলের কর্ণফুলি ও হালদা নদীতেও পাওয়া যায়। ঘূর্ণি পানি, সাপিল নদী সবখানে এরা বাস করে। শুশুক বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সাঙ্গু, কর্ণফুলি, হালদা নদীর শাখা-প্রশাখায় পাওয়া যায় । বুড়িগঙ্গ নদীতে এক সময় অনেক ডলফিন ছিল। ধারণা করা হয়ে থাকে, সারা পৃথিবীতে এ প্রজাতির সদস্য সংখ্যা ৪০০০-৫০০০টি হতে পারে। বাংলাদেশ ছাড়াও ইন্ডিয়া, নেপাল ও পাকিস্তানে শুশুক বিস্তৃত ।
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনঃ
প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত আহরণ, পুনঃস্থাপন ও সুরক্ষাদানকে সংরক্ষণ বা কনজারভেশন বলে । যে পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাণিকূলের সুষ্ঠু ও আহরণযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করে তাদেরকে ধ্বংস অথবা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তখন সেই পদ্ধতিকে প্রাণিবৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Animal Diversity Conservation) বলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোই হটস্পট নামে পরিচিত। প্রধানত দুভাবে জীববৈচিত্রা সংরক্ষণ করা যায়, যথা -
১) স্বস্থানে সংরক্ষণ বা ইন-সিটু কনজারভেশন (In-situ Conservation) এবং
২) অন্যস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু কনজারভেশন (Ex- situ Conservation)
In situ Conservation:
কোনো প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তার নিজস্ব পরিবেশে সংরক্ষণ করাই হলো ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-situ Conservation)।
ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-situ Conservation)- এর বিস্তৃতি নিম্নরূপ-
i. জাতীয় উদ্যান : প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের সর্বাঙ্গীণ রক্ষার জন্য জীবজন্তু ও গাছপালার স্বাভাবিক নিবাসের বিশাল অঞ্চল সংরক্ষণ করা হলে তা জাতীয় উদ্যান বলে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় উদ্যান হলো- ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি।
ii. ইকোপার্ক : পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো প্রাকৃতিক এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সার্বিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ইকোলজিক্যাল পার্ককে সংক্ষেপে ইকোপার্ক বলে। যেমন- মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক, মধুটিলা ইকোপার্ক প্রভৃতি।
iii. সাফারি পার্ক : সাফারি পার্ক এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি। যেখানে বন্য প্রাণীরা ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত থাকে, মুক্তভাবে বিচরণ করে এবং প্রজননের সুযোগ পায়। যেমন— ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক।
iv. অভয়ারণ্য : যে সংরক্ষিত অঞ্চলে বুনো গাছ-পালার সাথে নির্দিষ্ট বিশেষ কিছু বন্য প্রজাতির প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে তা হলো অভয়ারণ্য।
v. গেম রিজার্ভ : এমন একটি প্রাকৃতিক সংরক্ষিত এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ফাঁদ দিয়ে বন্য প্রাণী ধরা বা মারা নিষিদ্ধ। যেমন- টেকনাফ গেম রিজার্ভ।
চলনবিল
কাংলার হাওড়
কক্সবাজার সৈকত
টাঙ্গুয়ার হাওড়
এক্স-সিটু সংরক্ষণ বা অন্যস্থানে সংরক্ষণঃ
Convention on Biological Diversity (CBD 2005)-র ব্য অনুযায়ী, এক্স-সিট সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে জীববৈচিত্র্যকে তাদের প্রাকৃতিক বসতির বাইরে রেখে সংরক্ষণ। সাধারণত কোনো জীবের আবাসস্থল বিপন্ন হলে অন্যস্থানে সরিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা বহুকাল ধরে চলে আসছে। অন্যস্থানে সংরক্ষণে কতগুলো সনাতন এবং বহুল পরিচিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন- উদ্ভিদ উদ্যান, চিড়িয়াখানা, জিন ব্যাংক, ইন ভিট্রো টিস্যু কালচার ইত্যাদি। এছাড়া যুগ যুগ ধরে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কিছু উদ্ভিদ অন্য স্থানে সংরক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণ ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশ্বের কুঞ্জবন, তুলসি গাছ ইত্যাদি।
অন্যস্থানে সংরক্ষণে দুধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করে করা হয়। যথা-প্রচলিত (conventional) পদ্ধতি এবং জীবপ্রযুক্তির আন্দোলে (biotechnological aspects) । নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো ।
জিন ব্যাংক : উদ্ভিদের জিনতত্ত্বের সম্পদ (genetic resources) গুলোকে সংরক্ষণের এবং পৃথিবীর বিশাল ভারাইটি এবং তাদের বন্য প্রজাতিগুলো সংরক্ষণের ও উৎপাদনে জিন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংরক্ষিত উদি নমুনাগুলোকে সময়ে সময়ে অন্যানো হয় এবং এ থেকে নতুন বীজ উৎপন্ন করে সংরক্ষণ করা হয়।
বীজ ব্যাংক : বিশেষ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন উদ্ভিদের জিন সম্পদকে অন্য স্থানে সংরক্ষণের জন্য বীজ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ পদ্ধতিতে বিরাট উদ্ভিদ জনগোষ্ঠির বীজকে নির্দিষ্ট অবস্থায় সংরক্ষণ করে প্রকৃতি থেকে তাদের হারিয়ে যাওয়া রোধ করে। কিউ-এর রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনে বীজ ব্যাংকের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে যারা ধন্য অবস্থায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ধানের অনেক ভ্যারাইটি যেমন- রাধুনী পাগল, রঘুসাপ, কিমা সাল ইত্যাদি কৃষকরা সংরক্ষণ করে আসছেন। এ ধরনের সংরক্ষণকে সম্প্রদায়গত বীজ ব্যাংক (community seed bank) বলা যেতে পারে।ব্যাংক পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি কিছু বিশ (recalcitrant) সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত তকে টিস্যু। সাহায্যে সংরক্ষণ করা যায় না। পদ্ধতি ত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। -(In-vitro conservation In vitro সংরক্ষণ বলতে কাঁচের বোতলে কে বোঝায়। প্রকৃত অর্থে এটি টিস্যু কালচার যে সব প্রজাতির বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায় অঙ্গজ জনন। বন সংরক্ষণে এটিই একমাত্র উপায়।
In-vitro সংরক্ষণের আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে হিম সংরক্ষণ বা ক্রায়োপ্রিজারভেশন (cryopreservation) ক্রিয়ায় প্রিজারভেশন প্রক্রিয়ায় জীবিত বস্তু যেমন, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভাজক টিস্যু, কোষের প্রোটোপ্লাস্ট, জ্য অথবা একটি হার কোষ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু, ডিম্বাণু, জগ ইত্যাদিকে দীর্ঘদিন অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও মজুদ রাখা হয়। সাধারণত তরল নাইট্রোজেনে খুব শীতল অবস্থায় (১৯৬° সেঃ) রেখে সংরক্ষিত জীবজ বস্তুর সকল জৈবনিক মুত্তিয়াও বিপাকীয় (metabolic) কর্মকান্ড নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। এতে সংরক্ষিত জীবজন্তু এতে বিনষ্ট না হয় সেদিকেও যথাযথ নজর রাখা হয়। কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়া এ প্রক্রিয়ার সংরক্ষিত জীব বস্তুতে নেরুজ্জীবিত করা হয়। বর্তমানে এটি বহুল প্রচলিত ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ পদ্ধতি।
বর্তমানে আমাদের দেশে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যোগ্রিজারভেশন পদ্ধতির উপযোগিতা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সিলভার কার্প, কমন কার্প, রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণে এ প্রক্রিয়ার উপযোগিতা দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মহিষের শুক্রাণু সংরক্ষণ সাফল্যের সাথে চলে আসছে। বিশ্বের বেশ কিছু দেশে বিপন্ন জীব এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে এমন সব প্রাণীর গ্যামেট ও জনকে ক্রায়োপ্রিজারভেশনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ ।
জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের সংরক্ষণ অনেক সময় বিভিন্ন আবহাওয়াগত কারণে কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রাকৃতিক প্রজনন বাঁধাগ্রস্থ হয় এবং এদের সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। এ অবস্থান টিস্যু কালচার, ক্লোনিং ইত্যাদি জীব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে পুনরায় পরিবেশে জন্মানো হয়। এভাবে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।
উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical Garden) উদ্ভিদ উদ্যান বলতে এমন রক্ষিত এলাকাকে বোঝায় যেখানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা হয় অথবা অন্য আবাসস্থল থেকে এনে শিক্ষা, গবেষণা, জিমপুল উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ব্যবস্থাপিত হয়। সব দেশেই জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ভিদ উদ্যান রয়েছে। পরিকল্পিত সংরক্ষণ ছাড়াও এসব উদ্যান বিনোদনেও অবদান রাখে। উদাহরণ-জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান (National Botanical Garden)।
উদ্ভিদ উদ্যানগুলো অন্যস্থানে সংরক্ষণের জন্য সব চেয়ে সহজ উপায়। এখানে সংরক্ষিত নমুনাগুলো স্বাচ্ছন্দে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং এদের পুনরায় বন্য অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়। FAO এবং World Information and Early Warning System (WIEWS)-এর ডাটাবেজ-এ দেখা যায় পৃথিবীর ১৫০টিরও বেশি দেশে ২০০০ এর উপর উদ্ভিদ উদ্যান আছে। যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রজাতি বন্য অবস্থায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলোর অনেক বংশধরদের অস্তিত্ব খ কেবল উদ্ভিদ উদ্যানেই পাওয়া যায়। আবার যে সব প্রজাতি বিলুপ্তির প্রান্ত সীমানায় এসে পৌঁছেছে তাদেরও স্থান মিলেছে এবং উদ্যানে। কিউ এবং রয়াল বোটানিকাল গার্ডেনে আজও এমন ২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ স্বাচ্ছন্দে বেঁচে আছে যা তাদের স্ব স্ব দেশের আবাসে 'রেড ডাটা বুক এ হুমকিরান্ত কিংবা বিপন্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
উদ্ভিদ উদ্যানের বিপন্ন উদ্ভিদ থেকে যে সব উদ্ভিদের শংকার কারণ সম্বন্ধে জানা যায়, কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়েও তথ্য পাওয়া যায়। এতে মানুষের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। বোটানিকাল গার্ডে উদ্ভিদদের সুপ্ত অবস্থার জন্য কারণ সমন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায় এখন থেকে। এতে করে মানুষের হওয়ার শিক্ষা নেয়। এখানে জনসাধারণ জানতে পারে কোন উদ্ভিদগুলো বিপন্ন ও সু পরে ইনবিল্লাহ উদ্ভিদের স্বাচ্ছন্দভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা তা নয় কারণ এখান থেকে মানুষ উদ্ভিদের প্রতি অনুরাগী চিত্র সংরক্ষণ সমন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।
Promotion