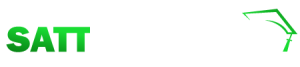পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে নাগরিকতা ও পৌরনীতির সম্পর্ক, নাগরিকতার ধারণা, সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের সাথে সরকার ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ধারণা ব্যবহার করে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নাগরিক জীবনে নানাবিধ সমস্যা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব ।
এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা -
• আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারব
• জনসংখ্যা সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব এবং সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব
• নিরক্ষরতার কারণ, প্রভাব ও সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারব
• খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সংকটের কারণ ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
• পরিবেশগত দুর্যোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারব • পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলার উপায় বর্ণনা করতে পারব
• সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উৎস, সমাজ জীবনে এর প্রভাব এবং তা নিরসনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
• নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারব
• নাগরিক সমস্যা সমাধানে নাগরিকের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারব ।
আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। শহর অথবা গ্রাম যেখানেই বসবাস করিনা কেন নাগরিক হিসেবে আমরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি নানারকম অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এছাড়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা পরিবার ও সমাজের সাথে যুক্ত থাকার ফলে কিছু পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যারও সম্মুখীন হয়ে থাকি । নাগরিক জীবনের এ ধরনের কিছু সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ।
১. জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার:
জনসংখ্যা সমস্যা কী ?
একটি দেশের সম্পদ ও কর্মসংস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে তখন জনসংখ্যা ঐ দেশের জন্য সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ, বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না । বর্তমানে জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে কোনো কোনো দেশের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সর্বত্র সব সমস্যার জন্য দায়ী নয় ৷
বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র:
জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৮ম এবং এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৫ম স্থানে অবস্থান করছে । এদেশের আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জায়গায় ১১০০ জন লোক বাস করে, যেখানে চীনে ১.৪ বিলিয়ন লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪০ জন লোক বাস করে আর ভারতে ১.২ বিলিয়ন লোকসংখ্যা সত্ত্বেও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৬২ জন বাস করে ।
২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭। অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। সীমিত সম্পদের কারণে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। শহরে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চাহিদা অনুযায়ী সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। গ্রামে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় সেখানকার বেকার মানুষ শহরে পাড়ি দিচ্ছে। এছাড়া আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমিতে এবং বনভূমি কেটে বসতি গড়ে উঠছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খাল-বিল, নদী-নালা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার মাধ্যমে এই সমস্যাকে সম্ভাবনায় পরিণত করছে । কিন্তু মোট জনসংখ্যার তুলনায় তা এখনো যথেষ্ট নয় ।
বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ:
১. জলবায়ুর প্রভাব : বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। তাই এদেশের জলবায়ু উষ্ণ। উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী হয় । ফলে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি ।
২. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ : বিবাহ আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধ ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে । বিশেষ করে অল্প আয়ের পরিবারগুলোতে এ প্রবণতা বেশি থাকে। এভাবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
৩. দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা : সাধারণভাবে সচেতনতার অভাব ও অধিকতর আয়ের প্রত্যাশায় দরিদ্র মানুষ অধিক সন্তান জন্মদান করে থাকে। এছাড়া কেউ কেউ মনে করেন যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তাঁরা একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করেন । ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ।
৪. শিক্ষার অভাব : শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতার কারণে ছেলেমেয়েদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা না করেই আমাদের দেশের মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে । ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
৫. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি : সামাজিক মর্যাদা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের জন্য বিয়ে একটি অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করা হয়। বিশেষভাবে কন্যা সন্তানের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে দ্রুত বিয়ে দেওয়ার প্রবনতা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। এতে করে জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ বাবা-মা ছেলেমেয়ে বড় হলে বিয়ে না দিলে কখন, কোথায়, কোন সামাজিক অপরাধ করে বসবে এই ভয়ে ভীত থাকে । এই ভয় এবং সমাজের চোখে হেয় হওয়ার আশঙ্কায় তারা দ্রুত ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে বিপদ এড়াতে চেষ্টা করে। এতে করে জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাচ্ছে ।
৬. সচেতনতার অভাব : ছোট পরিবার সুখী পরিবার-এরূপ সচেতনতার অভাব আমাদের দেশে বেশি। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাদির অভাব থাকায় এবং এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ:
দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে ।
১. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন : বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান একই রকম নয় । কাজেই যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করতে হবে । এতে জনগণের কর্মসংস্থান হবে আর জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যাবে ।
২. জনশক্তি রপ্তানি : দেশের যুব সমাজকে প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়বে ও বেকারত্ব দূর হবে । সরকার এ বিষয়ে ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ।
৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মানুষকে কাজ দিতে পারলে এবং অভাব থেকে মুক্ত করতে পারলে তারা নিজেরা আত্মসচেতন হবে এবং দায়দায়িত্ব বুঝতে পারবে ।
৪. শিক্ষার প্রসার : শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে । শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে । ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনে ।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদ, একই জমিতে একাধিক ফসল চাষাবাদ করতে হবে । কাঁচামাল তৈরি করে শিল্প গড়ে তুলতে হবে । কুটির শিল্পের তৈরি মালামাল দিয়ে বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে হবে । কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য যাতে ন্যায্যমূল্যে ও সহজে বিক্রি করা যায় তার জন্য বাজার এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। এসব করতে সক্ষম হলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে জনসম্পদে পরিণত হবে ।
৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা : উচ্চ জন্মহার রোধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ‘ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'–এই শ্লোগানকে কার্যকর করার জন্য সরকারকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে । পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে অধিক হারে মাঠকর্মী নিয়োগ করতে হবে । জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধপত্র সহজলভ্য করতে হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সেবা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে । তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ।
৭. জনসংখ্যানীতি গ্রহণ : ১৯৭৬ সালের জনসংখ্যানীতিকে আরও সংস্কার করে ২০০৪ সালে সরকার নতুন জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে । এই নীতির আওতায় সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে । এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করে দেশে প্রজনন হার হ্রাস করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করা। পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য, উপদেশ ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা; গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জন্মনিয়ন্ত্রণের সুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা; নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়তা করা। মেয়েদের ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছরের পূর্বে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। জনসংখ্যানীতির এসব দিক বাস্তবায়ন করতে হবে।
৮. সুবিধাবঞ্চিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণ : বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান উন্নত করতে হবে এবং গরিব ও দুস্থদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একসাথে কাজ করতে হবে ।
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়:
বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সচেতন নাগরিক হিসেবে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা সকলের নাগরিক দায়িত্ব । প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারি এবং অন্যকেও সচেতন করতে পারি । দ্বিতীয়ত, আমাদের বা প্রতিবেশী পরিবারে কোনো নিরক্ষর শিশু বা ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আমরা শিক্ষার সুযোগ দিয়ে উৎসাহিত করতে পারি, যাতে সে জনসম্পদ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা শুধু পরিবার নয় রাষ্ট্রের ও জাতির জন্যও বোঝা । তবে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে তা জাতির জন্য সম্পদে পরিণত হবে।
২. নিরক্ষরতা:
নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসেনা বরং সমাজের বোঝা স্বরূপ । নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই। সরকারের প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন' (Total Literacy Movement) শুরু করে । সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশি । এর অন্যতম কারণ তাদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। দরিদ্র শ্রেণির সন্তানেরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারে না । অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী টাকার অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না । এর মধ্যেও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, বেসরকারি ব্যাংক এবং সংস্থা অর্থ সাহায্য দিয়ে দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে অবদান রাখছে ।
নিরক্ষরতা দূরীকরণ : সরকার ও নাগরিকের করণীয়:
নিরক্ষর জনসমষ্টিকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা সরকারের পক্ষে একা সম্ভব নয় । শিক্ষিত সকল মানুষকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। আর যারা নিরক্ষর, তাদের নিজেদেরকেও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হতে হবে। সকলে সম্মিলিতভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে ।
দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য সরকার ও নাগরিকদের যেসব কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, সেগুলো আলোচনা করা হলো ।
১. তথ্য সংগ্ৰহ: নিরক্ষর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকা ও অবস্থানভেদে প্রচলিত পেশার সমস্যা ও সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে । সরকার প্রকল্প গ্রহণ ও টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে । সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে ।
২. বয়স্ক শিক্ষা: গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাদানে সরকারকে বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও) নিয়োজিত করতে হবে । এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত বেকারদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে ।
৩. কর্মমুখী শিক্ষা: সাধারণভাবে নিরক্ষর বয়স্করা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় আগ্রহী হয় না, তাদেরকে তাদের পেশার সাথে সংযুক্ত করে কর্মমুখী শিক্ষার আওতায় আনতে পারলে তারা তাদের অর্জিত শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান সহজে ভুলবে না ।
৪. শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালুকরণ: নিরক্ষরদের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নয়, তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে । এরূপ ঋণ, অনুদান, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষিত ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে । জনগণ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বদান্যতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ।
৫. নাগরিকদের অংশগ্রহণ: নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে সর্বস্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন কাজ করছে। যেমন— আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, ইউসেপ ইত্যাদি । সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতির শক্ত ভিত রচিত হবে। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত হবে ।
নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের বাসায় কেউ নিরক্ষর থেকে থাকলে তাকে অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি । অথবা বন্ধুদের সাথে মিলে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ক্লাব গড়ে তুলতে পারি । আমরা দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি । নাগরিক হিসেবে আমাদের এই কাজ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।
৩. খাদ্যনিরাপত্তা:
খাদ্যনিরাপত্তা কী?
খাদ্যনিরাপত্তা বলতে খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি—এই তিনটি বিষয়কে বোঝানো হয়। অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যে যেহেতু খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চাউলের প্রাধান্য রয়েছে, সেহেতু চাউলের সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতাই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের মূল বিষয় । বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী খাদ্যভিত্তিক দারিদ্র্যের শিকার। মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২,১২২ কিলোক্যালরি গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত খাবার কেনার সামর্থ্য তাদের নেই । খাদ্যে ক্যালরি ঘাটতি ছাড়াও এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য সুষম নয় । তাদের প্রতি বেলার খাদ্যেই শস্যের প্রাধান্য রয়েছে । তারা প্রতিদিন যে ক্যালরি গ্রহণ করে, তার ৮০ শতাংশই আসে শস্য হতে, যার মধ্যে চাউলই প্রধান । চর্বি, তেল এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য তারা সামান্যই গ্রহণ করে । এই ধরনের সমতাহীন খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বিশেষভাবে শিশুদের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।
খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার কারণ:
১. কম খাদ্য উৎপাদন : জনসংখ্যার তুলনায় দেশে ফল, ডাল, তৈলবীজ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন কম। অন্যদিকে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার স্বল্পতার কারণে দেখা দেয় খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা ।
২. জনগণের কম আয় : আমাদের দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বিশ্বের বেশিভাগ দেশের তুলনায় কম । জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে তাদের পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য কেনা সম্ভব হয় না । ফলে দেখা দেয় খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা ।
৩. পুষ্টি জ্ঞানের অভাব : জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে পুষ্টি জ্ঞানের অভাব রয়েছে । আর এই জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা সঠিক স্বাস্থ্য উপযোগী খাদ্য বেছে নিতে পারে না ।
বর্তমানে সরকার দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানি করছে। এছাড়া সরকার স্বল্পমূল্যে দরিদ্র লোকজনের খাদ্য ক্রয় করার সুযোগ প্রদান করে থাকে। বিশেষভাবে দুর্যোগের সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। তবে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না ।
খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের উপায়:
খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে দরকার হয় একটি সঠিক খাদ্যনীতি। দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা বিধানই বাংলাদেশের খাদ্যনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । সরকার কর্তৃক শস্য মজুদ জরুরি অবস্থায় খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সরবরাহকে নিশ্চিত রাখে । প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে খাদ্যঘাটতি দেখা দিলে দরিদ্র শ্রেণি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর এই সংকট মোকাবেলায় সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট ব্যয়ের ৯৫ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে। এর মধ্যে রয়েছে ত্রাণ প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয় উপার্জনকারী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন। সরকারের খাদ্য সাহায্য কর্মসূচিগুলোর মধ্যে Vulnerable Group Development (VGD), Food For Education 4 Vulnerable Group Feeding (VGF) –এই তিনটি কর্মসূচি অন্যতম।
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার কাঠামো ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। কারণ কৃষকগণ যদি খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে সহায়তা না পায় তবে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষককে সহজ শর্তে ঋণ দিলে কৃষক এই ঋণ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।
এছাড়া খাদ্যে ভেজাল খাদ্যের নিরাপত্তার একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। মানবস্বাস্থ্যের জন্যও তা মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রচলিত আইন ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনবোধে আইন সংস্কার করে ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে ।
খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়:
২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত ৪৪ শতাংশ মানুষ । ২০০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে। এই হতদরিদ্র মানুষ খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে না । নাগরিক হিসেবে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের জন্য আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জেনে তা নিশ্চিত করতে নিজেরা উদ্যোগ নিতে পারি। বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় আমরা নানা রকম শস্য চাষ করে শস্যের চাহিদা মেটাতে পারি । ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি ।
৪. পরিবেশগত দুর্যোগ:
আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, মাটি এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ । সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি । মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয় ।
পরিবেশগত দুর্যোগের কারণ:
পরিবেশকে ঘিরেই মানুষ বেড়ে উঠে। আবার মানুষের কারণে কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিয়তই পরিবেশ দূষিত হয় । শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে একের পর এক গাছ-পালা কেটে, বন উজাড় করে মানুষ শিল্প-কারখানা গড়ে তুলেছে । এর ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : মাটি, বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে । নগরের শিল্প-কারখানাগুলো জলাধারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নর্দমার পানিতে ফেলায় তা নদীতে মিশে পানি দূষিত করছে । এছাড়া জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলেও পানি দূষিত হচ্ছে । দূষণের কারণে এখন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত । শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদও ক্রমেই একই পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে । ঢাকার বাইরে নদ-নদীগুলোর অবস্থাও একই রকম। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী মারাত্মক দূষণের শিকার । মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত সিমেন্ট কারখানাগুলোর দূষণে সে এলাকার পানি, জমি ও বায়ু বিষাক্ত হয়ে পড়েছে ।
পরিবেশ বিপর্যয়ের আরেক দৃষ্টান্ত হলো বনাঞ্চল হ্রাস ও এর অবক্ষয় । যেমন : ইটের ভাটার জ্বালানি হিসেবে, বাসাবাড়ির রন্ধন কাজে জ্বালানি হিসেবে, ভবন নির্মাণ ও ঘরের জানালা-দরজার জন্য এবং আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যাপক হারে কাঠের ব্যবহার হচ্ছে । একটি দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বন থাকা প্রয়োজন । অথচ আমাদের দেশের মোট আয়তনের ১৭ শতাংশ রয়েছে।
ক্ষতিকর দিক:
বনের সংকোচন, জলাধারগুলোর অধিগ্রহণ ও দূষণের ফলে দেশের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে । দেশীয় প্রজাতির শস্য, মাছ, গাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতি আজ সর্বাত্মক হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ আন্দোলনের চাপে সরকার পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও তা প্রায়ই মানা হচ্ছে না। তদুপরি বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে । ফলে শহরে, এমনকি গ্রামে বর্জ্য হিসেবে প্লাস্টিক ও জৈবিকভাবে অপচনশীল অন্যান্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ছে। মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চিকিৎসাবর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত হারে বাড়ছে এবং এর মধ্যে অনেক বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে যাচ্ছে । পৃথক ও সুষ্ঠু অপসারণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে এসব বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং পরিবেশকে বিষাক্ত করছে ।
এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে আক্রান্ত করছে এবং করবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে লবণাক্ততার প্রসার, নদীপ্রবাহের চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি ও রোগ মহামারীর প্রসার । ঘনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। সে কারণে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনই বাংলাদেশের জন্য আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সবাইকে সমষ্টিগতভাবে সচেতন হতে হবে ।
পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ:
বস্তুত, বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি । বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে । ভয়াবহ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।
১. অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা ।
২. মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া ।
৩. যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা ।
৪. শিল্প-শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।
৫. যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলা ।
৬. বনায়ন বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করা ।
৭. ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বৃক্ষরোপণ আন্দোলন জোরদার করা ।
৮. পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করা ।
৯. পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এ সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা ।
১০. প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা ।
১১. ইটের ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া ।
১২. স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, যাতে তারা পরিবেশের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকে ।
১৩. অধিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা ।
১৪. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও অংশগ্রহণে রাজি করানো ।
১৫. ক্ষতিকারক উপাদানগুলোর পরিমাপ করার জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়:
নাগরিক হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে । আমাদের উচিত অন্যায়ভাবে কোনো গাছ না কাটা, পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের আঙিনাসহ বাড়ি ও রাস্তার আশে-পাশে গাছ লাগানো, ক্ষতিকর পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার না করা, আশপাশের ড্রেনে বর্জ্য না ফেলা এবং নিজেরা সংগঠিত হয়ে সমাজের মানুষকে পরিবেশদূষণের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা ।
৫. সন্ত্রাস
সন্ত্রাস কী?
সন্ত্রাসের মূল কথা হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্যসাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা । এটা যেমন দৃষ্কৃতকারীরা বা সমাজবিরোধীরা করতে পারে, তেমনি সমগ্র রাষ্ট্রে তথা সমগ্ৰ বিশ্বের পটভূমিতেও এমন চেষ্টা হতে পারে। সন্ত্রাস সমাজে যুগ যুগ ধরে চলছে। সন্ত্রাসের প্রধান উৎসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।
♦ কোনো লক্ষ্য অর্জনে সহিংস কর্মপন্থা গ্রহণ।
♦ বঞ্চিত শ্রেণির মানবাধিকার রক্ষার নামে সহিংস এবং অন্যান্য চরমপন্থী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ।
♦ সহিংসতার লক্ষ্যে নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ।
♦ অধিকার আদায়ে আইনগত বিধান ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় থাকা সত্ত্বেও সহিংস কর্মপন্থা ব্যবহার করা ।
সন্ত্রাসের ধরন:
অপরাধী চক্রের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাস:
অপরাধী চক্র সংগঠিতভাবে সন্ত্রাস চালায় । এদের এক শীর্ষ নেতা থাকে, যে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নিজের নিয়োজিত লোক দ্বারা ভীতি প্রদর্শন, চাঁদাবাজি, খুন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড করে থাকে। এরা নানাভাবে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।
রাজনৈতিক সন্ত্রাস:
কোনো কোনো রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা গোষ্ঠীবিশেষ রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। ধর্মের নামেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে দেখা যায়। শ্রেণি-সংগ্রামের নামেও কোনো কোনো দল বা সংগঠন সহিংস তৎপরতায় লিপ্ত হয়। কখনো কখনো রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে দেখা যায় ।
আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস:
কোনো গোষ্ঠী তাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে পারে । একসময় শ্রেণি- শত্রু খতমের নামে আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো সহিংস পন্থায় সাধারণ মানুষ হত্যা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করে থাকে ।
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস:
অনেক সময় রাষ্ট্র নানা অজুহাতে সন্ত্রাসী পন্থা অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীর উপর দমন-পীড়ন চালায় । এরূপ অবস্থা হলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস । যেমন : ইসরাইল রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর বিভিন্ন সময় এ ধরনের তৎপরতা চালিয়ে আসছে । রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সংখ্যালঘু বা ভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপরও এরূপ আক্রমণ পরিচালিত হতে দেখা যায় ।
সন্ত্রাসের কারণ: সন্ত্রাস দুটি কারণে সংঘটিত হয়, ক) সাধারণ কারণ, খ) বহিঃস্থ কারণ ।
ক) সাধারণ কারণ :
১. অর্থনৈতিক বৈষম্য: কোনো সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন থাকলে একশ্রেণির লোক অধিক ধনী হয় এবং অন্য শ্রেণি অধিকতর দরিদ্র হয় । এ অবস্থা বঞ্চিতদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এছাড়া বেকারত্ব আমাদের দেশে একটি সামাজিক ব্যাধি । যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজের কর্মক্ষম যুবসমাজের উপর। এর ফলে যুবসমাজ অনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য নির্মাণে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ হয় ।
২. সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি: একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি রাজনীতি হয় ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার, তাহলে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাসের জন্ম অস্বাভাবিক নয় । কারণ, ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের জন্যই সন্ত্রাসীদেরকে লালন-পালন করতে হয় ।
৩. সুশাসনের অভাব: অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের দায়িত্ব । কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে প্রশাসন অনেক সময় নীরব ভূমিকা পালন করে । এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। যেমন : দুর্বল প্রশিক্ষণ, পুরনো অস্ত্র, পুলিশ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যহীন অনুপাত ও আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জামের স্বল্পতা সন্ত্রাস দমনে আইন- প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাকে দুর্বল করে। এসব কারণে অনেক দুর্বল সন্ত্রাসীরাও শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হয় । তাছাড়া উন্নত প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে অনেক সময় বিদ্যমান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দ্বারা সমকালীন সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না ।
খ) বহিঃস্থ কারণ:
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যেমন অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ কাজ করে, তেমনি এর পিছনে বাইরের প্রভাবও থাকতে পারে । অবৈধ অস্ত্রের যোগান, অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে কাজ করে বলে ধারণা করা হয় ।
সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়
বাংলাদেশে সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে । সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সে জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক ।
১. সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ : সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। রাজনৈতিক বা অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে সংঘটিত সন্ত্রাস দমনের জন্য চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কমে আসবে।
২. পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন : সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে ও যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে হবে এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এখানে প্রায় ৮০০ মানুষের জন্য একজন পুলিশ সদস্য। এ অবস্থার নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিশের সংখ্যা, পুলিশ ফাঁড়ি, থানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।
৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকার ভাতা প্রদান: দেশে কুটির শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। বেকারত্ব দূরীকরণ সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর দেশের মতো না হলেও ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার মতো বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার । সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকার ভাতা উত্তম ব্যবস্থা ।
৪. সর্বজনীন শিক্ষা ও মূল্যবোধের জাগরণ : সবার জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় । এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে ।
৫. রাজনৈতিক দলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেওয়া : রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না । কোনো দল সন্ত্রাসীদের মদদ দিলে বা আশ্রয় দিলে সে দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে । এমন দলের কোনো সদস্যকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না, এ মর্মে সংসদে আইন তৈরি করতে পারে ।
৬. প্রশাসনিক কঠোরতা : সন্ত্রাস দমন, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন যাতে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে ।
৭. গণসচেতনতা : জনগণের সচেতন প্রতিরোধ সন্ত্রাস দমনে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবদ্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে ।
নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়:
নাগরিক হিসেবে আমরা সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন থাকব। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কেও আমরা জানব । সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করব । সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলব ।
৬. নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার
নারী নির্যাতন কী?
বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী, নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া, কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। নিচে নারী নির্যাতনের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, যাতে আমাদের দেশের নারী নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে ।
কন্যাশিশুদের উপেক্ষা:
ঘটনা ১: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে পড়ে মীনা । শৈশব থেকেই সে ছিল খুব মেধাবী । তার এক বছরের বড় ভাই তারই সাথে এক ক্লাসে পড়ত । এইচএসসি পাস করার পর মীনা সিলেট মেডিকেল কলেজ ও তার ভাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল । মীনার বাবা তার ছেলেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করালেও মীনাকে খরচের অজুহাত দেখিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। পারিবারিক বঞ্চনার কারণে মীনার ডাক্তার হওয়ার আজন্ম লালিত স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে ।
যৌতুক:
ঘটনা ২: নবম শ্রেণির ছাত্রী মর্জিনা গ্রামে বসবাস করে। মর্জিনার বাবা পৈতৃক জমি থেকে যে ফসল পায় তা দিয়ে কোনোভাবে পরিবারের খরচ মেটায় । চার ভাইবোনের পরিবারে মর্জিনা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তার বাবা তাকে এক মুদি দোকানদারের সাথে বিয়ে দেয়। কিন্তু তার স্বামী মন দিয়ে দোকানদারি করে না বলে দোকানে লোকসান হতে থাকে । বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মর্জিনার স্বামী তাকে তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য বলতে থাকে। বছর দুই পরে সে বিদেশে যাবে বলে মর্জিনাকে বাবার বাড়ি থেকে জমি বেচে দুই লক্ষ টাকা এনে দেওয়ার জন্য চাপ দেয় । তার শ্বশুরবাড়ির সবাই স্বামীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে টাকা নিয়ে আসার জন্য বলতে থাকে । এ নিয়ে প্রায়ই স্বামীর বাড়ির লোকের সঙ্গে মর্জিনার বিরোধ চলতে থাকে । এরপর হঠাৎ একদিন মর্জিনাকে তার শোবার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ।
বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ:
নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে । এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীকে মনে করে অবলা অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম । ফলে নারীর স্থান হচ্ছে সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে । একই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে অবহেলা করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদের অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে নারীরা এখনও অবহেলিত ও নির্যাতিত ।
১. অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব:
অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা নারীর অবস্থানকে সমাজে ও পরিবারে শক্ত করে । কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী এখনো স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল । ফলে, সংসারের কোনো কেনাকাটা, খরচ করা বা শখ পূরণের জন্য নারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের বাবা, ভাই ও স্বামীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হয়। এখনও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাবে অনেক নারী নির্যাতনের শিকার হয় ।
২. সচেতনতার অভাব:
আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র । দরিদ্র পরিবারে নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত । ফলে সে তার অধিকার সম্পর্কে থাকে অসচেতন। আর এই সুযোগে স্বামী, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমাজ নারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে থাকে ।
নারী নির্যাতন রোধে করণীয়:
সমাজে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন রোধ করা অত্যাবশ্যক। নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের মাধ্যমে তা সম্ভব । এজন্য নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । এছাড়াও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিচের পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ ।
১. আইনের কঠোর প্রয়োগ : নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার । আইনের মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তবে তা সংশোধন করে আইনকে আরও শক্তিশালী করা সরকারের গুরুদায়িত্ব। নারী নির্যাতনকারীদের যথাযথভাবে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
২. সচেতনতা বৃদ্ধি : পরিবার, স্কুল ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনে নারী নির্যাতন বিরোধী বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নাটক, কবিতা, আবৃত্তি, গান, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী নির্যাতনকারীর শাস্তি ও পরিণতি তুলে ধরতে হবে । এটা যে একটা ঘৃণ্যতম অপরাধ এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় তা বুঝতে হবে। নারী পুরুষ
সকলে মিলে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে ।
৩. আইনি সহায়তা : অনেক ক্ষেত্রে নারীরা আদালতে নির্যাতনের সঠিক বিচার পায়না। বিশেষ করে দরিদ্র নারীরা অর্থের অভাবে আদালতে যেতে পারে না । তাই এ ধরনের নারীদের জন্য রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আইনী সহায়তা দিতে এগিয়ে আসতে হবে ।
Read more