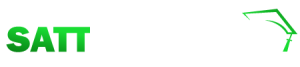নানান রঙের শতরঞ্জি
হরেক রকম গান।
লোকশিল্প, লোকনৃত্য
তিস্তাপারের প্রাণ।
অবশেষে চলে এলো সে প্রতীক্ষিত কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমণের দিন। শীতের কুয়াশার চাদর সরিয়ে ভোরের রাঙা সূর্যটা উকি দিচ্ছে পুব আকাশে। সবাইকে সুপ্রভাত জানিয়ে অবনী দেখে নিল সবাই প্রয়োজনীয় সব কিছু ঠিকমতো নিয়েছে কিনা। আকাশ ভ্রমণ নির্দেশনা সম্বলিত একটি ম্যাপ বের করল। এর মধ্যে শামস মামা একটা ভ্যান নিয়ে উপস্থিত হলো। মামা সবার উদ্দেশ্যে বলল ভারসাম্য (balance) ঠিক রেখে ভ্যানে বসে পড়। মামা দেখতে পেল ভারসাম্য ঠিক হয়নি। একপাশে চারজন অন্য পাশে দুজন হয়েছে। তিনি বললেন ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য অনুপাত (proportion) সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। আকাশ বলল মামা ভারসাম্য ও অনুপাতের বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলো। মামা বলল সমীর, অবনী আর আকাশ ভ্যানের ডান পাশে বসো। আমি, ইরা আর আগুন বাম পাশে বসি তারপর তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। অনুপাত মানে হলো তুলনা, একই রকমের দুটি রাশির বা বস্তুর মধ্যে তুলনাকে অনুপাত বলে। উপাদানের সঠিক ও সমান অনুপাতকে ভারসাম্য বলে। মামা বলল এবার তোমাদের একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা দিই।
এই ভ্যানটা তিন চাকার যান, এর ডান এবং বাম পাশে দুটি এবং সামনে একটি চাকা আছে। সামনের চাকাটি দিক নির্দেশনা ঠিক রাখে আর পেছনের চাকাগুলো মূল ওজন বহন করে। ফলে উভয় ঢাকার উপর সমান অনুপাতের ওজন হওয়া জরুরি। তাই আমরা মোটামুটি সমান সাইজ ও ওজনের তিনজন করে উভয় দিকে বসলাম তাতে ভারসাম্য ঠিক হলো। এবার ভ্যানটি চালাতে সুবিধা হবে।
এই বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও অনুপাত ও ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছবি আঁকায় অনুপাত হলো ছবিতে ব্যবহৃত আকার-আকৃতি, রং, পরিসর, বুনটসহ ইত্যাদি উপাদানের মধ্যকার তুলনা। এই সকল উপাদানের সমান ও সঠিক ব্যবহারকে বলে ছবি আঁকার ভারসাম্য।
ছবি আঁকায় দু'ধরনের ভারসাম্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। যেমন- প্রতিসম ভারসাম্য (symmetrical balance) ও অপ্রতিসম ভারসাম্য (asymmetrical balance)।
প্রতিসম ভারসাম্য
যার উভয় দিকের অনুপাত সমান।
প্রতিসম ভারসাম্য
অপ্রতিসম ভারসাম্য
যার উভয় দিকের অনুপাত সমান থাকে না। ভারসাম্য সম্পর্কে আমরা পরে আরও জানব।
অপ্রতিসম ভারসাম্য
নকশার ক্ষেত্রে প্রতিসম ভারসাম্য আর চিত্র রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিসম ভারসাম্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।
মামা বলল তবে চল তোমাদেরকে এঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।
এই সকল আলোচনা করতে করতে ভ্যানটি বাস স্টেশনে এসে থামল। তাদের এবারের গন্তব্য পঞ্চগড় হয়ে রংপুর।
রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড় এই ৮টি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ গঠিত। তিস্তা এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদী। শতরঞ্জি, ভাওয়াইয়া গান আর সাঁওতাল নাচ এই বিভাগের লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।
এর মধ্যে বাস রংপুর এসে পৌঁছাল। বাস থেকে নেমে মামা এক ব্যক্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাত মেলাল। তিনি বাস স্টেশনে আমাদের সবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মামা সবাইকে জানালেন ইনি আমার বন্ধু রাইসুল ইসলাম। সবাই রাইসুল মামাকে সালাম আর অভিবাদন জানাল। শামস মামা বললেন আমরা একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি পড়েছি চারুকলা বিভাগে আর রাইসুল পড়েছে সংগীত বিভাগে। দুটি আলাদা বিভাগের ছাত্র হলেও আমরা সবসময় একসাথে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখতাম। এর মধ্যে রাইসুল মামা বললেন তোমরা নিশ্চয়ই পঞ্চরত্ন। তোমাদের কথা আমি শামসের কাছ থেকে শুনেছি। এখন প্রথমে সবাই আমাদের বাড়িতে যাব সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে যাব নিসবেতগঞ্জ বা শতরঞ্জি গ্রামে।
দুপুরের খাবার টেবিলে রাইসুল মামা বললেন আজকে তোমাদের রংপুরের তিনটি ঐতিহ্যবাহী খাবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথমটি হলো পাটশাক ও খাবার সোডা দিয়ে রান্না করা 'শোলকা', দ্বিতীয়টি হলো নাপা শাক দিয়ে রান্না করা 'প্যালকা', আর শেষেরটি হলো ছোট মাছের শুকনো শুঁটকি আর কচুর ডাটা দিয়ে তৈরি 'সিদল'। গরম ভাতের সাথে এই তিন ঐতিহ্যবাহী খাবার খেয়ে পঞ্চরত্র অভিভূত হয়ে গেল। খাবারের ফাঁকে শামস মামা বললেন ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় খাবার হলো নিজস্ব সংস্কৃতির রূপ। এসব ঐতিহ্যবাহী খাবার না খেলে স্থানীয় সংস্কৃতিকে জানাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
খাবার শেষে রাইসুল মামার নেতৃত্বে সবাই বেরিয়ে পড়ল শতরঞ্জি গ্রামের উদ্দেশ্যে।
রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত নিসবেতগঞ্জ। এই অঞ্চলে হস্তশিল্পজাত পণ্য হিসেবে শতরঞ্জি তৈরি হয়। ঐতিহ্যবাহী পণ্য হিসেবে এর রয়েছে কয়েক শত বছরের গৌরব গাঁথা। বর্তমানে বাংলাদেশের একটি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা Geographical Indication (GI) হিসেবে যা স্বীকৃতি পেয়েছে অর্থাৎ এটি যে আমাদের নিজস্ব পণ্য তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।
পূর্বে এই এলাকার নাম ছিল পীরপুর। ১৮৩০ সালে এক ব্রিটিশ কালেক্টর মিস্টার নিসবেত এই পীরপুর এলাকায় এসে শতরঞ্জি দেখে মুগ্ধ হন। তিনি শতরঞ্জির উন্নয়ন ও প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। পরে তাঁর সম্মানে এই এলাকাটির নামকরণ করা হয় নিসবেতগঞ্জ। শতরঞ্জি সম্পর্কে এসব কথাগুলো বলছিলেন রাইসুল মামা।
শতরঞ্জি পৃথিবীর প্রাচীনতম বুনন শিল্পের মধ্যে অন্যতম। শতরঞ্জি তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী বুনন পদ্ধতিতে। এর মধ্যে আমরা একটা শতরঞ্জি কারখানায় প্রবেশ করলাম। শতরঞ্জি তৈরি হয় পিট লুম বা গর্ত তাঁতে।
মাটিতে একটা গর্ত তৈরি করে তাতে পা ঢুকিয়ে বুনন শিল্পীরা বসেন। তাঁতের প্যাডেলগুলো মাটির নিচে তাদের পায়ের কাছে থাকে। মাটির সমতলের কিছুটা উপরে তাঁতের কাঠামোটা শক্তভাবে মাটির সাথে পৌঁতা থাকে। কাঠামোতে অটকানো টানাগুলো রশি দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি ইঞ্চিতে মোট আটটি করে রশি টানা থাকে। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের সুতা হাতে গুনে আড়াআড়িভাবে পার করা হয়। এভাবেই জ্যামিতিক বিন্যাসে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। এভাবে নির্দিষ্ট মাপ সম্পন্ন হলে তা তাঁত থেকে কেটে নেওয়া হয়। এসব শতরঞ্জি বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে।
শতরঞ্জির নকশায় ব্যবহারিত মোটিফ অনুযায়ী তাকে ঐতিহ্যবাহী নকশা আর আধুনিক নকশা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মোটিফ হল নকশার একটি একক। যা একটি প্যাটার্ন তৈরি করতে পুনরাবৃত্তিকভাবে ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যবাহী নকশায়, জাফরি, নারীর মুখ, হাতির পা, রাজা-রানী, নাটাই, প্রজাপতি, ঘুড়ি, বাঘবন্দি, পালকি, রাখালবালক, কলসি কাঁখে রমণী, মোড়া ফুল, জামরুল পাতা, রথ পাড়ি, দাবারঘর, পৌরাণিক চরিত্র, নবান্ন, পৌষপার্বণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ নানা মোটিফ দেখা যায়।
আধুনিক নকশায়, কাবাঘর, মসজিদ, মিনার, পুষ্পিতপাতা, পানপাতা, বুটিদার জরি ও তেরছি নকশা, মাছ, পাখি, নৌকা, গ্রামের দৃশ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি ধরনের মোটিফ দেখা যায়।
আগের দিনে শতরঞ্জি তৈরিতে পাটের সুতা ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে বিভিন্ন রকমের সুতা ব্যবহার করা হয়। উজ্জ্বল রঙের সুতার ব্যবহারের কারণে বর্তমানের শতরঞ্জি অনেক বেশি বর্ণিল। এসব শতরঞ্জি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে যার ফলে অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। এর মাধ্যমেই দেশীয় শিল্প কীভাবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে তা শামস মামা জানাল। এভাবে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে কি করে নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়। সেই সাথে খুঁজে বের করতে হবে দেশের সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার পথ। সবকিছু দেখে শুনে পফরত্রের কাছে মনে হচ্ছিল তারা যেন কোনো অন্নপুরীতে আছে। শতরঞ্জি কারখানার সকল বুনন শিল্পীকে বিদায় জানিয়ে সেদিনের মতো তারা বাড়ি ফিরে আসল। শামস মামা বললেন নকশা করার পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য এবার তোমাদের কিছু অনুশীলন করাব।
এই পাঠে শতরঞ্জির বিভিন্ন মোটিফ দিয়ে ছক আঁকা কাগজে নকশা অনুশীলন করব। নকশা বড় করা ও স্থানান্তর করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।
উপরের ছবিতে দেওয়া শতরঞ্জির মোটিফগুলোর উপরে এক সেন্টিমিটার করে ছক এঁকে নেবো। সে মাপ অনুযায়ী সাদা কাগজে ছক এঁকে তাতে মোটিফটি হুবহু আঁকার চেষ্টা করব। এরপর মোটিফটি কাগজের ভান পাশে উলটো ভাবে এঁকে খুব সহজে নতুন নকশা তৈরি করা যাবে। মোটিফগুলোতে বিপরীতভাবে রঙের ব্যবহার করে একটা খসড়া নকশা তৈরি করব। এই অনুশীলনের জন্য আমরা পেনসিল, রংপেনসিল, বিভিন্ন রঙের কলমসহ সহজলভ্য যেকোনো রকমের রং ব্যবহার করতে পারি। কাজটি বুঝার জন্য আমরা নিচে দেয়া ছবিগুলো দেখতে পারি।
মামা বলেন এবার তোমাদের জানাব খসড়া নকশাটা কিভাবে প্রয়োজনমতো আনুপাতিক হারে বড় করা যায়। এবং তা কাগজ থেকে কাপড়সহ প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর স্থানান্তর করা যায়।
ছোট মোটিফ বা নকশা বড় করে আঁকার পদ্ধতি
- খসড়া নকশাটির উপর এক সেন্টিমিটার করে ছক এঁকে নিতে হবে।
- যে অনুপাতে খসড়া নকশাটা বড় করা প্রয়োজন সে অনুপাতে কাগজ অথবা যে উপকরণের উপর বড় করে আঁকতে হবে তাতে ছক এঁকে নিবো। যেমন-নকশার উপরে আঁকা এক সেন্টিমিটারের ছকটিকে প্রয়োজনমতো উপকরণের উপর এক ইঞ্চি থেকে এক ফুটের ছক এঁকে ভাতে নকশাটা বড় করে আঁকতে হবে।
- এভাবে তোমরা যেকোনো নকশাকে যতটুকু ইচ্ছা বড় করতে পার।
কাগজে আঁকা নকশা কিভাবে কাপড়সহ অন্যান্য উপকরণে স্থানান্তর করা যায়
- খসড়া নকশাটির উপর ট্রেসিং পেপার বসিয়ে তাতে নকশাটি এঁকে নেবো। আমরা কি জানি ট্রেসিং পেপার কি? ট্রেসিং পেপার হলো একধরনের স্বচ্ছ কাগজ যা কোনো ছবিকে ছাপ দিয়ে আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রেসিং পেপার পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে হালকা নারিকেল তেল ঘষে নিজেদের মতো করে ট্রেসিং পেপার বানিয়ে নিতে পারি।
- ট্রেসিং পেপারে আঁকা রেখা ধরে কিছুটা পর পর সূচ দিয়ে ছিদ্র করে নেবো।
- এবার নির্দিষ্ট কাপড় আথবা যে উপকরণের উপর আমরা খসড়া নকশাটা স্থানান্তর করতে চাই তার সঠিক স্থানে ট্রেসিং পেপারটা আটকে তার ছিদ্রগুলোর উপর কাপড়ে ব্যবহার করা গুঁড়া নীল দিয়ে হাল্কাভাবে ঘষতে হবে। এভাবে ঘষার ফলে দেখা যাবে ছিদ্রগুলো দিয়ে নীলের গুঁড়াগুলো কাপড়ে গিয়ে লাগছে এবং ট্রেসিং পেপারে আঁকা নকশাটি বিন্দু বিন্দু নীল রঙে কাপড় বা প্রয়োজনীয় উপকরণে ফুটে উঠেছে।
- এভাবে কাপড়সহ যেকোনো উপকরণের উপর নকশা স্থানান্তর করে নিজেদের ইচ্ছামতো নতুন পণ্য তৈরি করা যায়।
শতরঞ্জির মোটিফে নতুন পণ্যের নকশা
তরঞ্জির বুনন, নকশা তৈরি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে শামস মামা বললেন শোনো তোমাদেরকে আজ এমন একজন শিল্পীর কথা বলব যিনি তাপিশ্রী (tapestry) নামক বুনন শিল্পকে এক অনন্য শিল্পমাধ্যম হিসেবে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি হলেন শিল্পী রশীদ চৌধুরী।
বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী রশীদ চৌধুরী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, লেখক, ভাস্কর, শিক্ষক ও সংগঠক। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা সরকারি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৫৪ সালে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে এক বছরের বৃত্তি লাভ করে স্পেনের মাদ্রিদে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি চার বছরের বৃত্তি লাভ করে ফ্রান্সের প্যারিসের ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য ও তাপিশ্রী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এই সময়ে বিখ্যাত শিল্পী জ ওজাম্-এর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লিডারশিপ গ্র্যান্ট পুরস্কারে ভূষিত হয়ে ১৯৭৫ সালে শিক্ষাসফরে যুক্তরাষ্ট্রে যান।
১৯৬৯ সালে শিল্পী রশীদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া, ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন প্রবর্তিত পথ ধরে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার জন্য শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে শিল্পী রশীদ চৌধুরীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
দেশের লোক সংস্কৃতির বিষয়সমূহ তাঁর শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল রঙে। ইসলামি ক্যালিগ্রাফির নান্দনিক প্রভাবও তাঁর শিল্পকর্মে দেখা যায়। তিনি চিত্ররচনা করেছেন তেলরঙে, টেম্পারা, গোয়াশে এবং জলরঙে। এছাড়া, পোড়ামাটিতে ভাস্কর্য, ফ্রেস্কো ও বিভিন্ন মাধ্যমে ছাপাই চিত্র করেছেন। তিনি পাট-রেশমের সমাহারে তাপিশ্রী (tapestry) বুনন শিল্পমাধ্যমে নির্মাণ করেছেন তার উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম। শিল্পের এই মাধ্যমে তিনি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শিল্পী হিসেবে বিবেচিত।
দেশ বিদেশের সরকারি ভবন ও দপ্তরে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্পী রশীদ চৌধুরীর তাপিশ্রী (বুনন শিল্প) সংগ্রহে আছে। তাপিতী শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে তিনি একুশে পদক এবং ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
শিল্পী রশীদ চৌধুরীর কিছু শিল্পকর্ম
আলোচনা শেষে রাতের খাবারের পরে বসল প্রসিদ্ধ ভাওয়াইয়া শিল্পী রাইসুল মামার গানের আসর। প্রথমে তিনি ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে জানালেন-হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের মায়াবী জনপদের গান হলো ভাওয়াইয়া। তিস্তা, ধরলা, তোরখা, মনসা নদীবিধৌত অঞ্চলে এ গানের সবচেয়ে বেশি চর্চা হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলা রংপুর ও দিনাজপুর জুড়েই ভাওয়াইয়া গানের উর্বর ভূমি। মূলত 'ভাও' অর্থাৎ ভাব এবং সংস্কৃত শব্দ 'আওয়াই' অর্থ জনরব শব্দ দুটি থেকেই ভাওয়াইয়া গানের নামকরণ হয়েছে। এ অঞ্চলের রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যেও 'ভাও' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। ভাওয়াইয়া ছাড়াও এ অঞ্চলে মেয়েলি শীত, যোগীর গান, পালা বা কাহিনি গান, জারি গান, গোয়ালির গান বেশ জনপ্রিয়।
তরাই অঞ্চলে প্রচুর মহিষের বাথান দেখা যায়। তরাই হলো দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত সমতল ভূমি আর মহিষের বাথান হলো মহিষের চারণভূমি। যেখানে মহিষের পাল নিয়ে পালকেরা তৃণভূমিতে চড়িয়ে বেড়ায়। এ সময়ে রাখালের কাজ থাকত খুবই কম। অলস মুহূর্ত কাটানোর জন্য তারা মহিষের পিঠে চড়ে গান বাঁধতো। সেগুলোতে সুর দিয়ে আপন মনে গেয়ে উঠত। পাহাড়ের পাদদেশীয় উপত্যকা বা তরাই অঞ্চল থেকে মহিষ পালকের কন্ঠের সে সকল গান বা ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিত হতো বলেই ভাওয়াইয়া গানের সুরে বিশেষ ভাঁজ লক্ষ্য করা যায়। দোতারা ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম সহযোগী যন্ত্র। গরু কিংবা মহিষের গাড়িতে চলার সময় যে দোলা অনুভূত হয়, ভাওয়াইয়া গানেও ঠিক সে দোলাতেই দোতারা বাজানো হয়। শিল্পীরা নিজ হাতে স্থানীয় উপকরণেই গড়ে নেয় এসকল দোতারা। দোতারা বাদ্যযন্ত্রকে উদ্দেশ্য করেও অসংখ্য ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
গাড়িয়াল বন্ধুর গান। গরুর রাখাল কিংবা গরুর গাড়ির চালক নিজে এই গান করেন। কখনও কখনও গাড়িয়ালকে উদ্দেশ্য করেও এই গান করা হয়:
বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
ওকি ওরে ঐমতন মোর গাড়ির চাকা পথে পথে ঘোরে রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলও রাজপন্থে।
বিয়ানে উঠিয়া গরু গাড়িত দিয়া জুড়ি
ওরে সোনা মালার সোনার বাদে চান্দের দ্যাশে ঘুরিরে।
গাড়ির চাকা ঘোরে আরও মধ্যে করে রাও
ওরে ঐমতো কান্দিয়া উঠে আমার সর্বগাও রো
মইষাল বন্ধুর গান: মহিষের বাথানের রাখাল কিংবা মহিষের গাড়ির চালক এই গান করেন। কখনও কখনও মহিষের গাড়ির চালককে উদ্দেশ্য করেও এটি গীত হয়।
ওকি মইষাল রে
ঘাটের উপরে দিয়া বাদাম
মইযালী গানে দোতারা বাজান
প্রাণ কান্দে মোর তোর ভাওয়াইয়া গানে রে।
(সংক্ষেপিত)
মাহত বন্ধুর গান: হাতির চালক বা মাহত এই গান নিজে করে থাকেন। অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে যেখানে হাতির চলাচল, সেখানে বেশি শুনতে পাওয়া যায়। আবার কখনও মাহত বন্ধুকে উদ্দেশ্য করেই এ সুর গাওয়া হয়। নিচের গানটি দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া হয়ে থাকে।
মেয়ে কণ্ঠ-
তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তির নড়ান হস্তির চড়ান হস্তির পায়ে বেড়ি
ওরে সত্যি করিয়া কনরে মাহুত কোনবা দেশে বাড়িরে।
ছেলে কন্ঠ-
হস্তির নড়ান হস্তির চড়ান, হস্তির গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কংরে কন্যা গৌরিপুরে বাড়িরে।
(সংক্ষেপিত)
সমীর ভাওয়াইয়া গানের এরকম প্রকারভেদ বেশ মনোযোগের সাথেই খেয়াল করছিল। সে রাইসুল মামাকে জিজ্ঞাসা করল ভাওয়াইয়া গানের সুর খুবই দীর্ঘ এবং টানা। এভাবে টানা সুরে গান গাওয়া কিভাবে সম্ভব? উত্তরে রাইসুল মামা বললেন-এটা হলো চর্চার বিষয়। তুমি যত বেশি সারগম বা স্বরচর্চা করবে তত বেশি দম ও সুরের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
একথা শুনেই ইরা বলল চলো তাহলে আমরা লম্বা সুরে স্বরচর্চা করি। আমরা আগেই যে কাহারবা তাল শিখেছি। কাহারবার ধীর লয় বা গতিতে চলে এমন সারগম চর্চা করতে চাই। রাইসুল মামা তাদের অনুশীলনের জন্য নিচের সারগমটি শিখিয়ে দিলেন।
এই পাঠে আমরা কাহারবার ধীর লয় বা গতিতে চলে এমন সারগম চর্চা করব।
আরোহণ-
অনুশীলনের পর রাইসুল মামা বললেন এই উত্তরের জনপদে ভাওয়াইয়া গানের মতো জনপ্রিয় একটি নাচ হলো সাঁওতাল নাচ।
কৃষিজীবী সাঁওতাল পরিবারে রয়েছে বার মাসে তের পার্বণ। নৃত্য, গীত প্রিয় সাঁওতাল উৎসব এলেই বাড়ির উঠোনে বাজে মাদল, শিঙ্গা, মন্দিরা আর ঢোল। উৎসবে মেতে ওঠে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই। বিভিন্ন ঋতুকে কেন্দ্র করে থাকে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বছর শুরুই হয় ফাল্গুন মাস থেকে। ফাল্গুন মাসে শালই উৎসব হয়ে থাকে, চৈত্র মাসে হয় বঙ্গাবঙ্গি, হোম হয় বৈশাখ মাসে, আশ্বিনে দিবি, আর পৌষে হয় সোহরাই। আর এই উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো সাঁওতাল মেয়েদের দলবদ্ধ নৃত্য। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্বন হলো বাহা উৎসব। ফাল্গুনের রাঙা পলাশের মতন রঙ্গিন এই বাহা উৎসব। এই উৎসবেরও প্রধান আকর্ষন নাচ। পুরুষেরা বাজায় ধামসা, মাদল, টিকারা, বাঁশি। আর পরনে থাকে ধুতি। মাথায় পরে কখনও ময়ূরের সরু পালক, কখনও মোটা একগুচ্ছ পালক, কখনও মাথায় শুধু লাল রঙের কাপড়। আর মেয়েরা কোমর জড়িয়ে শাড়ি পরে। তারা কানে কানপাশা, গলায় হার, হাতে ময়ূরের পালক এবং পায়ে ঘুন্ডুর লাগিয়ে নাচে অংশগ্রহণ করে। ছয় থেকে সাত জনের বেশি নানা বয়সের মেয়েরা দলগত ভাবে এই নাচে অংশগ্রহণ করে। সাঁওতাল নাচে মূলত ঝুমুর তাল বাজানো হয়।
এই পাঠে আমরা সাঁওতাল নাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করব
পদচলন
অর্ধেক গোলাকারে পাশাপাশি সকলে দাঁড়িয়ে তিন পা আগায়। আবার তিন পা পিছিয়ে তাল রক্ষা করে। পায়ে থাকে ঘুশুর। এভাবে পাশাপাশি চলতে থাকে।
সামনে-পিছনে চলার সময় প্রতি পদক্ষেপেই শরীরে একটি ঝোঁক থাকে। ঠিক যেন নদীর ঢেউয়ের মতন। বাজনার লয় বাড়ার সাথে সাথে পদচলনের গতি বৃদ্ধি হয়। সাথে দেহের ঝোঁকের দুলুনিও বৃদ্ধি হয়।
ছয় থেকে সাত জনের বেশি হলে একই ভাবে আরেকটি দল গঠন করে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এরপর দুটি দল একইসাথে ডান থেকে বাম দিকে, আবার বাম থেকে ডান দিকে ঘুরে নাচ করে। নাচের ভিন্নতা আনার জন্য দ্রুত লয়ের সাথে সাথে উবু হয়ে একই পদচলনের সাথে তারা নাচ করে থাকে।
মুখভঙ্গি
সাঁওতালদের নৃত্য মূলত আনন্দের নৃত্য। তাই এই নৃত্যের মুখভঙ্গিও হবে সদা হাসোজ্জ্বল।
পরের দিন সকালে তারা রওনা হলো নয়াবাদ মসজিদ দর্শনে। দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের নয়াবাদ গ্রামে অবস্থিত এই অনন্য সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শনটি।
মসজিদের প্রবেশদ্বারের ওপর ফারসি ভাষায় রচিত লিপি থেকে এর নির্মাণ তথ্য জানা যায়। পশ্চিমা দেশ থেকে আগত মুসলিম স্থাপত্যকর্মীরা টেপা নদীর পশ্চিম তীরে নয়াবাদ গ্রামে মোকাম তৈরি করেন এবং সেখানে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।
মসজিদটি আয়তাকার, যার তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মাঝের গম্বুজটি দুপাশের গম্বুজের তুলনায় কিছুটা বড়। মসজিদটির চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির মিনার রয়েছে। মসজিদে মোট ১০৪টি আয়তাকার ফলক রয়েছে ফলকগুলোতে লতাপাতা ও ফুলের নকশা রয়েছে। মোঘল স্থাপত্য নিদর্শন সম্বলিত নয়াবাদ মসজিদটি আমাদের দেশের এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন।
দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে দিনাজপুর-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পশ্চিমে টেপা নদীর পারে কান্তনগর গ্রামে এ মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি স্থাপিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নির্দশন রয়েছে এ মন্দিরে। বর্গাকৃতির মন্দিরটি একটি আয়তাকার প্রাঙ্গণের উপর স্থাপিত। মন্দিরটি তিনটি ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে। মন্দিরটির ভিত্তি থেকে শুরু করে চূড়া পর্যন্ত ভেতরে ও বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে।
পোড়ামাটির ফলকগুলোতে মহাভারত ও রামায়ণের বিস্তৃত কাহিনীর অনুসরণে মনুষ্য মূর্তি ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণের নানা কাহিনি, সমকালীন সমাজ জীবনের বিভিন্ন ছবি এবং জমিদার অভিজাতদের বিনোদনের চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বনের ভেতর শিকার দৃশ্য, হাতি, ঘোড়া, উট সহযোগে রাজকীয় শোভাযাত্রা, কুরুক্ষেত্র ও লঙ্কার প্রচন্ড যুদ্ধের দৃশ্যাবলি চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছে এসব পোড়ামাটির ফলকগুলোতে।
কান্তজীর মন্দিরে প্রায় পনের হাজার পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। অপূর্ব পোড়ামাটির ফলক আর দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলি সম্পন্ন কান্তজীর মন্দির আমাদের দেশের এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন।
নয়াবাদ মসজিদ ও কান্তজীর মন্দির পরিদর্শনের সাথে সাথে সকলে বন্ধুখাতায় কিছু পোড়ামাটির ফলকের ড্রইং এবং তথ্য-উপাত্ত লিখে নিল।
এরপর তারা তাজহাট জমিদারবাড়ি এবং সেখানে অবস্থিত 'রংপুর জাদুঘর' সহ আন্যান্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে তারা গেল মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ রক্তগৌরব দেখতে।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ২৮ শে মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে সারা দেশের মতো রংপুরে ছাত্র জনতার মিছিল মিটিং আর প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শহরে। ২৮ শে মার্চ মুক্তিকামী বীর বাঙ্গালির সাথে সাথে ওঁরাও, সাঁওতালসহ রংপুরের সকল মানুষ ঢোল বাজিয়ে ঘাঘট নদীর পাড়ে একত্রিত হয়। সেখান থেকে তারা বাঁশের লাঠি আর তীর-ধনুক হাতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। মুক্তিকামী মানুষ সেনানিবাসের ৪০০ গজের মধ্যে আসতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেশিন গানের গুলিতে শতশত মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে নিসবেতগঞ্জের মুক্তিকামী মানুষের এই মহান আয়োৎসর্গের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঘাঘট নদীর তীরে নির্মিত হয়েছে রক্তগৌরব স্মৃতিস্তম্ভটি। এই স্মৃতিস্তম্ভের দন্ডাকার অংশের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। এর নকশায় তীর ধনুক আর দেশীয় অস্ত্র প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের বেদিটি অপেক্ষাকৃত কম উঁচু বৃত্তাকার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। নীরবে ধীরে ধীরে তারা সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভের জায়গাটি ঘুরে দেখল। এক গভীর অনুভূতিতে ভরে গেল তাদের মন। শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে গেল মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাওয়া আমাদের এই দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ নিল তারা। এরপর তারা যাত্রা করল পদ্মাপাড়ের উদ্দেশে।
এই অধ্যায়ে আমরা যা করব
- বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে এবং বুঝে ছবি আঁকার অনুপাত ও ভারসাম্যের নিয়মনীতি আল্লস্থ করার চেষ্টা করব।
- বইয়ে দেওয়া শতরঞ্জির মোটিফ দিয়ে ছক আঁকা কাগজে নকশার খসড়া তৈরি করব।
- ছক এঁকে কিভাবে ছোট নকশাকে প্রয়োজন মতো বড় করা যায় তা অনুশীলন করব। বইয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ইচ্ছামতো উপকরণের উপর নকশা স্থানান্তর করে নতুন পণ্য তৈরি করব।
- কাহারবা তালে ধীর লয়ে যে আরোহণ ও অবরোহণটি দেওয়া আছে তা অনুশীলন করব। ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে জানব এবং নিজেদের মত করে গাওয়ার অনুশীলন করব।
- দলীয়ভাবে সাঁওতালি নাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করব।
- নিজেদের এলাকায় ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করব। যদি থাকে তবে তার ছবি এঁকে রাখব এবং বর্ণনা বন্ধুখাতায় লিখে রাখব
- শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব
Read more