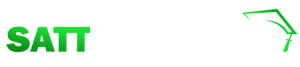আমরা দেখেছি একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান অনেক ধরনের সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে। যেমন: রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো, রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ ও ইনসুলিন দেওয়া, রোগীকে হুইলচেয়ার ব্যবহারে সহায়তা করা প্রভৃতি। এগুলোকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল কেয়ারগিভিং কার্যক্রম যা একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের ক্লিনিক্যাল দক্ষতার উল্লেখযোগ্য মানদন্ড নির্দেশ করে। এই কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকাটা অতীব জরুরি। অন্যথায় রোগীর নানারকম অসুবিধা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা
- ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে ঔষধ খাওয়াতে পারবো
- রক্তের গ্লুকোজ পরিমাণ করতে পারবো
- রোগীকে ইনসুলিন দিতে পারবো
- ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্যাম্পল বা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করতে পারবো
- সেবাগ্রহীতাকে সঠিক পজিশনে রাখতে পারবো
- সেবাগ্রহীতাকে এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে পারবো
- হুইলচেয়ার ব্যবহারে রোগীকে সহযোগিতা করতে পারবো।
উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা মোট দুই আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করবো। এই জবের মাধ্যমে আমরা রক্তের গ্লুকোজ মেপে ইনসুলিন দিতে এবং পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারবো ।
১.১ ঔষধ প্রদান করা
প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশি রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার সাথে পরিচিত। আমরা অসুস্থ হলে বা সুস্থ থাকার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ডাক্তার তখন আমাদের শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে পথ্য- ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকেন। প্রায় প্রতিটি মানুষই নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে ঔষধ সেবন করে থাকে। আমরা আমাদের বাসা-বাড়িতেও পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় শারীরিক নানা অসুবিধার কারণে ঔষধ নিতে দেখি। আবার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অসুস্থ ব্যক্তি যিনি নিজে নিজে ঔষধ নিতে পারেন না, তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিয়মমাফিক ঔষধ খাওয়ানো একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রধানতম দায়িত্ব। এ কারণে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে মুখে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য এ সংক্রান্ত কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক।
১.১.১ ঔষধ বা ড্রাগ
যে সকল দ্রব্য রোগ নির্ণয়, আরোগ্য লাভ, উপশম, প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যা মানবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে তাকে ঔষধ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঔষধ এমন দ্রব্য যার আরোগ্য এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে অথবা যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে; Drug (ড্রাগ বা ঔষধ) হচ্ছে এমন একটা agent যেটিকে Diagnosis (ডায়াগনোসিস), Prevention (প্রিভেনশন) এবং Treatment (ট্রিটমেন্ট)করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে Diagnosis মানে হচ্ছে কোনো রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বা Reagent ব্যবহার করা হয়। Prevention মানে শরীরে যাতে কোনো রোগ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য আগে থেকে শরীরকে প্রস্তুত করে রাখা। যেমন Vaccine বা টিকা হচ্ছে এক ধরনের ঔষধ যেটি ব্যবহার করলে শরীরে ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট রোগ সাধারণত আক্রমণ করতে পারে না। Treatment মানে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় তবে সেই রোগকে নিরাময় করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা। বিভিন্ন ধরনের Antibiotic আছে যেগুলো treatment এর কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায় ঔষধ হতে পারে থেরাপিউটিক বা রোগনিরাময়কারী, প্রোফাইলেকটিক বা প্রতিরোধমূলক এবং ডায়াগনস্টিক বা রোগ নিৰ্ণয়মূলক ।
ঔষধ বিজ্ঞানের কতিপয় টার্ম / পরিভাষা
- ফার্মাকোলজি: বিজ্ঞানের যে শাখায় একটি ঔষধের উৎস থেকে শুরু করে এটি মানব দেহের উপর যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে “ফার্মাকোলজি” বলে। ফার্মাকোলজি'র দু'টি প্রধান শাখা হলো- ফার্মাকোকাইনেটিকস ও ফার্মাকোডাইনামিক।
- ফার্মাকোকাইনেটিকস: ফার্মাকোলজির যে শাখায় ঔষধের শোষণ, বন্টন, বিপাক এবং নিষ্কাশন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে “ফার্মাকোকাইনেটিকস” বলে।
- ফার্মাকোডাইনামিক: ফার্মাকোলজির যে শাখায় দেহের উপর ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে “ফার্মাকোডাইনামিক” বলে।
- ক্লিনিকাল ফার্মাকোলজি: চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখা জীব ও মানব দেহের উপর চিকিৎসার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।
- নিউরোফার্মাকোলজি: যে শাখা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর ঔষধের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- সাইকোফার্মাকোলজি: যে শাখা মস্তিস্কের উপর ঔষধের ক্রিয়া ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, আচরণগত পার্থক্য নির্ণয় ও শারীরতাত্বিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- পোসোলজি: যে শাখা কিভাবে ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান (নির্ভর করে রোগীর বয়স, ওজন, লিঙ্গ, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর) নিয়ে আলোচনা করে ।
- ফার্মাকোগনসি: যে শাখা ভেষজ গুনাগুণ সম্পনড়ব উদ্ভিদ বা প্রাণীজ পদার্থ থেকে চিকিৎসাগত দ্রব্যাদির আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, সুষ্ঠু বন্টন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- ফার্মাকোজেনেটিক্স: যে শাখা বিভিন্ন জাত, বিভাগ, বর্ণ, তারতম্য ভেদে ঔষধের প্রভাবে পার্থক্য নিরুপণ করা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমানের ও সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়াযুক্ত ঔষধ নির্বাচন করা নিয়ে আলোচনা করে।
- ফার্মাকোজেনোমিক্স: যে শাখা ঔষধ প্রযুক্তিতে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এই সম্পর্কিত বিদ্যমান ঔষধের গুনাবলি এবং নতুন ঔষধ আবিস্কারের নিমিত্তে গবেষণা করে।
১.১.২ বিভিন্ন প্রকার ঔষধ
ঔষধ বা ড্রাগকে তাদের উৎস, কার্যকারিতার ধরন, ওষধি ক্রিয়া ও গুণাগুণ প্রভৃতি নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। উৎসের উপর ভিত্তি করে ঔষধকে নিম্নোক্ত ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-
১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ: ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, সামুদ্রিক ও খনিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ।
২. রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ: এ সকল ড্রাগের কিছু অংশ প্রাকৃতিক ও কিছু অংশ রাসায়নিক উপায়ে তৈরি হয়। যেমন: স্টেরয়েডীয় ড্রাগ।
৩. রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত ড্রাগ
৪. প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: হরমোন ও এনজাইম বা উৎসেচক।
৫. অণুজীব উৎস হতে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: এন্টিবায়োটিক।
৬. জীবপ্রযুক্তি ও জীনপ্রকৌশলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: হাইব্রিডোমা টেকনিক ।
৭. তেজস্ক্রিয় বস্তুর মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: Stereotactic Body Radiation থেরপী, Potassium Iodide (K1) ইত্যাদি।
আরেক ধরনের মুখ্য শ্রেণিবিভাগ হলো-
- সিনথেটিক বা রাসায়নিক উপায়ে তৈরি ড্রাগ
- জৈবলব্ধ উপাদান যেমন- রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন, ভ্যাক্সিন বা প্রতিষেধক, স্টেম সেল থেরাপি ইত্যাদি।
কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে ঔষধকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-
- এন্টিপাইরেটিকস: এগুলো জ্বর (পাইরেক্সিয়া বা পাইরেসিস) কমায় ।
- এনালজেসিক: এরা বেদনা বা ব্যথার উপশম করে (ব্যথানাশক ) ।
- এন্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ: ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- এন্টিবায়োটিক: জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে।
- এন্টিসেপটিক: পোড়া, কাটা কিংবা ক্ষতের আশেপাশে জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে।
- মুড স্ট্যাবিলাইজার: লিথিয়াম এবং ভ্যালপ্রোমাইড এ কাজ করে।
- এন্টি স্পাজমোডিক: স্পাজম বা পেট ব্যথা কমায়।
- হরমোন রিপ্লেসমেন্টস: প্রিমারিন। হরমোনের স্বল্পতা দূরীকরনে ব্যবহৃত হয়।
- এন্টিহেলমেনথিক: এগুলো কৃমিনাশক ঔষধ।
১.১.৩ ঔষধ কিভাবে কাজ করে?
ঔষধ সাধারণত মুখে খাওয়ার মাধ্যমে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ঔষধ মুখে খাওয়ার পর পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে এগুলো বিশোষিত হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং দেহের যে সমস্ত অংশে রক্তের সরবরাহ আছে সেখানে ঔষধ বহন করে নিয়ে যায়। যে সব ঔষধ ইনজেকশন হিসেবে দেওয়া হয় সেগুলো সরাসরি রক্ত স্রোত বা ব্লাড স্ট্রীমে মিশে। এজন্য ইনজেকশন তাড়াতাড়ি কাজ করে। ঔষধ শুধুমাত্র দেহের একটি অংশে কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেও রক্তস্রোত এই ঔষধকে দেহের অনেক অংশে নিয়ে যায়। সেজন্য দেহের অন্যান্য অংশেও ঔষধ অযাচিতভাবে কাজ করতে পারে। যেমন : এসপিরিন- ইহা স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে ব্যথা উপসম করে। কিন্তু এটা আবার পাকস্থলীর ঝিল্লীতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে (যা ক্ষতিকর হতে পারে), তাছাড়া এসপিরিন সন্ধির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে (যা উপকারী হতে পারে)। এ ধরনের ফলাফলকে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা সাইড ইফেক্ট বলা হয়। এছাড়াও এসপিরিন রক্তকে পাতলা করে বলে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের দেওয়া হয়। দেহে ঔষধের কাজ বিভিন্ন রকম হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু নীচে বর্ণনা করা হলো:
১। যে সমস্ত ঔষধ রোগ জীবানুকে ধ্বংস করে। যেমন-
- এন্টিবায়োটিক- যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, এমক্সাসিলিন, কোট্রাইমোক্সাজল, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ। এছাড়াও new generation এর আরো অনেক antibiotics আছে।
- এন্টিপ্যারাসাইটিক- যা পরজীবিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কৃমি হলো পরজীবি। এলবেনডাজল, মেবেনডাজল, লিভামিসল ইত্যাদি কৃমিনাশক ঔষধ।
২। যে সমস্ত ঔষধ কোনো অঙ্গ বা তন্ত্রের উপর কাজ করে। যেমন-
- স্নায়ুতন্ত্রের উপর: উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রশান্তিদায়ক বা স্নায়ুর উত্তেজনা শান্তকারক ঔষধ (Tranquilizer/Sedative), যেমন- ডায়াজিপাম। ব্যথানাশক ঔষধ (Analgesic), যেমন- প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ডিসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি। জ্বর উপসমকারী ঔষধ (Antipyretic), যেমন- প্যারাসিটামল। অনুভূতিনাশক ঔষধ ( Anaesthetic), যেমন-লিগনোকেইন (Lignocaine) ইত্যাদি।
- জরায়ুর উপর: প্রসবের পর রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ঔষধ জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচন বাড়িয়ে দেয়। যেমন-অক্সিটোসিন, আরগোমেট্রিন।
- ফুসফুসের উপর: হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এ ঔষধ ফুসফুসের বাতাস প্রবেশের পথকে প্রসারিত/বড় করে দেয়। এগুলোকে ব্রংকোডাইলেটর (Bronchodilator) বলা হয় । যেমন- সালবিউটামল, থিওফাইলিন ইত্যাদি।
৩। যে সমস্ত ঔষধ খাদ্যের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে: এসব ঔষধ খাদ্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ যোগান দেয় যখন কোনো ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাচ্ছে না অথবা তা শরীরে বিশোষিত (Absorption) হচ্ছে না। যেমন: ভিটামিন-এ, আয়রন, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।
৪। যে সমস্ত ঔষধ দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ঠিক করে: যেমন- এন্টাসিড, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি। খাবার স্যালাইন একজন রোগীর ডায়রিয়াজনিত কারণে নির্গত পানি ও লবনের অভাব পূরণ করে।
রোগ/উপসর্গ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ঔষধের পরিচিত :
| ক্র. | রোগ/উপসর্গ | নির্দেশিত ঔষধ (জেনেরিক নাম) |
| ১ | শ্বাস তন্ত্রের সংক্রমণ | ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, কোট্রাইমক্সাজল |
| ২ | জ্বর ব্যথা | প্যারাসিটামল, এসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, এন্ডোমেথাসিন |
| ৩ | পেট ব্যথা | হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড, ডোটাভেরিন |
| ৪ | হাপানী | সালবিউটামল, এমাইনোফাইলিন, থিওফাইলিন |
| ৫ | সাধারণ সর্দি-কাশি এলার্জি | প্রোমেথাজিন, ক্লোরফেনিরামিন |
| ৬ | চুলকানি ও খোসপাঁচড়া | বেনজাইল বেনজোয়েট, পারমেথ্রিন |
| ৭ | কৃমি | মেবেনডাজল, এলবানডাজল |
| ৮ | রক্তস্বল্পতা | আয়রণ ও ফোলিক এসিড |
| ৯ | বমি, বমি ভাব | ডমপেরিডোন মেলিয়েট |
| ১০ | ম্যালেরিয়া | ক্লোরোকুইন, কুইনাইন |
| ১১ | অনিদ্রা ও মৃদু শান্তকারক | ডায়াজিপাম |
| ১২ | মুখের কোনায় বা জিহবায় ঘা | রিবোফ্লাবিন |
| ১৩ | অপুষ্টি, দুর্বলতা | ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, মাল্টিভিটামিন |
ড্রাগ স্টোরেজ বা ঔষধ সংরক্ষণ
ক্লিনিক বা বাসায় যেখানেই হোক না কেন, ঔষধের সংরক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক সময়ে মডেল ফার্মেসীগুলোতে ঔষধ সংরক্ষণ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সেই ঔষধ আমাদেরকে সেবাদান কেন্দ্রে কিংবা বাসাবাড়িতে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়। এ সকল জায়গায় বেশি তাপ, বাতাস, আলো এবং ময়েশ্চার ওষুধকে নষ্ট করতে পারে। তাপ ও ময়েশ্চারে ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল জাতীয় ঔষধ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে ওষুধ। সেই ওষুধ খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে। আবার তরল ইঞ্জেকশন বা সিরাপ একবার সেবনের পর বেশিদিন রাখা উচিৎ নয়। ইনসুলিন ও লিকুইড অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বেশি সাবধানতা নেওয়া উচিত। যেমন, ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সাধারণত ৩০দিন পর্যন্ত ঠিক থাকে ইনসুলিন। তাই এ ধরনের ঔষধকে ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আরো কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা যায়, যেমন:
- ওষুধের খাপ থেকে ওষুধ খুলে রাখা যাবে না ।
- ঠাণ্ডা এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হবে ওষুধ। ড্রেসার ড্রয়ার কিংবা কিচেন ক্যাবিনেটে রাখা যেতে পারে ওষুধ। স্টোরেজ বক্স বা তাকে রাখা যেতে পারে ওষুধ। না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওষুধ।
- তবে, আগুন, স্টোভ, সিঙ্ক এবং গরম কোনো সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ওষুধের বোতল থেকে তুলোর বল বের করে নিতে হবে। কারণ, এই তুলো থেকে ময়েশ্চার জন্ম নিতে পারে। প্লাস্টিকের ব্যাগে ওষুধ রাখা যাবে না। রাখলে ওষুধের প্রভাব কমে যেতে পারে।
- একটি পাত্রে অনেক ওষুধ একসঙ্গে না রাখাই উত্তম। অন্যথায় মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই বদলে যেতে পারে ওষুধের রং, গন্ধ। শিশুদের নাগাল থেকে দূরে রাখতে হবে ওষুধ।
১.১.৪ রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন
যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক না কেন, ঔষধ সাধারণত শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থান বা জায়গা দিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। Route বলতে বোঝায় এমন একটা পথ যার মধ্য দিয়ে একটা মেডিসিন (Drug) শরীরে প্রবেশ করে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে কাজ করে। ড্রাগ যখন শরীরে কাজ করে তখন তাকে Pharmacological Action বলে। তাহলে একটি ড্রাগ শরীরে কোন পথে প্রবেশ করবে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে যাবে, সেই রাস্তার সাথে মেডিসিনের সম্পর্ক কেমন হবে সেটাকে ঔষধের রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ( routes of administration) বলে। একটি ড্রাগ কি ধরনের রুট দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবে ও কাজ করবে তা কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলো হচ্ছে-
ক. ঔষধের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন: একটা ড্রাগ কঠিন, তরল নাকি গ্যাসীয় তার উপর নির্ভর করবে সেই ড্রাগ কোন পথে মানবদেহে প্রবেশ করবে। উদাহরণস্বরূপ; Solid বা কঠীন ড্রাগগুলো শরীরে প্রবেশের পর সেটি ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরাতে পরিণত হয় (Disintegration ঘটে) এবং সবশেষে শরীরে শোষিত হয় (Dissolve ঘটে)। আবার Liquid বা তরল ঔষধ শরীরে প্রবেশের পর কেবলমাত্র শোষিত হয় বা Dissolve হয়। অন্যদিকে গ্যাসীয় ড্রাগগুলো শরীরে নাক বা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে এবং সরাসরি এরা ফুসফুসে কাজ করে। এছাড়া ড্রাগ এর রুট নির্ভর করে সেটির দ্রাব্যতা এবং pH এর উপরেও।
খ. নির্দিষ্ট কাজের জন্য পছন্দসই জায়গা: এর মানে হচ্ছে একটা ঔষধ শরীরের ঠিক কোন জায়গায় কাজ করবে সেটা নির্বাচন করা। যদি আমাদের গালে ব্রণ উঠে তবে চিকিৎসক এমন ঔষধ দিয়ে থাকেন যেটা শুধুমাত্র গালের ওই ব্রণের অংশটাতে কাজ করে। আবার আমরা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে চিকিৎসক এমন ঔষধ দিয়ে থাকেন যেটা পুরো শরীর জুড়ে কাজ করে। কাজেই Route of Drug Administration এক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা পালন করে এবং ড্রাগের পথ ঠিক করে দেয়, যাতে সে আমাদের শরীরের নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে ।
গ. ঔষধ শোষিত হবার শতকরা হার: এর মানে হচ্ছে একটি ঔষধ কোন পথে প্রবেশ করালে তা শরীরে সর্বোচ্চ পরিমানে শোষিত হবে সেটা। সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়ার জন্য ঔষধকে এমন রুটের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করাতে হবে যাতে সেটি সর্বোচ্চ পরিমানে শোষিত হয়।
ঘ. ঔষধের বিপাক: ঔষধের মেটাবলিজম বা বিপাক বলতে ঔষধ শরীরে প্রবেশের পর তার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনকে বুঝায়। এটিকে ঔষধের বায়োট্রান্সফর্মেশনও বলা হয়ে থাকে। ঔষধের বিপাক দুই ধরনেরঃ First pass, By pass | First pass হচ্ছে গতানুগতিক পথ দিয়ে ড্রাগের পথ চলা, যেমন আমাদের মুখ দিয়ে কোনো ট্যাবলেট সেবন করলে সেটা অন্ননালী দিয়ে পাকস্থলীতে যাবে, সেখান থেকে অস্ত্রে যাবে, তারপর যকৃত হয়ে রক্তে যাবে। এক্ষেত্রে ড্রাগের কার্যক্ষমতা কমে যাবে। কিন্তু সরাসরি সে ড্রাগকে যদি রক্তে প্রয়োগ করা হয় তবে সেটি পুরোপুরি কাজ করবে। এই পদ্ধতিকে By pass বলে।
ঙ. কার্যকারিতার দ্রুততা: এর মানে হচ্ছে ঔষধ শরীরে প্রবেশের পর কত দ্রুত কাজ করবে। এক্ষেত্রেও Route of Drug Administration ভূমিকা রাখে। মুখে খাওয়ার ঔষধের চেয়ে সরাসরি শিরার মাধ্যমে রক্তে ইনজেকশন প্রয়োগ করলে সেটি অধিকতর দ্রুত কাজ করে।
চ. রোগীর অবস্থা: রোগী যদি শিশু হয় তবে তাকে সিরাপ বা Liquid জাতীয় ড্রাগ দিতে হয়, রোগী যদি কোমাতে থাকে তবে তাকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ শরীরে দিতে হয়, রোগী যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তবে তাকে ট্যাবলেট / ক্যাপসুল হিসেবে ড্রাগ খাওয়ানো যেতে পারে।
এ সকল বিষয় বিবেচনা করেই একজন চিকিসক Drug এর Route নির্বাচন নির্ধারণ করে থাকেন।
বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হলেও রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন মূলত দুই প্রকার :
১. এন্টেরাল (Enteral): এটি হচ্ছে ড্রাগ চলাচলের এমন পথ যেখানে ড্রাগ সরাসরি ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। যেমন- Oral Route, এটির মাধ্যমে মুখ দিয়ে ট্যাবলেট, সিরাপ ক্যাপসুল ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্তে পৌছায়। এই রুট ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সহজ। এটির অসুবিধা হচ্ছে এটি First Pass পদ্ধতি যেখানে ড্রাগের কার্যক্ষমতা কিছুটা কমে যায়, সাথে সাথে এই ড্রাগ শরীরে কাজ করে না। কিছুটা সময় নেয়।
২. প্যারেন্টাল (Parental): কোনো ড্রাগ যদি ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদান্ত বাদে অন্য কোনো পথে শরীরে প্রবেশ করে সঠিক জায়গাতে গিয়ে কাজ করে তবে তাকে Parental রুট বলে। Parental Route নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত। যেমন:
ক. সাবলিঙ্গুয়াল (Sublingual) রুটঃ আমাদের জিহবার নিচে যদি কোনো ট্যাবলেট রাখা হয় তবে সেটি জিহবার নিচের ক্যাপিলারির মাধ্যমে সরাসরি নির্দিষ্ট জায়গার পৌছে যায়, ক্ষুদ্রান্ত – বৃহদান্তে যায় না।
খ. বাক্কাল (Buccal Route) রুট: যখন কোনো ট্যাবলেট মুখের ভেতর গালের কোণায় রাখা হয় তখনও ক্যাপিলারির মাধ্যমে সেটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে চলে যায় ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদান্ত পার না হয়েই।
গ. রেকটাল (Rectal) রুট: শরীরের Rectal অংশে সরাসরি ড্রাগ প্রয়োগ করা যায়, এক্ষেত্রে সেটি দ্রুত কাজ করে।
ঘ. সাব-কিউটেনিয়াস (Sub-cutaneous) রুট: শরীরে যখন ত্বকের নিচে ড্রাগ পৌছানোর জন্য ইনজেকশন দেওয়া হয় তখন ড্রাগ যে রাস্তা ধরে সরাসরি নির্দিষ্ট অংশে যায়, তাকে Sub Cutaneous Route বলে। যেমন- ডাইবেটিকস রোগীর ইনসুলিন এই ধরনের route ফলো করে । এটির সুবিধা হচ্ছে ড্রাগ সরাসরি কম সময়ে কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছে যায়। এর অসুবিধা হচ্ছে এটির ফলে ত্বকের নিচে থাকা নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষতি হতে পারে।
ঙ. ইনহেলেশনাল (Inhalational Route) রুট: যখন গ্যাসীয় ড্রাগ সরাসরি ফুসফুসে যায় তখন এই route কাজ করে। এক্ষেত্রে সরাসরি ড্রাগ ফুসফুসে গিয়ে সেখানকার কৈশিকজালিকার (Capillary) মাধ্যমে রক্তে পৌছে যায়। তাই এই ধরনের পথ ব্যবহারের ফলে ড্রাগটি খুব দ্রুত শরীরের ভেতরে কাজ করতে পারে।
চ. ন্যসাল (Nasal) রুট: এক্ষেত্রে নাকের ভেতরে ড্রপলেট আকারে ড্রাগ ব্যবহার করা হয়, যেখানে ড্রাগটি নির্দিষ্ট পথ ধরে শরীরের কাঙ্খিত জায়গায় পৌছে যায়। এই পথকে Nasal Route বলে। যেমন – সোয়াইন ফ্লু এর ড্রাগ তরল প্রকৃতির। নেবুলাইজার নামক যন্ত্রের মাধ্যমে এই ড্রাগকে নাকের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ফ্লু’এর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করানো হয়।
ছ. ইন্ট্রামাস্কুলার (Intramuscular) রুট: ইনজেকশনের মাধ্যমে পেশীর ভেতরে ড্রাগ সাপ্লাই দেওয়া ক্ষেত্রে এই Route কাজ করে। এক্ষেত্রেও ড্রাগ খুব দ্রুত কাজ করা শুরু করে কিন্তু একটা অসুবিধে হলো এই সিস্টেমে পেশীতে বেশ ব্যথা অনুভূত হয়।
জ. ইন্ট্রাভেনাস (Intravenous) রুট: যে Route ব্যবহার করে শরীরের রক্তনালী বা Vein এর মধ্যে ড্রাগ প্রয়োগ করলে সেটি শরীরের মধ্যে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেটিই Intravenous route বলে। অর্থাৎ যে route এর ফলে ড্রাগ একদম ঠিক জায়গায় ঠিকমত কাজ করে সেটাই Intravenous route. এটি প্রয়োগের সুবিধা হচ্ছে খুব দ্রুত এটি শরীরে কাজ করতে পারে। তবে এর একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে যদি ভুল জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয় তবে সেই জায়গা থেকে ড্রাগকে আর বের করে আনা যায় না এবং রোগী এক্ষেত্রে প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে। প্রধানত 1st & Quick Action এর জন্য শরীরে এই Route system ব্যবহার করে ড্রাগ প্রয়োগ করা হয়।
ঝ. ইন্ট্রা-আর্টিকুলার (Intra-articular) রুট: যেসব ড্রাগকে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে, দুটো হাড়ের সংযোগস্থলে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে Intraarticular Route বলে।
ঞ. ইন্ট্রা-আর্টারিয়াল (Intra-arterial) রুট: যেসব ড্রাগ আর্টারিতে সাপ্লাই দেওয়া হয় সেগুলো এই Route অনুসারে কাজ করে।
এছাড়া আরো একধরনের রুট হচ্ছে টপিক্যল রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন। টপিক্যাল ঔষধগুলো শরীরের ত্বক বা শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যেমন: ক্রিম, ফোম, জেল, লোশন, মলম প্রভৃতি। ডাক্তার বা নার্সরা হাসপাতালে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রুট ব্যবহার করলেও, পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে আমরা কেবলমাত্র মুখে খাওয়ার ঔষধ, টপিক্যাল এডমিনিস্ট্রেশন এবং সাব-কিউটেনিয়াস ইনজেকশন প্রভৃতি নিয়ে কাজ করবো।
১.১.৫ ঔষধের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ পথের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ
প্রধান প্রধান প্রয়োগ পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নীচে উল্লেখ করা হলো:
১) মুখে খাওয়া (Oral Route)
সুবিধা:
ক) নিরাপদ, সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং তুলনামূলকভাবে খরচ অনেক কম।
খ) সহজেই প্রয়োগ করা যায়। রোগী নিজে বা তার আত্মীয়স্বজন ঔষধ প্রয়োগ করতে পারে।
গ) সূঁচ ফোড়ানোর ভয় ও উদ্বেগ থাকে না এবং ব্যথা পাওয়া বা ব্যথা সহ্য করতে হয় না।
ঘ) এই পথে ব্যবহৃত ঔষধ ইনজেকশনের মত সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
অসুবিধা:
ক) অনেক সময় বমি হতে পারে এবং গৃহীত ঔষধ বেরিয়ে যেতে পারে।
খ) কিছু কিছু ঔষধ পাচক রস দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেজন্য দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৌছায় না।
গ) কিছু ঔষধ খাদ্যের সাথে মিশে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে যা সহজে বিশোষিত হতে পারে না।
ঘ) ডায়রিয়ার কারণে পর্যাপ্ত সময় অন্ত্রে না থাকার ফলে অনেক ঔষধ সম্পূর্ণরূপে বিশোষিত হতে পারে না।
ঙ) কিছু ঔষধ অন্ত্র থেকে মোটেই বিশোষিত হয় না।
চ) অন্ত্রে বিশোষিত হতে সময় লাগে তাই ইনজেকশনের তুলনায় মুখে খাওয়ার ঔষধ দেরীতে কাজ শুরু করে।
ছ) জরুরি অবস্থা, অজ্ঞান, মুখে খেতে চায়না ও অসহযোগী রোগীদের ক্ষেত্রে এই পথে ঔষধ প্রয়োগ উপযুক্ত নয়।
২) জিহ্বার নিচে (Sub-lingual Route)
এই পথে ঔষধ জিহ্বার নীচে রেখে আস্তে আস্তে গলতে দেওয়া হয়। জিহ্বার শ্লেষ্মা ঝিল্লীর মাধ্যমে এগুলো রক্ত স্রোতের সাথে মিশে যায় এবং খাওয়ার ঔষধের মত গিলতে হয় না এবং পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।
সুবিধা:
ক) অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিশোষিত হয়।
খ) চাহিদা অনুযায়ী ফল লাভের পর অবশিষ্ট ঔষধ ফেলে দেওয়া যায়।
অসুবিধা:
ক) যে সেকল ঔষধ স্বাদে অতৃপ্তিকর এই পথ সেসব ঔষধের জন্য উপযুক্ত নয়।
৩) ইনজেকশন (Injection)
সুবিধা:
ক) দ্রুত বিশোষিত হয়, যেহেতু পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় না।
খ) ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়।
গ) ঔষধের পরিমাণ শুদ্ধরূপে নিরূপন করা যায়।
ঘ) অজ্ঞান ও অসহযোগী রোগীদেরকে প্রয়োগ করা যায়।
ঙ) অতিরিক্ত বমির জন্য যে সব রোগী ঔষধ খেতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে এই পথে ঔষধ প্রয়োগ ফলদায়ক।
অসুবিধা/সাবধানতা:
ক) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থান জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে ও জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
খ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে ব্যথা ও এমনকি ফোঁড়া হতে পারে।
গ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে রক্তনালী বা স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। স্নায়ুর আঘাতের ফলে মাংসপেশী দুর্বল ও অবশ হতে পারে ।
ঘ) নিজে নিজে প্রয়োগ করা উচিত নয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন হয়।
ঙ) মাংসপেশীতে দেবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দেওয়া উচিত নয়।
১.১.৬ ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
সকাল থেকে গা-হাত-পায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথাটাও ঝিম ঝিম করছে। তাই তড়িঘড়ি করে একটি পেন কিলার খেয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আর এভাবে চলতে চলতে তৈরি হল পেইন কিলার অ্যাডিকশন। জ্বর হলে না জেনে বুঝে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া, ব্যথা হলে যখন তখন পেইন কিলার খাওয়া, এসিড হলে মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড খাওয়া এগুলো তো রোজকার রুটিন। কিন্তু কেউ যে কিছু না ভেবেই অ্যান্টিবায়োটিক, পেইন কিলার বা অন্য কোনো ওষুধ খেয়ে ফেলে, এতে কিন্তু সমস্যা আছে। যেমন: এলার্জিক রিয়েকশন ও এনাফাইলেকটিক শক। তাই জেনে রাখ বভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে।
ড্রাগ ওভারডোজ
১। অনেকে ভাবেন, কড়া ডোজে বেশি ওষুধ খেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। ওষুধ না জেনে খাওয়ার ফলে রোগী ছটফট করতে থাকেন, বুক ধড়ফড় করে, ঘাম হয়, ব্লাড প্রেশার ওঠানামা করে, হার্টবিটও কম-বেশি হয়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। এক একটি ওষুধের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া একেক রকম। তাই একে অপরের সাথে গুলোয়ে ফেলা উচিত নয়।
২। ড্রাগ ওভারডোজ বাড়াবাড়ি রকমের হলে, দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি কড়া প্রয়োজন। স্যালাইনও দিতে হতে পারে। আর যদি বার বার ড্রাগ ওভারডোজ হয়, তাহলে মনোবিদের সাহায্য নিয়ে কাউন্সেলিং করাও।
৩। প্রেগনেন্সির সময় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না। অন্যথা গর্ভস্থ সন্তানের হার্টের সমস্যা, স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা, জন্ডিস, ব্লাড সুগার কমে যাওয়া, ইত্যাদি নানা রকমের অসুখ হতে পারে।
১.১.৭ ঔষধের মাত্রা ও প্রচলিত শব্দ
ঔষধের মাত্রা (Drug Dosage )
ঔষধের মাত্রা বলতে বুঝায় কি পরিমাণ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে তার পরিমাণ কে। ঔষধের মাত্রা সাধারণভাবে নিচের এককগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
ক. ওজন- গ্রাম (gm) বা মিলিগ্রাম (mg)
খ. পরিমাণ (Volume)- মিলিলিটার (ml) বা কিউবিক সেন্টিমিটার (cc)
গ. ইউনিট (Unit).
ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রভাবিত করে:
১। দেহের ওজন - রোগীর ওজন যত কম হবে ঔষধের মাত্রাও তত কম হবে।
২। প্রয়োগের পথ - ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুলের তুলনায় ইনজেকশনের মাত্রা কম হয়।
৩। রোগের তীব্রতা - কখনও কখনও অসুখের তীব্রতা বেশী হলে বেশী মাত্রায় ঔষধ দরকার হয়।
৪। প্রয়োগের ব্যবধান - একই ঔষধ কম ব্যবধানে ব্যবহার করলে বেশী ব্যবধানের চেয়ে মাত্রা কম দরকার হয়।
৫। গর্ভাবস্থা - অনেক ঔষধ গর্ভাবস্থায় কম মাত্রায় দেওয়া হয়।
১.১.৮ ঔষধ খাওয়ানোর নিয়মাবলি
রোগ হলে সুস্থ হওয়ার জন্য ওষুধ সেবন করতে হয়। কোনো ওষুধই নিজে নিজে খাওয়া ঠিক নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে লিখিত প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে ওষুধ সেবন করা জরুরি। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কেয়ারগিভিং কাজে রোগীকে প্রায়ঃশই ঔষধ খাইয়ে থাকেন অথবা ঔষধ খাওয়াতে সহযোগীতা করে থাকেন। তবে ওষুধ সেবনের সময় কিছু ভুলের কারণে এর সম্পূর্ণ উপকারিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এসব ভুলের কারণে পরবর্তীকালে রোগীর শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এমনকি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ঔষধ খাওয়ানোর সাধারণ কিছু নিয়মাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:
- শুরুতে ওষুধ খাওয়ার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া উচিত। রোগী হাতে ওষুধ খেতে অক্ষম হলে, সেক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। কারণ, আমাদের শরীরের প্রায় সকল রোগই ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্যারাসাইট ইত্যাদির জন্য হয়ে থাকে। আর হাত পরিস্কার না করে ওষুধ খেলে ওই জীবানু আরো বেশি করে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- এবার চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষধের সাথে ফার্মেসি থেকে কিনে নিয়ে আসা ঔষধ ভালোভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। মিল না থাকলে সে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ ভুল ওষুধ মৃত্যু ঢেকে আনতে পারে। প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।
- এবার দেখতে হবে ওষুধের মেয়াদ আছে কিনা! ওষুধের মোড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেওয়া থাকে। মেয়াদবিহীন ওষুধ বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
- ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক সঠিক রুটের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ঔষধ খাওয়াতে হবে। যেমন, কোন ঔষধ খাবার আগে খেতে বলা হয়, আবার কোনটি বলা হয় খাবার পরে। এই সমস্ত নির্দেশনা সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে সুস্পষ্টভাবে লিখা থাকে। কেয়ারগিভারকে সেই সমস্ত নির্দেশনা ভালোমত পড়ে, বুঝে অনুসরণ করতে হবে।
ঔষধ খাওয়ানোর ছয়টি বিষয়:
১. সঠিক রোগী বা ব্যক্তি: রোগীর নাম, বয়স, রোগ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সাথে মিলিয়ে সঠিক রোগীকে সনাক্ত করতে হবে।
২. সঠিক ওষধ: ঔষধের নাম, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ডোজ, রুট, অন্যান্য নির্দেশন যাচাই করে সঠিক ঔষধ সনাক্ত করা ।
৩. সঠিক ডোজ বা পরিমাণ: সঠিক পরিমানের ঔষধ নিতে হবে।
৪. সঠিক রুট: ডাক্তার যেভাবে ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য প্রেসক্রিপশনে লিখেছেন সেই রুট নির্ধারণ করা।
৫. সঠিক সময়: নির্ধারিত সময়ে ঔষধ খাওয়ানো ।
৬. সঠিকভাবে রেকর্ড করা: সমস্ত কাজ সমাপ্ত হবার পর সঠিকভাবে রেকর্ড শীটে রেকর্ড করা।
পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ভালোভাবে বুঝে তারপর ঔষধ খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে কোনপ্রকার ভুল করা যাবেনা। কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ডাক্তার, নার্স বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ডাক্তাররা সাধারণত কোন ঔষধ কখন ও কিভাবে খেতে হবে তা কিছু সংক্ষেপিত শব্দ দিয়ে লিখে থাকেন। যেমন :
- bid- দিনে ২বার। অর্থাৎ ১২ ঘন্টা পর পর ।
- tid- দিনে ৩বার। অর্থাৎ ৮ ঘন্টা পর পর।
- qid - দিনে ৪ বার। অর্থাৎ ৬ ঘন্টা পর পর।
- hs- রাতে শুবার সময়।
- ac- খাবার আগে
- pc- খাবার পরে
- NPO- মুখে কোন কিছু খাওয়া যাবে না ইত্যাদি।
সকল ধরনের ওষুধ ডাক্তারদের পরামর্শে অনুযায়ী সঠিক সময় মত রোগীকে সেবন করাতে হবে।
১.২ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ও ইনসুলিন প্রদান
আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, রক্ত আমাদের শরীরের অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যন্তরীণ পরিবহন মাধ্যম। এটি বাহিত হয় শিরা বা ধমনীর মধ্য দিয়ে। রক্ত দেহের প্রতিটি টিস্যুতে পৌঁছে দেয় খাবার ও অক্সিজেন। টিস্যুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোধের জন্য এ খাবার ও অক্সিজেন অপরিহার্য। এছাড়া দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হরমোন রক্তের মাধ্যমেই পৌঁছে যায় অগ-প্রত্যশে নিশ্চিত করে ওই অরে কর্মক্ষমতাকে। এমনই একটি হরমোনের নাম হচ্ছে ইনসুলিন। ইনসুলিন একটি প্রোটিনধর্মী হরমোন। এটি দেহের অপ্রয়োজনীয় গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে দেহকে সঠিক পরিমাণের গ্লুকোজ সরবরাহে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণ এই হরমোনটি তৈরি হয় দেহের প্যানক্রিয়াস নামের অঙ্গে। বাংলায় প্যানক্রিয়াসকে বলে অগ্ন্যাশয়। এই শিখনফলে আমরা রক্তের গ্লুকোজের নরমাল ফ্যাল্যু, এর তাৎপর্য, বহুমূত্র রোগ এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবো। ইনসুলিন পরিমাপ করার পাশাপাশি ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী বহুমূত্র রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট কার্যীৰগীও আমরা এই শিখন ফলে অনুশীলন করব।
১.২.১ রক্তের গ্লুকোজ ও এর স্বাভাবিক মাত্রা
শর্করা মানবদেহের শক্তির ফুল জোগানদাতা। শর্করা ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ বা চিনি। আমরা যখন শর্করা জাতীয় খাবার খাই, সেটি যে খাবারই হোক, যে পরিমাণই হোক, শরীরে সেই খাবার গ্লুকোজ হিসেবেই জমা হয়। শরীরের স্বাভাবিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য এই গ্লুকোজের নিয়মিত ভার্শন বা নিয়ন্ত্রন অতীব জরুরি, যে কাজটি করে থাকে ইনসুলিন নামক হরমোন যেটি নিঃসৃত হয় অগ্নাশয়ের আইলেট্স অব লেঙ্গারহেন্ স থেকে। রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ না করলে হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও দৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো জটিলতার ঝুঁকি রয়েছে। মানবদেহে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ নিম্নরুপ:
খাওয়ার আগে প্রতি লিটার রক্তে ৩.৯-৫.৬ মিলিমোল এবং খাওয়ার ২ ঘন্টা পর ৭.৮ মিলিমোলের নি গ্লুকোজের মাত্রা থাকলে তাকে স্বাভাবিক বলা যায়। এর বেশি হলেই কোনো ব্যক্তির ডায়াবেটিস আছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে বয়স, অন্যান্য অসুখ, ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা, গর্ভাবস্থা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে রক্তে গ্লুকোজের লক্ষ্যমাত্রা ভিন্নতর হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। কোনো কোনো গ্লুকোমিটার মিলিগ্রাম এককে গ্লুকোজের ফলাফল দেয়, এ ক্ষেত্রে এই মাত্রাকে ১৮ দিয়ে ভাগ করলে মিলিমোল এককে ফলাফল পাওয়া যাবে।
নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা
সুস্থ্য বা অসুস্থ্য যেকোনো বয়সের মানুষের জন্যই নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে অন্তত একদিন অবশ্যই রক্তের গ্লুকোজ মেপে দেখা উচিত। আর ডায়াবেটিক বা বহুমূত্র রোগীর জন্য ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রক্তের এ পরীক্ষা দিনের বিভিন্ন সময়ে করতে হতে পারে যেমন: সকালে খালি পেটে, নাশতার দুই ঘণ্টা পরে, দুপুরে খাওয়ার আগে ও পরে, রাতে খাওয়ার আগে ও পরে প্রভৃতি। রোগী যদি নিজে নিজে করতে সক্ষম না হয়, গ্লুকোমিটার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান বা কেয়ারগিভার খুব সহজেই এই পরীক্ষাটি করতে পারে। প্রাপ্ত ফলাফল ভালোভাবে রেকর্ড করে ডাক্তার বা নার্সকে রিপোর্ট করতে হয়।
রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতি :
রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য জরুরি। এই জরুরি কাজটিই কেবলমাত্র এক ফোঁটা রক্ত ব্যবহার করে তাতক্ষনিকভাবেই সম্পাদন করা যায়। সে জন্য প্রয়োজন হয় গ্লুকোমিটার নামক একটি যন্ত্র। গ্লুকোমিটার থাকলে সহজে ঘরে বসে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই কাজটি করতে পারেন। যন্ত্রটি হাতের কাছে রাখা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে বিভিন্ন নামে গ্লুকোমিটার পাওয়া যায়। সকল গ্লুকোমিটারের ক্ষেত্রেই রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করার পদ্ধতি একই রকম। নিচে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:
১। প্রথমেই কেয়ারগিভারকে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে। রোগীকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করবে এবং তার অনুমতি গ্রহণ করবে।
২। গ্লুকোমিটারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কার্যকারিতা যাচাই করে নিতে হবে। সুঁই বা নীডল লেনসেট পেনে ঠিকভাবে লাগিয়ে নিতে হবে।
৩। রোগীর যে আঙুল থেকে রক্ত নেয়া হবে সেটি নির্বাচন করতে হবে। অ্যালকোহল প্যাড বা জীবাণুনাশক দিয়ে আঙুলের মাথা পরিষ্কার করে নিয়ে পুরোপুরি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
৪। গ্লুকোমিটারে একটি পরীক্ষার স্ট্রিপ প্রবেশ করাতে হবে। গ্লুকোমিটারের মডেলভেদে স্ট্রিপ আলাদা হয়, তাই শুধু তোমার মিটারের জন্য নির্দিষ্ট স্ট্রিপ ব্যবহার কর। নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ স্ট্রিপ ব্যবহার করা যাবেনা, এতে ভুল ফলাফল আসতে পারে। স্ট্রিপের কৌটা খোলার পর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়ে নির্দেশিকায় লেখা তথ্য অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক গ্লুকোমিটারে স্ট্রিপ প্রবেশ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা চালু হয়ে যায়।
৫। সুই বা ল্যানসেট (যা একটি কলমের মধ্যে থাকে) দিয়ে রোগীর হাতের আঙুলের অগ্রভাগ ফুটো করতে হবে। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন আঙুল ব্যবহার করা উচিৎ। স্বতঃস্ফুর্তভাবে বের হয়ে আসা বড় এক ফোঁটা রক্তই যথেষ্ট।
৬। রক্তের ফোঁটা পরীক্ষার স্ট্রিপের নির্দিষ্ট জায়গায় স্পর্শ ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ গ্লুকোমিটারভেদে ভিন্ন (০.৩ থেকে ১ মাইক্রো লিটার) হতে পারে। খুব কম বা ছোট রক্ত হলে মিটারে কোনো ফলাফল নাও আসতে পারে। রক্ত নির্দিষ্ট সেনসরে লাগলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোষিত হয় এবং মিটারটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পর্দায় প্রদর্শন করবে।
৭। তারিখ ও সময় দিয়ে প্রাপ্ত ফলাফল রেকর্ড করে রাখতে হবে এবং ব্যবহৃত সুই এবং স্ট্রিপ নির্দিষ্ট ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র গুছিয়ে রাখতে হবে।
চিকিৎসককে রিপোর্ট করার সময় গ্লুকোজের রেকর্ড চার্ট সরবরাহ করতে হবে, যাতে রেকর্ড করা গ্লুকোজের মাত্রা দেখে ডাক্তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
১.২.২ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ অথবা ডায়াবেটিস মেলিটাস (ইংরেজিতে Diabetes mellitus) একটি হরমোন সংশ্লিষ্ট রোগ। দেহে অগ্ন্যাশয় যদি যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ হয় তাকে ‘ডায়াবেটিস' বা ‘বহুমূত্র রোগ’। একে মধুমেহ রোগও বলা হয়ে থাকে। এসময় রক্তে চিনি বা শর্করার অতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে কিছু অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, যেমন- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বার বার ক্ষুধা পাওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা লাগা ইত্যাদি। ইনসুলিনের ঘাটতিই হল এ রোগের মূল কথা। ইনসুলিন হল অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন, যার সহায়তায় দেহের কোষগুলো রক্ত থেকে গ্লুকোজকে নিতে সমর্থ হয় এবং একে শক্তির জন্য ব্যবহার করতে পারে। ইনসুলিন উৎপাদন বা ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা-এর যেকোনো একটি বা দুটোই যদি না হয়, তাহলে রক্তে বাড়তে থাকে গ্লুকোজ। আর একে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ঘটে নানা রকম জটিলতা, দেহের টিস্যু ও বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হতে থাকে।
প্রকারভেদ:
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ টাইপ ওয়ান (টাইপ-১) ডায়াবেটিস ও টাইপ টু (টাইপ-২) ডায়াবেটিস। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শরীরে তখন গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে এর কারণ খুজে বের করতে পারেনি। তবে বিশ্বাস করা হয় যে এর পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে অথবা অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও এমনটি হতে পারে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের শতকরা ১০ শতাংশ এই টাইপ ওয়ানে আক্রান্ত। অন্যদিকে টাইপ টু ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন উৎপন্ন হয়না অথবা এই হরমোনটি ঠিক মতো কাজ করে না। সাধারণত মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ ব্যক্তিরা টাইপ টু ডায়াবেটিসে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও যাদের ওজন বেশি এবং যাদেরকে বেশিরভাগ সময় বসে বসে কাজ করতে হয় তাদেরও এই ধরনের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ এর সাধারণ লক্ষণসমূহ
- ঘন ঘন ক্ষুধা পাওয়া
- অল্প কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া
- শরীরে এনার্জির অভাব বোধ করা
- প্রচুর পরিমাণে এবং ঘন ঘন পানির পিপাসা পাওয়া
- ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া
- হঠাৎ করে ওজন খুব বেড়ে যাওয়া বা খুব কমে যাওয়া
- চোখের ঝাপসা দেখা।
- জিভ শুকিয়ে যাওয়া
- গা চুলকানো, কেটে যাওয়া ক্ষত শুকোতে বেশি সময় নেয়া
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের কারণসমূহ
যে কেউ যে কোনো বয়সে যেকোনো সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে-
- যাদের বংশে বিশেষ করে বাবা-মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।
- যাদের ওজন অনেক বেশি ও যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করেন না।
- যারা বহুদিন ধরে কর্টিসোল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন।
- যেসব মহিলার গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ছিল বা যাদের পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রম থাকে।
- যাদের রক্তচাপ আছে এবং রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকে।
ডায়াবেটিস-সংক্রান্ত জটিলতা
ডায়াবেটিস এর কারণে ধীরে ধীরে দেহে বিভিন্নরকম জটিলতা দেখা দেয়, যত দীর্ঘ সময় ধরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত থাকে জটিলতা তত বাড়তে থাকে। যা কখনো কখনো মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যে হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, কিডনিজনিত সমস্যা বা কিডনি ফেইলিওর, চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং তা থেকে অন্ধত্ব ইত্যাদি সমস্যা অন্যতম। এছাড়াও ডায়েবেটিক ফুট বা পায়ের আলসার ও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আরেক আতংক, এর ফলে অনেক সময় রোগীর পাও কেটে ফেলতে হতে পারে। চর্মরোগ, শ্রবণজনিত সমস্যা, বিষণ্নতা ইত্যাদিও হতে পারে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হুট করে কমে গেলেও বিপদ হতে পারে। আবার হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রাধিক্যতায় রোগী ডায়াবেটিক কোমায় (অজ্ঞান) চলে যেতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম, মাথা ঘোরা, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, খিঁচুনি এমনকি এ থেকে অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে যদি সঠিক সময়ের মধ্যে তা ঠিক না করা হয়।
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের প্রতিরোধ
ডায়াবেটিস প্রতিরোধ-এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু করণীয় নিম্নরূপ:
- কায়িক শ্রম ও নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা যা ওজন ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
- খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার রাখা যেমন ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি ।
- শস্যদানা যেমন গম, ভুট্টা, বার্লি ইত্যাদি বা এসব থেকে তৈরি খাবার যেমন ব্রেড বা পাস্তাজাতীয় খাবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। এটি শুধু ডায়াবেটিস নয়, অন্য আরো অনেক ধরনের রোগ যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- খাদ্য তালিকা থেকে শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া বা খুব অল্প পরিমাণে রাখা।
এগুলো মেনে চলা ছাড়াও যাদের পরিবারে বা রক্তের সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়দের মাঝে ডায়াবেটিস আছে তারা ৪৫ বছর বয়সের পর নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে পারেন। এছাড়াও ৪৫ বছর বয়সের আগেও যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে তবে সেই ব্যক্তিও পরীক্ষা করাতে পারেন।
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগীর ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই ডায়াবেটিস এখন এক মহামারী রোগ। মাত্র কয়েক দশক আগেও এটি ছিল খুব স্বল্প পরিচিত রোগ। অথচ বর্তমানে শুধু উন্নত বিশ্বেই নয়, বরং উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত বিশ্বেও অসংক্রামক ব্যাধির তালিকায় ডায়াবেটিস অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৭৯ লাখ ৫০ হাজার এবং প্রতি বছর গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ নতুন করে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্থূলতা বা ওজন বৃদ্ধি, মেদবাহুল্য, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, মানসিক চাপ, ধূমপান ইত্যাদির কারণে এ রোগে আক্রান্তের হার বাড়ছে। এ ছাড়াও অনিয়িমিত জীবনযাপন, দ্রুত নগরায়ন এবং পাশাপাশি উচ্চ শর্করা এবং কম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। বংশগত কারণেও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। কোন ধরনের ডায়াবেটিস তার উপর নির্ভর করে নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়, মুখে খাওয়ার ঔষধ, ইনসুলিন ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়েট মেনে চলা এবং নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা ডায়াবেটিস চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার যুক্ত করা এবং চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার ত্যাগ করা জরুরি। প্রতিবেলায় একবারে বেশি করে না খেয়ে বারে বারে অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করতে ডায়াবেটিস রোগীদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি ‘ডি’ মেনে চলা জরুরি। যেমন- ডায়েট, ডিসিপ্লিন এবং ড্রাগ। ডায়াবেটিক রোগীর খাদ্যাভ্যাসে কিছু সাধারণ নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত, যেমন-
- তিনবেলার খাবার ছয়বারে ভাগ করে খেতে হবে এবং কোনো বেলার খাবারই বাদ দেওয়া যাবে না।
- চর্বিজাতীয় খাবার কম গ্রহণ এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্য পরিহার করতে হবে।
- ওজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা মেনে চলতে হবে।
- খাবার খেতে অসুবিধা হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করে ঔষুধ সমন্বয় করে নিতে হবে।
- প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
ডায়াবেটিস রোগীর ব্যায়াম
ডায়াবেটিস রোগীরা সাধারণত শারীরিকভাবে সক্ষম হলে নিয়মিত হাঁটা, জগিং, ব্যায়াম ইত্যাদি করতে পারেন। ব্যায়াম রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে হাঁটা। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট করে হাঁটতে হবে। দিনের যেকোনো সময় হাঁটা যায়। এ ছাড়া ট্রেডমিলে হাঁটা বা দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইক্লিং, দড়িলাফ ইত্যাদি হাঁটার বিকল্প ব্যায়াম হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই কাজগুলো করা সক্ষম হয়না। তখন পরোক্ষ উপায়ে ব্যক্তিটিকে কিছুটা নড়া-চড়া করানো যেতে পারে। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই কাজগুলো করতে হয় ।
১.২.৩ ইনসুলিন প্রদান
ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইনসুলিন একটি প্রধানতম চিকিৎসা। বিভিন্ন ধরনের ইনসুলিন বাজারে পাওয়া যায়। রাসায়নিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে কোনোটিকে স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি, আবার কোনোটিকে দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সারা দিনের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা। এসব ইনসুলিন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীর সঙ্গে আলোচনা করে তার জন্য উপযোগী নির্দিষ্ট মাত্রা – দিনে দুই, তিন ও চারবার, আবার অনেক ক্ষেত্রে দুই ধরনের ইনসুলিনই নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সাধারণত যখন মুখে খাওয়ার ঔষধ রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, তখনই কেবল ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন রোগীর শরীরে দেওয়া হয়ে থাকে।
ইনসুলিন কি?
ইনসুলিন আমাদের দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পাকস্থলীর পেছনে থাকা অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস নামের একটি গ্রন্থি থেকে এটি তৈরি হয়। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজ অর্থাৎ সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ডায়াবেটিস হলে দেহে সুগার নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত তিনভাবে ঘটতে পারে—
১. শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি না হয়ে
২. পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হয়েও সেটি সঠিকভাবে কাজ না করলে। একে ‘ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বলা হয়
৩. শরীরে ইনসুলিন তৈরি হওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে
ইনসুলিন প্রোটিনজাতীয় একটি হরমোন। মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করা হলে অন্যান্য প্রোটিনের মতো এটিও হজম প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায়। ফলে রক্তপ্রবাহে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে না। তাই এটি ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুল হিসেবে সেবন করা যায় না। ইনসুলিন যেন রক্তপ্রবাহে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে সেটি নিশ্চিত করার জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। রোগীর ডায়াবেটিসের ধরন এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী ডাক্তার ইনসুলিনের ধরন ও ডোজ নির্ধারণ করে দিবেন।
ইনসুলিন নেওয়ার পদ্ধতি
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেক রোগীকেই রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইনসুলিন নিতে হয়। কিছু সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে অনেকে শরীরের ভুল স্থানে ভুল ডোজে ইনসুলিন নিয়ে ফেলেন। একারণে একদিকে রক্তের সুগার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে চামড়া শক্ত হয়ে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। এই অনুচ্ছেদে ইনসুলিন সিরিঞ্জ ও ইনসুলিন পেনের সাহায্যে ইনসুলিন নেওয়ার উপায় তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে রোগী নিজেই সহজ ও সঠিকভাবে ইনসুলিন নিতে পারবেন। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানও রোগীকে সঠিকভাবে ইনসুলিন প্রদান করতে পারবে।
ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:
১. ইনসুলিন: বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক ইনসুলিন।
২. ইনসুলিন সিরিঞ্জ অথবা ইনসুলিন পেন: ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সিরিঞ্জ অথবা পেন – যেকোনো একটি ব্যবহার করা যায়।
- ইনসুলিন সিরিঞ্জঃ এই বিশেষ সিরিঞ্জগুলো বিভিন্ন সাইজের হতে পারে। ইনসুলিনের ধরনভেদে নির্দিষ্ট সাইজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয়। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সিরিজে ইনসুলিন নিয়ে এরপরে ইনজেকশনটি করতে হয়৷
- ইনসুলিন পেন বা কলম: এটি দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যাতে আে থেকেই ইনসুলিন ভরা থাকে। কলমের ভেতরের ইনসুলিন শেষ হয়ে গেলে কলমটি ফেলে দিতে হয়। আরেক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যেটির ভায়াল অথবা কার্তুজ (কার্টিজ) পরিবর্তন করে বারবার ব্যবহার করা যায়।
এসব কলমের সাথে আলাদাভাবে সুই ব্যবহার করতে হয়। সুইগুলো কেবল একবার ব্যবহার করা যায়। এসব সুঁইকে কেবল ত্বকের নিচে বা সাব-কিউটেনিয়াস উপায়ে দিতে হয়— পেশী অথবা শিরার মধ্য দিয়ে দিতে হয় না। বলে এগুলো বেশ ছোটো ও সরু হয়।
৩. ধারালো বস্তু ফেলার নির্দিষ্ট স্থান: হোম কেয়ার সেটিংসে ধারালো বন্ধু ফেলার জন্য একটি ঝুড়ি নির্দিষ্ট করে রাখা যেতে পারে যেখানে ব্যবহৃত সুইটি নিরাপদে ফেলে দেওয়া যাবে। হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন রঙের কন্টেইনার থাকে। সেক্ষেত্রে লাল রঙের কন্টেইনারে ব্যবহৃত সুইটি ফেলতে হবে।
ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার নিয়ম
আটটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে রোগী নিজেই ঘরে বসে ইনসুলিন সিরিঞ্জ এর সাহায্যে ইনসুলিন নিতে পারেন। আবার একই ধাপ অনুসরণ করে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানও ইনসুলিন প্রদান করতে পারে। ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—
ধাপ ১: হাত ভালোভাবে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
ধাপ ২: ইনজেকশনটি শরীরের কোন জায়গায় দেওয়া হবে সেটি ঠিক করে নিতে হবে। ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো শরীরের চর্বিযুক্ত স্থান। যেমন: তলপেট (নাভির নিচের অংশ), উরু অথবা নিতম্ব প্রভৃতি স্থান। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। আগে যেখানে ইনসুলিন নেয়া হয়েছে তার থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। একই জায়গায় বারবার ইনজেকশন দিলে ওই জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যেতে পারে—যা পরবর্তীতে ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিতে পারে।
ধাপ ৩: ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ইনসুলিনটি বেছে দাও। ইনসুলিনের মেয়াদ আছে কি না সেটি বোতলের গায়ে লেখা তারিখ থেকে জেনে নাও। ইনসুলিন ব্যবহারের পূর্বে সাধারণত বোতল বা ভায়াল ঝাঁকিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে ঘোলা প্রকৃতির ইনসুলিন ব্যবহারের পূর্বে ইনসুলিন পুরোপুরি মিশে যাওয়া পর্যন্ত ভায়ালটি দুই হাতের তালুর মাঝে রেখে আলতো করে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের প্যাকেটে থাকা নির্দেশনাটি ভালোমতো পড়ে নিতে হবে।
ধাপ ৪: ইনসুলিন সিরিঞ্জটি মোড়ক থেকে বের করে ওপরের ক্যাপটি খুলে নাও। সিরিঞ্জটি খাড়া করে ধর। এবার সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বা দণ্ড টেনে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যত ইউনিট ইনসুলিন নিতে হবে ততটুকু (তত cc বা ml) বাতাস সিরিঞ্জে প্রবেশ করাও। ইনসুলিনের ধরনভেদে নির্দিষ্ট সাইজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয়। তা নাহলে ভুল ডোজে ইনসুলিন নেওয়ার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইনসুলিন নেওয়ার সময়ে ইউনিট অনুযায়ী উপযুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। ডাক্তারের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।
ধাপ ৫: ইনসুলিনের ভায়ালটি খাড়া করে ধরে বোতলের ভেতরে সিরিঞ্জের সুঁইটি পুরোপুরি ঢুকিয়ে দাও । এরপর সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বা দণ্ড চেপে সিরিঞ্জের ভেতরে থাকা বাতাস ভায়ালে ঢুকিয়ে দাও। এতে করে সিরিঞ্জে ইনসুলিন তুলতে সুবিধা হবে। এবার ভায়ালটি উল্টো করে ধরে নির্ধারিত ইউনিটের চেয়ে সামান্য বেশি ইনসুলিন সিরিঞ্জে টেনে নাও। খেয়াল রাখবে ভায়ালের ভেতরে সুঁইয়ের মাথার চারিদিকে যেন ইনসুলিন থাকে এবং কোনো বাতাস না থাকে।
ধাপ ৬: এরপর এমনভাবে সিরিঞ্জটি ধর যেন সুঁই ওপরে ও প্লাঞ্জার নিচে থাকে। সিরিঞ্জের গায়ে আলতো করে কয়েকটি টোকা দাও যেন ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা ওপরের দিকে উঠে আসে। এবার যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ সিরিঞ্জের নিচের দিকে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দিন। এই কাজটিকে বলা হয় ‘প্রাইমিং’। সুঁই ও সিরিঞ্জের ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা এই পদ্ধতিতে বের করা যায়। ফলে ডোজ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। এভাবে সিরিঞ্জে যেন কেবল নির্ধারিত ডোজের ইনসুলিন থাকে সেটি নিশ্চিত কর।
ধাপ ৭: যেখানে ইনজেকশনটি নিবে সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না সেটি নিশ্চিত কর। এক্ষেত্রে এলকোহল সোয়াব ব্যবহার করা যেতে পাড়ে। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বক আস্তে চিমটি দিয়ে উঠিয়ে নিতে পার। এবার সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুইটি শরীরে পুরোপুরি প্রবেশ করাও। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো সিরিঞ্জ খালি না হয় ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখ।
ধাপ ৮: সুঁইটি বের করে ফেলার আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায় সেজন্য এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনে নাও। ত্বকে চিমটি দিয়ে রাখলে তা সরিয়ে নাও। এবার সুইটি বের করে ফেল। অবশেষে সুইসহ সিরিঞ্জটি নিরাপদ স্থানে ফেলে দাও।
ইনসুলিন পেন বা কলম দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার নিয়ম
ইনসুলিন পেন এর সাহায্যে সাতটি সহজ ধাপে ইনসুলিন নেওয়া যায়। ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—
ধাপ ১: হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
ধাপ ২: ইনজেকশনটি শরীরের কোন জায়গায় দিবে সেটি ঠিক কর। ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো শরীরের চর্বিযুক্ত স্থান। যেমন: তলপেট (নাভির নিচের অংশ), উরু অথবা নিতম্ব। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ইনজেকশন নেওয়া উচিত। আগে যেখানে ইনসুলিন নেওয়া হয়েছে তার থেকে থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। একই জায়গায় বারবার ইনজেকশন দিলে ওই জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যেতে পারে—যা পরবর্তীতে ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিবে।
ধাপ ৩: ইনসুলিন পেন এর বাইরের ও ভেতরের ক্যাপ খুলে এতে সুঁইটি লাগিয়ে নাও। ডায়াল ঘুরিয়ে দুই ইউনিটে নিয়ে আসুন। এরপর পেনটিকে সোজা করে ধর। যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ পেনের পেছনে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দাও। এই কাজটিকে বলা হয় ‘প্রাইমিং’। সুঁই ও ইনসুলিন ভায়াল বা কার্তুজের ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা এই পদ্ধতিতে বের করা যায়, ফলে ডোজ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
ধাপ ৪: এবার ডায়াল ঘুরিয়ে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডোজটি বাছাই কর। যেখানে ইনজেকশনটি নিবে সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না তা নিশ্চিত কর।
ধাপ ৫: সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুইটি শরীরে প্রবেশ করাও। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বক আস্তে চিমটি দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ডায়ালটি জিরোতে (০) ফেরত না যায়, ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখ।
ধাপ ৬: সুইটি সরানোর আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায়, সেজন্য ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনে নাও। ত্বকে চিমটি দিয়ে রাখলে তা সরিয়ে নাও ।
ধাপ ৭: সুঁইটি সরিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলে দাও।
ইনসুলিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: অনেকেই ইনসুলিন ইনজেকশন শুরু করার আগে এটি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কারও কারও সুঁই দেখে ভয় লাগতে পারে, কেউ কেউ অস্থির বোধ করতে পারে, ব্যথা নিয়ে চিন্তিত হতে পারে—এমনকি অনেকে অন্যদের সামনে ইনজেকশন নিতে লজ্জা অথবা ভয় পেতে পারে। এই ধরনের অনুভূতি হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দায়িত্ব হচ্ছে রোগীকে সঠিকভাবে কাউন্সেলিং করা। পরিচিত কোনো আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী অথবা প্রতিবেশী যদি ইনসুলিন ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাদের সাথেও এই ব্যাপারে রোগীকে কথা বলানো যেতে পারে। ডায়াবেটিস ও ইনসুলিন নিয়ে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, তাই এসব আলোচনা থেকে রোগী তার নিজের জন্য উপযোগী কিছু পরামর্শ পেতে পারে। অন্যান্য ঔষধের মতোই ইনসুলিন নিলে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন:
- মাথাব্যথা, বমি বমি লাগা, সর্দিজ্বর অথবা ফ্লু এর মতো লক্ষণ
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া: ইনসুলিনের সবচেয়ে কমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া। রক্তে গ্লুকোজ তথা সুগারের পরিমাণ ন্যূনতম স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অনেকে একে সংক্ষেপে ‘হাইপো' হিসেবে চেনেন। মূলত ইনসুলিন নিতে হয় এমন ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ইনসুলিন নিলে অথবা ইনসুলিন নেওয়ার পরে খাবার না খেলে এই অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ঘন ঘন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ভুল ডোজে ইনসুলিন নেওয়া। তাই এমন ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে কথা বলে সঠিক ডোজ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।
- ইনজেকশনের জায়গায় কালশিটে দাগ পড়া: ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার সময়ে চামড়ার নিচের কোনো ছোটো রক্তনালিকায় আঘাত লাগলে তা থেকে ত্বকে কালশিটে দাগ পড়তে পারে। যারা নিয়মিত ইনসুলিন নেয় তাদের ইনজেকশন নেওয়ার পদ্ধতিতে ত্রুটি না থাকলেও, কখনো কখনো এমন কালশিটে হতে পারে। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ইনসুলিন দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং রোগীকেও সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল সুঁইয়ের সাইজ পরিবর্তন করে অথবা প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার পরে ব্যবহৃত সুই পরিবর্তন করে এমন কালশিটে দাগ পড়া কমিয়ে আনা যায়।
- ইনজেকশনের জায়গা ফুলে যাওয়া: একই জায়গায় বারবার ইনসুলিন নেওয়া হলে জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যায়। একে মেডিকেলের ভাষায় ‘লাইপো-হাইপারট্রফি' বা সংক্ষেপে ‘লাইপো’ বলা হয়। এমন ফোলা ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। তাই প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বেছে নিতে হবে। আগেরবার যেখানে ইনসুলিন নেওয়া হয়েছে সেটি থেকে অন্তত এক সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। বেশ কিছুদিন পার হওয়ার পরেও ‘লাইপো’ বা ফোলা সেরে না উঠলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
১.৩ স্যাম্পল কালেকশন বা নতুনা সংগ্ৰহ
আমরা জানি যে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমেই একজন সুস্থ অথবা অসুস্থ রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সঠিক রোগ নির্ণয় বা ডায়গনসিস এবং চিকিৎসার সিদ্ধান্তগুলো আংশিকভাবে এই পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। তাই সঠিক ফলাফলের জন্য যথাযথভাবে রোগীকে প্রভুতকরন, নমুনা সংগ্রহ এবং পদ্ধতি হল একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই যে সমস্ত সেটিংসে নানা ধরনের নমুনাগুলো সংগ্রহ করা হয় সে সমস্ত জায়গায় দায়িত্বে থাকা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের বর্তমান প্রচলিত জীৰাণুমুক্ত কৌশলগুলো অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। যেমন, সুঁচ, সিরিঞ্জ, ক্যাথেটার, কলোস্টমি ব্যাগ, বাটারফ্লাই নিডল, গিপিই এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জীবানুমুক্তকরন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সতর্কতামুলক জ্ঞান থাকা জরুরি। মনে রাখতে হবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এমন সব জৈবিক উপাদানকে বিষাক্ত উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে এর বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতি সমূহ গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। রোগীদের এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উভয়ের নিরাপত্তার জন্য নমুনা সংগ্রহকারী এবং প্রস্তুতির সাথে জড়িত সকলকেই বর্তমানে সুপারিশকৃত সকল মান বজায় রেখে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।
স্যাম্পল বা নমুনা: ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে যে পদার্থ নেওয়া হয় তাকে নমুনা (Specimen) বলে। যেমন: রক্ত, মল, কফ, প্রসাব, সোয়াব ইত্যাদি।
বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল: চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসংখ্য পরীক্ষা রয়েছে এবং যেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। তবে সাধারণত যে সমস্ত নমুনাসমূহ সংগ্রহ করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:
| ক) রক্তের নমুনা: এটি করার জন্য প্রশিক্ষিত কেউ (সাধারণত একজন ফেবোটোমিস্ট, ভাষার বা নার্স ) দ্বারা রক্তনালী (কৈশিক, শিল্পা এবং কখনও কখনও ধমনী) থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিশেষ সংগ্রহের টিউবে রক্ত বের করার জন্য একটি সুই ব্যবহার করে নমুনা নেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু রক্তের নমুনা আঙুলের খোঁচা দিয়ে পাওয়া যেতে পারে যা শুধুমাত্র এক ফোঁটা রক্ত দিয়েই করা যায়, যেমন গ্লুকোজ পরীক্ষা। | |
| খ) মল সংগ্ৰহঃ ব্যাক্তিকে টয়লেটে পাঠিয়েই সাধারণত এই নমুনা নিজেকেই সংগ্রহ করতে বলা হয়। তবে মুমূৰ্ষ রোগীর কাছ থেকে সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হতে পারে। মলের সাথে যাতে প্রসাব মিশ্ৰিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখাটাই এই নমুনা সংগ্রহের মূল সাবধানতার বিষয়। এই অধ্যায়ে পরবর্তীতে মল সংগ্রহের পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। | |
| গ) প্রসাবের নমুনা: এই নমুনা সংগ্রহের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীকে একটি পাত্রে বা কন্টেইনারে প্রস্রাব ধরার জন্য বলা হয়। কন্টেইনারে প্রসাব ধারনের পূর্বে মূত্রনালীর বাইরের অংশের সংস্পর্শের দ্বারা যাতে নমুনা দুষিত না হয় সে জন্যে রোগী কীভাবে যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করবে সে বিষয়ে নির্দেশনাবলি দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্যক্তিকে কিছু প্রসাব নিঃসরণ করার পর মার পথে কিভাবে কন্টেইনারে প্রসাব সংগ্রহ করবে সে ব্যাপারেও স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রদান করা হয়। রোগীর অবস্থাভেদে কখনও কখনও ক্যাথেটার থেকেও বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে । | |
| ঘ) কফ সংগ্রহ: এই নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে রোগীকে যতটা সম্ভব ফুসফুসের ভিতর দিক থেকে কাশির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। (একজন স্বাস্থ্যকর্মী এ কাজটি করার জন্য রোগীকে সহায়তা করতে পারেন।) কোনো কিছু পান অথবা খাবারের পূর্বে কৃষ্ণ সংগ্রহের জন্য সকাল বেলাকেই মোক্ষম সময় বলে বিবেচনা করা হয়। এ সময় রোগীকে কন্টেইনারে রুফ দেওয়ার আগে ধীরে ধীরে কয়েকবার গভীর শ্বাস নেওয়ার পরে কাশি দিতে বলা হয়। সংগৃহীত কফ অপেক্ষাকৃত ঘন হওয়া উচিত যেন সেটা সাধারণ লালা মিশ্রিত না হয়। | |
| ঙ) নাসোফেরেজিয়াল সোয়াব (Nasopharyngeal Swab ) সংগ্রহ : এটি ক্লিনিকাল পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ধতি যেটি রোগীর অনুনাসিক ক্ষরণ এর পিছনে থেকে নাক এবং গলা থেকে সোয়াৰ সংগ্রহের মাধ্যমে করা হয়। নাকের শেষ প্রান্তে গিয়ে গলার পিছনের দেওয়াল Nasopharynx) থেকে একটি প্লাস্টিকের সৃষ্টি ( সোয়াব বেষ্টিত সৰু কাঠি দিয়ে এই নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। এটি নাকে প্রবেশের সাথে সাথেই রোগী হাঁচি দিতে শুরু করে। যার ফলে নাকের শেষ পর্যন্ত যাওয়া এবং সেখানে স্টিকের কটন সোক করার জন্য নুন २ সেকেন্ড স্টিকটি ধরে রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রে যিনি নমুনা নিবেন তাকে ভালোভাবে পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুরেপমেন্ট (PPE) পরতে হয় ইনফেকশন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। |
১.৪ রোগীকে সঠিক পজিশনিং ও স্থানান্তর করা
পজিশনিং বলতে একজন রোগীকে বিছানায় বা অন্য কোথাও সঠিকভাবে শোয়ানো কিংবা বসানোকে বুঝানো হয় যাতে করে তার শরীরের এলাইনমেন্ট নিরপেক্ষ থাকে এবং রোগীর সর্বোচ্চ আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আমরা সুস্থ মানুষেরাও সাধারণত একভাবে বেশিক্ষণ শুয়ে বা বসে থাকতে পারিনা। হাতে-পায়ে ঝিম ঝিম ধরাসহ আরো অনেক সমস্যা সামনে এসে হাজির হয়। ঠিক তেমনি একজন রোগী যিনি শারীরিক বা মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে কেয়ারগিভারের সহায়তা নিচ্ছেন, তাকেও আমাদের উচিৎ হবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট নিয়মে পজিশনিং করা। বিশেষ করে অজ্ঞান রোগী কিংবা সম্পূর্ণরূপে বিছানায় শয্যাশায়ী রোগীর (Bed Ridden Patient) ক্ষেত্রে এটি অতীব জরুরি। অন্যথায় প্রেসার সোরের মত মারাত্মক অসুবিধা তৈরি হতে পারে। আবার নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে হাসপাতালে বা বাসাবাড়িতে থাকা রোগীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে হয়। যেমন; টয়লেট করানো, গোসল করানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। হুইলচেয়ার থেকে বিছানা, বিছানা থেকে হুইলচেয়ার, চেয়ার থেকে হুইলচেয়ার এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে। সঠিকভাবে স্থানান্তর করতে না পারলে রোগী পড়ে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। একজন রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করা কেয়ারগিভারের অত্যাবশ্যকীয় একটি দক্ষতা। এই অংশে রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করার উপায় অনুশীলন করার পাশাপাশি হুইলচেয়ারের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।
১.৪.১ রোগীকে সঠিক পজিশনে রাখা ও স্থানান্তর করার গুরুত্ব
কখন করতে হয়: যখন একজন রোগী-
- শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হয়।
- শারীরিক কোনো সমস্যাগ্রস্ত কিংবা তীব্র ব্যথা থাকে যেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হয়।
- প্রেসার আলসারে আক্রান্ত থাকেন কিংবা প্রেসার আলসারে আক্রান্ত হবার ঝুকিতে থাকেন।
- মস্তিস্কের সমস্যায় ভুগেন যেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যহত হচ্ছে।
- রেস্টলেস কিংবা অস্থীর প্রকৃতির।
- দাঁত মাজা, গোসল করা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজকর্ম বিছানাতেই সম্পন্ন করতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা নিজে নিজে করতে পারছেন না।
- কোন নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিংবা অপারেশন কিংবা অন্য কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবেন।
গুরুত্ব:
- সঠিক পজিশনিং ও স্থানান্তর রোগীকে শরীরবৃত্তীয়ভাবে স্বক্রিয় রাখে। রোগীর রক্ত ও স্নায়ুবিক চলাচলকে স্বাভাবিক রাখে।
- প্রেসার সোর বা প্রেসার আলসার প্রতিরোধে গুরুত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- সঠিভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করার মাধ্যমে রোগীকে আরাম ও স্থিরতা প্রদান করা সম্ভব, এতে রোগী নির্ভার অনুভব করে
- সঠিক পজিশনিং ডাক্তার, নার্সদের কিছু কিছু পদ্ধতি সম্পন্ন করতে সুবিধা প্রদান করে
- রোগীর পড়ে যাওয়ার আশংকা কমায় এবং রোগীর নিরাপত্তা জোরদার করে। এতে রোগীর বিভিন্ন ইনজুরির ঝুঁকি হ্রাস পায়।
- সঠিভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করা গেলে রোগী অনেক কাজ নিজে নিজেই সম্পন্ন করতে পারে। যেমন: দাঁত মাজা ও মুখ ধোয়া, খাবার খাওয়া প্রভৃতি। এতে রোগীর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়।
প্রেসার আলসার:
রোগী শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হলে একটি খুব জটিল সমস্যা তৈরি হতে পারে যার নাম প্রেসার আলসার। একে প্রেসার সোর বা বেড সোর নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা এক ধরনের ক্ষত যাহা রোগীর শরীরে বিছানা, ম্যাট্রেস বা অন্য কোনো শক্ত কিছুর সাথে দীর্ঘদিন চাপের ফলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত রোগীর দেহের হাড় সংশ্লিষ্ট অংশে (Bony Prominense; উচ্চারণ: বোনি প্রমিনেন্স) এটি বেশি হয়ে থাকে। এ ধরনের কিছু স্থানের উদাহরণ হচ্ছে: মাথার পিছনের অংশ, দুই কাঁধের শক্ত অংশ, কনুই, নিতম্ব, পুহুদেশীয় অংশ, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি ও ছিল প্রভৃতি। এ ধরনের অংশ যখন দীর্ঘক্ষণ চাপ খেয়ে থাকে, তখন আস্তে আস্তে এ সমস্ত অংশের টিস্যুতে অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হয়, যার ফলে টিস্যুগুলো সরে যেতে থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক চামড়ায় এভাবে ফাটল ধরে যার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে প্রেসার সোর বা চাপ ক্ষত।
প্রেসার আলসারের পর্যায়: প্রেসার আলসার সাধারণত ৪টি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা:
| প্রথম পর্যায়: জায়গাটি লালচে, ফ্যাকাশে অথবা কালচে বর্ন ধারন করে এবং চাপ বন্ধ করার ১ মিনিটের মধ্যে তার স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসেনা। জায়গাটি আশেপাশের অংশগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে একটি বেশি শক্ত, নরম, উষ্ণ বা ঠাণ্ডা, অথবা বেশি ব্যথাদায়ক থাকতে পারে। ত্বকের রঙ কালো এরকম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি শুরুর দিকে বুঝতে পারা একটু কঠিন বটে। |
দ্বিতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে জায়গাটিকে গোলাপি বা লালচে রঙের টিস্যুসহ একটি অগভীর খোলা ক্ষতের মত দেখাবে। মাঝে মাঝে এটিকে ফোস্কার মতোও দেখাতে পারে।
তৃতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে আরো অধিক টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চামড়ার নিচে অবস্থিত চর্বি এ পর্যায়ে দৃশ্যমান হয় ।
চতুর্থ পর্যায়: একটি গভীর গর্ত তৈরী হয়। মাংশপেশি কিংবা হাড় দৃশ্যমান হতে পারে।
প্রেসার আলসারের ঝুঁকিসমূহ:
১। ইমোবিলিট বা অনড় অবস্থা
২। অধিক বয়স
৩। ভঙ্গুর ও শুকনো ত্বক
৪। আর্দ্র ত্বক; যখন একটি ত্বক অপর ত্বকের সাথে কিংবা কোনো আর্দ্র বিছানার চাদরের সাথে লাগানো থাকে।
৫। অপুষ্টি
৬। নিম্ন মানের হাইড্রেশন; যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান না করা
৭। নিম্ন মানের রক্ত সঞ্চালন
৮। নিম্ন মানের অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি।
প্রেসার আলসার প্রতিরোধে করণীয়:
১। ত্বকের যত্ন করা
২। রোগীকে নড়াচড়া করা এবং নিজে নিজে নড়াচড়া করতে অনুপ্রেরণা দেওয়া
৩। ত্বকে ফাটল ধরার বিভিন্ন লক্ষণ পরীক্ষা করা
৪। নিয়মিত টয়লেট ব্যবহারে সহায়তা করা এবং পেরিনিয়াল কেয়ার প্রদান করা
৫। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার ও পানি পানে উৎসাহিত করা
৬। নিয়মিতভাবে পজিশন বা রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করা এবং ঘর্ষণ বা অন্য কোনো আঘাত যেনো রোগী না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা। সাধারণত প্রতি ২ ঘন্টা পর পর পজিশন বা রোগীর অবস্থানের পরিবর্তন করতে হয়।
৭। পরিষ্কার, পরিপাটি কাপড়চোপড় এবং বিছানার চাদর নিশ্চিত করতে হবে।
পজিশনিং এর প্রকারভেদ:
প্রেসার আলসার প্রতিরোধে সঠিক পজিশনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক ধরনের পজিশনিং এর কথা বলা আছে। এখানে কয়েকধরনের পজিশনিং যেগুলো একজন কেয়ারগিভারকে প্রায়শই সম্পন্ন করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:
সুপাইন পজিশন এটি মূলত চিত করে শোয়ানো। রোগী তার পিঠ বিছানার সমান্তরালে রেখে মাথা উপর দিকে দিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে থাকেন। বাড়তি আরাম ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন বালিশ, ম্যাট্রেস, সাইড রেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। | |
প্রোন পজিশন রোগীকে তার বুক-পেট বিছানার সাথে রেখে এবং মাথা একপাশে দিয়ে সোজা করে শোয়ানো হয়। বাড়তি আরাম ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে বালিশ, ম্যাট্রেস, সাইড রেইল ইত্যাদি। | |
লেটারাল পজিশন রোগীকে একপাশে কাত করে শোয়ানো হয়, যেক্ষেত্রে তার এক পা আরেক পায়ের উপরে থাকে। করিজিয়াল রিজিওন বা পুচ্ছদেশীয় হাড়ের উপর চাপ কমাতে এই পজিশন উপকারী। এটি লেফট ও রাইট | লেটারেন্স পজিশন এই দুইভাবে বিভক্ত। | |
সিম'স পজিশন এক্ষেত্রে রোগীকে সুপাইন ও প্রোন এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি অবস্থানে রাখা হয় যেক্ষেত্রে রোগীর এক পাশের হাত-পা সামনের দিকে এবং অন্য পাশের হাত-পা পিছনের দিকে থাকে। কোনো অবস্থাতেই হাত যেনো রোগীর শরীরের নিচে চাপা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। | |
ফাওলার্স পজিশন রোগীর বিছানার মাথার দিকে অংশ ৪৫ ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা হয়। কোমরের উপর ভর দিয়ে রোগী এক্ষেত্রে আধশোয়া অবস্থায় থাকে। রোগীকে বিছানায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য এটি একটি সুবিধাজনক পজিশন। | |
সেমি- ফাওলার্স পজিশন রোগীর বিছানার মাথার দিকে অংশ ৩০ ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা হয়। যেসকল রোগীর হৃৎপিন্ড কিংবা ফুসফুসের সমস্যা আছে এবং যাদের নল দিয়ে তরল খাবার দিতে হয়, তাদেরকে সাধারণত এই ধরনের পজিশনে রাখা হয়। | |
ট্রেভলেনবার্গ পজিশন এক্ষেত্রে রোগী মাথা পায়ের নিচে নামিয়ে রোগীকে চিত্রের ন্যায় সমান্তরালে রাখতে হয়। হাপোটেনশন কিংবা এধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে এ ধরনের পজিশনিং কার্যকরি। এটিকে ভাইটাল অরগানসমুহে রক্ত চলাচলকে বাড়িয়ে দেয়, যেমন মস্তিষ্ক ও হৃৎপিন্ড। |
চিত্র ১.১০: বিভিন্ন প্রকার পজিশনিং
সঠিকভাবে পজিশনিং পদ্ধতি
পজিশনিং করার সময় রোগী ও কেয়ারগিভার উত্তরেরই ইনজুরি এড়ানোর জন্য এ কাজটি অত্যন্ত সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। উপরোল্লেখিত পজিশনগুলোর কিছু নির্দিষ্ট উপায় থাকলেও যেকোনো পজিশনিং এর ক্ষেত্রেই এর মুলনীতি আসলে একই রকম। যেমন:
১। পদ্ধতিটি রোগীকে ব্যাখ্যা করা ও বুঝিয়ে বলা। কি করতে যাওয়া হচ্ছে সেটি রোগীকে শুরুতেই বুঝিয়ে বলতে হবে। পাশাপাশি সেটি কেন করা হচ্ছে, করলে কি উপকার হবে আর না করলে কি হতে পারে তাও নরম সুরে বলতে হবে। রোগীর কাছ থেকে এভাবে ভালো সম্পর্কের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে পজিশনিং করলে সেটি রোগী অনুসরণ করে থাকে।
২। রোগীকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে রোগী তার সাধ্যমত সহযোগীতা করে। আগেই ঠিক করে নিতে হবে রোগী কি কিছুটা সহায়তা করতে পারবে নাকি একেবারেই পারবেনা। যদি মনে হয় রোগীর পক্ষে সহযোগীতা করা সম্ভব তাহলে সেটি করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে করে রোগীর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়।
৩। আর যদি মনে হয় যে রোগীর পক্ষে কোনোপ্রকার সহযোগীতা করা সম্ভব নয়, তাহলে প্রয়োজনে অন্য কারো সাহায্য নিতে হবে। কোনভাবেই রোগীকে মাটিতে ফেলে দেওয়া যাবেনা। অনেক সময় খুব ভারি রোগীকে উত্তোলন, পজিশনিং কিংবা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।
৪। সম্ভব হলে কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন: বেড বোর্ড, স্লাইড বোর্ড, বালিশ, পেশেন্ট লিফ্ ট, স্লিংস, হোয়েস্ট ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে পজিশনিং ও ট্রান্সফারের কাজটি সহজ হয়।
৫। রোগীর বিছানা প্রয়োজন মত উপর-নিচে এডজাস্ট করে নিতে হবে। বর্তমানে রোগীর বিছানা সাধারণত মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক হয়ে থাকে যেখানে সুইচ বোর্ডের বাটন টিপে প্রয়োজন মত ৪৫ বা ৩০ ডিগ্রি কোণে মাথার বা পায়ের দিকে বিছানা এডজাস্ট করে রোগীকে পজিশন করা যেতে পারে। আবার সাধারণ বিছানার ক্ষেত্রে ঘাড়ের নিচে ও পিঠে অতিরিক্ত বালিশ বা ম্যাট্রেস দিয়ে মাথার দিকটা উঁচু করা যেতে পারে। পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে পা গুলোকে উপরে তুলে পজিশনিং করা যায়।
৬। নিয়মিত পজিশন বা অবস্থানের পরিবর্তন করা। মনে রাখতে হবে, যেকোনো পজিশনই রোগীর জন্য ক্ষতিকর যদি সেটি অনেক লম্বা সময় ধরে রাখা হয়। তাই খেয়াল করে প্রতি দুই ঘন্টা পর পর রোগীর অবস্তার পরিবর্তন করিয়ে দিতে হবে। এতে করে রোগীর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায় এবং প্রেসার আলসারের ঝুঁকি হ্রাস পায়।
৭। রোগীর শরীর যাতে দেওয়ালে বা বিছানায় ঘষা না খায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোগী স্থানান্তর করার সময় রোগীকে ভারসহ উত্তোলন করতে হবে যাতে করে কোথাও ঘষা লেগে রোগীর ক্ষতি না হয়।
৮। নিজের ও রোগীর উভয়েরই সঠিক বডি মেকানিক্স বা এনাটমিক্যাল এলাইনমেন্ট বজায় রাখতে হবে।
- নিজেকে যথাসম্ভব রোগীর কাছাকাছি রাখতে হবে।
- প্রয়োজনে নিজের হাঁটু ভাঁজ করতে হবে এবং পা দুটো যথেষ্ঠ পরিমাণ ফাঁকা করে দাঁড়াতে হবে।
- রোগীর পজিশনিং, লিফটিং বা ট্রান্সফারের সময় হাতের বা পায়ের উপর ভর দিয়ে শক্তি প্ৰয়োগ করতে হবে। কোমরের উপর ভর দেওয়া যাবেনা। এতে নিজের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি হতে পারে।
- রোগী নড়ানোর সময় পেটের মাংশপেশিকে শক্ত করে রাখা যেতে পারে। এতে বলপ্রয়োগ সহজ হয়।
১.৪.২ রোগীকে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের উপায়
রোগীকে নানা প্রয়োজনে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হয়। যেমন; টয়লেট করানো, গোসল করানো, খাবার খাওয়ানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি। শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম বয়স্ক ব্যক্তি বা যে কোনো বয়সের রোগীকে বিভিন্ন পরিপুরক যন্ত্রের সাহায্যে এই স্থানান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরেকটু বিষদভাবে জানতে পারবো। এই অংশে আমরা রোগীকে কেবলমাত্র বিছানা থেকে হুইলচেয়ার ও হুইলচেয়ার থেকে বিছানায় স্থানান্তরের কৌশল অনুশীলন করবো।
বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তরঃ
রোগীর মাথা ও কাঁধ বিছানার উপরে উত্তোলন করা:
প্রস্তুতি-
১। সঠিকভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
২। প্রয়োজনীয় উপকরন সংগ্রহ করতে হবে
৩। রোগীকে সঠিকভাবে সম্ভাষণ জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে ।
৪। রোগীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।
৫। রোগীকে পদ্ধতিটি বর্ণনা করতে হবে এবং সাধ্যমত সহায়তা করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।
৬। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানার উচ্চতা এডজাস্ট করে নিতে হবে যাতে করে স্বাচ্ছন্দের সাথেই কাজটি করা যায়। বিছানার চাকা অবশ্যই লক করে নিতে হবে।
৭। সম্ভব হলে রোগীকে সুপাইন পজিশনে রাখতে হবে।
পদ্ধতি-
১। বিছানার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে এক পারের সামনে আরেক পাঁয়ের পজিশন নিতে হবে
২। রোগী যদি সক্ষম হয় তাহলে তাকে তার হাত তোমার নিজের হাতের নিচে রেখে শক্ত করে আকড়ে ধরতে বলতে হবে। আর যদি না পারে তাহলে কেয়ারপিতারকে একাই রোগীর হাত শক্ত করে ধরতে হবে।
৩। এক হাত দিয়ে রোগীর নিকটবর্তী হাত শক্ত করে ধরে অপর হাত দিয়ে রোগীর কাঁধে শক্ত করে সাপোর্ট দিতে হবে (চিত্রের ন্যায়)।
৪। এবারে নিজের দুই পায়ে ভর দিয়ে দুই হাতের সাহায্যে রোগীর মাথা উপরে উত্তোলন করতে হবে। রোগীকে সাধ্যমত সহযোগীতা করার কথা বলতে হবে।
৫। কাঁধের নিচে হাত দিয়ে রোগীর পিঠে ও ঘাড়ে বালিশ বা কুশন রেখে উচ্চতা ঠিক করে নিতে হবে যাচ্ছে রোগী তার নতুন পজিশনে আরামদায়কভাবে বসতে পারেন। এই কাজটি ইলেকট্রিক বেঞ্চেও খুব সহজেই করা যায়।
৬। এবার রোগীকে সতর্কতার সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী ফাওলারস, সেমি-ফাওলাস বা অন্য কোন পজিশনে বিছানায় রাখতে হবে।
সমাপ্তি-
১। রোগীর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, আরামদায়ক অবস্থা ও শারীরিক অবস্থান বজায় রাখতে হবে।
২। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানার উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে যাতে করে কেয়ার প্ল্যান অনুযায়ী নির্ধারিত সেবাটি খুব সহজেই প্রদান করা যায় ।
৩। কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হবে।
৪। হাত ধুয়ে নিতে হবে।
৫। রেকর্ড সম্পাদন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।
৬। রোগীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মটি সম্পাদন করতে হবে।
রোগীকে বিছানায় একপাশ থেকে অন্য পাশে সরানো প্রস্তুতি ও সমাপ্তি আগের মতই। পার্থক্য কেবল প্রক্রিয়া গত। মৌলিক কিছু ধাপ নিম্নরূপ:
১। বিছানার উচ্চতা একটি নামিয়ে নিতে হবে এবং রোগীকে মাথা উঁচু করার জন্য বলতে হবে। যদি রোগী করতে সক্ষম না হয় তাহলে পূর্বের পদ্ধতি অনুশীলন করে আগে রোগীর মাথা উচিয়ে পিছনে থেকে বালিশটি সরিয়ে নিতে হবে।
২। একই নিয়মে বিছানার দিকে মুখ করে দুই পায়ের পজিশন ঠিক করে দাঁড়াতে হবে।
৩। রোগীর দুই হাত চিত্রের ন্যায় বুকের উপর ক্রস করে রাখতে হবে।
৪। একহাত রোগীর খাড়ের পিছনে এবং অপর হাত রোগীর কোমরের উপরে রাখতে হবে। এক দুই তিন বলার মধ্যেই রোগীর শরীরকে খুব সাবধানে নিজের দিকে গড়িয়ে বিছানার একপাশে নিয়ে আসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই রোগী যেনো বিছানা থেকে পড়ে না যায়।
৫। এবার হাতের পজিশন পরিবর্তন করতে হবে। একহাত রোগীর কোমরের উপরের অংশে একবার আরেকহাত রোগীর পায়ের উপরের অংশে রাখতে হবে। সুপাইন পজিশনে রেখে রোগীর সর্বোচ্চ আরাস ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীকে সাধারণত বিছানার একপাশ থেকে অন্য পাশে সরানো হয় কোন নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করার জন্য। যেমন, বেড মেকিং, কিংবা চেস পরিবর্তন করা ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট সেবা প্রদানের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে।
রোগীকে বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর করা: এক্ষেত্রে প্রস্তুতি ও সমাপনি কাজের ধারা একই হওয়ায় সেগুলো পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছেনা। রোগীকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি আগে থেকেই প্রভুত করে নিতে হবে। যেমন: ট্রান্সফার বেল্ট, হুইলচেয়ার, রোগীর পোশাক ও জুতা প্রভৃতি। প্রক্রিয়া:
১। হুইলচেয়ারটিকে বিছানার কাছে রোগী যে পাশে বেশি শক্তি অনুভব করেন সে পাশে রাখতে হবে। হুইলচেয়ারের পা দানিটি ভাঁজ করে রাখতে হবে এবং হুইলচেয়ারের ঢাকার লক অবশ্যই বন্ধ করে রাখতে হবে। অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।
২। সুবিধামত বিছানার উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে।
৩। বিছানার দিকে মুখ করে আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে এক পায়ের সামনে আরেক পাঁয়ের পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে হবে। একহাত রোগীর পিঠে ও আরেকহাত রোগীর পায়ের উপরের অংশে শক্তভাবে রেখে এক দুই তিন বলার মধ্যেই নিজের শরীরকে বাকিয়ে রোগীকে বিছানার একপাশে সিটিং পজিশনে নিম্নে আসতে হবে।
৪I এবারে প্রয়োজন মত রোগীর জামাকাপড় পরিবর্তন অন্য কোনো কাজ করা যেতে পারে। সিটিং পজিশনে রোগীকে রেখে ২-১ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে রোগীর কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা।
৫। এরপর ট্রান্সফার বেল্টটি রোগীর কোমরে শক্ত করে আটকে দিতে হবে।
৬। রোগীকে দাড়া করানোর জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা যায়। একটি হচ্ছে, চিত্রের ন্যায় রোগীর পিছনে হাত দিয়ে ট্রান্সফার বেস্টটি শুরু করে আকড়ে ধরতে হবে অথবা ট্রান্সফার বেস্ট না থাকলে রোগীর দুই বাহুর নিচ দিয়ে তার দুই কাঁধে শক্ত করে ধরতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর দুই হাত কেয়ারগিভারের ঘাড়ের উপর দিয়ে দুই পাশে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য বলতে হবে। আর যদি কোনো সাহায্যকারী থাকে, তাহলেও কাজটি একইভাবে আরো সহজেই সম্পাদন করা যায় ।
৭। রোগীকে শক্ত করে সাপোর্ট দিয়ে এক দুই তিন পর্যন্ত বলার সাথে সাথেই রোগীকে বসা থেকে পাড় করিয়ে ফেলতে হবে। এরপর রোগীকে ধীরে ধীরে চেয়ারের দিকে পিছনে করে নিয়ে যেতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেনো রোগীকে দুই একটির বেশি কদম ফেলতে না হয়।
৮। চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে রোগীকে ধীরে ধীরে বসার জন্য বলতে হবে। বসানোর পর রোগীর দুই হাতকে একটির পর একটি করে নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে চেয়ারের হাতলে রাখতে হবে।
৯। এরপর রোগীকে সঠিকভাবে আরামদায়ক পজিশনে বসতে সহায়তা করতে হবে। পা দানি খুলে রোগীর পা দুটো এর উপর রাখতে হবে।
১০। ট্রান্সফার বেস্ট অপসারণ করতে হবে এবং হুইলচেয়ারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বেল্টের লকটি লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজন হলে হুইলচেয়ারের লকটি খুলে রোগীকে নির্দিষ্ট জায়গায় অতীব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।
১.৫ ইনটেক ও আউটপুট চার্ট
কোনো রোগী গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের (মুখের) অথবা শিরাপথ (প্যারেন্টালি) -এর মাধ্যমে যেসব তরল/খাবার আকারে গ্রহণ করে (ইনটেক) এবং যা কিছু নিষ্কাশিত বা অপসারণ (আউটপুট) করে তা যে চার্টে বা টুলসে রেকর্ড করা হয় তাকে ইনটেক এবং আউটপুট চার্ট বলে। কখনও কখনও এটি ফ্লুয়েড-ব্যালেন্স চার্ট হিসাবেও পরিচিত। সাধারণত মিলিলিটার (ml) হিসেবে ইনটেক ও আউটপুট চার্টে পরিমাণ লিখা হয়।
১.৫.১ ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং-এর গুরুত্ব
ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিকাল কেয়ার প্রক্রিয়া যা রোগের -
ক) অগ্রগতি এবং উপকারের পাশাপাশি চিকিৎসার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো নির্ধারণে সহায়তাকরে।
খ)ইনটেক ও আউটপুট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেয়ারগিভারগণ স্বাস্থ্যসেবার সাথে সাথে রোগীর তরল ও পুষ্টির সঠিক চাহিদা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে ।
গ) আউটপুট পরিমাপ পর্যবেক্ষণ করে প্রস্রাবের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতের পাশাপাশি স্বাভাবিক মলত্যাগ করছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।মোটকথা ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং চিকিৎসা- প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।
| ইনটেক হিসেবে যা পরিমাপ করা হয় | আউটপুট হিসেবে যা পরিমাপ করা হয় |
ইনটেক হিসেবে যেসব জিনিস পরিমাপ করা হয় তা হল - ক) ওরাল ইনটেক, খ) টিউব ফিডিংস, গ) ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড, ঘ) মেডিকেশন, ঙ) টোটাল প্যারেন্টেরাল নিউট্রিশন, চ) ব্লাড প্রোডাক্টস, ছ) ডায়লাইসিস ফ্লুইডস ইত্যাদি। | আউটপুট হিসেবে যেসব জিনিস পরিমাপ করা হয় তা হল- ক) ইউরিন, খ) তরল পায়খানা গ) বমি, ঘ) চেষ্ট ড্রেইনেজ ইত্যাদি। |
ইউরিন পরিমাপ ও স্যাম্পল গ্রহণ
বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইউরিন খুবই উল্লেখযোগ্য একটি স্যাম্পল বা নমুনা। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী তাই কেয়ারগিভারকে প্রায়শই ইউরিন বা প্রস্রাবের স্যাম্পল নিতে হয়। আবার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিমাপ করতে হয় শরীর থেকে কতটুকু তরল প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে গেছে সেটিও। এক্ষেত্রে যে রোগী সজাগ, সতর্ক এবং নিজে নিজেই প্রস্রাব করতে পারেন, তিনি প্রতিবার প্রস্রাব করার সময় একটি ইউরিনাল বা বোতলে প্রস্রাব সংগ্রহ করতে পারেন। কেয়ারগিভারও এ কাজে সহযোগীতা করতে পারেন। আবার, যে সমস্ত রোগীর প্রস্রাবে সমস্যা হয়, তাদেরকে অনেক সময় ডাক্তার-নার্সরা কেথেটার পরিয়ে দেন। অনেক সময় আবার অপারেশনের আগে ব্লাডার বা মুত্রথলি খালি করতেও এটি ব্যবহৃত হয়। ইউরিনারি কেথেটার হচ্ছে রাবার বা সিলিকোনের তৈরি বিশেষ এক ধরনের নল যেটি মূত্রনালী দিয়ে প্রবেশ করানো হয় যেখান দিয়ে প্রস্রাব এশে এর সাথে সংযুক্ত একটি ব্যাগে জমা হয়। এই ব্যাগটিকে বলা হয় ইউরোব্যাগ।
ইউরোব্যাগে মিলিলিটার এককে দাগ কাটা থাকে যেটা দেখে ঘণ্টায় ইউরিন আউটপুট কত হলো তা দেখা যায় এবং প্রয়োজনমত ইউরিন স্যাম্পলও নেয়া যায়। সাধারণত ১০০০ মিলি. বা ১ মিটার পর্যন্ত প্রসাব এখানে জা হতে পারে। তাই ইউরোব্যাগটি পূর্ণ হয়ে গেলে এটি পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দেওয়া কেয়ারপিভারের দায়িত্ব। সেই সাথে কখনো কখনো নতুন ইউরোব্যাগ সংযুক্ত করতে হয়। নিচে একটি কেথেটারাইজড রোগীর ইউরোব্যাগ থেকে আউটপুট দেখা ও ইউরিন স্যাম্পল সংগ্রহের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:
১. প্রথমেই সঠিক উপায়ে হ্যান্ড ওয়াশ করে পিপিই পরে নিতে হবে।
২. স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌটা বা পাত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে নিতে হবে।
৩. রোগীর কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিতে হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।
৪. রোগীর আরামদায়ক অবস্থানে রেখে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. কতক্ষণ আগে ইউরিন ব্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছিলো সেটি জেনে নিতে হবে এবং সর্বেশেষ ইউরিনের পরিমাণ দেখে ইউরিন আউটপুট কত হলো তা দেখে নিতে হবে।
৬. স্যাম্পল কালেকশনের নির্দেশনা থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্যাম্পল কালেকশন করে নিতে হবে। এজন্য ইউরো্যাগের চাবি সাবধানতার সাথে খুলতে হবে যাতে করে প্রস্রাব রোগীর শরীরে বা আশেপাশে ছড়িয়ে না যায়।
৭. ইউরিন দ্বারা ইউরোব্যাগ পরিপূর্ণ হয়ে যাবার মত মনে হলে ব্যাগটি সাবধানে খুলে নিয়ে প্রস্রাবটুকু টয়লেটে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার ব্যাগ বা নতুন ইউরোব্যাগ আবার লাগিয়ে দিতে হবে।
৮. ক্যাথেটারের টিউব ধরে টানাটানি করা যাবেনা এবং রোগীর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
৯. সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ইনটেক-আউটপুট চার্টে ইউরিন আউটপুটের পরিমাণ ও সময় লিখে রাখতে হবে।
১০. গৃহীত স্যাম্পল কৌটায় সঠিকভাবে ল্যাবেল করে ল্যাবে পাঠাতে হবে।
কোলোষ্টোমি ব্যাগ:
কোলোস্টোমি ব্যাগ হচ্ছে প্রাটিকের তৈরি বিশেষ এক ধরনের ব্যাগ যেটিকে রোগীর পেটের উপর দিয়ে অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করে মন পদার্থ সংগ্রহ করা হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার একটি ছোট অপারেশনের মাধ্যমে এই কাজটি করে থাকেন। সাধারণত নিম্নোক্ত সমস্যা আছে এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে কোলোটোসি ব্যাগ প্রয়োজন হয়।
- অস্ত্রের গুরুতর ইনফেকশন যেমন: ডাইভার্টিকুলাস
- ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিস
- কোলন বা অন্ত্রের আঘাত
- মলদ্বার বা কোলনের কোনো অংশে অবস্ট্রাকশন (বামা) বা ইনফেকশন এবং এনাল ফিস্টুলা।
কোলোস্টোমি ব্যাগের যত্ন নেয়া
১. প্রথমেই সঠিক উপায়ে হ্যান্ড ওয়াশ করে পিপিই পরে নিতে হবে।
২. স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌটা বা পাত্র এবং অন্যান্য উপকরন সঙ্গে নিতে হবে।
৩. রোগীর কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিতে হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।
৪. রোগীর আরামদায়ক অবস্থানে রেখে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. কবে কোনোটোমি ব্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছিলো সেটি জেনে নিতে হবে এবং সর্বেশেষ পরিমাণ দেখে আউটপুট কত হলো তা দেখে নিতে হবে।
৬. স্যাম্পল কালেকশনের নির্দেশনা থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্যাম্প কালেকশন করে নিজে হবে।
৭. সাবধানতার সাথে কোলোস্টোমি ব্যাগের পাউচ সরিয়ে ব্যাপটি খুলে নিয়ে আসতে হবে। স্টোমা ও চামড়ার চারপাশ পরিষ্কার পানিতে জীবাণুযুক্ত পক্ষের টুকরা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
৮. পুরানো ব্যাগটি সঠিক উপায়ে ডিজপোস করে নতুন ব্যাগটি সংযুক্ত করে দিতে হবে।
৯. সংযুক্ত ব্যাগ ধরে টানাটানি করা যাবেনা এবং রোগীর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
১০. সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ইনটেক-আউটপুট চার্টে স্টুল আউটপুটের পরিমাণ ও সময় লিখে রাখতে হবে।
১১. গৃহীত স্যাম্পল কৌটায় সঠিকভাবে ল্যান্সে করে ল্যাবে পাঠাতে হবে।
জব ১: রক্তের শর্করা পরিমাপ করা
পারদর্শিতার মানদন্ড- প্রশক্ষিনার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়কেবার অনুসরণ করার গ্লুকোমাটার ব্যবহাররে মাধ্যমে ব্লাড গ্লুকোজ পরমিাণরে পরতসিম্পন্ন করতে পারব।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা ;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং ক্ষ্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।
ব্যক্তিগত সুরক্ষ সরজা (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): ব্লাড গ্লুকোজ মিটার, টেস্ট স্ট্রিপ, ল্যান্সেট ডিভাইস ও নিডল, সার্গ বক্স, ডাই সোয়াব (অ্যালকোহল সোয়াব), রেকর্ড চার্ট।
কাজের ধারাবাহিকতা: প্রথমে মেডিক্যাল গাইডলাইন অনুযায়ী নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে গ্লুকোমিটার ব্যাবহারের মাধ্যমে রাজ গ্লুকোজ পরিমাপের কাজটি সম্পন্ন করবে।
অর্জিত দক্ষতা / ফলাফল: প্রশিক্ষনার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে রক্তে শর্করার পরিমাপ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে।
ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।
জৰ ২: ক্যাথেটার দিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ করার দক্ষতা অর্জন
পারদর্শিতার মানদন্ডঃ
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রভুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়াল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা:
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং ফ্যাগগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।
ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জান (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।
প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়ালসঃ
১। ফলিস ক্যাথেটার, ২। ইউরিন ব্যাগ, ৩। এ্যালকোহল প্যান্ড, ৪। ড্রাই কটন বল, ৫। ৫.০ সিসি ডিম্পবেল সিরিঞ্জ, ৬। ২৯ সাইজের নিডেল, ৭। প্লাস্টিক প্রসাবের কন্টেইনার, ৮। কালো মারকার, ৯। রোগীর রেকর্ড ফাইল, ১০। সাবান, ১১। পানি, ১২। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ১৩। স্যাম্পল লেভেল, ১৪। টিস্যু পেপার, ১৫। বর্জ্য ধারক ইত্যাদি।
কাজের ধারা
১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পড়।
২। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ কর এবং প্রস্তুত কর।
৩। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধোয়ার স্বাস্থ্যবিধি সম্পাদন কর।
৪। রোগীকে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর এবং মৌখিক সম্মতি নাও ।
৫। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি নমুনা চাহিদা (Riquisition) প্রস্তুত করা
৬। নমুনা সংগ্রহের জন্য রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নাও।
৭। একের পর এক ধাপ মেনে ফোলির ক্যাথেটার থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্রাব একটি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংগ্রহ কর।
৮। নমুনার ধরন, রোগীর নাম, বয়স, লিঙ্গ এবং নমুনা সংগ্রহের তারিখ এবং সময় পাত্রের গায়ে লেবেল করে দিন।
৯। ব্যবহৃত হয়েছে এমন বর্জ্য নির্ধারিত বর্জ্য খারকে রাখ।
১০। নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।
১১। উপযুক্ত তাপমাত্রার অবস্থায় নমুনা সংরক্ষণ কর ।
১২। ল্যাবে অবস্থানরত ব্যক্তির সাথে সমন্বয় কর এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠান।
১৩। সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার কর।
১৪। নির্দেশ অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করা।
কাজের সতর্কতা:
- কাজের সময় পিপিই ব্যবহার কর।
- প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহের জন্য সিরিজের সাথে সুই সংযুক্ত করা।
- ক্যাথেটারের সংযোগস্থলে বা ঠিক নীচে ড্রেনেজ টিউব আরটারি ফরসেফ দিয়ে ক্লাম্প করে বন্ধ কর।
- যেখান থেকে নিডেল প্রবেশ করবে সেই স্থানটি এ্যালকোহল প্যাড দিয়ে পরিষ্কার কর।
- ফোলি ক্যাথেটারটিতে ৪৫ ডিগ্রী কোণে আলতোভাবে সুই ঢোকান।
- ফোলি ক্যাথেটার থেকে সুই প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজন পরিমাণে প্রসাব সংগ্রহ করে সুই বের কর এবং উক্ত নমুনা একটি জীবাণুমুক্ত পাত্রে ঢেলে দিন।
- ক্ল্যাম্প খুলে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে গজিশনিং কর। খেয়াল রাখবে কোন অপরিষ্কার উন্মুক্ত স্থানে যেন ক্যাথেটার অথবা প্রসাবের কন্টেইনারে স্পর্শ না লাগে।
অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর ক্যাথেটার থেকে প্রস্রাবের নমুনা সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারবে।
ফলাফল বিশ্লেষন ও মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।
Promotion