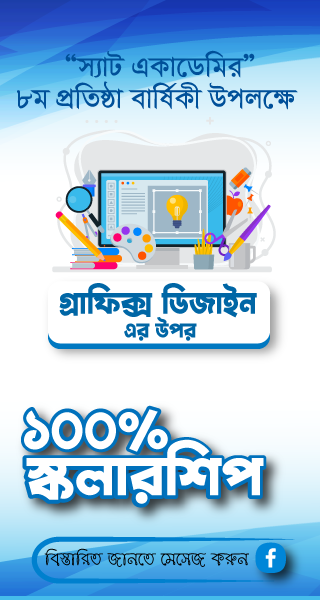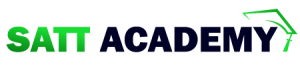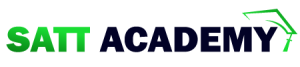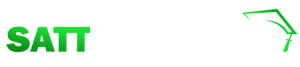১৪.১ ভূগর্ভস্থ পানি (Ground Water):
তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ির আশপাশে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা কিংবা হ্রদ-হাওড়ের পানি দেখেছ। শুধু তাই নয়, নিশ্চয়ই বর্ষাকালে আকাশ ভেঙে বৃষ্টিও হতে দেখেছ তাই তোমাদের ধারণা হতে পারে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের এই পানি বুঝি পৃথিবীর পানির বড়ো একটা অংশ। আসলে এটি মোটেও সত্যি নয়,
চিত্র ১৪.১: পৃথিবীর নানা ধরনের পানি এবং তার পরিমাণ
ভূপৃষ্ঠের এই পানি পৃথিবীর মোট পানির অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ (চিত্র ১৪.১)। পৃথিবীর মোট পানির ৭৪ শতাংশ পানি হচ্ছে সমুদ্র মহাসমুদ্রের লোনা পানি, মাত্র 2 শতাংশ পানি হচ্ছে স্বাদু পানি। স্বাদু পানির এই 2 শতাংশকে যদি 100 ভাগ ধরে নিই তাহলে তার 69 শতাংশ রয়েছে বরফ বা হিমবাহ আকারে মেরু অঞ্চলে এবং উঁচু পর্বতশৃঙ্গে। বাকি 31 শতাংশের 30 শতাংশই হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি, যেটি রয়েছে মাটির নিচে। বাকি 1 শতাংশ পানি হচ্ছে খাল-বিল-নদীনালা বা মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদির পানি।
আমরা বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হতে দেখি। যখন স্থলভাগের উপর বৃষ্টিপাত হয় তখন এবং তারও কিছু সময় পর পর্যন্ত বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। যেমন-
১) গাছের ডালপালা, পাতা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে বা ঝরে পড়ে বৃষ্টির পানি মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছে। একে বলা যেতে পারে উদ্ভিজ্জের পৃষ্ঠস্থ প্রবাহ (Through flow)। গাছপালার আবরণ না থাকলে বৃষ্টির পানির ফোঁটা সরাসরি উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে।
(২) বৃষ্টির পানির বড়ো একটি অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীনালায় যায় এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে সাগর মহাসাগরে মেশে। একে বলে পৃষ্ঠতলীয় প্রবাহ (Surface Runoff)।
(৩) কিছু পানি ভূপৃষ্ঠস্থ মাটির ভেতর প্রবেশ করে থাকে। একে বলে অনুপ্রবেশ (Infiltration)। এই পদ্ধতিতে পানি মাটির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা স্থানে সঞ্চিত হয় যা গাছ তার প্রয়োজনে গ্রহণ করতে পারে।
বাকি পানি মাটির নিচে শিলার ফাঁকা স্থান বা ফাটল ভেদ করে আরও গভীর প্রবেশ করে এবং ভূগর্ভস্থ পানি হিসেবে সঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে মাটি অথবা শিলার অভ্যন্তরের ফাটল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা স্থানগুলো সম্পূর্ণ পানি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। পানি ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় যদি সেখানে কোনো অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে পৌঁছায় তখন সেই পানি আরও গভীরে যেতে পারে না। বরং সেই শিলাস্তরের উপরে অবস্থিত শিলা বা অবক্ষেপের (Sediments) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা ফাটলের মাঝে জমা হতে থাকে। এর ফলে যে ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরি হয় তাকে বলে অ্যাকুইফার (Aquifers)। আলগা শিলার মাঝে প্রচুর ফাঁকা স্থান থাকায় তার মাঝে পানি প্রবেশ ও সংরক্ষিত থাকতে পারে তাই বালু, বেলেপাথর, চুনাপাথর প্রভৃতি দ্বারা গঠিত আলগা স্তর ভালো অ্যাকুইফার হিসেবে কাজ করে।
প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের অবস্থানের ভিত্তিতে অ্যাকুইফার (চিত্র ১৪.২) দুই ধরনের হয়ে থাকে; যেমন-
(১) উন্মুক্ত অ্যাকুইফার (Unconfined Aquifers),
(২) আবদ্ধ অ্যাকুইফার (Confined Aquifers)
চিত্র ১৪.২: দুই ধরনের অ্যাকুইফারের অবস্থান। এখানে লক্ষণীয় যে ভূগর্ভে কোথাও কোথাও পানি জমতে কয়েক হাজার এমনকি কয়েক লক্ষ বছরও লাগতে পারে।
১৪.১.১ উন্মুক্ত অ্যাকুইফার :
ভূগর্ভস্থ কোনো পানির স্তর থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত যদি অনুপ্রবেশযোগ্য শিলাস্তর থাকে তবে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সহজে তার ভিতর প্রবেশ করতে পারে। এজন্য এই স্তরের পানি উত্তোলন করে ফেললেও সেটি পুনরায় পূর্ণ হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে ভূপৃষ্ঠে যদি কংক্রিটের স্তর, রাস্তা, দালান বা অন্যান্য স্থাপনার কারণে অপ্রবেশ্য স্তর সৃষ্টি করা হয় তবে উন্মুক্ত অ্যাকুইফারের পানি পুনরায় পূর্ণ হওয়া ব্যাহত হয়। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে সেই স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর (Water Table) পূর্বের অবস্থানে তুলনায় নেমে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই সকল এলাকায় পানি উত্তোলন করতে হলে নলকূপ বা পাম্পের পাইপ মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করাতে হবে।
উন্মুক্ত অ্যাকুইফারের চেয়ে মাটির অনেক গভীরে আবদ্ধ অ্যাকুইফার অবস্থিত। এই অ্যাকুইফারের উপরে এবং নিচে দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে। এই অপ্রবেশ্য স্তরে পানি প্রবেশ করতে পারে না বলেই চলে। যদি অপ্রবেশ্য স্তরে কোনো ফাটল বা ছিদ্র থাকে সেক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই সেই ছিদ্র বা ফাটল থেকে পানি ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসবে। উপরের পাথরের স্তরের ভর এবং প্রবেশ্য অংশ থেকে প্রবেশ করা পানির চাপে এই স্তরের পানি অধিক চাপে থাকে বলে এরকম হয়ে থাকে। আবদ্ধ অ্যাকুইফারের ছিদ্র বা ফাটল দিয়ে ভূগর্ভে থাকা উচ্চ চাপের পানি বাইরে বের হয়ে আসলে তাকে আর্টেশিয়ান কূপ (Artesian well) বলা হয়।
১৪.২ বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ভূমিরূপ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আমরা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নদীর পলিবাহিত সমতলভূমি দেখি। এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে রয়েছে পাহাড় ও টিলা। সিলেট বিভাগের অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে নিচু হাওড় অঞ্চল। আমরা যদি বাংলাদেশ ছেড়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে তাকাই তাহলে মরুভূমি, হিমবাহ, উঁচু পর্বত, উপত্যকা, মহাসাগরের নিচে গভীর খাত, হ্রদ, আগ্নেয়গিরি এরকম আরও অনেক বিচিত্র ভূমিরূপ দেখতে পাব। এসব ভূমিরূপ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণেও একধরনের ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয়ে অন্যধরনের ভূমিরূপে রূপান্তরিত হতে পারে।
এই অধ্যায়ে আমরা ভূমিরূপ গঠনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানব। পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু শক্তি কাজ করে ভূ-অভ্যন্তর থেকে এবং কিছু শক্তি কাজ করে ভূপৃষ্ঠের বাইরে থেকে। কাজেই প্রাকৃতিক যেসব কারণে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-
(১) ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া (Endogenic Process) এবং Md. Mahfuzar Rahman
(২) ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়া (Exogenic Process)
১৪.৩ ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া
এই ধরনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভূমিরূপের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং শক্তি কাজ করে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে। আমরা পূর্বের শ্রেণিগুলোতে প্লেট টেকটোনিক সম্পর্কে জেনেছি। মূলত প্লেট টেকটোনিকের সঙ্গে ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া জড়িত। এক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে ওপরের স্তর বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত শিলাসমূহে আকার ও অবস্থানের পরিবর্তন দেখা যেতে পারে অথবা ভূ-অভ্যন্তর থেকে ম্যাগমা বের হয়ে এসে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়,
(১) বলের প্রভাবজনিত বিকৃতি (Diastrophism)
(২) আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত (Volcanism)
১৪.৩.১ বলের প্রভাবজনিত বিকৃতি (Diastrophism)
ভূপৃষ্ঠের শিলার উপর বল প্রযুক্ত হলে শিলার আকার ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন শিলার উপর প্রযুক্ত বলটি কতটুকু এবং কোনদিকে কাজ করেছে তার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দুই ধরনের বল কাজ করে। যেমন-
(ক) সংকোচন বল (Compression force)
(খ) প্রসারণ বল (Extension force)
সংকোচন বা প্রসারণ বলের ক্ষেত্রে শিলার উপর দুই দিক থেকে প্রযুক্ত বলের কারণে শিলার সংকোচন এবং বিকৃতি ঘটে।
চিত্র ১৪.৩: ভাঁজে উঁচু বা তোরণ আকৃতির অংশ অ্যান্টিক্লাইন বা উত্তল ভাঁজ এবং নিচু বেসিনের মতো অংশকে সিনক্লাইন বা অবতল ভাঁজ বলে।
ভাঁজ (Folding): আমরা পূর্বে জেনেছি যে বিভিন্ন প্রকার শিলার কাঠিন্য বিভিন্ন রকম। ফলে তাদের উপর প্রযুক্ত বল সহ্য করার ক্ষমতাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠস্থ শিলায় যদি দুই দিক থেকে পরস্পরমুখী সংকোচন বল কাজ করে তাহলে সেই শিলার বিকৃতি ঘটে এবং তাতে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে শিলার শুধু আকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু তা ভেঙে যায় না। ভাঁজের উঁচু অংশকে উত্তল ভাঁজ অ্যান্টিক্লাইন এবং নিচু অংশকে অবতল ভাঁজ বা সিনক্লাইন (চিত্র ১৪.৩) বলে। অ্যান্টিক্লাইনে পাহাড়শ্রেণি এবং সিনক্লাইনে উপত্যকা সৃষ্টি হয়। আমরা যদি এই বিজ্ঞান বইটি টেবিলে রেখে দু দিক থেকে চাপ দিই তবে দেখা যাবে বইয়ের মাঝের অংশ ভাঁজ হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। এখানে যেমন- অনেকগুলো পাতা ভাঁজ হয়ে যায় তেমনি ভূপৃষ্ঠে শিলার যে অনেকগুলো স্তর একটি আরেকটির উপরে অবস্থিত সেগুলো ভাঁজ হয়ে যায় ।
পাহাড় এবং উপত্যকা ছাড়াও আরেক ধরনের ভূমিরূপ হচ্ছে মালভূমি। মালভূমি মূলত অধিক উচ্চতায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ সমতল বা আংশিক তরঙ্গায়িত ভূমি। মালভূমির চারদিক খাড়া ঢালযুক্ত যা অনেকটা টেবিলের মতো। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মালভূমি হলো- পামির মালভূমি, ইরানের মালভূমি ইত্যাদি। পানি ও হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, প্লেট টেকটোনিক প্রভৃতি কারণে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে।
চুতি (Faulting): কোনো স্থানের ভূপৃষ্ঠে শিলার উপর সংকোচন বা প্রসারণ বল প্রয়োগের ফলে যদি তাতে ফাটলের সৃষ্টি হয় তখন সেই ফাটল তল বরাবর একটি শিলার খণ্ড অপরটির থেকে বিভিন্ন দিকে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে । শিলা প্রযুক্ত বল সহ্য করতে না পারার কারণে তাতে ফাটল সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড অপরটির থেকে,
(১) নিচে নেমে যেতে পারে অথবা
(২) অনুভূমিকভাবে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, কিংবা
(৩) উপরে উঠে যেতে পারে। সেই হিসেবে চ্যুতি তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন-
(ক) স্বাভাবিক চ্যুতি: স্বাভাবিক চ্যুতির ক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড অপর শিলাখণ্ড থেকে নিচে নেমে যায়। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে যে অংশটি উপরে উঠে থাকে তা নিম্নগামী শিলাখণ্ডের সঙ্গে স্থূলকোণে অবস্থান করে (ছবি)। ঊর্ধ্বগামী শিলাখণ্ডের দৃশ্যমান অংশকে চ্যুতি খাড়াই বলা হয়।
(খ) স্ট্রাইক-স্লিপ চ্যুতি: এই ধরনের চ্যুতির ক্ষেত্রে দুটি শিলাখণ্ড পাশাপাশি অবস্থান পরিবর্তন করে। খাড়া দিকে অবস্থান পরিবর্তন না হওয়ায় এক্ষেত্রে কোনো চ্যুতি খাড়াই দেখা যায় না।
(গ) বিপরীত চ্যুতি: এই ধরনের চ্যুতির ক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড অপর একটি শিলাখণ্ডের উপরে উঠে যায় এবং ঊর্ধ্বগামী শিলাখণ্ডের কিছু অংশ নিচের শিলাখণ্ডের উপর ঝুলে থাকে। এই ঝুলন্ত অংশটি ভেঙে নিচে পড়ে এবং ভূমিধসের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে নিচে অবস্থানকারী শিলাখণ্ডের সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী শিলাখণ্ড সূক্ষ্মকোণে অবস্থান করে (ছবি)। এই কোণ অতিরিক্ত কম হলে (১০ ডিগ্রির চেয়ে কম) তাকে ওভারথ্রাস্ট চ্যুতি বলে।
১৪.৩.২ আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত (Volcanism)
পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টির ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একটি চমকপ্রদ ভূমিরূপ (চিত্র ১৪.৭) হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। এক্ষেত্রে ভূ-অভ্যন্তর থেকে গলিত পাথর, ছাই, বিভিন্ন গ্যাস, জলীয় বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ইত্যাদি বাইরে বের হয়ে আসে। গলিত পাথর ভূ-অভ্যন্তরে থাকলে তাকে ম্যাগমা বলে, সেই ম্যাগমা বা গলিত পাথর বাইরে বের হলে তাকে লাভা বলে (চিত্র ১৪.৮)। বিভিন্ন ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। লাভার ধরনের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরি দুই ধরনের হতে পারে; যেমন-
চিত্র ১৪.৭: গত ১২ মে) বছরের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হওয়া আগ্নেয়গিরির অবস্থান। এখানে প্রতিটি ডট দ্বারা একটি না ক্ষেত্রবিশেষে একগুচ্ছ আগ্নেয়গিরি বুঝানো হয়েছে।
বিস্ফোরক ধরনের: একটি আগ্নেয়গিরি কী ধরনের হবে সেটি লাভার বৈশিষ্ট্য, তাতে গ্যাসের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। লাভার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে গলিত সিলিকার (SiO) শতকরা পরিমাণ।
চিত্র ১৪.৮: আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন অংশ
লাভাতে যদি সিলিকার শতকরা পরিমাণ বেশি হয় তবে সেটি অ্যাসিডিক টাইপের লাভা হয়। এই ধরনের লাভা বেশি ঘন ধরনের হয় বলে সহজে বের হয়ে আসতে বা প্রবাহিত হতে পারে না। এই ধরনের লাভা নির্গমনকারী আগ্নেয়গিরিগুলো বিস্ফোরক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত মাউন্ট সেন্ট হেলেন।
লাভাতে যদি সিলিকার শতকরা পরিমাণ বেশি হয় তবে সেটি অ্যাসিডিক টাইপের লাভা হয়। এই ধরনের লাভা বেশি ঘন ধরনের হয় বলে সহজে বের হয়ে আসতে বা প্রবাহিত হতে পারে না। এই ধরনের লাভা নির্গমনকারী আগ্নেয়গিরিগুলো বিস্ফোরক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত মাউন্ট সেন্ট হেলেন।
আবার আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার ভিত্তিতে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন-
১. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি: যেসব আগ্নেয়গিরিতে বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাত চলছে (চিত্র ১৪.৯)।
চিত্র ১৪.৯: ২০১৭ সালে পেরুতে সাবানকায়া (Sabancaya) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।
২ . সুপ্ত আগ্নেয়গিরি: এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে অতীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে সেটি অনেক বছর ধরে বন্ধ আছে। ম্যাগমা প্রকোষ্ঠ পুনরায় ম্যাগমা দ্বারা পূর্ণ হলে আবার ভবিষ্যতে এতে অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনা আছে।
৩. মৃত আগ্নেয়গিরি: এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে অতীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতে আর অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই।
আগ্নেয়গিরির গঠন বা তা দেখতে কেমন তার ওপর ভিত্তি করেও অনেক ধরনের আগ্নেয়গিরি হতে পারে। এছাড়া মহা আগ্নেয়গিরি (Super Volcano) নামে আরেকটি ধরন রয়েছে। এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে কয়েক লক্ষ বছরে একবার অগ্ন্যুৎপাত হয়। অন্যান্য আগ্নেয়গিরি তুলনায় নির্গত লাভা ও অন্যান্য বস্তুর পরিমাণও অনেক বেশি। ইন্দোনেশীয় মাউন্ট টোবা (Mount Toba) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন জাতীয় উদ্যান এ ধরনের আগ্নেয়গিরির উদাহরণ। মহা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলে এবং সেটি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হলে তা পুরো পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে পারে।
আমরা এতক্ষণ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে জানলাম। তবে আগ্নেয়গিরির কারণে ভূ-অভ্যন্তরে এমন অনেক গঠন সৃষ্টি হয় যা উপরের শিলা বা মাটি ক্ষয় হয়ে গেলে তবেই দেখা যায়।
সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি :
স্থলভূমির মতো সমুদ্রের নিচেও আগ্নেয়গিরি পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে অগ্ন্যুৎপাতও হয়ে থেকে। এই ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা বের হয়ে আসে সেগুলো সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে এসে জমাট বেধে পানির নিচে পর্বতমালার সৃষ্টি করে থাকে। যখন এই পর্বতমালার উচ্চতা অনেক বেড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে তখন সেগুলো সাগর- মহাসাগরে দ্বীপ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে টঙ্গা নামে একটি দ্বীপকে এভাবে গড়ে ওঠা সবচেয়ে নতুন একটি দ্বীপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (চিত্র ১৪.১০)।
চিত্র ১৪.১০: প্রশান্ত মহাসাগরে সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি দিয়ে তৈরি টঙ্গা নামে দ্বীপ।
১৪.৪ ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়া (Exogenic):
ভূমিরূপ সৃষ্টিতে এই ধরনের প্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের বাইরের বস্তু ও শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেসব বস্তুর দ্বারা এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাদেরকে বলা হয় এজেন্ট (agent)। ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়ায় পানি, বায়ু এবং বরফ, এই তিনটি এজেন্ট কাজ করে। ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়ায় তিনটি মূল ধাপ রয়েছে; যেমন-
১. ক্ষয় কার্য,
২. পরিবহণ
৩. অবক্ষেপণ
এই প্রতিটি ধাপেই বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। তবে কোথায় কোনো ধরনের এজেন্ট দ্বারা এই তিনটি ধাপে ভূমিরূপ গঠিত হবে তা নির্ভর করে সেই স্থানের অবস্থান ও জলবায়ুর উপর। যেমন- যেসব স্থানে পানির প্রাচুর্য রয়েছে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেসব স্থানে পানি ভূমিরূপ সৃষ্টির এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।
শুষ্ক স্থানে পানির অভাব থাকে। সেক্ষেত্রে বায়ু এজেন্টের ভূমিকা পালন করে। আবার অতি ঠান্ডা অঞ্চলে বরফ এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।
১৪.৪.১ ক্ষয়কার্য (Erosion)
প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা শিলার দুর্বল ও ক্ষয় হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিচূর্নিভবন (Weathering) বলে। প্রথমে ভূপৃষ্ঠের শিলা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এজেন্ট দ্বারা অন্য স্থানে অপসারিত হয়। তিন প্রক্রিয়ায় বিচূর্নিভবন হতে পারে। যেমন-
১. ভৌত বিচূর্নিভবন
২. রাসায়নিক বিচূর্নিভবন
৩. জৈব বিচূর্নিভবন
ভৌত বিচূর্নিভবন (Physical Weathering):
এই প্রক্রিয়ায় শিলা বিভিন্ন ভৌত শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং খণ্ড বিখণ্ড হয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে শিলার গঠনকারী খনিজসমূহের রাসায়নিক গঠন অক্ষুণ্ণ থাকে, শুধু শিলার আকার এবং আকৃতির পরিবর্তন হয়। যেমন- একটি বড়ো গ্রানাইট (এক ধরনের আগ্নেয় শিলা) পাথর ভৌত বিচূর্নিভবনের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি পাথরে পরিণত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভৌত বিচূর্নিভবন প্রক্রিয়ার মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এরকম:
হিমজনিত প্রক্রিয়া (Frost action): ঠান্ডা অঞ্চলগুলোতে পাথরের মাঝে ফাটলে দিনের বেলা তরল পানি প্রবেশ করে এবং রাতের অধিক ঠান্ডায় তা জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পানি বরফে পরিণত হলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং ফাটলের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ফাটল আরও বর্ধিত হয়। দিনের বেলায় সূর্যের তাপে সেই বরফ গলে আবার পানিতে পরিণত হয় এবং রাতের তৈরিকৃত বড়ো ফাটলে আরও অধিক পানি প্রবেশ করতে পারে । পরে তা রাতে আবার বরফে পরিণত হলে তা পাথরে অধিক চাপ সৃষ্টি করে এবং ফাটলকে আরও বর্ধিত করে। এভাবে কঠিন শিলা ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলায় পরিণত হয় ।
লবণ স্ফটিক গঠনজনিত (Salt crystal growth): এই প্রক্রিয়াটি হিমজনিত প্রক্রিয়ার মতোই, তবে এক্ষেত্রে পাথরের ফাটলে চাপ সৃষ্টি করে লবণের স্ফটিক। পৃথিবীর বিভিন্ন শুষ্ক অঞ্চলে পানি দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। ফলে সেই পানিতে অবস্থিত দ্রবীভূত লবণ স্ফটিকে পরিণত হয়। লবণের স্ফটিক যত বৃদ্ধি পায়, পাথরের মাঝে ফাটলে তা তত বেশি চাপ সৃষ্টি করে এবং ভৌত বিচূর্নিভবন সংঘটিত হয় ।
তাপের পরিবর্তন জনিত (Thermal Action): কিছু স্থানে দিন ও রাতে তাপমাত্রার মাঝে অনেক পার্থক্য থাকে। সেসব স্থানে দিনে সূর্যের তাপে শিলা প্রসারিত হয় এবং রাতে ঠান্ডায় সংকুচিত হয়। আমরা জানি শিলা বিভিন্ন ধরনের খনিজের মিশ্রণ। বিভিন্ন ধরনের খনিজ তাপের কারণে বিভিন্ন হারে প্রসারিত হয়। ফলে শিলার মাঝে বিভিন্ন অংশে চাপের পার্থক্যের কারণে তা ভেঙে যেতে থাকে।
এক্সফলিয়েসন (Exfoliation): মাটির নিচে গভীরে যেসব শিলা থাকে তা উপরের মাটি এবং শিলার চাপে কিছুটা সংকুচিত অবস্থায় থাকে। সময়ের পরিবর্তনে উপরের শিলা বা মাটি অপসারিত হলে নিচের শিলা ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত হয়। এসব শিলার উপরে প্রযুক্ত চাপ না থাকায় তা প্রসারিত হয় এবং সমান্তরাল অনেকগুলো ফাটল সৃষ্টি হয়। এভাবে শিলা পেঁয়াজের খোসার মতো স্তরে স্তরে ভাঙতে থাকে ।
রাসায়নিক বিছর্নিভবন (Chemical Weathering)
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা শিলা বিচূর্ণ হলে তা রাসায়নিক বিচূর্নিভবন সংঘটিত করে। এক্ষেত্রে শিলা শুধু আকারে নয়, রাসায়নিক গঠনেও পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিচূর্নিভবনও বিভিন্ন রকম হতে পারে; যেমন-
জারণ (Oxidation) বায়ু এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন শিলার খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নতুন ধরনের পদার্থ সৃষ্টি করে। সাধারণত ধাতব খনিজসমূহ এই প্রক্রিয়ায় অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে নতুন পদার্থ পূর্বের খনিজের তুলনায় গঠনগতভাবে দুর্বল হয় এবং সহজে ভেঙে যায়। অনেক সময় নতুন সৃষ্ট পদার্থ আয়তনের বৃদ্ধি পায় এবং শিলায় চাপ সৃষ্টি করে তা ভাঙতে সাহায্য করে।
পানিযোজন (Hydration): শিলা গঠনকারী খনিজসমূহ পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে একাধিক নতুন যৌগ গঠন করতে পারে। যেমন- গ্রানাইট শিলায় (যা একটি অত্যন্ত কঠিন শিলা) অবস্থিত একটি খনিজ ফেল্ডসপার। পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে তা অপেক্ষাকৃত নরম ক্লে বা কাদা এবং সিলিকা বালুতে পরিণত হয়।
আর্দ্রবিশ্লেষণ (Hydrolysis): এক্ষেত্রে পানির অণু খনিজের যৌগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভিন্নধর্মী খনিজ গঠন করে। যেমন- অ্যানহাইড্রাইট নামক খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে জিপসাম গঠন করে।
অম্লীয় বিক্রিয়াজনিত (Acid reaction): বায়ুতে অবস্থিত কার্বন Md. Mahfuzar ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির পানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দুর্বল কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিড কার্বনেট জাতীয় শিলার সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে এবং সেই শিলাকে ক্ষয় করে ফেলে। চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি শিলা বিভিন্ন অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রাসায়নিকভাবে ক্ষয় হয়ে থাকে। আমরা অনেকেই মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য অথবা ভিত্তিপ্রস্তর ক্ষয় হতে দেখেছি যা মূলত অম্লীয় বিক্রিয়াজনিত কারণে হয়ে থাকে
চিত্র ১৪.১৫: অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে ক্ষয় হওয়া মার্বেল পাথরে তৈরিকৃত ভাস্কর্য
জৈব বিচর্নিভবন (Biological Weathering): উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কার্যক্রমের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শিলা চূর্ণ- বিচূর্ণ হতে পারে। যেমন- কিছু কিছু উদ্ভিদ পাথরে জন্মাতে পারে। এসব উদ্ভিদের শিকড় পাথরের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে আরও গভীরে প্রবেশ করে এবং এর ফলে পাথরে ফাটলের সৃষ্টি হয়। সময়ের পরিক্রমায় সেই পাথর ক্ষয় হয়ে আরও ছোটো টুকরায় পরিণত হয়। আমরা অনেকেই বিভিন্ন দালানের গায়ে বট বা পাকুর গাছ জন্মাতে দেখেছি। এসব গাছের শিকড়ের কারণে ভবনের দেয়ালে বা ছাদে ফাটল সৃষ্টি হয়। ছোটো ছোটো অণুজীব দ্বারাও শিলা ক্ষয় হতে পারে। এক্ষেত্রে সে সকল অনুজীব থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক শিলা ক্ষয়ে সাহায্য করে (চিত্র ১৪.১৬)।
চিত্র ১৪.১৬: স্পেনের লা পালমায় (La Palma) ব্যাসল্ট নামক আগ্নেয় শিলায় লাইকেন দ্বারা জৈব বিচূর্নিভবন
১৪.৪.২ পরিবহণ (Transportation)
বিচূর্নিভবনের পর পানি, বায়ু অথবা বরফ দ্বারা সেই অবক্ষেপ (Sediment) পরিবাহিত হয়। এক্ষেত্রে অবক্ষেপ কী দ্বারা পরিবাহিত হচ্ছে তার উপরে সেই পরিবহণের গতি নির্ভর করে। যেমন- নদীতে পানি দ্বারা পরিবহণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত সংঘটিত হয়। অপরদিকে বরফ বা হিমবাহের দ্বারা পরিবহণ তুলনামূলকভাবে অনেক ধীরগতিতে (দিনে দুই থেকে তিন ফুট) হয়ে থাকে। বায়ুর গতিবেগের পরিবর্তনের সঙ্গে অবক্ষেপ পরিবহণের গতি ভিন্ন হতে পারে। পরিবহণের এজেন্টের উপর ভিত্তি করে নির্ভর করে কত বড় আকারের অবক্ষেপ পরিবাহিত হবে। যেমন- পাহাড়ি নদীগুলোতে অনেক বড়ো আকারের পাথরের টুকরো
চিত্র ১৪.১৭: বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ।
পরিবাহিত হয়। হিমবাহতেও বড়ো আকারের পাথর পরিবাহিত হতে পারে। অপরদিকে বায়ুর ঘনত্ব পানির তুলনায় প্রায় এক হাজার ভাগে এক ভাগ হয় হওয়ায় তা বড়ো আকারের অবক্ষেপ পরিবহণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বালি বা ধূলিকণা বায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবহণ কয়েকশো মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। শুনে তোমাদের অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, আফ্রিকার মরুভূমিগুলো থেকে মিহি সিল্ট জাতীয় ধূলিকণা পরিবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় এসে জমা হতে পারে।
১৪.৪.৩ অবক্ষেপণ (Deposition)
পানি বায়ু এবং বরফের দ্বারা পরিবাহিত অবক্ষেপ অবশেষে বিভিন্ন স্থানে জমা হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। যেমন- নদীবাহিত পলি জমা হয়ে প্লাবনভূমি গঠন করে। সমুদ্রে নদীর পানি যেখানে মেশে সেখানে বদ্বীপ গঠিত হয় (চিত্র ১৪.১৭)। বায়ুবাহিত ধূলিকণা জমা হয়ে লোয়েস (Loess) নামক উর্বর ভূমি গঠন করে। মরুভূমির বিভিন্ন আকারের বালিয়াড়িও বায়ুবাহিত বালি জমা হয়ে তৈরি হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বায়ু প্রবাহের সঙ্গে অবস্থান পরিবর্তন করে। হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত অবক্ষেপ জমা হয়ে বিভিন্ন ধরনের মোরেইন (Moraine) নামক ভূমিরূপ গঠন করে (চিত্র ১৪.১৮)।
১৪.৫ বিভিন্ন ভূমিরূপে জীববৈচিত্র্যের ধরন
ভূমিরূপের গঠন এবং ধরনের উপর ভিত্তি করে সেই স্থানের জীববৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। আমরা পৃথিবীব্যাপী পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমতলভূমি, মরুভূমি প্রভৃতি নানা ধরনের ভূমিরূপ দেখতে পাই। বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপে জলবায়ু এবং পরিবেশ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যা সে স্থানের জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে। যেমন- মরুভূমিতে জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক এবং পানি অত্যন্ত দুর্লভ। সেখানে দিন অত্যন্ত উষ্ণ এবং রাত অত্যন্ত শীতল হয়ে থাকে। তাই সেখানে বসবাসকারী প্রাণী এবং জন্মানো উদ্ভিদ অনন্য বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। মরুভূমির ক্যাকটাস তার কাণ্ডে প্রচুর পানি জমা রাখতে পারে। অপরদিকে মরুভূমির উট, ছোটো ইঁদুর, ছোটো পতঙ্গ, সাপ প্রভৃতি সামান্য পানি গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে পারে।
উঁচু পাহাড় বা পর্বত সাধারণত অত্যন্ত দুর্গম হয়ে থাকে। তাই সেখানে বসবাসকারী জীবজন্তুও সেই স্থানের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে থাকে। যেমন- পাহাড়ে বসবাসকারী ছাগল অত্যন্ত উঁচু এবং বিপজ্জনক খাড়া ঢাল ধরে চলাচল করতে পারে। বেশি উঁচু পর্বতসমূহ এবং পৃথিবীর শীতপ্রধান স্থানসমূহ বরফে আচ্ছাদিত থাকে। তাই সেখানে জন্মানো অনেক গাছ কোনাকার হয়ে থাকে। এতে করে সেই গাছের উপরে পড়া তুষার সহজে ঝরে পড়তে পারে। একই সঙ্গে সেইসব স্থানের প্রাণীদের শীত সহনশীলতা বেশি এবং সাধারণত তাদের চামড়ার নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং বাইরে লম্বা লোম থাকে। এসব তাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে। পৃথিবীর শীতল ও পাহাড়ি স্থানগুলোতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হলো তুষার চিতা, এন্ডিয়ান কন্ডর, লম্বা শিঙের ভেড়া, আইবেক্স, পাহাড়ি গরিলা, লিঙ্কস ইত্যাদি।
সমতলভূমি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থাকলেও সেখানে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সেই স্থানের জলবায়ু অক্ষাংশের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই বিভিন্ন স্থানের সমতল ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে।
Promotion