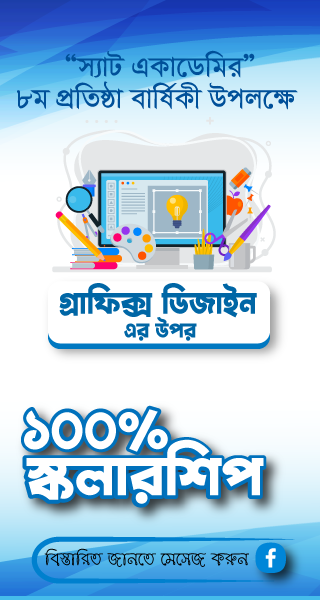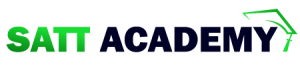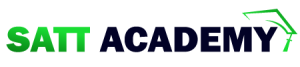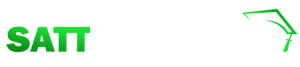প্রাচীন সভ্যতাসমূহ
ভূমিকা
পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আর এ কারণে মানব সভ্যতার বিকাশ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে শিকারী সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে মানুষ নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করে। কৃষিভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এই দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নত কর্ম কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাসও শুরু করে। ধারণা করা হয় এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে পশুটানা লাঙ্গল, চাকাওয়ালা গাড়ি, পালসহ নৌকা, প্রাথমিক ধাতু শিল্প এবং প্রাথমিক ধরনের পৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আর এ সকল আবিষ্কার একের পর এক ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে পূর্ব ইউরোপ ও তৎসংলগ্ন উত্তর আফ্রিকায়। যার ফলে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, পূর্ব ইউরোপের নিম্ন বলকান অঞ্চল ও মিসরে প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আধুনিক মানব সমাজ এ সকল সভ্যতার নিকট ঋণী। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ ইউনিটে প্রাচীন নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিষ্কার, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব।
এই ইউনিটের পাঠসমূহ
পাঠ ১: মিসরীয় সভ্যতা
পাঠ ২: সুমেরীয় সভ্যতা
পাঠ ৩: ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
পাঠ ৪: পারসিক সভ্যতা পাঠ ৫: হিব্রু সভ্যতা
পাঠ ৬: গ্রিক সভ্যতা
পাঠ ৭: রোমান সভ্যতা
পাঠ-১.১
মিসরীয় সভ্যতা
উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-
প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন; প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় ধর্মবিশ্বাস, লিখন পদ্ধতি, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
মুখ্য শব্দ
মিসরের নীলনদ, ‘ফারাও’, র্যামেসিস, ‘আমন রে’, পিরামিড ও মমি
ভূমিকা:
মানুষ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এই দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত ছিল কৃষি ভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে। যার কারণে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নতি ও কর্ম-কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করে। আর মিসরীয় অঞ্চলের এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে বিভন্ন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এ সকল আবিস্কারের কারণে মিসরে প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আর তাই আধুনিক মানব সমাজ মিসরের এ সভ্যতার নিকট থেকে উপকৃত হয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পাঠে প্রাচীন মিসরীয় নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিষ্কার, ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি আলোচনা করব।
মিসরীয় সভ্যতার কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির দেশ মিসর। এছাড়া বর্তমান উত্তর আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ এই মিসর। আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে নীলনদের অববাহিকায় মিসরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সুদান নামক রাষ্ট্রটি অবস্থিত। এর পূর্ব দিকে বয়ে গেছে লোহিত সাগর এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত লিবিয়া। আর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত তিউনিসিয়া। নীল নদের দান বলে খ্যাত মিসর ভৌগোলিক দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চল (Upper) এবং উত্তরাঞ্চল (Lower) এই দু'ভাগে বিভক্ত । মিসরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নীলনদ ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়েছে। বর্ষার সময় নীল নদের দু'কূল প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হতো। ফলে মিসরে উভয় অঞ্চলে পলিমাটি জমে
মিসর নীলনদের দান নীলনদের পানি উপচে দু'কূল ছাপিয়ে যাবার ফলে নবোপলীয় যুগের মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য বিষয়াদি ভাসিয়ে নিঃস্ব করে ফেলত। প্রাচীন মিসরে প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষির উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে কৃষি
উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ ও পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। নীলনদের দু'কুলে ৪ মাস স্থায়ী এ বন্যার সময় গাছ-গাছড়া পচে গিয়ে এবং এর সাথে জলধারায় পাহাড়ি লাল পাথুরে মাটি মিশে এক উর্বর পলিমাটির সৃষ্টি হতো। এ কারণে মিসরের এ অঞ্চলসমূহের জমি খুব উর্বর হতো। বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডটাস মিসরের উৎকর্ষতা দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি মিসরকে “নীলনদের দান” বা “The gift of the Nile” বলে উল্লেখ করেছেন।
মিশরের নীলনদ
প্রাচীন মিসরীয় রাজনৈতিক ইতিহাস
ধারণা করা হয়, মিসরীয় সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ পর্যন্ত সময়কালকে মিসরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। রাজা মেনেস নামে এক শক্তিশালী সামন্ত রাজা খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁকে মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। উচ্চ মিসরের রাজধানী ছিল থিস (Thebes)। দক্ষিণ মিসরের মেম্ফিশ শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করা হয়। রাজা মেনেসের পর থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিসরে ৩১টি রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। তা হচ্ছে প্রথমত: প্রাক রাজবংশীয় যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), প্রাচীন রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০-২৩০০), সামন্ত যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০-২১০০), মধ্য রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০-১৭৮৮), বৈদেশিক হিক্সসদের আক্রমণ (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০-১৫৮০) এবং নতুন রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮০-১০৯০) পর্যন্ত।
প্রাচীন মিসরীয় শাসন ব্যবস্থা
নীল নদের অববাহিকায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সূচনা হয় প্রাক-রাজবংশীয় যুগে। এ যুগে মিসরীয়রা কৃষি কাজে সেচব্যবস্থার বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার করে। এ ছাড়া তারা লিখন পদ্ধতি, উন্নতমানের কাপড়, সৌরপঞ্জিকা প্রস্তুত করতে শিখে। ৩২০০ খ্রি: পূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ প্রাচীন রাজত্বকালের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। রাজা মেনেস উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে এক করে একটি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মিসরের সম্রাটদের ‘ফারাও' বলা হতো। ফারাও শব্দের অর্থ ‘বড়বাড়ি’ । বিশাল প্রাসাদে বসবাসকারী ফারাওদের মনে করা হতো ঈশ্বরের সন্তান। তাঁরা একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ‘ফারাও’রা নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য ভাই-বোনের সাথে বিয়ের প্রচলন করেন। সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন একজন উজির বা প্রধানমন্ত্রী। মিসরের ‘ফারাও’ বা সম্রাটের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাজা মেনেস, প্রথম আহমোজ, রাজা তুথমোস, সম্রাট ইখনাটন, তৃতীয় আমেনহোটেপ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় র্যামেসিস। পরাক্রমশালী তৃতীয় র্যামেসিসের মৃত্যুর পর শক্তিশালী শাসক না থাকায় ‘ফারাও’ বা সম্রাটদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানা পরিবর্তনের পর ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পার্সীয়ানদের হাতে এ সভ্যতার পতন ঘটে। প্রাচীন মিসরীয়দের জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়
ধর্ম বিশ্বাস
প্রাচীন মিসরীয়রা বিশ্বাস করত যে, প্রকৃতিকে দেবদেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। তাই প্রাচীন মিসরীয় সমাজে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। প্রধান ধর্মীয় নেতা ছিল রাজা বা ফারাও । তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল ‘আমন রে' (Ammon Re)। নীলনদের দেবতা নামে খ্যাত ছিল ওসিরিস (Osiris)। মিসরীয়রা আত্মার অবিনশ্বরতা ও পূনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল দেহ ছাড়া আত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হবে। এজন্যই তারা ফারাও বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে মমি প্রস্তুত করত। মমিকে যুগ পরস্পরায় অক্ষত রাখার জন্য নির্মাণ করা হয় সমাধি স্তম্ভ পিরামিড। তবে ধর্ম বিশ্বাসে ন্যায় অন্যায়ের বা পাপ-পূণ্যের বিশ্বাসও জড়িত ছিল। মিসরীয় সমাজে পুরোহিতদের দৌরাত্ম ছিল ব্যাপক। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭৫ অব্দে রাজা চতুর্থ আমেনহোটেপের নেতৃত্বে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিনি প্রধান পুরোহিতদের মন্দির থেকে বহিস্কার করে একক দেবতা এটন (Aton) (বা একেশ্বর) এর পূজা করার নির্দেশ দেন। তাদের ধারণা ছিল, পাপ-পূণ্যের বিচারের মাধ্যমে পুণ্যবানকে সুখময় স্থানে ও পাপীকে অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ করা হবে।
লিখন ও লিপি পদ্ধতি
তোলার সাথে
সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের অন্যতম প্রধান অবদান লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। নগরসভ্যতা গড়ে মিসরীয়রা প্রথম লিখন ও লিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্র লিখন পদ্ধতি। এটি গ্রীকদের দেয়া নাম। যার অর্থ দাঁড়ায় ‘পবিত্র লিপি'। এ হায়ারোগ্লিফিক পদ্ধতির রূপ পাওয়া গিয়েছে। এ লিখন পদ্ধতি তার চারিত্রিক বিন্যাসের দিক থেকে তিনটি রূপ পায়। যেমন- চিত্রভিত্তিক, অক্ষরভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক। খোদাই কাজ করা বা চিত্রে প্রদর্শন করা- এই পদ্ধতির ২৫টি বর্ণ ছিল এবং প্রতিটি বর্ণ একটি বিশেষ চিহ্ন বা অর্থ প্রকাশ করতো। মিসরেই প্রথম মানব জাতি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবনে সক্ষম হয়। প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নতমানের কাগজের আবিষ্কার মিসরীয়দেরই অবদান। A B B H 00 F G K L N ++ Q R S T
হায়ারোগিণ্ঢফিক
দর্শন ও বিজ্ঞান
আধুনিক সভ্যতা অনেকটা প্রাচীন মিসরীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের নিকট দায়বদ্ধ। সে যুগে জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন মিসরে কারিগরিবিদ্যার প্রসার লাভ করেছিল। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে নানা প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কার হয়। মিসরীয়রা গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শি ছিল বলে জানা যায়। তারা নিকটবর্তী নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করার কৌশলও আয়ত্ব করেছিল। মিশরীয়রা নীলনদের জোয়ার-ভাটা নির্ণয় এবং এ সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান আয়ত্ন করেছিল। মিসরীয় বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। তারা যোগ-বিয়োগের ব্যবহার জানলেও গুণ ও ভাগ করতে জানতো না । মধ্য রাজবংশের যুগ থেকে মিসরীয়গণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন । মিসরীয়রা চক্ষু, দন্ত ও পেটের পীড়া রোগের চিকিৎসা আবিষ্কারে সক্ষম হয়। তারা বিভিন্ন রোগ ও ঔষধের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং ‘মেটেরিয়া মেডিকা” (Materia Medica) বা ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করেন। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য মিসরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী এক ধরনের ঔষুধ আবিষ্কার করেছিল। ধারণা করা হয় সে যুগে দাঁত, চোখ ও পাকস্থলি প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিল।
পিরামিড
মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়। প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আশ্চর্য নিদর্শন ‘পিরামিড’। পাথর দিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরী ত্রিকোনাকার পিরামিড আজও মিসরের কায়রো শহরের অদূরে সভ্যতার ইতিহাস বহন করছে। এ সকল পিরামিডের অভ্যন্তরে মিসরের রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের মৃতদেহ (মমি) করে রাখা হয়েছে। লক্ষাধিক পাথর টুকরো করে নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে এই পিরামিড তৈরী করা হতো এবং এক একটা পিরামিড চার থেকে পাঁচশ ফুট উচু ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মিসরীয়দের বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশল কি পরিমান উন্নত ছিল। মিসরে অনেক পিরামিড আছে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ফারাও খুফুর পিরামিড।
মিসরীয় সভ্যতার পতন
প্রাচীন মিসরের বিশতম রাজবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন একাদশ রামসেস। এ সময় মিসরে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১০৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে থিবস শহরের প্রধান পুরোহিত বা ধর্মযাজক সিংহাসন দখল করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিসর অধিকার করলে মিসরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে। অতঃপর ৩৩২ খ্রিঃপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার মিসর অধিকার করেন। তারপর থেকে মিসরে “টলেমী রাজবংশ” প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমী রাজবংশ দীর্ঘদিন মিসর শাসন করে। এই বংশেরই রাণী ছিলেন বহু আলোচিত ও জগত খ্যাত রানী ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রার সময় মিসর বারবার রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কালক্রমে রোমানরা মিসরে রোমান শাসন বিস্তার করে। মিসর থেকে রোমানদের দূরে রাখতে রোমান সম্রাটদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন চতুর ক্লিওপেট্রা। মিসরীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয়েছিল নিজের ভাই টলেমির সঙ্গে। এর কয়েক বছর পর জুলিয়াস সিজার পম্পেই বিজয়ের মাধ্যমে মিসরে আসেন। তিনি প্রেমে পড়েন ক্লিওপেট্রার । জুলিয়াস সিজারের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সমর্থনে টলেমি রাজ্যচ্যুত হন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।
সুমেরীয় সভ্যতা
উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি
সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি বা উন্মেষ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;
সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ও
প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন ।
মুখ্য শব্দ
‘এনসি’, আক্কাদীয় রাজ্য, ‘ডুঙি’, ‘গিল গামেশ’, ‘জিগগুরাট’ ও ‘কিউনিফর্ম'
ভূমিকা : আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (যথাক্রমে দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলো একত্রিতভাবে ‘মেসোপটেমীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। একে অনেকে ‘Fertile Crescent' বা 'অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি ও বলে থাকে। ৪০00 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিসরীয় সভ্যতার সমসাময়িক মেসোপটেমীয় সভ্যতা অনেকগুলো জাতির অবদানে গড়ে ওঠে। এ সকল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, কাসাইট, অ্যাসিরীয় এবং ক্যালডীয়রা অন্যতম। ‘মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ-যার অর্থই হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। আর দুই নদী বলতে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিলো সুমেরীয় জাতি।
সুমেরীয় সভ্যতা
৫০০০ খ্রিস্টপূর্বে সুমেরীয় জাতি মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এরা অ-সেমিটিক জাতিগোষ্ঠি এবং মধ্য এশিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লিখন পদ্ধতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, আইন কানুন প্রণয়ন, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি সুমেরীয়রাই প্রথম শুরু করে।
সুমেরীয় রাষ্ট্র
কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে সুমেরীয়রা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। সুমেরীয়রা কতকগুলি নগরের গোড়াপত্তন করেছিল। এগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী উর ছাড়াও সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র ছিল লাগাস, কিস, ইরিদু এবং উরুক অন্যতম। সুমেরীয় সভ্যতায় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের পদবী ছিল ‘পাতেজী’। সুমেরীয়রা প্রথম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খাল খনন, জলাশয় ও বাঁধ নির্মাণ করে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং নিজেদের উন্নতি ঘটিয়ে নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮টি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব নগর রাষ্ট্রের প্রশাসকরা ‘এনসি' নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত শাসক সারগন সুমেরের নগর রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সুমেরিয়ায় সারগনের প্রতিষ্ঠিত আক্কাদীয় রাজ্য দুশো বছর স্থায়ী ছিল। সুমেরীয়দের পরবর্তী বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট ‘ডুঙি’। সম্রাট ডুঙির নেতৃত্বে সুমেরীয়গণ খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। ডুঙি সুমের জাতির জন্য সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন (Code) প্রচলন করেন। সুমেরীয় সমাজে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল ।
সুমেরীয় সমাজ
বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল সুমেরীয় সমাজ ব্যবস্থা। প্রথমস্তরে ছিল শাসক ও ধর্মযাজক, দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ নাগরিক এবং তৃতীয় স্তরে ছিল ক্রীতদাস সম্প্রদায়। শাসকগণ নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি দাবি করে দেশ শাসন করতেন। দাসদাসীরা শাসকদের সেবায় নিয়োজিত থাকতো। স্বাভাবিক ভাবেই দাসদাসী এবং কৃষক ছিল সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়।
সুমেরীয়দের প্রতিশোধমূলক আইন
সাধারণভাবে সুমেরীয়দের আইনকে বলা হয় প্রতিশোধমূলক আইন। অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি। সুমেরীয়দের আইনের মূল বিষয় ছিল, প্রথমতঃ অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য তদ্রুপ শাস্তি দেয়া ।
দ্বিতীয়তঃ একধরণের বিচার আদালত বিদ্যমান ছিল, যেখানে বাদী বিবাদী উভয়কেই হাজির করা হতো। তৃতীয়তঃ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য কঠোর ছিল। অথচ সামরিক বাহিনীতে একমাত্র অভিজাতদেরই অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল। অন্যান্য সমাজের মতো সুমেরীয় আইনও গড়ে ওঠেছিল তাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যদিয়েই। সুমেরীয়দের বিখ্যাত সম্রাট ‘ডুঙি’ প্রথম আইন সংকলন করেন। সুমেরীদের আইন ব্যবস্থা পরবর্তী সমসাময়িক সভ্যতাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। সুমেরীয় আইনের মূল অধ্যায় ছিল- ক. প্রতিশোধমূলক আইন, খ. আইনে অসমতা এবং গ. আকস্মিক ও ইচ্ছাকৃত হত্যার স্বল্প পার্থক্য।
অর্থনৈতিক কাঠামো
সুমেরীয়দের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। মিসরের মত এখানে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সুমেরীয় সমাজে ভূমি দাসের অস্তিত্ব ছিল। তবে কারিগরী কাজে নিপুন শ্রমিকরা উচ্চ পারিশ্রমিক লাভ করতো। সুমেরীয় অর্থনীতির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষক হিসেবে এরা ছিল বেশ উঁচু স্তরের। তাদের সেচ ব্যবস্থা ছিল উন্নততর। ফসল উৎপাদনের পরিমানও ছিল বেশী। সুমেরীয়দের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের এক বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুমেরীয় ‘সীল’ দেখে অনুমান করা হয় সম্ভবত ভারতের সাথেও তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সুমেরীয়রা প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম মৃত্রিকাস্তুপের উপর শহর, গ্রাম এবং মন্দির গড়ে তোলে । সুমেরীয় ধর্ম
অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় সুমেরীয়রা অনেক দেব দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তাদের এক একটি দেবতা এক একটি নামে পরিচিত ছিল। যেমন বিখ্যাত দেবতা ‘শামাশ” (সূর্যদেবতা), ‘এনলিল' (বৃষ্টি, বন্যা ও বায়ুর দেবতা), পানির দেবতা ‘এনকি’, প্লেগ রোগের বিশেষ দেবতা ‘নারগাল’ এবং ‘ইস্টারা’ (নারী জাতির দেবতা) নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল নার্গাল। সুমেরীয় সভ্যতায় মিসরীয় সভ্যতার অনেক প্রভাব থাকলেও পরকালের ধারণা বা পুনরুজ্জীবন (স্বর্গ-নরক) ধারণা জন্ম লাভ করেনি মিসরীয়দের মধ্যে। সম্ভবতঃ এই কারণে সুমের অঞ্চলে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার অট্টালিকা, সমাধি বা মমির প্রবণতা দেখা যায় না। তাই তারা মৃতদেহকে কবর দিতো।
সুমেরীয় সাহিত্য
সুমেরীয়রা বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশী মিসরীয়দেরকেও অতিক্রম করেছিল। যেমন, সুমেরীয়রা ‘গিল গামেশ’ নামক মহাকাব্য রচনা করেছিল। ইউরুকের কিংবদন্তী রাজা গিলগামেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই বিখ্যাত ‘গলগামেশ’ নামক মহাকাব্য। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।
সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতি
সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম কীর্তি ছিল একধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। এই পদ্ধতি ছিল প্রথমতঃ চিত্রলিপি এবং পরবর্তীতে তা শব্দলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এই লিখন পদ্ধতি ‘কিউনিফর্ম' নামে পরিচিত। কাঁদা মাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাংকন দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতো। যা মেসোপটেমীয় লিপি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এ সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে এ কিউনিফর্ম (Cuneiform) চিত্রলিপির প্রায় চার হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে। এসকল কিউনিফর্ম বর্ণভিত্তিক নয়, বরং একে বলা যেতে পারে অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি ।
সুমেরীয় স্থাপত্য ও শিল্প
কিউনিফর্ম
ধারনা করা হয় সুমেরীয়রা নগর সভ্যতায় পোড়া ইটের প্রথম ব্যবহার। তবে মিসরীয়দের মতো সুমেরীয়রা পাথরের ব্যবহার করতো না বলে তাদের তৈরী ইমারত দীর্ঘস্থায়ী হতো না। সম্ভবতঃ সুমের অঞ্চলে পাথর দুস্প্রাপ্য ছিল। তবে তাদের নগর পরিকল্পনা ছিল খুবই নিখুঁত। দালানের দেয়াল ইটের তৈরী হলেও ছাঁদ ছিল কাঠের দ্বারা তৈরী। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি ‘জিগগুরাট' নামক ধর্মমন্দির। প্রায় প্রতি নগরেই এইরূপ জিগগুরাট নামক ধর্মমন্দির বা ইমারত তৈরী হয়েছিল। সুমেরীয়দের অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল গণনা পদ্ধতি, গুণভাগ নির্ণয়, চন্দ্র ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি তৈরী, পানি দ্বারা
ব্যাবিলনিয়া (/ˌbæbɪˈloʊniə/) ছিল মধ্য-দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক ও সিরিয়া) ভিত্তিক একটি প্রাচীন আক্কাদিয়ান-ভাষী রাজ্য এবং সাংস্কৃতিক এলাকা। ১৮৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি ছোট অ্যামোরাইট-শাসিত রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল, যেখানে ব্যাবিলন ছিল একটি ছোট প্রশাসনিক শহর। [১] আক্কাদিয়ান সাম্রাজ্যের (২৩৩৫-২১৫৪ খ্রিস্টপূর্ব) সময় এটি ছিল নিছক একটি ছোট প্রাদেশিক শহর কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতকের প্রথমার্ধে হাম্মুরাবির রাজত্বকালে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় এবং একটি প্রধান রাজধানীতে পরিণত হয়। হাম্মুরাবির রাজত্বকালে এবং তার পরে, ব্যাবিলোনিয়াকে "আক্কাদের দেশ" বলা হতো, আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী গৌরবের কথা উল্লেখ করে।
সুমের এবং আক্কাদ নামের এলাকা দুইটি ব্যাবিলনিয়ার অংশ ছিলো। খ্রিস্টপূর্ব যাবো ২৩ শতকে আক্কাদের রাজা সারগনের সময়কালের একটি কাদামাটির ফলকে প্রথম ব্যাবিলনিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে অ্যামোরাইট নামের এক জাতি বাস করত। এরা খ্রীষ্টপূর্ব 1894 অব্দে মেসোপটেমিয়ায় এসে সুমের ও আক্কাদ নগরীর মাঝামাঝি ব্যাবিলন নামক স্থানে একটি সভ্যতা গড়ে তোলে। এটিই ব্যাবিলন সভ্যতা নামে পরিচিত। ব্যাবিলন শব্দটির অর্থ "দেবতার নগরী"। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটি যেখানে সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছে সেখানেই গড়ে তোলা হয়েছে এই নগরী। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি এবং প্রথম রাজা ছিলেন বিখ্যাত অ্যামোরাইট নেতা সুমুয়াবাম। নগরীর ঘর-বাড়ি গুলো রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো। প্রতিটি নগরে নির্মাণ করা হয়েছিলো জিগুরাট। বরিসিবাপ নগরের জিগুরাটটি ছিলো সাত তলাবিশিষ্ট। 650 ফুট উচু পিরামিডের মতো জিগুরাটে ছিলো বিচার কক্ষ, স্কুল কক্ষ ও সমাধি।
ব্যাবিলন ছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ নগরী। ১৭৭০ থেকে ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়টিতে ব্যাবিলনই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহর। ২ লাখেরও বেশি জনসংখ্যার প্রথম নগরী বলেও মনে করা হয় ব্যাবিলনকে। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের দিকে ব্যাবিলন নগরীটি সুরক্ষিত ছিল বিশাল আকারের প্রাচীরের আড়ালে। পুরো নগরী বেষ্টন করে ছিল ২ স্তরের প্রাচীর, যেন প্রথম প্রাচীরের পতন ঘটলেও দ্বিতীয়টি দিয়ে শত্রু ঠেকানো যায়। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে এ দেয়ালগুলো ছিল ৩০০ ফুট উঁচু, ৮০ ফুট চওড়া ও ৫৫ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। অবশ্য বর্তমানকালের ঐতিহাসিকদের মতে হেরোডোটাস বাড়িয়ে বলেছিলেন। তাদের মতে দেয়ালগুলো ছিলো ৯০ ফুট উঁচু ও ১০ মাইল লম্বা। এ দুই দেয়ালের মাঝে ছিল পরিখা, যা শত্রুপক্ষের জন্য শহরের ভেতরে প্রবেশ করাকে রীতিমতো অসম্ভব করে রেখেছিল। আরও ছিল ওয়াচ টাওয়ারগুলোতে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা। এছাড়া ইউফ্রেটিস নদী শহরটির মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। ফলে অবরুদ্ধ থাকাবস্থায় পানির সরবরাহ নিয়েও তাদের চিন্তার কিছু ছিল না। ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের রাজা ২য় সাইরাস, যিনি ‘সাইরাস দ্য গ্রেট’ নামেই বেশি পরিচিত। তিনি আক্রমণ করে বসেন ব্যাবিলনে। কিন্তু ব্যাবিলনের সৈন্যরা সাইরাসের এ আক্রমণকে পাত্তাই দেয়নি। তারা তখন ফসল কাটার উৎসবে ব্যস্ত ছিল। শহরের নিরাপত্তা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা ব্যাবিলনের সৈন্যদের কাছে সাইরাস যেন ছিলেন এক শিশু। কিন্তু চারদিকে প্রাচীর ঘেরা শহরের ভেতর বহমান ইউফ্রেটিস নদীর প্রবেশপথে গেট নির্মাণ করে রাখলেও এদিকে বাড়তি আর কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখেনি তারা। শহরটির সৈন্যরা কখনও আশা করেনি, পানির নিচে কেউ সেই গেট ভেঙে তাদের শহরে আক্রমণ চালাবে। এছাড়া পানির নিচে কেউ এত দীর্ঘ সময় ধরে দম আটকে রাখতে পারবে বলেও মনে করেনি তারা। আর তাদের ঠিক সেই জায়গা দিয়েই আক্রমণ করলেন সাইরাস। নদীর আশপাশে বিভিন্ন খাল ও অন্যান্য জলাশয় খনন করে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ব্যবস্থা করলেন তিনি। ফলে নদীতে পানির স্তর নিচে নেমে যায়। তখনই দেখা মেলে গেটগুলোর। এরপর এক রাতে গোপনে তার সৈন্যরা সেখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এর মূল ফটকটি খুলে দেয়। এরপর মৌমাছির ঝাঁকের মতো শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে সাইরাসের বাহিনী। প্রকৃত অবস্থাটি ব্যাবিলনের সৈন্যদের বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। যখন বুঝল ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে। আর দিনরাত নাচগান ও মদের রাজ্যে ডুবে থাকায় তারা সেভাবে প্রতিরোধও গড়তে পারেনি। সাইরাস দ্য গ্রেটের সৈন্যদলের কাছে কচুকাটা হতে হয়েছিল তাদের।
সমাজ[উৎস সম্পাদনা]
ব্যাবলনীয় সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো। উচু শ্রেণীতে ছিলো রাজা, পণ্ডিত, পুরোহিত ও সৈন্য। এদের নিজস্ব জমি ছিলো। শিল্পী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীরা ছিলেন মধ্য শ্রেণীতে। আর নিন্ম শ্রেণীতে ছিলো কৃষক, সাধারণ শ্রমিক ও দাসরা। ব্যাবলনীয় সমাজে যুদ্ধবন্দীদের দাস করা হতো।
রাজা হাম্বুরাবি[উৎস সম্পাদনা]
ব্যাবিলনীয় সভ্যতার রাজা হাম্বুরাবি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি ছিলেন ব্যাবিলনের ষষ্ঠ রাজা। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব 1792 অব্দে ব্যাবিলনের রাজা হন। তিনি খন্ড-বিখন্ড নগররাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলকে ব্যাবিলনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। ব্যাবিলনের সর্বাধিপতি এ রাজা খ্রীষ্টপূর্ব 1750 অব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
পারস্য ইরানের প্রাচীন নাম। ১৯৩৫ সাল পর্যন্তও বহির্বিশ্বে ইরান "পারস্য" নামে পরিচিত ছিল, যদিও ইরানিরা বহুযুগ ধরে নিজেদের দেশকে ইরান নামেই ডেকে এসেছে।
প্রথম পারসিক সাম্রাজ্য[উৎস সম্পাদনা]
আর্য জাতির বিভিন্ন গোত্র খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে ইরানীয় মালভূমিতে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেদেস ও পারসিক গোত্রদ্বয়। মেদেস গোত্রীয় লোকেরা মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশে বাস করা শুরু করে। পারসিক জাতির লোকেরা ঊর্মিয়া হ্রদের পশ্চিমের পার্সুয়া নামের অঞ্চল থেকে এসেছিল; এরা ইরানীয় মালভূমির দক্ষিণ অংশে বাস করা শুরু করে এবং অঞ্চলটির নাম দেয় পার্সুমাশ। পারসিকদের প্রথম বড় নেতার নাম ছিল হাখ'মানেশ, এক যুদ্ধবাজ সেনাপতি। হাখ'মানেশ ৬৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ জীবিত ছিলেন। মেদেস জাতির লোকেরা পারসিকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করত। ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহান কুরুশ [Cyrus the Great] পারসিকদের রাজা হন এবং এর পর পারসিকদের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। কুরোশ মেদেসীয় বা মেদীয়দের পরাজিত করেন, ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ লিদিয়া রাজ্য এবং ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন জয় করেন। কুরোশের অধীনে পারস্য এশিয়ার অন্যতম মহাশক্তিতে পরিণত হয়। কুরুশের পুত্র ২য় কামবুজিয়েহ ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশর বিজয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ৫২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট ১ম দরিয়ুশ ক্ষমতায় আসার পর সিন্ধু নদ পর্যন্ত পারস্যের পূর্ব সীমানা প্রসারিত করেন। তিনি নীল নদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করান এবং সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্যকে ঢেলে সাজান। তার নাম হয় মহান দরিয়ুশ। ৪৯৯ থেকে ৪৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরে পারসিকদের অধীনে বসবাসরত আয়োনীয় গ্রিকরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের শক্তহাতে দমন করেন। এরপর বিদ্রোহীদের সহায়তা দানের শাস্তি হিসেবে তিনি ইউরোপীয় গ্রিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। কিন্তু ৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ম্যারাথনের যুদ্ধে দরিয়ুশের সৈন্যরা গ্রিকদের কাছে পরাজিত হয়। দরিয়ুশ মারা যাবার আগে গ্রিকদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন। তার পুত্র ১ম খাশয়র্শ' পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু তিনিও ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সালামিসের নৌযুদ্ধে এবং পরের বছরগুলিতে আরও দুইটি স্থলযুদ্ধে গ্রিকদের কাছে পরাজিত হন।
খাশয়র্শ'-এর অভিযানগুলি ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের শেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। খাশয়র্শ'-এর দ্বিতীয় পুত্র সম্রাট ১ম আর্দাশির-এর আমলে মিশরীয়রা গ্রিকদের সহায়তায় পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ৪৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাদের দমন করা হলেও এটি ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম বৃহৎ আক্রমণ এবং এভাবেই এর পতন শুরু হয়।
মহাবীর আলেকজান্ডার ও সেলুকাসীয় রাজবংশ[উৎস সম্পাদনা]
খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে পারস্যে অনেকগুলি বিপ্লব ঘটে। শেষ পর্যন্ত ম্যাসেডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার ৩৩৪ থেকে ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করেন এবং সম্রাট ৩য় দরিয়ুশের সৈন্যদের পরাজিত করে পারস্য বিজয় করেন। পারস্য আলেকজান্ডারের বিশাল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। আলেকজান্ডার তার সেনাবাহিনীতে বহু পারসিক সেনাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তার নির্দেশে সমস্ত গ্রিক উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারেরা পারসিক মহিলাদের বিয়ে করেন। ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হলে তার সেনানেতাদের মধ্যে পারস্যের সিংহাসন দখলের লড়াই শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১ম সেলেউকুস বা সেলুকাস পারস্যের রাজা হন। তিনি পূর্বে সিন্ধু নদ থেকে পশ্চিমে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিশাল এলাকার রাজা ছিলেন। তার বংশধরেরা পারস্যে সেলুকাসীয় রাজবংশ গঠন করে। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত পার্থীয় জাতির লোকেরা সেলুকাসীয় রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপর আরও প্রায় চারশত বছর পারস্য পার্থীয়দের অধীন সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। পারসিকরা এসময় ছিল পার্থীয়দের অধীন একটি প্রজারাজ্যের অধিবাসী।
সসনীয় রাজবংশ[উৎস সম্পাদনা]
২২৪ খ্রিষ্টাব্দে পারসিক জাতির রাজা ১ম আর্দাশির পার্থীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হর্মুজের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। তিনি এক নতুন পারসিক রাজবংশের পত্তন করেন, যার নাম সসনীয় রাজবংশ। এরপর তিনি পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দখল করেন এবং শেষে ভারত আক্রমণ করেন। সেখানে পাঞ্জাব তাকে করপ্রদানকারী এক রাজ্যে পরিণত হয়। এরপর তিনি আর্মেনিয়া জয় করেন। আর্দাশির ছিলেন অগ্নি-উপাসক জরথুষ্ট্রবাদী। তার সময় পারস্যতে জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম সরকারি ধর্মের মর্যাদা পায়। ২৪১ খ্রিষ্টাব্দে আর্দাশিরের ছেলে ১ম শাপুর ক্ষমতায় আসেন। তিনি বাইজেন্টীয় রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দুইবার যুদ্ধে যান এবং এভাবে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের এক বড় এলাকা পারস্যের অধীনে আনেন। কিন্তু ২৬০ থেকে ২৬৩ সালের মধ্যে তিনি তার বিজিত এলাকাগুলি রোমের মিত্র, পালমিরা রাজ্যের শাসক ওদেনাথুসের কাছে হারান। এরপর সম্রাট নারসেস আবার বাইজেন্টীয় রোমানদের সাথে যুদ্ধে যান এবং ২৯৭ সালে রোমান সেনাবাহিনী তার বাহিনীকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। তিনি শেষ পর্যন্ত রোমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করেন এবং পারস্যের সীমানা ইউফ্রেটিস নদী থেকে পূর্বে সরিয়ে টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত নিয়ে আসেন। এছাড়া আরও অনেক অঞ্চল হাতছাড়া হয়। রাজা ২য় শাপুর, যিনি ৩০৯ থেকে ৩৭৯ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন, রোমানদের সাথে পরপর তিনটি যুদ্ধে অংশ নেন এবং অনেক হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।
পারস্যের এরপরের শাসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ১ম ইয়াজদেগের্দ। তিনি ৩৯৯ থেকে ৪২০ সাল পর্যন্ত শান্তিতে শাসন করেন। তিনি প্রথমে পারস্যের খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং নিজেও খ্রিস্টান হবার চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম জরথুষ্ট্রবাদে ফিরে যান এবং খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। তার ছেলে ৫ম বাহরামও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অব্যাহত রাখেন। বাহরাম ৪২০ সালে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু রোমানরা ৪২২ সালে তাকে পরাজিত করে। শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে রোমানরা প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের রাজ্যে জরথুষ্ট্রীয়দের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেবে যদি পারস্যে খ্রিস্টানদের একই মর্যাদা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর দুই বছর পরে বাইজেন্টীয় রোমানদের গির্জা পশ্চিম রোমের গির্জা থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।
৫ম শতকের শেষদিকে মধ্য এশিয়া থেকে শ্বেত হুন জাতির লোকেরা পারস্য আক্রমণ করে এবং ৪৮৩ সালে পারস্যের রাজা ২য় ফিরোজকে পরাজিত করে। এরপর কিছু বছর ধরে তারা আক্রমণ না করার প্রতিদান হিসেবে পারস্য থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে যায়। ৪৮৩ সালে পারস্যের খ্রিস্টানরা নেস্তরবাদকে সরকারী ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। রাজা ১ম কাভাধ মাজদাক নামের এক জরথুষ্ট্রীয় ধর্মীয় নেতার অনুশাসনের প্রতি দুর্বল ছিলেন। কিন্তু ৪৯৮ সালে তার অর্থোডক্স খ্রিস্টান ভাই জামাস্প তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরে শ্বেত হুনদের সহায়তায় ৫০১ সালে কাভাধ আবার ক্ষমতায় আসেন। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে দুইটি অমীমাংসিত যুদ্ধে অংশ নেন। ৫২৩ সালে তিনি মাজদাকের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং মাজদাকের অনুসারীদের গণহারে হত্যা করেন। কাভাধের পুত্র ছিলেন ১ম খসরোও। তিনি সম্রাট ১ম জুস্তিনিয়ানের অধীন বাইজেন্টীয় রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দুইটি যুদ্ধ করেন এবং পারস্যের সীমানা ককেশাস ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ১ম খসরোও ছিলেন সবচেয়ে পরাক্রমশালী সসনীয় রাজা। তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসনের সংস্কারসাধন করেন এবং সরকারী ধর্ম হিসেবে জরথুষ্ট্রবাদকে পুনর্বহাল করেন। তার পৌত্র ৩য় খসরোও ৫৯০ থেকে ৬২৮ সাল পর্যন্ত পারস্য শাসন করেন। উল্লেখ্য, তার শাসনামলে আরবে মুহম্মদ ও ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। যদিও বাইজেন্টীয় সম্রাট মরিসের সহায়তায় তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, ৩য় খসরোও ৬০২ সালে বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের সাথে এক দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু করেন। ৬১৯ সাল নাগাদ তিনি এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং মিশর দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু বাইজেন্টীয় সম্রাট হেরাক্লিউস এসে তার গতিরোধ করেন এবং ৬২২ থেকে ৬২৭ সালের মধ্যেই পারসিকেরা তাদের পুরানো সীমান্তে ফেরত যেতে বাধ্য হয়।
৩য় ইয়াজদেগের্দ ছিলেন সসনীয় রাজবংশের শেষ রাজা। তার আমলেই আরবদেশের মুসলমানেরা পারস্য আক্রমণ করে ও শেষ পর্যন্ত পারস্য বিজয় করে।
পাঠ-১.৫
হিব্রু সভ্যতা
উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-
■ হিব্রু জাতির উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। • হিব্রু সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
হিব্রু ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
মুখ্য শব্দ
হিব্রু জাতি, ইসরাইল, জুদাহ রাজ্য, জেরুজালেম, একেশ্বরবাদ ও ‘অ্যাপক্রিপা’
হিব্রুদের পরিচয়
হিব্রু জাতি প্রাচীন মিসরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার পর প্রাচীন মানব সভ্যতায় অবদান রেখেছিল। হিব্রুরাই ইহুদী ধর্মের অনুসারী এবং ইসরাইলী জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন ফোরাত নদীর (ইউফ্রেটিস নদী) অপর পাড় থেকে যে সব মানবগোষ্ঠী বিতাড়িত হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে-তারাই হিব্রু জনগোষ্ঠী। হিব্রু শব্দের অর্থ ‘বিদেশী’ (Alien) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই নৃতাত্ত্বিক অর্থে হিব্রুরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়। মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয় উৎস থেকে আহরিত হয়েছিল হিব্রু সভ্যতার অনেক উপাদানই ।
হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস
হিব্রু জাতির বসবাসের অঞ্চলসমূহ
হালিব
ভূমধ্যসাগর
দামেস্ক
হেবরন
আরব উপদ্বীপ
সিনাই পর্বত
লোহিত সাগর
হিব্রু জাতির বসবসাসের অঞ্চল
হিব্রু জাতি খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে তাদের আদি পুরুষ ইব্রাহিমের (আ:) (আব্রাহাম) নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় একত্রে বসবাস শুরু করে। অতঃপর ইব্রাহিমের (আ:) এর পৌত্র ইয়াকুব (আ:) (জ্যাকব) হিব্রুদের নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। ইয়াকুব এর অপর নাম ‘ইসরায়েল’ থেকেই উক্ত জাতি ইসরাইলী নামে পরিচিতি। খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরাইলীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে প্রতিবেশী মিসরে গমন করে কিন্তু সেখানে তারা ফারাওদের অধীনে দাসত্ব বরণ করে । খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২৫০ অব্দে নবী মুসা (আ:) (মোজেস) মিসরে আবির্ভূত হয়ে হিব্রুদের মুক্ত করে সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হন। এখানে এসে হিব্রুরা দেবতা যেহোভা'র উপাসনা শুরু করে। অতঃপর দাউদ (আ:) (ডেভিড) এর নেতৃত্বে তারা প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) দখল করে এবং জেরুজালেম শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। দাউদ (আঃ) হিব্রু জাতিকে সুসংহত করেন। তাঁর এর মৃত্যুর পর সুলায়মান (আ:) (সলোমন) হিব্রুদের রাজা মনোনীত হন। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী ও সুপণ্ডিত। খ্রিস্টপূর্ব ৯৩৫ অব্দে সুলায়মান (আ:) মৃত্যুবরণ করলে হিব্রু জাতির পতন শুরু হয়। জেরুজালেম রাজ্য দ্বিখন্ডিত হয়ে উত্তরে ইসরাইল এবং দক্ষিণে ‘জুদাহ রাজ্যে' বিভক্ত হয়। পরে এ্যাসিরীয়গণ হিব্রুরাজ্য এবং ক্যাল্ডীয় রাজা নেবুচাঁদনেজার ‘জুদাহ’ রাজ্য দখল করেন। প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে হিব্রু জাতির উত্থান সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। হারন কানান ফিলিস্তিনলা ব্যাবিলন মেসপটেনিয়া
তাওরাত বা ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) হিব্রু ধর্মের (ইহুদী জাতির) প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মুসা (আ:) এর নেতৃত্বে তারা একেশ্বরবাদের প্রতীক হিসেবে যেহোভার আরাধনায় আকৃষ্ট হয়। মুসা (আ:) এর মৃত্যুর পর হিব্রু ধর্ম কুসংস্কারে পতিত হয়। নিরাকার আল্লাহর স্থলে জেহোভাকে তারা আকার-বিশিষ্ট একেশ্বর বলে মনে করত। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে পারস্যের হাতে জেরুজালেমের পতন ঘটলে হিব্রুরা পারস্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন বন্দীদশায় থাকার পর এক পর্যায়ে হিব্রুদের মধ্যে নব চেতনার উদ্ভব হয়। এ যুগে ইহুদীরা জরথুস্ত্র ধর্মের প্রভাবে আসে এবং আবার একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হয়।
হিব্রু আইন
হিব্রুদেরও আইন তৈরীতে এ্যামোরাইটদের ন্যায় যথেষ্ট অবদান আছে। তবে তাদের আইন অনেকটা হাম্মুরাবীর আইনের দ্বারা প্রভাবিত। ব্যাবিলনীয় আইনের অনুকরণে তারা যে আইন তৈরী করে তা ‘ডিউটোরোনোমিক কোড' নামে পরিচিত ছিল। এই কোড হাম্মুরাবীর আইনের চেয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। তাদের প্রণীত অনুশাসনে গরীব- দুঃখীদের স্বার্থরক্ষা, মানবতা, সুক্ষ্ম বিচার, সুদ গ্রহণে শাস্তির ব্যবস্থা এবং দাসদের মুক্তির যথাযথ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই আইনের প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা মজবুত হয়।
হিব্রু সাহিত্য
হিব্রুদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাহিত্য কর্ম ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এবং ‘অ্যাপক্রিপা’য় (Apocryphal) লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুসার (আ:) এর অনেক বাণী ওল্ড টেস্টামেন্টে সংগৃহীত করা হয়েছে। “উইজডম অব সলোমন” একটি শ্রেষ্ঠ ইহুদী সাহিত্য গ্রন্থ। এ ছাড়া “সোলেমানের গীতিকা” (Songs of Solomon) হিব্রুজাতির জনপ্রিয় গীতিকা। ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এর দ্বিতীয় পুস্তক ('The Book of Exodus') ছিল মূলত মুসা (আ:) এর জীবনবৃত্তান্ত। ষষ্ট পুস্তকটি (“The Book of Joshus') মহাকাব্যের মানসম্মত ছিল। এখানে হিব্রু বীর ও জনগনের ঘটনাবহুল জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অষ্টম পুস্তকে (‘The Book of Ruth') নারীদের অবস্থান ও চরিত্র করুণ রসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। হিব্রু শিল্পকলা এবং স্থাপত্য অতুলনীয়। দাউদ (আ:) জেরুজালেমকে ঐশ্বর্যশালী তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। জেরুজালেমে এখনো অনেক স্থাপত্য তাঁর কীর্তি বহন করছে যা আজও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।
হিব্রু দৰ্শন
গ্রীকদের পূর্বে হিব্রুরা বিস্ময়কর দর্শনের জন্ম দিতে পেরেছিল। এই দর্শন মানুষ ও জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছিল। পুরাতন টেস্টামেন্টে তাদের অনেক দার্শনিক-মতবাদ পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে ‘Book of Proverbs' এবং 'Apocryphal Book of Ecclesiasticus - পুরাতন টেস্টামেন্টের এই দুই অংশে হিব্রুদের প্রাথমিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে।
পারস্য প্রভাবের ফল
হিব্রু ধর্ম উন্নয়নের চূড়ান্ত স্তর ছিল পারস্য প্রভাবের ফল। এই স্তর ছিল ৫৩৯ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। পারস্য প্রভাবের এ সময় ইহুদী ধর্মে একটি বড় রকমের অলোড়ন হচ্ছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরজীবন ও অশুভ শক্তি হিসেবে শয়তানের অস্তিত্ত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। জাগতিক জীবনের ভোগ বিলাশের চেয়ে হিব্রুদের কাছে পরজীবনের শান্তির প্রশ্নটিই বড় হয়ে পড়ে। যাতে হিব্রু ধর্মে একেশ্বরবাদী চেতনার কঠোরতার প্রকাশ ঘটে।
গ্রিক সভ্যতা
উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি
গ্রিক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে জানতে পারবেন; হেলেনিক ও হেলেনিষ্টিক সভ্যতার পার্থক্য বুঝতে পারবেন ও
গ্রিক দর্শন-সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
মুখ্য শব্দ
বলকান উপকূল, ‘ওসেনিয়ান' (সাগরীয়) সভ্যতা, ‘হেলাস’ ‘ইলিয়ড’ এবং ‘ওডিসি’
গ্রিক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল
ইউরোপ মহাদেশের গ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করে গ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। বলকান উপকূলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গ্রিক প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তৃত। ভূ-প্রকৃতিই দেশটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে; দক্ষিণ গ্রিস, মধ্য গ্রিস ও উত্তর গ্রিস। মেসিডোনিয়ান অধিপতি আলেকজাণ্ডারের শাসনামলে এ সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক মিসর, ইসরাইল, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত থাকার কারণে গ্রিক সভ্যতাকে ‘ওসেনিয়ান (সাগরীয়) সভ্যতা বলা হয়। অপরদিকে মিসর, ব্যাবিলন সভ্যতা ছিল নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।
গ্রিকদের রাজনৈতিক ইতিহাস
প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা
প্রাচীন গ্রিক সমাজের বিশেষত্ব দাসপ্রথা, গ্রিকদের আগে আর কোন সমাজই দাসত্বের বুনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে নাই । গ্রিকদের আদি বাসস্থান গ্রিসে নয়। গ্রিসে আসার পূর্বে তারা থিসালি ও এপিরাসে বাস করত। গ্রিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে পতন পর্যন্ত এর রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, এ সভ্যতাকে ২টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা: ১. হেলেনিক যুগ, ২. হেলেনিস্টিক যুগ।
হেলেনিক সভ্যতা
গ্রিক সভ্যতায় দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তর হেলেনিক সভ্যতা এবং দ্বিতীয় স্তরে হেলেনিস্টিক সভ্যতা। গ্রিকরা তাদের ‘হেলাস’ বলতো। তাই গ্রীক সভ্যতার উন্মেষ বা আদিপর্ব হেলেনিক যুগ। কেবল গ্রিক উপদ্বীপ কেন্দ্রিক এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র বিন্দু ছিল এথেন্স। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৩৩৬ অব্দ পর্যন্ত হেলেনিক যুগ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রাজা ফিলিপ কর্তৃক মেসিডোনিয়া কেন্দ্রিক নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রিকরা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাইরের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে পরবর্তীতে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয় তা-ই হেলেনিস্টিক যুগের সভ্যতা। হলাস
হোমারিক যুগ (১২০০-৮০০ খ্রি :)
গ্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে আদিকালকে ‘হোমারিক যুগ' বলা হয়। গ্রিক কবি হোমারের নাম থেকে এ যুগের নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি। বিখ্যাত কবি হোমার ‘ইলিয়ড’ এবং ‘ওডিসি’ নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। তার রচনাবলী থেকে গ্রিক ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, লোক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হোমারিক যুগে সমগ্র গ্রিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সংস্থায় (Village / Rural Community) বিভক্ত ছিল এবং স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হতো।
নগর রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ও গণতান্ত্রিক এথেন্স
খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে হোমারিক যুগের অবসান ঘটে। হোমারিক যুগের গ্রাম সম্প্রদায়গুলি ভেঙ্গে কালক্রমে নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এথেন্স, থিস, মেগারা, স্পার্টা এবং করিন্থ প্রভৃতি নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এগুলির মধ্যে এথেন্স ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক বাহক। এথেন্সই ছিল গ্রিসের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ৫৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সোলন নামক একজন সংস্কারক এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পদক্ষেপসমূহ (১) ৪০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন, (২) সংসদ বা সাধারণ পরিষদে নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি, (৩) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠন। এছাড়া প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখেন। এই সংস্কারের ফলে এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে ক্লিথিনিস জনগণের সহায়তায় এথেন্সের ক্ষমতায় আসেন। তিনি এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রতিভূ (Father of Athenian Democracy) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ সময়ে পারস্য কর্তৃক গ্রিস আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘ দিন গ্রিক- পারস্য যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।
গ্রিক-পারস্য যুদ্ধ
পারস্যের অ্যাকামেনীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরাস। তিনি প্রথমে গ্রিক অভিযান করেন এবং নগর রাষ্ট্র সমূহের ওপর ধ্বংসলীলা চালান। সাইরাসের পর পারস্য সম্রাট দারিয়ুস গ্রিক আক্রমণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে ম্যারাথন নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রিকরা পারস্য বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। উল্লেখ এ যুদ্ধের ঘটনাকে স্মরণ করে পরবর্তীতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। প্রতি ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করত। ফলে এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতা অপসারিত হয়ে গ্রিকদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ম্যারাথনে পরাজয়ের পর দারিয়ুসের পুত্র জারেক্সস খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে গ্রিক যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু থার্মোপলীর যুদ্ধে পারস্য বাহিনী আবার পরাজিত হয়। গ্রিকদের বিজয়ের ফলে গ্রিক গণতন্ত্র আরো সুদৃঢ় হয় এবং গ্রিসের মূলভূখণ্ড থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত গ্রিক গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রিক গণতন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আজও স্বরণীয়।
পেরিক্লিসের যুগ
দেশাত্মবোধে উজ্জিবিত গ্রিকরা এথেন্সের নেতৃত্বে এক সমৃদ্ধিশালী গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই বিকশিত গণতন্ত্র ও সমাজকে আরো চূড়ান্ত শিখরে তোলেন বিখ্যাত পেরিক্লিস। তাঁর সময়ে (খ্রি: পূর্ব ৪৬১-৪২৯) সমগ্র গ্রিসের গণতন্ত্র, স্থাপত্যকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ লাভ করে। এই কারণে তাঁর সময়কালে পেরিক্লিসের যুগ বলা হয়। পেরিক্লিসের সময়ে নাট্যকার সোফোক্লিস, দার্শনিক এনাক্সাগোরাস, নাট্যকার ইউরিপিডিস রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।
হেলেনিক সভ্যতার পতন
খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসের দুটি শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ সময় স্পার্টা নগর রাষ্ট্রটি বরাবরই সামরিকতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ইতিহাসে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১-৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলে খ্যাত। এই যুদ্ধে এথেন্সের পতন ঘটে এবং স্পার্টা এথেন্স দখল করে নেয়। যার ফলে হেলেনিক সভ্যতারও পতন ঘটে।
হেলেনিস্টিক যুগ
আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গ্রিসের মেসিডোনীয় রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেসিডোনীয় রাজা ফিলিপ, এথেন্সসহ সমগ্র গ্রিক রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজা ফিলিপের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ইউরোপসহ শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য অধিকৃত হয়। আলেকজান্ডার এখন পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সম্রাট। ফলে গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক
নতুন যুগের সূচনা হয়। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। তাই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলেকজান্দ্রিয়ান বা হেলেনিস্টিক সভ্যতা বলে পরিচিত।
গ্রিক দর্শন ও সংস্কৃতি
পৃথিবী ব্যাপী সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক দর্শন গোটা বিশ্বের দর্শন ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। অদ্যাবধি জ্ঞানের জগতে যে সকল গ্রিক কবি দার্শনিক জ্ঞানের আলোক বর্তিকা বিতরণ করেছেন তাদের মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষাগুরু সক্রেটিস। সক্রেটিস এর ছাত্র প্লেটো ও প্লেটো এর ছাত্র এ্যারিস্টটল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রিক দার্শনিকদের যুক্তি, ব্যাখ্যা ও দর্শন জগতকে সমৃদ্ধিশালী করে। এই সকল যুক্তিবাদী দার্শনিককে সফিস্ট বলা হয়। গ্রিক দর্শনে অন্যতম দার্শনিক সক্রেটিস নিজের সত্য প্রকাশে অনড় থেকে শাসকের নির্দেশে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত উক্তি ‘নিজেকে জানো' (Know Thyself)। তাঁর শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটো শিষ্য এ্যারিস্টটলের সর্বকালের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। প্লোটো বারো বছর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে ক্ষেত্রে মতের কিছুটা অমিল ঘটলে এ্যারিস্টটল নিজেই ‘লাইসিয়াম' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক এবং লজ প্রভৃতি। এ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ লজিক, ফিজিক্স এবং পলিটিক্স প্রভৃতি। এ্যারিস্টটলের ‘পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থে রাজনীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়েছে। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দি রিপাবলিক'। আর বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডার নিজেও একজন দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক প্লেটো ।
‘একাডেমি' নামে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শিক্ষাগুরু প্লেটোর সাথে জ্ঞানের দার্শনিক সক্রেটিস
গ্রিক সাহিত্য
হোমারিক যুগে গ্রিক সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। যদিও হোমারের সাহিত্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’তে গ্রিকদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হোমারিকযুগের পরে গ্রিক সমাজে গীতিকাব্য ও শোক গাথার আবির্ভাব ঘটে। এ সকল শোক গাথায় ব্যক্তিগত প্রণয়কাহিনীর বিবরণ রয়েছে। সোলোন ছিলেন একজন বিখ্যাত গীতি কাব্য রচয়িতা। এছাড়া বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ ।
HERODOTUS
HISTORY OF THE PERSIAN WARS
ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস
গ্রিক ইতিহাস
ইতিহাসের জনক ছিলেন গ্রিসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রি:পূর্ব)। ইতিহাস শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘হিস্ট্রি' শব্দটি গ্রিক ভাষার শব্দ। তিনি মিসর, পারস্য ও ইতালি ভ্রমণ করে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া জেনোফার নামে এক ব্যক্তি ইতিহাস সংগ্রহে খ্যাতি অর্জন করেন।
গ্রিক বিজ্ঞান
বিজ্ঞান সাধনায় হেলেনিস্টিক যুগেও অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে সময়ে ইতিহাস গবেষণায় পলিবিয়াস, জ্যোর্তিবিদ্যায় এ্যারিস্টটল ও হিপারকাস, গণিতে বিখ্যাত পিথাগোরাস ও ইউক্লিড প্রমুখ মনিষীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
পাঠ-১.৭
রোমান সভ্যতা
উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-
রোমান সভ্যতা উৎপত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
রোমান সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস ও সময়কাল জানতে পারবেন ও
জ্ঞান বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
মুখ্য শব্দ
ভূমিকা:
| টাইবার নদী, ল্যাটিন ভাষা, ‘অগাস্টান যুগ’, নেবুচাঁদনেজার, ও ‘ঝুলন্ত উদ্যান
ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে- 'Rome was not build in a day'। এই প্রবাদ বাক্যটি রোমান সভ্যতার ক্ষেত্রে এমনিতেই স্থান পায়নি। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, উদ্ভাবন-ধ্বংসের পথ পাড়ি দিয়েই গড়ে উঠেছিল রোমান সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে রোমানরা গ্রিক সাম্রাজ্য দখল করে । রোমানরা ইতালি ও ইতালির পশ্চিম দিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশগুলো জয় করে। লাতিনদের একটি ক্ষুদ্র জাতি থেকে সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিকাশ হয়, মধ্য ইটালির ল্যাটিয়ামে রোম ছিল তাদের প্রধান শহর।
রোমান সভ্যতার উৎপত্তি
গ্রিক সভ্যতার সমসাময়িক রোমান সভ্যতা হেলেনিক ও গ্যালিয়া মধ্য সাগর মৌরিতানিয়া ভূমধ্য সাগর আরব উপদ্বীপ হেলেনিস্টিক সভ্যতার অনেক সংস্কৃতি করেছে।
ঐতিহাসিকদের ধারণা, ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রোমুলাস এর নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রোমান সভ্যতা
প্রাচীন রোমানগরীকে ‘বিশ্বের রাজধানী' বলা হয়। কারণ রোম নগরীর সঙ্গে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া-এই তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত যোগাযোগ ছিল। রোমীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসহ উত্তরে ব্রিটেন, জার্মানী; পূর্বে মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণে মিসর ও লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
রোমান ইতিহাস
ঐতিহাসিকগণ রোমান সভ্যতার ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। (ক) রাজতন্ত্র যুগ (৭৫৩-৫১০ খ্রিস্টপূর্ব), (খ) প্রজাতন্ত্র যুগ (৫১০-৬০ খ্রিস্টপূর্ব), (গ) প্রথম কনসুলেট যুগ (৬০-৩১ খ্রিস্টপূর্ব), (ঘ) সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টান যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪) (ঙ) অগাস্টান পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য (১৪-৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত।
অগাস্টান যুগ
জুলিয়াস সিজারসহ (সিজার রোমান সম্রাটদের উপাধি) অনেক বিখ্যাত শাসক রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। কিন্তু সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪ খ্রিস্টাব্দ) রোমের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে রোমীয় সভ্যতায় স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে রোমীয় ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞানচর্চা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এই জন্য ইতিহাসে তাঁর
সময়কালকে ‘অগাস্টান যুগ' (Augustan Age) বলা হয়।
জ্ঞান-বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান:
রোমীয় সাহিত্য
রোমান সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গ্রিক সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শিক্ষিত রোমানরা ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতো। সে যুগে রোমান সাহিত্য চর্চা ছিল ব্যাপক। মলিয়ে প্লুটাস এবং টেরেন্স ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার। রোমীয় সাহিত্যে নাটকের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। গীতি কাব্যকার ক্যাটুলাস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। এ ছাড়া সিসিরো এবং ভার্জিল সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন। অগাস্টান পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবি জুভিনাল ছিলেন একজন ব্যঙ্গধর্মী কবি। সে যুগে সাহিত্য-চর্চায় স্বাধীনতা ছিল। ক্যাটুলাস রোমান শাসক পম্পি এবং জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধেও বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও গীতি কাব্য রচনা করেন।
ইতিহাস
রোমান ক্লোসিয়াম নাট্যশালা
সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ইতিহাস চর্চাও রোমে সমৃদ্ধি অর্জন করে। সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে তেমন প্রভেদ ছিল না। সাহিত্যের প্রধান উপাদানই ছিল ইতিহাস। রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন টিটাস লিভি (Titus Livius); খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯-১৭ খ্রিস্টাব্দ), ট্যাসিটাস (৫৫-১১৭ খ্রি:) এবং প্লুটার্ক। এ সকল রোমান ঐতিহাসিকরা লিভিকে পম্পিয়ান হিসেবে অভিহিত করেন। লিভির বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ The History of Rome from the Foundation of the City, ট্যাসিটাস-এর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Annals' এবং 'Histories' আর প্লুটার্ক এর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'The Parallel Lives' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সব গ্রন্থে লেখকরা তৎকালীন রোমান সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিশৃংখলা, সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিবরণ দেন। রোমের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান উৎস হচ্ছে লিভির রচিত রোমের ইতিহাস।
রোমান ধর্ম
রোমানরা গণপ্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে শাসনকার্যে ধর্মীয় প্রভাব বা পুরোহিততন্ত্র পাকাপোক্ত হয়ে বসতে পারেনি। তাদের দেবদেবীর মধ্যে গ্রিকদের মতো মানবিক গুণাবলী আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রিক ধর্মের সঙ্গে রোমীয় ধর্মের বৈসাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত গ্রিক দেবতা জিউস, রোমানদের নিকট আকাশের দেবতা জুপিটার হিসেবে খ্যাত। গ্রিক দেবতা এথেনার জায়গায় রোমীয় দেবতা মিনার্ভা স্থান দখল করে। রোমের প্রেমের দেবতা ছিলেন ভেনাস। বাতাস এবং সমুদ্রের দেবতা নেপচুন রোমানদের নিকট খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। রোমীয় ধর্মচর্চা ছিল রাজনৈতিক ও ইহজাগতিক।
রোমানরা দর্শনের ক্ষেত্রেও গ্রিক প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই রোমান দর্শনের সূত্রপাত। রোমীয় দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিসিরো (Cicero), লুক্রেটিয়াস ( Lucretius)। লুক্রেটিয়াস ছিলেন গ্রিক এপিকিউরিয়ান মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Nature of Things' অপর দিকে সিসিরো ছিলেন গ্রিক স্টয়িক মতবাদের অনুসারী। তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘On Duty' তে স্টয়িক মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়।
রোমান আইন
প্রাচীন সভ্যতায় রোমানদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো রোমান আইন ব্যবস্থা (Roman Law)। রোমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন (সিভিল ও ক্রিমিনাল'ল) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই সংকলিত হয়। এই আইনগুলি জনগণের সুবিধার্থে কাঠের ফলকে খোদিত করে রাজপথে প্রকাশ্যে টানিয়ে রাখা হতো। এ আইনগুচ্ছকে বলা হতো দ্বাদশ তালিকা (Twelve Tables)। বিশিষ্ট আইনবিদ ছিলেন গেইয়াস, আলপিয়ান প্যাপিনিয়ান এবং পলাস। সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এদেরকে আইনের ব্যাখ্যা ও মামলা নিস্পত্তির অধিকার দেয়া হয়। এদের দ্বারা আইন সংস্কারের মাধ্যমে রোমান আইন একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন আইনের তিনটি শাখা ছিল। (ক) জাস সিভিল (Jus Civile), (খ) জাস জেন্টিয়াম, (গ) জাস ন্যাচারাল। জাস সিভিল বা বেসামরিক আইন সকল রোমীয় নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। জাস জেন্টিয়াম বা জনগণের আইন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রযোজ্য এবং জাস ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক আইন মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে ন্যায় অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং মৌলিক অধিকার প্রাপ্ত। তাই, রাষ্ট্র বা সরকার তাকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এই আইনের প্রবক্তা ছিলেন দার্শনিক সিসেরো। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর পূর্ব-রোমে নতুনভাবে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।
রোমান সাম্রাজ্যের পতন
খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ইতালির কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। রোম এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোতে সর্বহারা দল ভিড় করে । রোমের দাস-মালিকরা গর্বের সঙ্গে বলত, রোমের ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তাদের শক্তিমান রক্ষীবাহিনী ও বিশাল সেনাবাহিনী অপরাজেয়। কিন্তু সেই শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। জার্মান ও পারসিকরা এক একটি রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি দখল করতে থাকে। যারা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অন্যদের দাস বানিয়েছে, আজ তারাই দাসে পরিণত হয় ।
রোমান শিল্পকলা
রোমনগরীকে কেন্দ্র করে রোমান স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা বিকশিত হয়। জুলিয়াস সিজারের আমল থেকে রোমীয় শিল্পকলার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। অগাস্টাস রোমীয় শিল্পকলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। রোম নগরীর স্থাপত্যে ইটের পরিবর্তে মার্বেল এবং মোজাইকের ব্যবহার শুরু হয়।
সারসংক্ষেপ :
রোমান সম্রাটগণ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী শাসন করেছেন। তাঁরা পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও শিল্পকলার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বমানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধশালী করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে রোম ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী নগরী। প্রচলিত আছে যে, রোম গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে (Rome ruled the world)।
Promotion