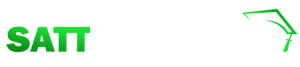Subject Content
স্বাধীন বাংলাদেশ
১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালিরা অনেক দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্... ানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ১৩ হাজার সদস্য ঐ দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধু সরকারকে মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান ও সামরিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। এ অধ্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, অভ্যুদয়,পুনর্গঠন, সামরিক শাসনামল, গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা ও আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হব।
পরিচ্ছেদ ২.১ :
মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক ও ক... ন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণকেহাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শপথ পাঠ করান। এতে জনগণের সম্পদ ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি অবিচল থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা চক্রান্ত শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। অন্যান্য সদস্যকেও তিনি হুমকি দেন। এসবই ছিল ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের ফল। ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ভুট্টোর ঘোষণাকে অজুহাত দেখিয়ে ৩ রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা না করে অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ফলে সকল সরকারি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। হরতাল চলাকালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুলোক হতাহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল এক জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সকল বাঙালিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণে আহ্বান জানান। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল। জানুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করার এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে 'ওয়ার্ল্ড 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' (World Documentary Heritage) 'বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কো অন্তর্ভুক্ত করেছে।৭ই মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষাকে সামনে একটি মাত্র গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায়, তা হলো 'স্বাধীনতা'। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ডাক দেন, সে ডাকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিকনির্দেশনা ছিল- 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, “রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা।” এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সঞ্জাম, যুদ্ধের কলা-কৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক পরিকল্পনার মাধ্যমে নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। বাঙালিরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে পাড়ায় ।
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্ৰা
৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার সকল অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিদুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে। এ সময় ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। অপরদিকে গোপন আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। ১৭ই মার্চ টিকা খান ও রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনক্সা তৈরি করে। ২৫শে মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা, অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হয়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ২৫শে মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরা বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা করে বহু মানুষকে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিনার ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় ও নৃশংসভাবে গণহত্যা ঘটায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ শে মার্চের রাত 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত। এ দিবসটি এখন 'জাতীয় গণহত্যা 'দিবস' হিসেবে স্বীকৃত। ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ওয়্যারপেসযোগে তা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলার জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুরু হয় পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাদের সঙ্গে বাঙালি, আনসার ও নিরর সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই ২৬শে মার্চ প্রথম গ্রহরে আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে (অর্থাৎ ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ“ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বালাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।”
স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার কারণে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় একই বেতার কেন্দ্র হতে জিয়াউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং এর বাঙালি সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।
মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম
১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননকে নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার' গঠন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ঐ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ'। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :
১. রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ
৪. অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী
৫. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
৬. পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী ন্যাপ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্ফর ন্যাপ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)-কে নিয়ে মোট ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী।মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য যারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।
বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেছিল। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এগুলো হলো—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও যুব ও অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম - প্রভৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করেন। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকার বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেছিল। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনা সদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এসব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এক্ষেত্রে টাংগাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন।
মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহিদ হন। আবার অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্যসন্তান হিসেবে মনে করবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসীম সাহসী এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করে। তাই এ যুদ্ধকে 'গণযুদ্ধ' বা 'জনযুদ্ধ'ও বলা যায়।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।
রাজনৈতিক দল
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান রাজনৈতিক দল হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক নেতৃত্বই মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। আওয়ামী লীগ প্রথমে পূর্ববাংলার জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে সংগঠিত করে। এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন করে বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। এতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, অপরিহার্যতা এবং এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণীত হয়। ২৫শে মার্চের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠিত হয়ে সরকার গঠন, মুক্তিবাহিনী গঠন, বিদেশে জনমত সৃষ্টি ও সমর্থন আদায়, যুদ্ধের অস্ত্রশসত্র সংগ্রহ এবং জনগণের মনোবল অটুট রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার ক্ষেত্রে সকল শক্তি, মেধা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান, ভারতে ১ কোটি শরণার্থীর ত্রাণ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ ছাড়াও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্ফর), কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি। এসব দলের নেতা ও কর্মীরা অনেকেই সশত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর সমর্থনে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপিসহ কতিপয় দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। দলগুলো শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস নামক বিশেষ বাহিনী গঠন করে। এসব বাহিনী হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীর সম্ভ্রমহানির মতো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। স্বাধীনতাবিরোধী এ বাহিনীগুলো মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও বাঙালিদের মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।
ছাত্র সমাজ
পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে বাঙালি জাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র সমাজ। ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে ১১ দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীরঅনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।
পেশাজীবী সাধারণ অর্থে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন পেশাজীবী। পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃপ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবদীপ্ত। পেশাজীবীদের বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পেশাজীবীদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। মুক্তিযুদ্ধে নারী
মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সপ্তগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অপরদিকে সহযোদ্ধা হিসেবে অাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুনা, মুক্তিযোদ্ধানের আশ্রয়দান ও তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এদেশের অগণিত নারী মুক্তিসেনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হন প্রায় তিন লাখ মা-বোন। তাঁরাও মুক্তিযোদাদের সহযাত্রী। তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারিভাবে তাঁদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৬ সালে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
গণমাধ্যম
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্যাদের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া, মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।
জনসাধারণ
সাধারণ জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালিরস্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুষ্টিমের এদেশীয় দোসর ব্যতীত সবাই কোনো না কোনোভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় নিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ করেছে, সেবা দিয়েছে ও খবরাখবর সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল অধিক। তাদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের আজকের স্বাধীন মানচিত্র, লাল-সবুজ পতাকা।
প্রবাসী বাঙালি
প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট প্রবাসী বাঙালিরা আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তাঁরা নিরলস কাজ করেছেন।
শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী
মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তথাপি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্র-পত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার' ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে তুলেছে।
স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান
বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃব বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নানা অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্ব দেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন-সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৯৪৮ - ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । কী সংস, কী রাজপথ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বদা সোচ্চার। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে "আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি পেশ ও ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনের মধ্যে ১২ বছর বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সামের পথ ধরে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। ২৫শে মার্চ নির বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে তিনি সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনের মধ্যে ১২ বছর বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সামের পথ ধরে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। ২৫শে মার্চ নির বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে তিনি সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর নামেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বলিষ্ঠ ও আপোসহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের চার নেতার একজন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের (১০ই এপ্রিল ১৯৭১) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা। ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল তিনি বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের কথা প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার তিনি সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ চির ২.৫। আজউদ্দীন আহমদ পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম গভীরভাবে যুক্ত। তিনিও জাতীয় চার নেতার একজন।
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী জাতীয় চার নেতার একজন, যিনি বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে খাদ্য, কর অ প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান খুবই গুরুদায়িত্ব ছিল। তিনি সফলভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন।
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান জাতীয় চার নেতার একজন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ान সপ্তাহ ও ত্রাণশিবিরে তা বিতরণ, প্রাবর্তী সময়ে শরণার্থীদেরপুনর্বাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান অপরিসীম। অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (১৯৬৮-১৯৬৯) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে গড়ে ওঠা আন্দোলন ৩ ৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দান ও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়া অধ্যাপক মোজাফ্ফার আহমেন (ন্যাপ-মোজাফ্ফার) ও কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটিতে এ তিন নেতা সদস্য ছিলেন। বাঙালি জাতি তাদের এদার সাথে স্মরণে রাখবে।
মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা :
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্বাধীনতাবিরোধী তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রি তথা জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।
ভারতের ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী নয় মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। এর ফলে বিশ্ববিবেক জাত হয়। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বর চিকিৎসা, পত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। ভারত ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড গড়ে তোলে। যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ১৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাসহ জেনারেল এ কে নিয়াজী নিঃশর্তে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান রাশিয়া। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী- ধর্ষণসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেলইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' (বিরোধিতা করা) প্রদান করে তা বাতিল করে দেয়। কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসামকে সমর্থন জানায়।
গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন এবং বাঙালিদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য, লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। তাছাড়া ব্রিটিশ নাগরিক বিখ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন পণ্ডিত রবি শংকর ও আলী আকবর খান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। ব্রিটেন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বের কোনো কোনো দেশ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।
জাতিসংঘের ভূমিকা : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে 'ভেটো' ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নেই।
বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশসত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূখণ্ডের সন্ধানী মানুষ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন, ১৬ই ডিসেম্বর তা বাস্তবে পূর্ণতা পায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নতুন যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে।মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যা বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।
পরিচ্ছেদ ২.২ :
স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমল ও পরবর্তী ঘটনাবলি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) শাসন ক্... মতা গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সরকার প্রধানের দায়িত্বতার গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক পুনর্গঠন, ভারতে অবস্থানরত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, সংবিধান প্রণয়ন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি তাঁর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির চক্রান্তে কতিপয় বিপথগামী সামরিক কর্মকর্তার অভ্যুত্থানে বিদেশে অবস্থানরত দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত পরিবারের সকল সদস্যসহ স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।
বিধ্বস্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া
বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন চারদিকে ছিল স্বজন হারানোর বেদনা, কান্না, হাহাকার আর ধ্বংসযজ্ঞ। অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, কলকারখানা, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ছিল বিধ্বস্ত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল অর্ধশূন্য। স্বাধীন বাংলাদেশের ছিল না কোনো সামরিক-বেসামরিক বিমান। ত্রিশ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, গ্রাম-গঞ্জের লাখ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ, সর্বোপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ ও আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।সুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়েই শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল ।যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন দায়িত্ব পালন ছাড়াও ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ :
নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করা : ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১২ই অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করে। ৪ঠা নভেম্বর উক্ত সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত ও ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা বলবত হয়। এই সংবিধানের মূলনীতি হলো- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার, ন্যায় বিচারসহ জনগণের সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হয়। গণপরিষদ : ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশবলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হন। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাস ও কার্যকর করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় এটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।
পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ : স্বাধীনতার পর আদমজীসহ বিভিন্ন কলকারখানার পাকিস্তানি অবাঙালি শিল্পপতিরা বাংলাদেশ ত্যাগ করলে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে বাংলাদেশের সম্পদে পরিণত করেন। কারখানা জাতীয়করণের ফলে শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক অবস্থানে চলে আসেন । প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ: পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষকগণ সরকারের কাছ থেকে যৎসামান্য বেতন-ভাতা পেতেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ- -খুদাকে প্রধান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিটি ১৯৭৪ সালে একটি গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির রূপরেখা উপস্থাপন করে। এভাবে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।
রিলিফ প্রদান ও রেশনিং প্রথা ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং মানুষজনকে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত কম্বল, খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ সাহায্য কণ্টন করেন। এছাড়া শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ব্রুয় করার জন্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সহায়-সম্বলহীন মানুষকে সাহায্যের জন্যে এটা ছিল এক অসাধারণ মানবিক পদক্ষেপ।
১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন : ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক।
নতুন অর্থনৈতিক পাঁচসালা পরিকল্পনা : বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্যে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে এবং প্রণীত হয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বকেয়া সুদসহ কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হয়।
শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচি : মুক্তিযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও তেলের মূল্যবৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বন্যায় দেশে খাদ্যোৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এসবের ফলে দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরে মজুদদার, দুর্নীতিবাজ এবং ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী তৎপর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সরকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি।নির্বাচনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়ন করাই হবে গণপরিষদের মূল লক্ষ্য। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। একজন নারী সদস্য এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। ন্যাপ (মোজাফ্ফর)-এর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (পরবর্তী সময় আওয়ামী লীগ নেতা) সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও আগ্রহী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে সংবিধান সম্পর্কে প্রস্তাব আহ্বান করে।
১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, “এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।" এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছিল প্রায় নয় বছর (১৯৪৭-১৯৫৬) আর ভারতের লেগেছিল প্রায় তিন বছর (১৯৪৭-১৯৪৯)। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র দশ মাসে বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতির জনকের এটা এক অসাধারণ অবদান।
১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
১৯৭২ সালের মূল সংবিধানটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। এ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ :
১৯৭২ সালের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি – জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলোকে রাষ্ট্রের মূল তত্ত্ব - হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মেটানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হয়। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার সরক্ষণ এ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবন ধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার ইত্যাদি সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানে বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদ সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এ সবিধানে বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ- সংবিধানের এ ঘোষণা দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [সূত্র: সংবিধানের প্রাধান্য ৭ (১)] সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা প্রদান করা হয়। সংবিধান পরিপন্থী কোনো আইনকে অসাংবিধানিক বলে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে সংবিধানের মর্যাদা ও প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখতে পারবে। এ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে 'ন্যায়পাল' পদ সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক যে কোনো নাগরিক 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এ নীতির ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এ সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, সমবায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি স্বীকৃত। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এ পর্যন্ত সতেরবার সংশোধন করেছে। তন্মধ্যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনী, জেনারেল এরশাদের সপ্তম সংশোধনী এবং খালেদা জিয়ার ত্রয়োদশ সংশোধনী সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘটে এক নির্মম, নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্য স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির মদদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতারএবং শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে। গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। এটিকে জাতির পিতা "দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন।
পররাষ্ট্রনীতি : পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাস করে, কারও প্রতি বৈরী আচরণ সমর্থন করবে না।' তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'-এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং পুনর্গঠনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করেন। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৪০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করাসহ নানাভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে। অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশ ও খাদ্যদ্রব্য ও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে।
ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ফেরত যাওয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী হিসেবে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহলকে অপপ্রচারের সুযোগ না দিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে ফিরে যায়। বিশ্ব ইতিহাসে বিদেশি সৈন্যদের এত দ্রুত স্বদেশে ফিরে যাবার নজির বিরল। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।
আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের এবং ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় প্রথম ভাষণ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের এবং ওআইসি এর সদস্যপদ লাভ করে। বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি' শাস্তি পদকে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মানের মর্যাদা লাভ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের হাল ধরতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে দেশি- বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যেও স্বপ্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।
১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন পটভূমি
সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এতে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অস্থায়ী সংবিধান আদেশের বিভিন্ন দিক হলো এই আদেশ বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ। এটি অবিলম্বে বলবৎ হবে। এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সরকারপ্রধান। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান।
একটি সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালেরমহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের, বাড়ি নম্বর-৬৭৭ নিজ বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপস্থিত কোনো সদস্যই ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এমনকি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেলও। একটি আধুনিক ও শোষণ-দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক তখন দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি মহলের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের মতো "দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নেও সফল হবেন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই ১৫ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই হত্যাকাণ্ড ছিল একটি নৃশংস ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। এটি ঘটেছিল গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এ হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। ১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে কতিপয় কলঙ্কময় অধ্যায় (১৫ই আগস্ট-৩রা নভেম্বর ১৯৭৫) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়ে সামরিক শাসন জারি করে এবং ২২শে আগস্ট মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে। ২৪শে আগস্ট জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহকে সরিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। ৩১শে আগস্ট এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৫ই আগস্টের হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' নামে সংবিধান ও আইনের শাসনবিরোধী একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৫ই আগস্টের হত্যার সঙ্গে জড়িত জুনিয়র সেনা অফিসাররা ব্যারাকে ফিরে না গিয়ে বঙ্গভবনে বসে দেশ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা (চেইন অব কমাণ্ড) ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ৩রা নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ৫ই নভেম্বর খন্দকার মোশতাক পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
জেলখানায় পৈশাচিক হত্যাকান্ড (৩রা নভেম্বর ১৯৭৫)
১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর গভীর রাতে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খুনিচক্র সেনাসদস্যরা দেশত্যাগের পূর্বে খন্দকার মোশতাকের অনুমতি নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে সেখানে বন্দি অবস্থায় থাকা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘটনা মোশতাকের পতন ত্বরান্বিত করে। খুনিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এ হত্যাকাণ্ড ছিল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত, স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও নীলনক্সার বাস্তবায়ন। ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকান্ড একই গোষ্ঠী সংঘটিত করে। উভয় হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ ধ্বংস ও দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।
পরিচ্ছেদ ২.৩ সেনা শাসন আমল (১৯৭৫-১৯৯০)
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবৈধ সেনা শাসন বহাল ছিল। দেশের সংবিধানকে উপেক্ষা করে খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম, জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আহসান উদ্দিন এবং জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দেশে সেনা শাসন ... হাল রেখে সুবিধামতো সময়ে জিয়াউর রহমান (১৯৭৫-১৯৮১) এবং জেনারেল এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০) নির্বাচন সম্পন্ন করে বেসামরিক শাসন চালু করেন। তাদের অগণতান্ত্রিক শাসন, জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কার্যকলাপ দেশের জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৯১ সালে পুনরায় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।
জিয়াউর রহমানের শাসন আমল (১৯৭৫-১৯৮১) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর মেজর ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অধীনে তিনি ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবার পরিজনসহ শাহাদাত বরণ করার পর খন্দকার মোশতাক সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর ২৪শে আগস্ট তিনি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে জিয়াউর রহমানকে নিযুক্ত করেন। ৩রা নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানে খন্দকার মোশতাকের পতন ঘটে এবং জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি হন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর পাল্টা সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের হত্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর আগে ৬ই নভেম্বর ভোররাতে গৃহবন্দি জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করতে যায় বঙ্গবন্ধুর খুনি ফারুকের ল্যান্সার বাহিনীর একটি দল। জিয়াউর রহমান মুক্তি পেয়ে সদ্য নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের অনুমতি ব্যতিরেকে বেতারে ভাষণ দিতে চলে যান এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দাবি করেন। পরে অবশ্য পদবি পরিবর্তন করে উপ-প্রধান আইন প্রশাসক হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রহসনমূলক গণভোটের (হ্যাঁ ভোট ও না ভোট) মধ্য দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও তার শাসন আমলে ২০টির ও বেশি সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং সেনা বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এসকল ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পর জিয়াউর রহমান বিচারের নামে অনেক নিরপরাধ সামরিক কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যদের সাজা, চাকরিচ্যুত এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেয়। জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের যেসব মৌলিক নীতি ও চেতনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল, তার বেশিরভাগই এ সময়ে বাতিল করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গকে তিনি সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ৭ই নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে ১৯৭৬ সালে সামরিক আদালতে প্রহসনের বিচার শেষে তারই আদেশে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৫ই আগস্টসহ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না মর্মে যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছিল তার মূল হোতাও ছিলেন জিয়াউর রহমান।
নির্বাচন ও দল গঠন
১৯৭৬ সালে কিছু শর্ত সাপেক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে ‘ঘরোয়া রাজনীতি' করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা বৈধকরণের লক্ষ্যে হ্যাঁ/না ভোটের আয়োজন করেন। এরপর তিনি নিজস্ব পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন দল থেকে নেতাকর্মীদের নিয়ে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন করেন।এ সময়ে রাজনৈতিক দল ভাঙ্গা-গড়ার কাজও চলে। পরিশেষে চাপের মধ্যে ১৯৭৮ সালের ৩ রা জুন দেশে প্রহসনমূলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন উপলক্ষে দুটি জোট গঠিত হয়। একটি ছিল জিয়া প্রতিষ্ঠিত 'জাগদল'-এর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট আর অপরটি হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট'। জিয়া ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী ছিলেন গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী। কারচুপির এ নির্বাচনে জিয়াউর রহমান সহজে বিজয় অর্জন করেন। সামরিক শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে প্রধানত শাসকের ইচ্ছারই বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান ইতোপূর্বে গঠিত জাগদল বিলুপ্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২০৭টি আসন পেয়ে বিএনপি জয়লাভ করে। উক্ত সংসদে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত যে সকল সামরিক বিধি, সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করা হয়, সেগুলো সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে পাস করা হয়। অবশ্য সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০০৮ সালে এক রায়ে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ৬ ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু করে রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের পুনর্বাসন করেন। তিনি সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করেন। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারের পথ তৈরি করেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চীন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ বাংলাদেশকে এই সময়ে স্বীকৃতি প্রদান করে। পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এ সময় বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নীতি অনুসরণ করে। জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে জিয়াউর রহমানের সাড়ে পাঁচ বছরের সেনা শাসনের অবসান ঘটে।
জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমল (১৯৮২-১৯৯০)
১৯৮১ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার জয়লাভ করেন। কিছু বিচারপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, দলীয় কোন্দল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দেখিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি সংবিধান স্থগিত করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিনকে অপসারণ করে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারির পর দেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। পত্র-পত্রিকা স্বাধীনভাবেসংবাদ পরিবেশন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শেখ হাসিনা, ড. কামাল হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদসহ বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার বা অন্তরীণ করা হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ করে। শুরু হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনে পুলিশি হামলায় ও সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে সেলিম, দেলোয়ার, শাহজাহান সিরাজ, জয়নাল, দিপালী সাহা ও রাউফুন বসুনিয়াসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। এরপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। এ জোটসমূহের আন্দোলনই ১৯৯০-এ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হন। জেনারেল এরশাদ সরকার পূর্ববর্তী জিয়াউর রহমান সরকারের অধিকাংশ নীতি অনুসরণ করে।
দল গঠন ও নির্বাচন
জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের শুরু থেকেই ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েন। ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলসমূহের দাবির মুখে দ্রুত রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে বাধ্য হন। ১৯৮৩ সালের ১ লা এপ্রিল ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১৪ই নভেম্বর প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ই মার্চ ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এরশাদ নিজেই জনদল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ এরশাদ লোক দেখানো প্রহসনমূলক গণভোটের আয়োজন করেন। এ গণভোটে জনগন "হ্যাঁ" / "না'র মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত করে। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০শে মে নতুন প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগস্ট জনদলসহ ৫টি ছোট দল নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। এই ফ্রন্টই ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন।
১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৭৬টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। পর্যবেক্ষকগণও এ অভিযোগের যথার্থতাকে সমর্থন করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে। প্রহসনমূলক এ নির্বাচনে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।
১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর থেকেই এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ এবং নাগরিক সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ ও একটি অর্থবহ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দল গণআন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালে সংসদ থেকে একযোগে বিরোধী দল পদত্যাগ করলে ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ দেশের প্রধান দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। ভোটারবিহীন, দলবিহীন এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ২৫১টি আসনে বিজয়ী দেখানো হয়। সরকার অনুগত আ.স.ম. রবের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী জোটকে ১১টি আসন দেওয়া হয়। বাকি আসনের ৩টি জাসদ (সিরাজ), ২টি ফ্রিডম পার্টি এবং ২৫টি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঝে বন্টন করা হয়।জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ৯ বছরের দীর্ঘ শাসনকালে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।
পরিচ্ছেদ ৩.৪: জোয়ার-ভাটা
পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সমুদ্রস্রোত ছাড়াও পানিরাশির নিজস্ব গতি আছে। এর ফলে প্রতিদিনই কিছু সময় সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আবার কিছু সময়ের জন্য তা নেমে যায়। সমুদ্রের পানি এভাবে নিয়মিতভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা... বলে। পৃথিবীর নিজের গতি এবং তার উপর চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবেই মূলত জোয়ার ভাটা সংঘটিত হয়। জোয়ার ভাটার নানা শ্রেণি রয়েছে। পৃথিবীর উপরও জোয়ার-ভাটা - নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।
জোয়ার-ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ
চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগকে অবিরাম আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যহ একস্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। এভাবে প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি একবার নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে। তবে জোয়ার ও ভাটা প্রতি ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর পর হয়। সমুদ্র পানিরাশির নিয়মিতভাবে এ ফুলে ওঠাকে জোয়ার (High Tide ) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Ebb or Low Tide) বলে। সমুদ্রের মধ্যভাগে পানি সাধারণত এক থেকে তিন ফুট উঁচু-নিচু হয়; কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর উপসাগরের গভীরতা কম বলে সেখানে পানিরাশি অনেক উঁচু-নিচু হয়। এ জন্য সমুদ্রের মোহনাথেকে নদীসমূহের গতিপথে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা অনুভূত হয়। জোয়ার-ভাটার কারণ : প্রাচীনকালে জোয়ার-ভাটার কারণ সম্পর্কে নানা ধরনের অবাস্তব কল্পনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও পৃথিবীর ওপর চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়। মহাকর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব এই মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে। একটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বের দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তিকে মহাকর্ষ শক্তি বা মহাকর্ষণ বলে। এই মহাকর্ষ শক্তির ফলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। যে বস্তু যত বড় তার আকর্ষণ শক্তি তত বেশি। কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ শক্তি কমে যায়। পৃথিবী এবং এর নিকটতম যে কোনো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। একে অভিকর্ষণও বলা হয় । সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা ২.৬০ কোটি গুণ বড় হলেও পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্ব থেকে অনেক বেশি। তাই পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সূর্য অপেক্ষা প্রায় বিগুণ। পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের যে আকর্ষণ তাই হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জোয়ার-ভাটা হয়।
কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি : পৃথিবী তার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের ওপর থেকে চারিদিকে দ্রুত বেগে ঘুরছে বলে তার পৃষ্ঠ থেকে তরল পানিরাশি চতুর্দিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। একেই কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal Force) বলে। পৃথিবী ও চন্দ্রের আবর্তনের জন্য ভূপৃষ্ঠের তরল ও হালকা জলরাশির ওপর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব অধিক হয়। এর ফলেই জলরাশি সর্বদা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তরল জলরাশি কঠিন ভূ-ভাগ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমনিভাবে কেন্দ্রাতিগ শক্তিও জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
জোয়ার-ভাটার শ্রেণিবিভাগ
জোয়ার-ভাটাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন- মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কটাল ও মরা কটাল। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। চাঁদের এই আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের নিকটবর্তী হয় সেখানে চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। ফলে পার্শ্ববর্তী স্থান হতে পানি এসে ঠিক চন্দ্রের নিচে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার হয়। একে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলে। মুখ্য জোয়ারের বিপরীত দিকে পানির নিচের স্থলভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ফলে তার ওপর চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের আকর্ষণের সমান থাকে। এতে বিপরীত দিকের পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চাঁদের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এতে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয়। দুই দিকের পানি সে স্থানে প্রবাহিত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি করে, তাকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার বলে। যখন পৃথিবীর একপাশে মুখ্য জোয়ার ও অন্যপাশে গৌণ জোয়ার হয় তখন দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থল থেকে পানি সরে যায়। মধ্যবর্তী স্থলের পানির ঐ অবস্থাকে ভাটা বলে।অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই পাশে এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর এক পাশে চাঁদ ও অপর পাশে সূর্য অবস্থান করে। ফলে এ দুই তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে থাকে এবং উভয়ের মিলিত আকর্ষণে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি - হয় তাকে তেজ কটাল বা ভরা কটাল বলে। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমকোণে অবস্থান করার ফলে চন্দ্রের আকর্ষণে এ সময়ে চাঁদের দিকে জোয়ার হয়।কিন্তু সূর্যের আকর্ষণের জন্য এ জোয়ারের বেগ তত প্রকা হয় না। এ রূপ জোয়ারকে মাসে দু'বার ভরা কটাল এবং দু'বার মরা কটাল হয়।
জোয়ার-ভাটার ব্যবধান : পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করছে চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পরিক্রমণ করে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথে ২৭ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ফলে পৃথিবীর একবার আবর্তনকালে অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র (৩৬০ + ২৭) বা ১৩° পথ অতিক্রম করে। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ই যেহেতু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে তাই পৃথিবী উক্ত ১৩° পথ আরও (১৩ X ৪) = ৫২ মিনিটে অগ্রসর হয়। ১° পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীর ৪ মিনিট সময় লাগে। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মুখ্য জোয়ার হওয়ার ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট পরে সেখানে গৌণ জোয়ার হয় এবং মুখ্য জোয়ারের ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর সেখানে আবার মুখ্য জোয়ার হয়। এভাবে প্রত্যেক স্থানে জোয়ার শুরুর ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাটা হয়ে থাকে।
পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব
পৃথিবী তথা স্থলভাগ, পানিরাশি ও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জোয়ার-ভাটার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। দৈনিক দু'বার করে জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে নদীর আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে পানি নির্মল হয় এবং নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হয় না। ফলে নদীর মুখ বন্ধ হতে পারে না। জোয়ার-ভাটার স্রোতে নদীখাত গভীর হয়। অনেক নদীর পাশে খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। পৃথিবীর বহু নদীতে ভাটার স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ফ্রান্সের লারান্স বিদুৎ কেন্দ্র ও ভারতের বান্ডালা বন্দরেও এরূপ একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে শীতপ্রধান দেশে নদীর পানি চলাচলের অনুকূলে থাকে। জোয়ারের সময় নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ অনায়াসেই নদীতে প্রবেশ করে, আবার ভাটার টানে সমুদ্রে চলে আসে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পেলে বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করে অথবা বন্দর ছেড়ে যায়। বন্দরে প্রবেশের পূর্বে জোয়ারের অপেক্ষায় জাহাজগুলো নদীর মোহনায় নোঙর করে থাকে। বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের পানি পদ্মা নদীতে গোয়ালন্দের কাছে এবং মেঘনা নদীতে ভৈরব বাজারের কাছাকাছি পৌঁছায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিকে আবদ্ধ করে শুকিয়ে লকা তৈরি করা হয়। ভরা কটালের সময় সমুদ্রের পানি কখনো প্রবল তরঙ্গে নদীর মোহনা দিয়ে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে বানের (Tidal bore) বা বন্যার সৃষ্টি করে। বানের পানির উচ্চতা ৩/৪ ফুট থেকে প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। যে নদীর মোহনা সংকীর্ণ বা সম্মুখে বালির বাঁধ থাকে, সেসব নদীতে প্রবল বান হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও বর্ষাকালে অমাবস্যায় জোয়ারে প্রবল বান হতে দেখা যায়। তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর এর বেগ কমে যায়। মেঘনা, ভাগীরথী, আমাজান প্রভৃতি নদীতেও প্রবল বান দেখা যায়। অসাবধানতাবশত কখনো কখনো এই বানে নৌকা, স্টিমার, জাহাজসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
পরিচ্ছেদ ১৪.২ : সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
জন্মের পর মানব শিশু প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সদস্যের সংস্পর্শে আসে। পরিবারের সকল সদস্যের আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এভাবে শিশু পরিবারের বাইরের পরিবেশ, যেমন- খেলার সাথি, পাড়া-প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প... রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে এবং সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে।
সামাজিকীকরণের ধারণা
সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন একপর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মকানুন রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ।
সামাজিকীকরণের উপাদান
তোমার শ্রেণির একজন সহপাঠী বন্ধুর আচরণ মূলত অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজেও প্রভাবিত হও। আচরণগত এই পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকে বলে মিথস্ক্রিয়া (interaction)। মানুষের সমাজ জীবনের মূল বিষয়ই হলো এই মিথস্ক্রিয়া। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিকীকরণ সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশে এ উপাদান তিনটির প্রভাব লক্ষ করা যায়।
সামাজিক পরিবেশ যে বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষ বিকশিত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের উপরও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিধি-ব্যবস্থা, সকল প্রকার প্রবণতা, সমস্যা প্রভৃতি। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ নিয়েই আমাদের সামাজিক পরিবেশ গঠিত। অর্থনৈতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশের অংশ। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নানাবিধ সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বাজার, জমিজমা, বাগান, গৃহপালিত পশু, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অর্থনৈতিকপরিবেশের উপাদান। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি মানুষের আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে । এগুলো সাংস্কৃতিক পরিবেশের অংশ। মানুষের সৃষ্টি করা উপাদানসমূহ নিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠিত। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, আচার-আচরণ, জ্ঞান- বিজ্ঞান সবই সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। মানুষের সামাজিকীকরণে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবও গভীর। উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয় এবং মনের প্রসারতা বাড়ে। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের কারণে মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে স্বীকৃত। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের পিছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বলা হয় প্রযুক্তিগত পরিবেশ। এ পরিবেশও সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, যেমন- কম্পিউটার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া প্রকৃতির উপাদানসমূহও মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।
সমাজ জীবন : সমাজ জীবন সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের সমাজ জীবন মূলত কতকগুলো আচার-আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যে সমাজে বসবাস করে, সে সমাজের জীবনধারা অর্থাৎ আচার-আচরণের সমষ্টিই হলো সমাজ জীবন। মানুষ সমাজের নানা কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এসব কর্মকান্ড ও অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আচরণের সাথে মানুষ রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে মানুষ অন্যের আচরণ অনুকরণ করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ অনুকরণ প্রবণতা থেকে মানুষ ভাষা, উচ্চারণ, কথা বলার ধরনসহ নানা বিষয় আয়ত্ত করে থাকে। সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জন্মদিন, বিয়ে, ঈদ, পূজা, বড়দিন, বুদ্ধের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাজ জীবনের এসব অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।
সামাজিক মূল্যবোধ : মূল্যবোধ আমাদের সমাজবদ্ধ জীবনের বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবনধারার মান পরিমাপ করা যায় মূল্যবোধের মাধ্যমে। কেননা, মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমেই সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্তি আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক আদর্শ। এই আদর্শের যারা সমাজের মানুষের মনোভাব, প্রয়োজন ও ভালোমন্দের নীতিগত দিক যাচাই করা যায়।মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধগুলো শিখে থাকে। সমাজের সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি হে-ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো সকল সমাজেই রয়েছে। মানুষ সমাজ থেকে এ মূল্যবোধগুলো অর্জন করে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জীবনধারার মাধ্যমে, যেমন- একজন বাংলাদেশি কিংবা ভারতীয় নাগরিকের মূল্যবোধ চীনাদের মূল্যবোধ থেকে পৃথক। বাংলাদেশি এবং ভারতীয়রা তাদের জীবনধারায় আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিকতা, অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অপরদিকে বৈষয়িক উন্নতি বা সমৃদ্ধিলাভই চীনাদের জীবনধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, যা ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।
সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: মানব জীবনে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করে।সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হয়। সমাজ জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই কর্তৃত্ববান ব্যক্তিবর্গ, যেমন- বাবা-মা, বড় ভাই-বোন, শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হই। আবার সমপর্যায়ের বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ও খেলার সাথি দ্বারাও প্রভাবিত হই। এক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখতে পাব বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাধ্যবাধকতার আর বন্ধুদের সাথে এ সম্পর্ক সহযোগিতার। এই দুই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমেই আমরা শিক্ষা লাভ করি। এভাবে আমরা ছকে উপস্থাপিত পরিবার, প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সমাজ, স্থানীয় গোষ্ঠী, গণমাধ্যম এবং বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসি। এসব পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা পরিবার সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে শিশুর জন্মের আগে থেকেই। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। এ বিষয় আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে জেনেছি। যে ধরনের পরিবারেই আমরা বেড়ে উঠি না কেন, পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমাদের শৈশব কাটে। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক জীবনের ভালো দিক এবং মন্দ দিক সবই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করছে। পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয়। আমরা সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো পরিবার থেকেই অর্জন করি। পরিবারের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো মা-বাবার মধ্যকার সম্পর্ক। মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আবার মা-বাবার মধ্যকার দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ মা-বাবা। আবার মা-বাবা এ দুজনার মধ্যে অধিকতর কাছের হলেন 'মা'। স্বভাবতই সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে মা হতেই। মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন ও ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম। মা শৈশবে শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন, শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণে এর প্রভাব লক্ষ করা যাবে। মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, বর্ণ শিক্ষার কৌশল, ছড়া শিক্ষা অনেক বিষয়ই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফল থেকে নিজ পরিবারে প্রয়োগ করে থাকি।
আমাদের সমাজের কোনো কোনো পরিবারে বাবা উপার্জন করেন। আবার মা-বাবা উভয়েই উপার্জন করেন। সংসার পরিচালনায় তাদের অনেক নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে হয়। মা-বাবার আচরণ ও মূল্যবোধ শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশুর আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব মা-বাবার আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বেরই ফল। এভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, নিকট আত্মীয়-স্বজনের আচরণও শিশুর আচরণে প্রভাব ফেলে। এসব বিষয় শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশী : নিজ পরিবার ব্যতীত যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারাই আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। যারা বাড়ির আশপাশে বসবাস করেন তারা হলো আমাদের প্রতিবেশী। শৈশব থেকেই ব্যক্তি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে বড় হতে থাকে। পরিবারের পরেই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর অবস্থান। শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পাশাপাশি বাড়িগুলোতে সমবয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতিবেশী দল গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী দল থেকে শিশু সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ঐক্য, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শিশুরা অংশগ্রহণ করে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে ওঠে এবং সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সম্প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীর যে কোনো অনুষ্ঠানে পরিবারের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে, যেমন- জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি। আবার কেউ অসুস্থ হলে নিকট আত্মীয়ের চেয়ে প্রতিবেশীই বেশি ভূমিকা পালন করে। প্রতিবেশীই সুখ-দুঃখের প্রথম অংশীদার। গ্রাম ও শহরভেদে প্রতিবেশীর সম্পর্ক ভিন্ন হয়। গ্রামীণ সমাজে প্রতিবেশীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্পর্কে তেমন কৃত্রিমতা থাকে না। শহরে প্রতিবেশীর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ নয়। তবে আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেকটা আপন হয়ে যায়। প্রতিবেশীরাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজ স্বীকৃত আচরণ মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন ভালো প্রতিবেশী।
বিদ্যালয় ও সহপাঠী : পরিবারের পর শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয় ও সহপাঠীর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিশুরা কতকগুলো সামাজিক আদর্শ বিদ্যালয় থেকে শিখে থাকে। এই আদর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে-শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা প্রভৃতি। শিশু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক, সহপাঠী, কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে। এসব উপাদান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুমনে নেতৃত্ব, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঐক্য, দেশপ্রেমবোধ, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতিবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কর্মজগতের জন্য উপযোগী করে তোলে। সমাজের অনুমোদিত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি শিশু বিদ্যালয় থেকেই শেখে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুও শিক্ষার্থীর আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভালো-মন্দের বিচারবোধ প্রভৃতিও শিশু বিদ্যালয় হতে শেখে। সুতরাং শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকের মূল্যবোধ ও আচরণ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে খেলা ও পড়ার সঙ্গী সাথির ভূমিকা রয়েছে। এদের মাধ্যমেই সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়। এই সঙ্গী-সাথির মধ্যে কখনো কখনো সমস্যা বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুরা সমস্যার সমাধান ও স্বন্দ্ব নিরসন কৌশল আয়ত্ত করে। খেলা ও পড়ার সঙ্গী সাথিদের মাধ্যমে শিশু নিজের আচরণের ভালো-মন্দ দিকের প্রশংসা বা সমালোচনা শুনতে পায়। এ ধরনের সমালোচনা থেকে শিশু সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শিক্ষা গ্রহণ করে। সমবয়সী শিশুদের আচার- আচরণ প্রায় একই প্রকৃতির। এদের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও রীতি-নীতি। এ কারণে সমবয়সী বন্ধুদলকে বলে 'অন্তরঙ্গ বন্ধুদল' (Peer Group)। শৈশব ও কৈশোরে এই সঙ্গী সাথি দলের পারস্পরিক আচরণিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। এ দলের প্রভাবে শিশু সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে। আবার সমাজের খারাপ দিকগুলোও গ্রহণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন হতে হবে।স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় সামাজিকীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজের মধ্যে শিশু ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। স্থানীয় সমাজ নির্দিষ্ট অঞ্চল ও স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে। এ সমাজের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, যা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ সমাজের মানবগোষ্ঠী, সামাজিক পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এছাড়া স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, আচরণ ব্যক্তির আচরণে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। এই সমাজের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটে। স্থানীয় গোষ্ঠী গোষ্ঠী বা দল হলো অনেক ব্যক্তির সমষ্টি, যাদের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটা সাংগঠনিক কাঠামোতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত মানবগোষ্ঠীই হলো সামাজিক গোষ্ঠী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, সাংস্কৃতিক ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো সামাজিক গোষ্ঠীর শিশু পরিবার থেকে প্রতিবেশী দলে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পেরিয়ে স্থানীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী বা সংঘ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে। গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। শৈশব হতেই শিশু এসব গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনের সদস্যদের সাথে আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে; যা তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশু হয়ে ওঠে সংস্কৃতিমনা, সাহিত্যপ্রেমী, ক্রীড়ামোদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়- স্বজনকে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে দেখে। শিশু-কিশোরেরা পরিবারে অন্যদের ধর্মীয় আচরণ যেমন- কোরান শরিফ, শ্রীমদভগবদ্গীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক পাঠ করতে দেখে ও শোনে। এসব বিষয় শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ইসলাম ধর্মের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এসব উৎসবের নানা কার্যক্রম শিশুমনে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমিয়ে দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশু-কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিশু মনে গভীর রেখাপাত করে। তাদের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারকে সংযত করে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে। পারস্পরিক কখন সুদৃঢ় করে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে। শিশু-কিশোরদের নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে। সম্প্রীতির শিক্ষা মনের সংকীর্ণতাকে দূরীভূত করে ।
গণমাধ্যম : বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যান-ধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমই গণমাধ্যম। আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি। সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোরেরা এসব পাঠ করে মনের খোরাকপূরণ করে। নিজেকে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। জীবন-জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। বেতার আমাদের শিক্ষা ও আনন্দ দান করে। বেতারের মাধ্যমে আমরা সংবাদ, গান-বাজনা, নাটক— নাটিকা, শিক্ষামূলক আলোচনা, কথিকা, খেলাধুলা, আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হই। সুতরাং বেতার ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যক্তির জীবনে প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সে বিজ্ঞানমনষ্ক হয়ে ওঠে। তার মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়। সামাজিক ও জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। সামাজিক চলচ্চিত্রের অনেক চরিত্র ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সামাজিক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন করে।
বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
গ্রাম ও শহর সমাজ মিলেই বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে। গ্রাম প্রধান দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিকীকরণ ঘটে গ্রামীণ পরিবেশে। গ্রামীণ পরিবেশে শিশুর সামাজিকীকরণ ও শহরে পরিবেশের বেড়ে ওঠা শিশুর সামাজিকীকরণে পার্থক্য রয়েছে।
বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- একক ও যৌথ পরিবার কাঠামো, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সহজ-সরল জীবন যাপন, জীবনযাত্রায় সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের প্রভাব প্রভৃতি। তাছাড়া এ সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় প্রতিবেশীসুলভ আচরণ, ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি গভীর মনোযোগ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রক্ষণশীলতা এ সমাজ কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গ্রামের শিশু-কিশোরেরা এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশেই বড় হতে থাকে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এ সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সাথে। এসব ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।
বাংলাদেশের শহর সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো: একক পরিবার কাঠামো, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি, জটিল সমাজ জীবন, শহরের সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব প্রভৃতি। পরিবেশের এরূপ বিভিন্ন উপাদানের সাথে ব্যক্তির আচরণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসব কিছু ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।
গ্রাম ও শহর সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কতকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। এ উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে- পরিবার, প্রতিবেশী, অন্তরঙ্গগোষ্ঠী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন ও খেলাধুলার সংঘ প্রভৃতি।
গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই শিশু লালিত-পালিত হয় পরিবারে। পরিবারেই শিশুর শৈশব কাটে। স্বভাবতই পারিবারিক জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রভাব শিশুর পরবর্তী জীবনে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। উভয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি পরিবারের যে সাধারণ মনোভাব থাকে তা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শিশুর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। শিশু পরিবারের মধ্যে কথা ও ভাষা শেখে, অনুকরণ করে পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ, অঙ্গীভূত করে পরিবারের = বিভিন্ন উপাদান। পরিবারের মাধ্যমেই সে নীতিবোধ, নাগরিক চেতনা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মত্যাগ, - ভালোবাসা প্রভৃতি শিক্ষা নিয়ে সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে।বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় পরিবেশেই প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশী দল রয়েছে। গ্রামের শিশু-কিশোর বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ কখনে আবদ্ধ থাকে, যা সামাজিকীকরণে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তবে শহরের পরিবেশে প্রতিবেশীর সাথে এরূপ সম্পর্ক দেখা যায় না। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি। সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক শহরের তুলনায় গ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক। এ অন্তরঙ্গ বন্ধু দলের মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল ও নীতিজ্ঞান লাভ করে থাকে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান শিশু-কিশোরেরা অন্তরঙ্গ বন্ধু দলের মধ্য থেকে অর্জন করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠ্যবই এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে শিশু এক সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, স্বভাবতই তখন তার ভূমিকার বিস্তৃতি ঘটে। এ বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তার ভূমিকা ও নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। এ পরিবেশে বিকশিত হয় শিক্ষার্থীর নিজস্ব গুণাগুণ, যোগ্যতা ও ক্ষমতা। শিক্ষার্থীর ওপর বিদ্যালয় পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব শহর ও গ্রামভেদে পার্থক্য সূচিত হয়। বাংলাদেশের শহরে কিন্ডারগার্টেন, আন্তর্জাতিক স্কুল প্রি-ক্যাডেটসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভুল রয়েছে। এসব স্কুলে নানা কারণে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের ঘাটতি দেখা দেয়। খেলার মাঠের স্বল্পতা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসব কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটায় শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। তবে গ্রামের ভুলগুলোতে সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপাদানের ঘাটতি কম। ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যক্তিমাত্রই শিক্ষা অর্জন শেষে কোনো না কোনো পেশা বেছে নেয়। শহরের পেশাগত ক্ষেত্র গ্রাম থেকে আলাদা। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে এই উভয় পরিবেশে পার্থক্য সূচিত হয়। তাছাড়া গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, প্রথা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ কাঠামো। এসব কিছুই ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।
জীববিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত ২,৭০,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং ১৫ লক্ষেরও বেশি প্রাণী-প্রজাতি শনাক্ত করেছেন । এসব প্রজাতির মধ্যে নানা কারণে ভিন্নতা দেখা যায়।
প্রাণীর বিভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal Diversity)
পৃথিবীর সমস্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্নতা দেখা যায় প্রজনন, পরিযায়ী (migration) সহ আরও অনেক বিষয়ে প্রাণিদের বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। প্রত্যেক প্রাণী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ... ন্ডিত হয়ে অন্য প্রাণী থেকে ভিন্ন । পৃথিবীর বিচিত্র পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্যমান অসংখ্য প্রাণীর বিচরণ রয়েছে। প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ প্রাণিবৈচিত্র্য নিচে বর্ণিত তিন প্রকার ।
ক. জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity): একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে জিনগত পার্থক্যের কারণে উক্ত প্রজাতির প্রাণিদের মধ্যে যে বৈচিত্র্যের উদ্ভব ঘটে তাকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে। এ ধরনের বৈচিত্র্য যেহেতু একই প্রজাতির মধ্যে ঘটে তাই একে অন্তঃপ্রজাতিক (intraspecific) বৈচিত্র্যও বলা হয়। যেমন-একজন আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ এবং একজন অস্ট্রেলিয়ান শ্বেতাঙ্গ মানুষ উভয়েই একই প্রজাতি অর্থাৎ Homo sapiens -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াসত্ত্বেও এদের দেহের গঠন, গায়ের রং, চুলের রং ও আকৃতি ইত্যাদিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। জিনগত পার্থক্যের কারণেই এদের মধ্যে বৈচিত্র্যতা দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত জিনগত বৈচিত্র্যের বিষয়টি কেবল গৃহপালিত প্রজাতি বা চিড়িয়াখানায় কিংবা উদ্ভিদ উদ্যানের প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো, বর্তমানে বন্যপ্রজাতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।
খ. প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity) : ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে প্ৰজাতিগত বৈচিত্র্য বলা হয় দুই প্রজাতির প্রাণী কখনোই এক রকম হয় না। একই গণভুক্ত প্রজাতিগুলোর মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা ও আঙ্গিক গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এ ধরনের বৈচিত্র্যকে আন্তঃপ্রজাতিক (interspecific) বৈচিত্র্যও বলা হয়। যেমন-রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Panthera tigris) এবং সিংহ (Panthera leo) একই গণভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। এদের মধ্যে গণপর্যায়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিল থাকলেও প্রজাতি পর্যায়ে ক্রোমোজোম সংখ্যা ও জিনের বিন্যাস ভিন্ন হওয়ার ফলে এদের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বিরাজ করে।
গ. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity): পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর সাথে জীবজগতের মিথস্ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশীয় একক বা বায়োম (biom) সৃষ্টি হয়) যেমন-মরু বায়োম, বনভূমি বায়োম, তৃণভূমি বায়োম ইত্যাদি। প্রতিটি বায়োমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বৈচিত্র্যময় জীব রয়েছে। বিভিন্ন বায়োমে বাসকারী জীবের বৈচিত্র্যকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলে। তুন্দ্রা বায়োমের শ্বেত ভল্লুক এবং বনভূমি বায়োমের ভাল্লুকের মধ্যে এ বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্রের একটি উদাহরণ।
প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Animal Classification):
১.দেহের আকার (Body shape):
ক. অণুবীক্ষণিক প্রাণী (Macro-animal) : এসব প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। যেমন- মাছের ফুলকার প্রোটিস্টার জীবাণু Trichodina anabas... ।
খ. বৃহত্তর প্রাণী (Macro-animal) : এসব প্রাণী আকারে বড় এবং খালি চোখে ভালোভাবে দেখা যায়। যেমন- Cavia porecellus (গিনিপিগ)।
২.সংগঠন ক্রমমাত্রা (Grades of organization):
ক. কোষীয় মাত্রার গঠন (Cellular grade of organization) : যে দেহগঠনে কিছু কোষ সম্মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজ করে সে ধরণের দেহগঠনকে কোষীয় মাত্রার গঠন বলে। এক্ষেত্রে এক ধরণের শ্রম বিভাজন দেখা যায়, যেমন কিছু কোষ জনন কাজে, অন্য কোষগুলো পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী এ ধরনের গঠন সম্বলিত সদস্য।
খ. কোষ টিস্যু মাত্রার গঠন (cell-tissue grade of organization) : সদৃশ কোষগুলো যখন একটি অভিন্ন কাজ সম্পন্নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা স্তরে গোষ্ঠীবদ্ধ বিন্যস্ত হয়ে টিস্যু নির্মাণ করে সে ধরণের গড়নকে কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন বলে।
গ. টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন (Tissue-organ grade of organization) : স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য যখন একাধিক টিস্যু-নির্মিত বিভিন্ন অঙ্গের সমাহার ঘটে তখন সে গঠনকে টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন বলে। Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণীদেহে এ গঠন মাত্রা সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে চক্ষুবিন্দু, প্রোবোসিস, জননাঙ্গ ইত্যাদি টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠনের উদাহরণ।
ঘ. অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন (Organ-sytem grade of organization) : উচ্চতর প্রাণীগোষ্ঠীতে এ ধরনের গঠন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে অঙ্গগুলো একত্রে কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য অঙ্গ-তন্ত্র (organ system) সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে সর্বোচ্চ মাত্রার গঠনে উন্নত করেছে। তন্ত্রগুলো (systems) দেহে শ্বসন, সংবহন, পরিপাক প্রভৃতি মৌলিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পর্বে (Phyla) এ ধরনের গঠন দেখা যায়। এ মাত্রার গঠন সসর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে নিমারটিয়ান (Nemartean) নামক এক সামুদ্রিক প্রাণীগোষ্ঠীতে।
৩.জীবন পদ্ধতি (way of living):
ক. মুক্তজীবী (Free living) : এসব প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না। যেমন- কবুতর (Columba livia)
খ. পরজীবি (Parasite) : এসব প্রাণী খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন- যকৃত কৃমি (Fasciola hepatica)।
৪.ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ (Cleavage and Development): যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননকারী প্রাণীর এককোষী জাইগোট মাইটোসিস কোষ বিভক্তির মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে। ডিমে কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ সম্পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক (holoblastic) কিংবা আংশিক বা মেরোব্লাসটিক (meroblastic) হতে পারে।
বিভাজন তলের উপর ভিত্তি করে ক্লিভেজ নিচে বর্ণিত তিন ধরনের –
অরীয় ক্লিভেজ (Radial cleavage) : এ ধরনের ক্লিভেজে বিভাজন তলগুলো জাইগোটকে সবসময় সুষম ও অরীয়ভাবে ভাগ করে। এর ফলে উৎপন্ন ব্লাস্টোমিয়ারগুলো সুষম আকৃতির ও অরীয়ভাবে সাজানো হয়। উদাহরণ : Arthropoda পর্বের প্রাণীদের ক্লিভেজ।
দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ (Bilateral cleavage) : এ ধরনের ক্লিভেজে দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজ ঘটে কিন্তু তৃতীয় বিভাজন হতে মধ্য রেখা বরাবর অনুপ্রস্থভাবে ক্লিভেজ সম্পন্ন হয়। এর ফলে চারটি করে দুই সারি কোষ সৃষ্টি হওয়ায় দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা দেয়। উদাহরণ : Chordata পর্বের প্রাণীদের ক্লিভেজ।
সর্পিল ক্লিভেজ (Spiral cleavage) : এ ধরনের ক্লিভেজও দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজ ঘটে এবং তৃতীয় বিভাজন হতে চক্রাকার ঘুর্ণনের ফলে অ্যানিমেল মেরুর (animal pole) ব্লাস্টোমিয়ারগুলো, ভেজিটাল মেরু হয়। উদাহরণ : Annelida ও Mullusca পর্বের প্রাণীদের ক্লিভেজ।
৫.ভ্রূণস্তর (Germ layers):
ক. দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়েকোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। স্তরদুটির মাঝে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় মেসোগ্লিয়া (mesoglea)। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা দ্বিস্তরী (যেমন- Hydra)
খ. ত্রিস্তরী বা ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Triploblastic animal) : ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো তিনটি কোষীয় স্তরে বিন্যাস্ত থাকে। তিনটি স্তরের মধ্যে বাইরের স্তরটিকে এক্টোডার্ম (ectoderm), মাঝেরটিকে মেসোডার্ম (mesoderm) এবং ভিতরেরটিকে এন্ডোডার্ম (endoderm) বলে। Platyhelminthes (ফিতাকৃমি- Taenia solium) থেকে শুরু করে Chordata (মানুষ – Homo sapiens) পর্ব পর্যন্ত প্রাণী সকল প্রাণী ত্রিস্তরী।
৬.প্রতিসাম্য (Symmetry): প্রতিসাম্য বলতে প্রাণীদেহের মধ্যরেখীয় তলের দুপাশে সদৃশ বা সমান আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায়।
ক. গোলীয় প্রতিসাম্য (Spherical symmetry) : একটি গোলককে যেভাবে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত যে কোনো তল বরাবর সদৃশ বা সমান অংশে ভাগ করা যায়। যেমন-Vlovox globator. (ফটোসিন্থেটিক প্রোটিস্ট)।এছাড়া Radiolaria (উদাহরণ- Acrosphaera trepanata) এবং Heliozoa (উদাহরণ- Gymnosphaera albida) জাতীয় প্রোটিস্টান জীবে এ ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়।
খ. অরীয় প্রতিসাম্য (Radial symmetry) : কোনো প্রাণীর দেহকে যদি কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর কেটে সদৃশ দুইয়ের বেশি সংখ্যক অর্ধাংশে ভাগ করা যায়। হাইড্রা (Hydra), জেলিফিশ (Aurelia), সী অ্যানিমন (Metridium)।
গ. দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য (Biradial symmetry) : কোনো প্রাণীদেহে যখন কোনো অঙ্গের সংখ্যা একটি কিংবা একজোড়া হওয়ায় অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ বরাবর শুধু দুটি তল পরস্পরের সমকোণে অতিক্রম করতে পারে, ফলে ঐ প্রাণীদেহে ৪টি সদৃশ অংশে বিভক্ত হতে পারে। এ ধরণের প্রতিসাম্য হচ্ছে দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য। Ctenophora (টিনোফোরা) পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ, যেমন- ceoloplana)
ঘ. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর শুধু একবার ডান ও বামপাশে (অর্থাৎ স্যাজিটাল তল) দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়, তখন তাকে দ্বিপার্শীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- প্রজাপতি (Pieris brassicae), ব্যাঙ (Fejervarya asmati), মানুষ (Homo sapiens) প্রভৃতি।
ঙ. অপ্রতিসাম্য (Asymmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে অক্ষ বা দেহতল বরাবর ছেদ করলে একবারও দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্য বলে । উদাহরণ -স্পঞ্জ (Cliona celata), আপেল শামুক (Pila globosa) ইত্যাদি।
৭.খন্ডকায়ন (Metamerism or Segmentation) :
কোনো প্রানীর দেহ যদি লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর একই রকম খন্ডাংশের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত হয়, তখন এ অবস্থাকে খন্ডকায়ন বা মেটারিজম (metamerism) বলে। প্রতিটি খন্ডকে বলা হয় মেটামিয়ার (metamere) বা সোমাইট (somite)।
ক. সমখন্ডকায়নবিশিষ্ট (Homonomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখন্ডকগুলো সদৃশ বা একই ধরনের হয়, সেসব প্রানীকে সমখন্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ- কেঁচোর খন্ডকায়ন।
খ. অসমখন্ডকায়নবিশিষ্ট (Heteronomous metamere) : যেসব প্রাণীদেহ খন্ডগুলো অসম বা ভিন্ন ধরনের হয়, সেসব প্রানীকে অসম খন্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ- পতঙ্গের খন্ডকায়ন।
৮.অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন (Tagmatization): Arthropoda পর্বের প্রাণীদেহ বাহ্যিকভাবে খন্ডায়িত, কিছু খন্ডক একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি করে। প্রতিটি অঞ্চল কে ট্যাগমাটা (tagmata) বলে। এমন অঞ্চলীকরন বলে অঞ্চালয়ন।
৯.প্রান্তিকতা (Polarity): যে প্রান্তে মুখ থাকে তাকে মাথা ও তার বিপরীত প্রান্তকে পায়ু বা লেজপ্রান্ত বলা হয়। এরকমভাবে যেকোনো প্রাণীর দেহের দুই প্রান্তের গঠনের ভিন্নতাই প্রান্তিকতা নামে পরিচিত। সাধারণত প্রাণীদেহের প্রান্তিকতা পাঁচ ধরনের।
ক. সম্মুখ প্রান্ত (Anterior end) : দেহের যে প্রান্তে মাথা থাকে।
খ. পশ্চাৎ প্রান্ত (Posterior end) : মাথার বিপরীত প্রান্ত।
গ. পৃষ্ঠীয় প্রান্ত (Dorsal end) : দেহের উপরের দিকের তল।
ঘ. অঙ্কীয় প্রান্ত (Ventral end) : দেহের নিচের দিকের তল।
ঙ. পার্শ্বীয় প্রান্ত (Lateral end) দেহের দুই পাশে অতল।
১০.তল (Planes): যে অঞ্চল বরাবর প্রাণীদেহকে ডান ও বাম বা অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বা সম্মুখ ও পশ্চাত অঞ্চল বরাবর দু ভাগে ভাগ করা যায়, তাকে তল বলে।
ক. মধ্যরেখীয় তল (Median or Sagittal plane): কেন্দ্রীয়, পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় অক্ষ বরাবর দেহকে পাড়শি ওভাবে সদৃশ ডান ও বাম অর্ধাংশে ভাগ করা যায়
খ. সম্মুখ তল (Frontal plane): লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর দেহকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় এ দুটি অংশে ভাগ করা যায়
গ. অনুপ্রস্থ তল (Transverse plane) : দেহের মধ্যে কোন বরাবর দেহকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অর্ধাংশে ভাগ করা যায়।
শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)
শ্রেণিবিন্যাস একটি সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি অনেক নীতি মেনে শ্রেণিবিন্যাস সম্পন্ন করতে হয়। নিচে প্রধান নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।
১. শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য (Taxonomic character) নির্ধারণ : ... ng>একটি ট্যাক্সন-সদস্যের যে বৈশিষ্ট্য অন্য ট্যাক্স বন্ধগত একই) থেকে তাকে পৃথক করতে পারে বা পৃথক করার সম্ভাবনা দেখাতে পারে সেটি ঐ ট্যাক্সনের শ্রেণিবন্ধগত বৈশিষ্ট্য। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রত্যেক ধাপে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হয়।
২. শনাক্তকরণ (Identification) : শ্রেণিবন্ধগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্যবেক্ষণে থাকা কোনো ট্যাক্সন-সদস্য পরিচিত বা আগে বর্ণিত হয়েছে এমন হতে পারে, কিংবা অপরিচিতও হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, এটি একটি নতুন ট্যাক্সন। তাই সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর সাথে তুলনামূলক বর্ণনার আলোকে নমুনা প্রাণিসমূহকে শনাক্ত করতে হবে।
৩. ক্যাটাগরিকরণ বা ব্যাংকভুক্তি (Categorization or Ranking) : যে সব প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে
শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশে বিভিন্ন বাপ অর্থাৎ ক্যাটাগরি বা র্যাংক-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সব প্রাণিগোষ্ঠীকে ট্যাক্সন (taxon: বহুবচনে taxa) বলে। ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক (taxonomic unit)। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত (র্যাংকভুক্ত) প্রাণীর জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীবর্গকে একেকটি ট্যাক্সন বলে। যেমন-Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, Homo, Homo sapiens একেকটি ট্যাক্সন। বিবর্তনিকভাবে সম্পর্কিত এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি বহনকারী প্রাণিগুলো (ট্যাক্সন)-কে একেকটি শ্রেণিবদ্ধগত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের আবশ্যিক (mandatory) ধাপ (র্যাংক বা ক্যাটাগরি) হচ্ছে ৭টি, যথা:- Kingdom, Phylum, Class, Order, Family. Genus ও Species |
৪. নামকরণ (Nomenclature): কোনো বিশেষ প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নামে শনাক্তকরণের পদ্ধতিকে বলা হয় নামকরণ। ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের পর কোন প্রাণী নতুন প্রমাণিত হলে উক্ত প্রাণীকে ICZN এর নিয়মানুযায়ী নামকরণ করতে হবে। সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus) সর্বপ্রথম নামকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এটি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি (Binomial Nomenclature System) নামে পরিচিত। এ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জীবের বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকে যার প্রথমটি গণ (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি প্রজাতি (species) নাম। গণ নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালার বড় অক্ষরে এবং প্রজাতি নামের আদ্যক্ষর ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। এভাবে দুটি ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ দিয়ে প্রাণীর নামকরণের পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ (binomial nomenclature) বলে। অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্যঅঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা যায়। (সে সব সদস্যকে ঐ নির্দিষ্ট প্রজাতির উপপ্রজাতি (subspecies) হিসেবে গণ্য করা হয়। তখন গণ ও প্রজাতি সমন্বিত দ্বিপদ নামটি উপপ্রজাতিসহ ত্রিপদ (Irinomial) নামে পরিচিত হয়। এভাবে, উপপ্রজাতিসহ কোনো প্রাণীর নামকরণকে ত্রিপদ নামকরণ (trinominal nomenclature) বলে। যেমন: ইউরোপীয়ান চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম Passer domesticus; কিন্তু নীলনদ এলাকার চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম Passer domesticus niloticus পাখি বিজ্ঞানী Schlegel (1844 ) সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এটি ICZN কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি।
কোনো জীবের নামকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং তা কতকগুলো নিয়ম অনুসারে সমাধান করা হয়। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Commission on Zoological Nomenclature (সংক্ষেপে ICZN) প্রণয়ন করে থাকে এবং নিয়মগুলো International Code on Zoological Nomenclature-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। নিামকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ানো হয়েছে]
৫. সংরক্ষণ (Preservation) : শ্রেণিবিন্যাসকৃত নমুনাকে বিস্তারিত তথ্যসহ (সংগ্রহকারীর নাম, সংগ্রহের স্থান, সময়, তারিখ ইত্যাদি) সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে অন্যান্য নমুনা শনাক্তকরণ সহায়ক হয় । এ কারণে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত প্রাণীর নমুনা প্রাকৃতিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিভাগীয় সংরক্ষণশালায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকে । নমুনাটি হতে পারে স্টাফ করা (stuffed) প্রাণী, চামড়া, কিংবা বিভিন্ন অংশ (শিং, লোম, মল ইত্যাদি) বা কংকাল। প্রাণিদেহ শুকনো বা তরলেও সংরক্ষণ করা যায় । ফরমালিন ও অ্যালকোহল হচ্ছে সংরক্ষণের ভালো তরল
মাধ্যম। বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মাত্রার ফরমালিন ও অ্যালকোহল, কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংরক্ষণ মাধ্যম নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব, শ্রেণিবিন্যাসে নমুনা সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অধ্যায়